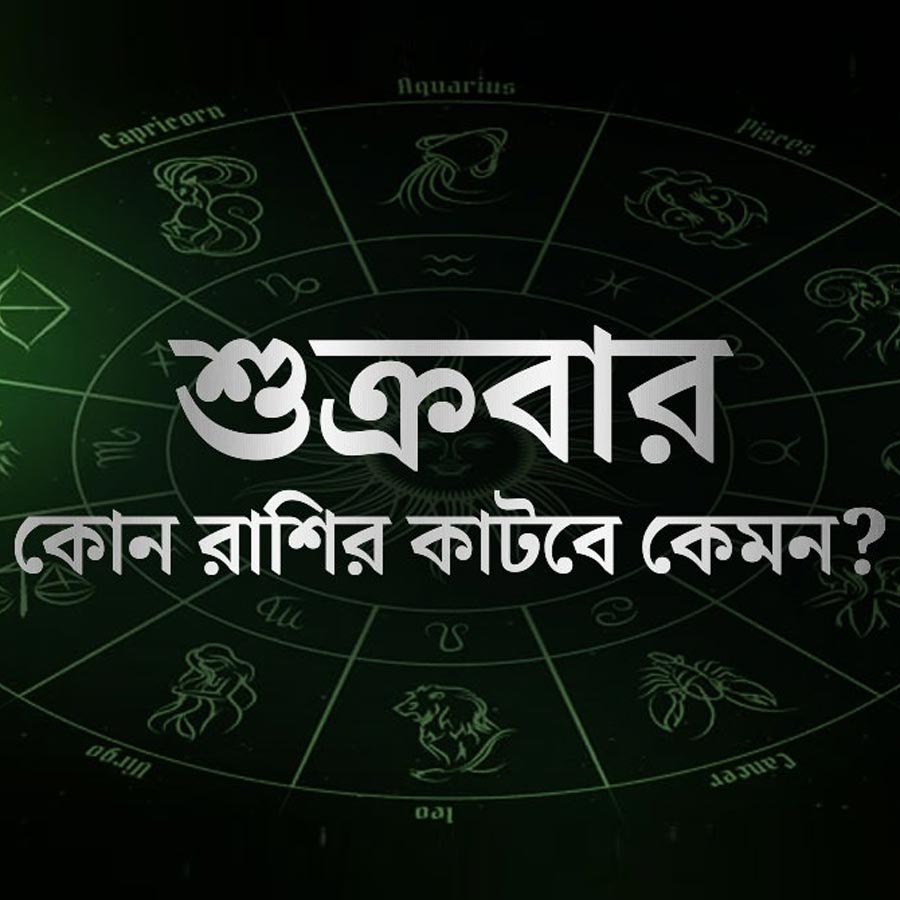পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। এক বন্ধুর। তাকে নেমন্তন্ন করেছিল এক সহকর্মী। বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষায় যথারীতি হাজির। গিয়ে বুঝতে পারে একটা ‘বুঝভুম্বুল’ (উত্তমর্ণ: তপন রায়চৌধুরী) ঘটে গিয়েছে। নেমন্তন্ন করেছে সহকর্মী, কিন্তু মাকে বলতে ভুলে গিয়েছে। মা জননী ফোন করে হোম ডেলিভারি আনিয়ে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেন। নাহ, ঘরের খাবারে সেবা না পেয়ে বন্ধুটির গোঁসা হয়নি। গ্রামের ছেলে সে। রেস্তরাঁর খাবারে বরং স্বাদবদল হয়েছিল।
এক সময়ে কেনা খাবারে অতিথি সৎকার হলে বিস্তর নিন্দে-মন্দ হত। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় বেশ রাগত স্বরেই ‘খাবারের জন্মকথা’ লিখেছিলেন ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় এল এম এস। প্রকাশকাল পৌষ ১৩৩৫ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে। ইংরেজি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ঘরে জামাই-কুটুম্ব বা আত্মীয়স্বজন এলে চটজলদি নানা ব্যঞ্জনের সঙ্গে লুচি বা ভাত তৈরি করে দেওয়া “সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বলিয়া অনেকে দোকানের খাবার, দোকানে ভাজা লুচি ডাল আলুর দম এমনকি ডিম মাংস খাইয়ে আপ্যায়িত করেন,” লিখেছিলেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, বিয়ের ‘পাকা খাওয়ান’তেও দোকানের লুচি-তরকারি প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব দেখেশুনে ডাক্তারবাবুর বিশ্লেষণ, “এ ব্যবস্থা আলস্য ও নীচতা জ্ঞাপক সন্দেহ নাই।”
লেখক রেগে গিয়েছিলেন কেন? সাধারণ ভাবে মনে হয়, নতুনের বরণ ও প্রচলনের জন্য যে সময়-অন্তর লাগে, তা পাননি তিনি। আর একটি কারণ হতে পারে, রীতিভঙ্গ। পাকা দেখার খাওয়ার আগে ‘এমনকি’ শব্দটি লক্ষণীয়। তিনি কি চেয়েছিলেন, এই রীতিতে অন্তত দোকানের খাবার না ঢুকুক? পাকা দেখার খাওয়াতে হবু কনের নিজের হাতে একটা-দুটো পদ ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতিনিধিদের রেঁধে খাওয়ানোর চল ছিল। দোকানের খাবার ঢুকে সেটাও বন্ধ হতে বসায় কি আপত্তি ছিল তাঁর? কিংবা অতিথিসেবায় ঘরের মেয়ে-বৌদের হাতের ছোঁয়া থাকলে, তা পয়সা ফেলে দায় মেটানোর চেয়ে বেশি আন্তরিক হয়— এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি?
আপ্যায়নে দোকানের খাবার পরিবেশন করায় রাজধানী ও শহরতলির কোনও পরিবারই লেখকের নিদারুণ শব্দবাণ থেকে রক্ষা পায়নি। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “আজকাল কলিকাতায় ত বটেই, কলিকাতার উপকণ্ঠেও সহস্র রকম ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথি সৎকার করিলেও, ২।৪টা দোকানের খাবার না দিলে যেন গৃহস্থের সম্ভ্রম বজায় থাকে না এবং অতিথি-অভ্যাগতদের যথেষ্ট খাতিরও করা হয় না— এমন একটা কদর্য ধারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।”
দোকানের খাবারের এ রকম অনুপ্রবেশের আগে আপ্যায়নের রীতিটা কী ছিল? শরণ নেওয়া যাক মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’র। তখন ‘যজ্ঞিবাড়ির রান্না’ গিন্নিরা নিজেরাই করতেন। যিনি যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, তিনি সেটি রাঁধতেন। “তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া সকলে সুখ্যাতি করিতেন।” দোকানের খাবার তো দূরের কথা, তখন পাচক-ব্রাহ্মণের প্রথাও ছিল না। কাঠের উনুনে মাটির হাঁড়ি-খুরিতে রান্না হত। এতে নাকি খাবারের স্বাদও ভাল হত।
স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনতারা হালদার ১৩৯২ বঙ্গাব্দে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র রবিবাসরীয়তে লিখেছিলেন, ‘আমার ছেলেবেলা’। এই লেখাতেও বাড়িতে তৈরি খাবারের কথা রয়েছে। সেটা অবশ্য দুর্গাপুজোর সময়ের মিষ্টি। প্রতি বছর পুজোয় প্রায় এক মণ মিষ্টি তৈরি হত তাঁদের বাড়িতে। গজা, তক্তি, মেচা, মগধের নাড়ু আরও নানা রকম। পিসিমার মেয়েদের বাড়িতে তত্ত্বে যেত সব। তিন-চার দিন আগে থেকে সকলে জীবনতারা মশায়দের বাড়িতে জড়ো হতেন। কার কত মিষ্টি দরকার সেটা জেনে নিয়ে উপকরণ কেনা হত। ময়দা, চিনি, সুজি, ঘি, নারকেল। তিনি লিখছেন, “সে এক এলাহি কাণ্ড! পাড়ার লোকেরা টের পেত হালদারবাড়ি মিষ্টি তৈরি হচ্ছে।” মিষ্টি তৈরির সময়ে মায়ের পাশে বসে থাকতেন বালক জীবনতারা। শিখতেন ‘উনুনে কখন ঘি তৈরি হবে, কিরকম আঁচে ভাজতে হবে’ ইত্যাদি। ১৯০৫ সালে জীবনতারার বয়স ছিল বারো বছর। আর মহেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। ‘যজ্ঞির রান্না’ তাঁর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা। বারো থেকে পনেরো বছর ধরা যাক। অর্থাৎ ১৮৮০ সালের কোঠার ঘটনা। বিবেকানন্দের মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ থেকে জীবনতারা পর্যন্ত বাড়ির খাবারের মহিমা বজায় ছিল। দোকানের খাবার তখনও তেমন কল্কে পায়নি। না পাওয়ার একটা কারণ সম্ভবত খাবারের দোকানের অপ্রতুলতা। মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁদের এলাকায় “তখন এত খাবারের দোকান ছিল না। সিমলা বাজারে একখানি দোকান ও বলরাম দে স্ট্রিটে একখানি।”
মহেন্দ্রনাথ দত্ত ভোজবাড়িতে দোকানের খাবারের রমরমা দেখেননি ছেলেবেলায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়সে পাচক-ব্রাহ্মণদের আগমন দেখে গিয়েছিলেন। যজ্ঞিবাড়ির রান্নার দায়িত্ব পাচক-ব্রাহ্মণদের হাতে চলে যাওয়ার কারণটি বেশ মজার। মহেন্দ্রনাথ সে জন্য দায়ী করেছেন ‘ভোজপণ্ডে’দের। এঁরা ভোজন পণ্ড করতেন। তাই এমন নাম। এরা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজবাড়িতে যেত, কিন্তু সেখানে গিয়ে বংশের কোনও “কুৎসা রটনা করিয়া সমস্ত পণ্ড করিত।” মুরুব্বি না খেয়ে গেলে অন্যরা খেতে পারতেন না। ভোজপণ্ডেদের ঠেকাতে রান্না করতে আনা হতে লাগল পাচক-ব্রাহ্মণদের। এঁরা ‘রন্ধন তেমন করিতে না পারিলেও ভোজপণ্ডেকে গালাগালি দিতে বিশেষ পটু’ ছিলেন। ভোজপণ্ডেরা অপমানিত হতে লাগলেন। তাঁদের প্রতাপ কমে গেল। পাচক-ব্রাহ্মণের চল নিয়ে মহেন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল। এঁদের কারণেই “গিন্নিদের হাতের সোনামুগের ডাল, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট উঠিয়া গেল। কলিকাতায় গিন্নিদের ভোজ-রন্ধন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার এই একটি কারণ।” মহেন্দ্রনাথের আক্ষেপ ‘ভারতবর্ষ’-এর রমেশচন্দ্রের মতোই। তবে তাতে ক্রোধের সুর নেই। মেনে নেওয়াই আছে।
গ্রামাঞ্চলের ছবিটা কেমন ছিল? ১৯০৪ সাল নাগাদ প্রকাশিত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘পল্লীচিত্র’ বইয়ে ষষ্ঠীর রাতে দুর্গাপুজো বাড়ির রান্নার উল্লেখ রয়েছে। রান্নাবাড়ির কোনও দিকে ভিয়েন বসেছে। কোনও দিকে লুচি ভাজার জন্য বড় বড় কাঠের কোটা, পিতলের পরাত, কড়াই, চাক্তা, বেলুন, ঝাঁঝরা বার করা হয়েছে। বারান্দায় বসে কুটনো কুটছেন পাড়ার ‘অনাথা বর্ষীয়সী বিধবারা’। পাচক-ব্রাহ্মণের উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই গৃহিণীদেরও। আন্দাজ করা যায়, এমন বিপুল আয়োজনের কান্ডারি পাচকেরাই। আবার সপ্তমীতে দেওয়ানজির বাড়িতে আহারাদির বিপুল আয়োজন। শুধু মিষ্টান্নের আয়োজনই বিশ রকম। এ মেঠাই রান্নাবাড়ির ভিয়েনেরই বোধহয়।
ঠিক কোন সময় থেকে ভোজবাড়িতে দোকানের খাবার ঢুকল, তা সমাজ-গবেষকেরা বলতে পারবেন। খাবারের দোকান বৃদ্ধি এবং রকমারি হওয়ার পরেই হয়তো। খাবারের দোকান বেশি হওয়ায় জলখাবারের পরিবর্তনও হয়েছিল নিশ্চয়ই। বালক মহেন্দ্র দত্ত সকালে খেতেন বাসি রুটি আর কুমড়োর ছক্কা। রুটি না থাকলে মুড়ি-মুড়কি। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, এক পয়সার মুড়ি একটা ছোট ছেলে খেতে পারত না। তবে দোকানে পাওয়া যেত জিবেগজা, ছাতুর গুটকে গজা, কুচো গজা, চৌকো গজা, গুটকে কচুরি ও জিলিপি।
এটা শহর কলকাতার চিত্র। গ্রামাঞ্চলেও জলখাবারের তেমন বৈচিত্র ছিল না। দীনেন্দ্রকুমারের ‘পল্লীচিত্র’-তে পুজোর আগে রাত জেগে ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটার কথা আছে। ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ঢেঁকিতে পাড় দিতে নেই। এ দিকে দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত সব বাড়িতেই চিঁড়ে লাগবে। তাই রাত জেগে কাজ। ঢাকি ও সঙ্গী বাজনদারদের কলাপাতায় চিঁড়ে আর দই খেতে দেওয়ার কথা বলছে ‘পল্লীচিত্র’। আবার ষষ্ঠীর দিন সকালে ঢাকি-ঢুলির আওয়াজে যে ছোট ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তার এক হাতে ছোট পাথির আধ পাথি মুড়ি আর এক হাতে আধখাওয়া শসা। ‘পাথি’ মানে ছোট চুপড়ি। লক্ষ্মীপুজোর দিনে ভুজো আর নাড়ু বিতরণ করা হত, বলছে ‘পল্লীচিত্র’। ভুজো মানে মুড়ি-মুড়কির জলপান। দশমীর রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়া সারার রীতির উল্লেখ করেছেন দীনেন্দ্রকুমার। সেখানে দরিদ্র গৃহিণীও একটা নাড়ু বা জিলিপি দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করছেন। এগুলো বাড়িতে তৈরিই সম্ভবত। তখন পাড়া-গাঁয়ে মিষ্টির দোকান কোথায়? থাকলেও তা দূরে। আর সারা গ্রামের বিজয়ার মিষ্টির ভারবাহী ছিল না সেই সব দোকান।
তার পর কখন যে দোকানের খাবার সর্বত্রগামী হয়ে উঠল! হালের কেটারিংয়ে খাওয়ানো বা প্যাকেটের ব্যবস্থা দেখলে রমেশচন্দ্র কী করতেন? নিশ্চয়ই সমাজমাধ্যমে ‘ফিলিং অ্যাংরি’ সাঁটানো লম্বা পোস্ট দিতেন। আর বিজয়া দশমীতে যদি দেখতেন দোকানের মিষ্টি! বিজয়া দশমীর জন্য বাড়িতে নাড়ু বা নারকেলের ছাপা সন্দেশ এবং কুচো নিমকি তৈরির চল নব্বই দশক পর্যন্ত ছিল। জীবনতারা হালদারের মায়ের হাতে তৈরি বিপুল মিষ্টান্নের মতো না হলেও ছিল। তার পর হারিয়ে গেল। এর বহুবিধ কারণ। প্রথমত, পরের প্রজন্মের এ সব ঘরোয়া মিষ্টি তৈরি শিখতে অনীহা। সময়াভাব আরও একটা কারণ। নাড়ু, নিমকি তৈরি ঝক্কিও। ফলে নব্বই দশকের গৃহিণীরা বৃদ্ধা হওয়ার পরে আর ধারা বজায় রাখতে পারলেন না। তা ছাড়া নারকেলের অভাবও ঘটে গেল। গ্রামাঞ্চলে এখন ডাবের ব্যবসা বহু জনের জীবিকা। ডাব বিক্রি বাড়ায় নারকেলের জোগান কম। জোগান কম বলে দামও আকাশছোঁয়া। ফলে বাড়িতে দোকানের মিষ্টি। এখনকার মিষ্টিমুখের বিজ্ঞাপনের দৌলতে চকলেটের জমানা। বিজয়ার প্রণাম সারতে আসা ছোটরা নাড়ুর থেকে চকলেট পেলে বেশি খুশি হবে। না-ও হতে পারে। তবে নাড়ুর থেকে অন্তত দোকানের মিষ্টি যে বেশি ‘প্রেফার’ করে, এটা নিশ্চিত।
এই যে ধারা বিলোপ বা ঐতিহ্যের সঙ্কট, এ নিয়ে আবার নতুন করে লেখা হতে পারে ‘খাবারের জন্মকথা’। তাতে মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতো ঐতিহ্য হারানোর দুঃখ থাকতে পারে। বা রমেশচন্দ্রের মতো রাগ। আবার সময়ের সঙ্গে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে পারে। বা নতুনের প্রতি অনুরাগ। ‘ফুড ডেলিভারি’ তো এখন অনুরাগের ছোঁয়াতেই রয়েছে। অতি সম্প্রতি কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে লিখেছেন পুজোর গল্প, ‘ভোগের বালাই’। গল্পে মজার ছলে লিখেছেন অনলাইনে ভোগের খিচুড়ি আনিয়ে নেওয়ার কথা। আজ যা মজা, কখনও তা-ই হয়তো হয়ে উঠবে পুজোর অঙ্গ। খুব সম্প্রতি শহরাঞ্চলে জন্মাষ্টমীর দিনও দেখা গেছে, কোনও স্থানীয় বৌ রাস্তায় বাড়ির পুজোর গ্যাস স্টোভ, বাসনপত্র নামিয়ে গরম গরম ভাজছেন তালের বড়া, মালপোয়া। সেগুলো ঠোঙায় ভরে বিক্রি করছেন বৌটির স্বামী। উড়ে যাচ্ছে হু-হু করে।
সময় নতুন কিছু আনবেই। তার আদরও হবে। পুরনো প্রথা পিছনে চলে যাবে। মহেন্দ্রনাথ নিজেও দেখে গিয়েছেন এমন চিত্র। তাঁর বয়সকালে ‘অসংখ্য খাবারের দোকান এবং রকমও অসংখ্য’। এর ফল কী হল? তিনি ছোটবেলায় দোকানে খাওয়া জিবেগজা, গুটকে কচুরির কথা লিখেছিলেন। “এখন সেসব জিনিস নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া লোকে অবজ্ঞা করে,” বড়বেলায় লিখে গিয়েছেন তিনি। সময় আমাদের শিখিয়েছে, সমকালীন খাবারদাবার খেয়ে নিতে হয় প্রাণ ভরে, না হলে তা কালের নিয়মে হারিয়ে গেলে আফসোস করতে হয়।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)