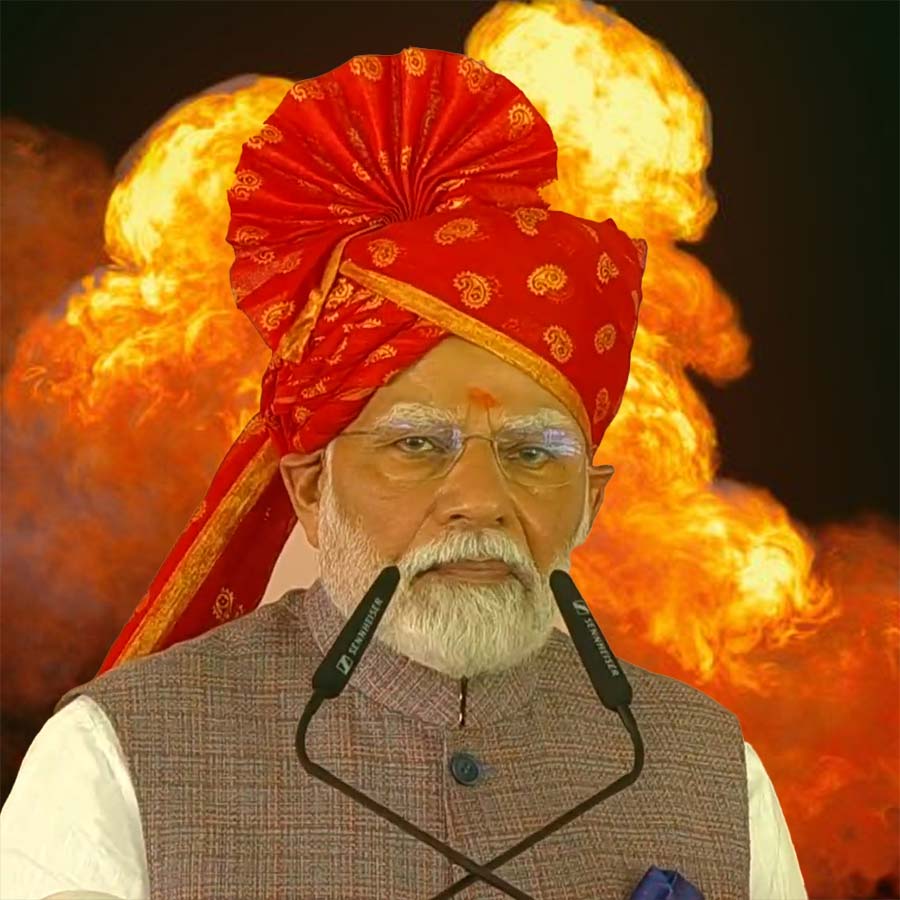কী ছিল স্বামী ঘুটঘুটানন্দের যোগসর্পের হাঁড়িতে? দুটো জায়গায় দু’রকম তথ্য। একটা জায়গা পুস্তক। অন্যটি সেলুলয়েড। চিন্ময় রায় আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চারমূর্তি’ সিনেমায় যোগসর্পের হাঁড়িতে ছিল রসগোল্লা। মুখে দিয়েই টেনিদারূপী চিন্ময়ের স্বাদ-সম্ভাষণ, ‘নবীন ময়রা’। পুস্তকের ‘চারমূর্তি’তে যোগসর্পের হাঁড়িতে কিন্তু রসগোল্লার সঙ্গে লেডিকেনিও ছিল। এই সহাবস্থান আশ্চর্যজনক। রসিকদের কাছে রসভঙ্গের শামিল। দুটো মিষ্টি যে দু’রকম! একটা ভাপা, আর একটা ভাজা। অভিজ্ঞ দোকানদারেরা এমনটা করবেন কি! লেখক হয়তো হাঁড়ির হাল করতে চাননি। তাই হাঁড়িতে ‘আইটেম’ বাড়িয়েছেন। তা ছাড়া দুটো হাঁড়ি করলে পরিস্থিতি তৈরিতেও বাধা আসত। মোট কথা, যোগসর্পের হাঁড়িতে রসগোল্লা ছিল।
আর একটু পিছনে ফেরা যাক। ১৯২৫ সালের ৫ নভেম্বরের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’। ওই দিন ‘ঔদরিকের সাজা’ শীর্ষক খুদে একটা খবর বেরিয়েছিল। গিরিজা সিংহ নামে এক জনের সাজার খবর। গিরিজা একটি মিষ্টির দোকানে ‘অনধিকার প্রবেশ’ করে ইচ্ছেমতো রসগোল্লা খেয়ে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর এক মাসের কারাবাসের সাজা হয়। অবশ্য কনস্টেবল প্রহারের অপরাধও ছিল। সেটা রসগোল্লা খাওয়ায় বাধা দেওয়ার জন্যও হতে পারে। খবরের লক্ষণীয় ঘটনা সাজা নয়, চোরের রসগোল্লাপ্রীতি। ওই দোকানে নিশ্চয়ই আরও কিছু মিষ্টান্ন ছিল। একশো বছর আগে মিষ্টির দোকানের শো-কেস এত সমৃদ্ধ থাকত না। কিন্তু বাংলায় শুধু রসগোল্লার দোকানও নিশ্চয়ই ছিল না!
রসগোল্লা-মুগ্ধতার আর এক ঘটনা। ঘটনার চরিত্র বিশ্বজনবিদিত এবং শ্রদ্ধেয়। তাঁর মুগ্ধতার বিবরণটি এ রকম, রসগোল্লা মুখে করে ‘একেবারে স্পন্দহীন! চক্ষু নিমেষ শূন্য!... কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র — (রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে)— চোখ চাহিয়া বলিতেছেন, ‘আমি-ভাল-আছি’। এই নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন। তখনও তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হননি। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-এ পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের রসগোল্লা-প্রীতি।
রসগোল্লার সর্বব্যাপ্ত মুগ্ধতাই বোধহয় বাঙালিকে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। জয় এসেছিল ওড়িশার বিরুদ্ধে। জয়ের স্মারক একটি দিবস। রসগোল্লা দিবস। ১৪ নভেম্বর। দিবস পালন করে সমাজমাধ্যমে রসগোল্লার স্তুতি তো হালের বিষয়। একশো বছরের বেশি আগে মুগ্ধ বাঙালি যে রসগোল্লার স্তব লিখে ফেলেছিল! সে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ইংরেজির ১৯১৭ সাল। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ‘রসগোল্লা (স্তব)’ লিখেছিলেন ‘শ্রীশশধর বর্ম্মণ’। স্তবে রসগোল্লাকে কৃষ্ণরূপে কল্পনা করে জয়গান করা হয়েছে। জন্ম, লীলা, কর্ম পেরিয়ে সেই স্তব যেন রসগোল্লার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন!
স্তবারম্ভ এমন ভাবে, ‘(জয়) হৃদয় কি নর্ত্তন/ বাঁটা-ছানা-মর্দ্দন/ বর্ত্তুলাকারে বিহরণ জী’। অর্থাৎ, তিনি আসছেন। ছানা বেটে, দলাইমলাই করে মেখে তৈরি হচ্ছে তাঁর গোলাকার অবয়ব। তাঁর আসার খুশিতে হৃদয় নেচে উঠছে ভক্তের। গোকুলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণ। আর রসগোলক বেড়ে উঠছে বারকোশে। কবি লিখছেন, ‘বারকোষ-মোহন, তদুপরি আসন/ শৈশব-বাল্য বয়সে জী’। বাল্যের পরে লীলাখণ্ড। কৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন বৃন্দাবনচন্দ্র রাধামোহন। কড়াইটাই যেন রসগোল্লার বৃন্দাবন। আর সেই কটাহ-বৃন্দাবনে চিনির রস হয়ে উঠছে ‘রাধা-প্রেম-রস’। কবি লিখলেন, ‘রাধা-প্রেম-রসে,/ বিহরতি হরষে/ কটাহ-বৃন্দাবনে জী’।
প্রেম উত্তুঙ্গ পর্যায়ে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার ‘কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে’ দশা। প্রেমের প্রগাঢ়তা বোঝাতে কবি শশধর লিখলেন, ‘টগবগ উত্তাপ/ বিরিঞ্চি বৈভব/ উড়কি বৃন্দাদূতি জী’। প্রেম এক বিরল বৈভব। তা নিঃসংশয়। কিন্তু উড়কি-তে এসে আটকাতে হয়। ‘চলন্তিকা’, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, উড়কি এক রকমের ধান বা খই। এটা জানা তথ্য। ছোটবেলায় ছড়ায় পড়া, ‘উড়কি ধানের মুড়কি দেব...’। এখানে তো উড়কি এই অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। রাধার সখী বৃন্দার উল্লেখ রয়েছে যে! ‘সরল বাঙ্গালা অভিধান’-এ উড়কির আর একটি অর্থ মিলল। নারকেল মালা অথবা তালের বীজ কিংবা কাঠের তৈরি একপ্রকার হাতা বা পলাকে উড়কি বলে। এ বার অর্থ পরিষ্কার। রসগোল্লারূপী কৃষ্ণকে কটাহ-বৃন্দাবনে রসরূপী রাধার সঙ্গে মিলনে সাহায্য করছে উড়কি। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ রাধিকার দূতী ছিল বড়াই বুড়ি। কড়াই-বৃন্দাবনে উড়কি হয়েছে বৃন্দাদূতী। ফোটানোর সময়ে মোদকেরা এখন লোহার ছানচা বা ডাবু দিয়ে গোল্লাগুলোকে রসে তোলেন-ফেলেন। আগে সেটা হত উড়কি দিয়ে। মিষ্টি ব্যবসায়ী বন্ধু রবিন জানাল, এখন রসগোল্লা তৈরিতে উড়কি ব্যবহার না হলেও ছানা ব্যবসায়ীদের অনেকে এটা ব্যবহার করেন।
কৃষ্ণ বড় হলেন। গোপীমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রের এ বার ঐশ্বরিক কাজে বেরিয়ে পড়ার পালা। তিনি হয়ে উঠবেন ভুবনমোহন। রসগোল্লাও কটাহ-বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে এল ‘কি সুঠাম কলেবর’ নিয়ে। তা দেখে ‘বিমোহিত চরাচর’। কৃষ্ণ সুদর্শন, কর্মবীর, যোদ্ধা, পরামর্শদাতা, বন্ধু। সকলকেই মোহিত করার ক্ষমতা রাখেন তিনি। শশধর কবির কল্পনায় রসগোল্লাও তাই। রসের গোলকটি— ‘আস্তিক-মোহন/ নাস্তিক তোষণ/ দর্শন-বিজ্ঞান-বিজয়ী জী/ (জয়) তুমি হে উপাস্য,/ তুমি যে নমস্য/ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জী’।
কৃষ্ণের আগমনই ছিল একটা ঘটনা। এখনকার ভাষায় ‘অ্যাপিয়ারেন্স’। অর্জুনের রথে তাঁর সারথি হওয়াই কাঁপিয়ে দিয়েছিল কৌরবকুলকে। রসগোল্লার ‘অ্যাপিয়ারেন্স’ অবশ্য ছিল জনমোহিনী। শশধর লিখছেন, ‘কর্মবাড়ীর তুমি মোহন জী/ তোমার প্রবেশে/ ভাসে সবে হরষে,/ দীয়তাং দীয়তাং রবে জী।/... বরযাত্রের হর্ষ-বিধায়ক জী’। এ দৃশ্য উপলব্ধির জন্য আজি হইতে শতবর্ষ পূর্বে পৌঁছতে হবে না। বড়দের কাছে সত্তর-আশি দশকের অনুষ্ঠানবাড়ির গল্প শুনলেই হবে। লোকে পাতে ফুল ফুটিয়ে রসগোল্লা খাচ্ছে। কেউ কেউ রসগোল্লা পরিবেশন করা লোকটিকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। পরিবেশনকারী সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ‘আপনি খান, আমি আছি।’ এই দৃশ্যেরই যেন বর্ণনা দিয়েছেন শশধর কবি। লিখেছেন, ‘পাতো পরি নাচো যবে,/ নয়নকি লাজ না রহে জী’।
আবার কোনও বাড়িতে নিমন্ত্রিতেরা পাতে কলাপাতা পড়ার পরে ফিসফিস করে আলোচনা করতেন, ‘রসগোল্লার ঢালাও ব্যবস্থা নাকি রেশনিং?’ গ্রামাঞ্চলে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকেও কিন্তু অনেক নেমন্তন্নবাড়িতেই রসগোল্লার ঢালাও ব্যবস্থা ছিল না। যদি ঢালাও হয়, তা হলে মাছের মাথা দিয়ে ডাল আর ছ্যাঁচড়ায় মন কম দিয়ে রসগোল্লা টানবেন। মিষ্টি মেপে খাওয়া এই ‘কলিকালে’ অনুষ্ঠান বাড়িতে রসগোল্লার সেই ‘ক্রেজ়’ বোঝা সম্ভব নয়।
আর বরযাত্রার হরষ? তা বেশ টের পেতেন কন্যার পিতাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ’ গল্পটি পড়লে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও বরযাত্রীদের তোয়াজ করতেই হত। আগে বরযাত্রী খাবে, তার পরে গ্রামের আমন্ত্রিতরা। কনেবাড়ির ‘রমণী’য়তা দেখতে ব্যস্ত হয়ে কোনও বরযাত্রী হয়তো খেতে বসতে ভুলে গিয়েছেন। তাঁকে বসানোর জন্য খেতে বসা গ্রামের লোককে তুলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটত। গ্রামের লোকের জন্য রসগোল্লা ‘রেশনিং’ হলেও বরযাত্রীদের ঢালাও ব্যবস্থা রাখতে হত। এই প্রথা ঘুচেছে। তবুও এখন মাঝে মাঝে খবর হয়, পাতে মাটন না পড়ায় বরযাত্রীদের তাণ্ডব।
শশধরের স্তব পাঠে দু’টো জায়গায় সংশয় জাগে। এক জায়গায় লেখা, ‘তব রূপ-কোকনদ,/ সুভঙ্গিম মনোমদ,/ রসে ডগমগ নিরেট জী’। আর এক জায়গায় স্তবকর্তা লিখেছেন, ‘তব হিয়া মাঝে,/ ক্ষীর বুটী রাজে,/ অর্পিত অতি যতনে জী’। সংশয় রসগোল্লার গড়ন নিয়ে। নিরেট হলে সেই রসগোল্লার হৃদমাঝারে ক্ষীরের বুটি ধরা থাকে কি? না বোধহয়। তা হলে কোন রসগোল্লার স্তব করেছেন কবি? এ সংশয় অবশ্য দূর করা যায়। পদাবলির কৃষ্ণ দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমন পাঁচ প্রকার রসে প্লুত হতে পারে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। রসগোল্লার রূপও কম নয়। নিরেট, গুটিওয়ালা, স্পঞ্জ। কেউ কেউ স্পঞ্জ পছন্দ করেন না। বর্ধমান, হুগলি, নদিয়ার নরম তুলতুলে রসগোল্লার প্রবল ফ্যান। আবার শীতের নলেন গুড়ের মনোলোভাকেও ধরতে হবে। হালের বেকড আর চকলেট রসগোল্লাও লোকের পছন্দ হচ্ছে। এমন কি ঝাল রসগোল্লাও এসেছে বাজারে। এ সবই কারও না কারও ‘উপাস্য-নমস্য’। তবে এখন রসগোল্লার বুকের মাঝে পরম যতনে ক্ষীরের বুটি পোরা মোদকের সংখ্যা কম। গুটির জায়গায় দানার চল হয়েছে বহু দিন। নকুলদানা। যে দানা এখন ভারী রাজনৈতিক। কেউ কেউ লোকাভাবে এবং খাটুনি কমাতে রসগোল্লায় নকুলদানাও দিতে চান না।
রসগোল্লার স্তব পাঠে কোনও কোনও জায়গায় আলী সাহেব স্মরণে আসতে পারেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ও তাঁর ‘রসগোল্লা’ রসরচনা। মনে হতে পারে, স্তবটি ক্লাসের বাংলা বইয়ের কবিতা, আর আলী সাহেবের সরেস রচনাটি ছাত্রবন্ধু। যাতে অর্থ ব্যাখ্যা সব পাওয়া যায়। ‘রসগোল্লা’ বহুপঠিত। তবুও স্মরণমাল্য গাঁথতে চুম্বকে কাহিনিটা বলে নেওয়া যেতে পারে। আলী সাহেবের রচনার ঝান্ডুদা বিশ্বনাগরিক। কাজের সূত্রে এত দেশে ঘোরেন যে, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বোঝা যায় না, তিনি বিদেশ থেকে আসছেন না যাচ্ছেন। গল্পের প্রেক্ষাপট ইটালির ভেনিস বন্দর। ঝান্ডুদা জাহাজ থেকে নেমেছেন। কিন্তু আটকে গিয়েছেন চুঙ্গিঘর তথা বন্দরের কাস্টমস অফিসে। ঝান্ডুদার সঙ্গে ছিল টিনের কৌটোবন্দি রসগোল্লা। নিয়ে যাচ্ছিলেন লন্ডনে, তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের জন্য। ভেনিস বন্দরের এক ছোকরা অফিসার কিছুতেই টিনের রসগোল্লা ছাড়বেন না। টিন খুলিয়ে দেখাতে হবে তাঁকে। কৌটো খুললে রসগোল্লা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বাধ্য হলেন ঝান্ডুদা। টিন খুলতে হওয়ায় গেলেন খেপে। কাউন্টারে চড়াও হলেন। ছোকরাকে খাইয়েই ছাড়বেন। তার আগে চুঙ্গিঘরের লাইনে দাঁড়ানো সকলকে রসগোল্লা বিলিয়েছেন। তাঁরা বিদেশি। তা সত্ত্বেও রসগোল্লার আস্বাদে রসবোধে ঘাটতি হয়নি তাঁদের। হট্টগোলে চুঙ্গিঘরের বড়কর্তা এসে উপস্থিত। তাঁকেও খাওয়ানো হল রসগোল্লা। খেয়ে ছোকরা অফিসারকে বড়কর্তার ভর্ৎসনা, ‘তুমিও একটা গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?’
স্তবের দু’টি শ্লোক, ‘তুমি সার অগমের’ অথবা ‘তব মোহমন্ত্রে/ বদনকি যন্ত্রে/ (কি) অপূর্ব সঙ্গীত উত্থিত জী’। অগম শব্দটির তিনটি অর্থ মিলছে— গতিহীন, দুর্বোধ এবং যেখানে কিছুই নির্ণয় হয় না। তিনটি অর্থই ঝান্ডুদার চুঙ্গিঘরের বখেড়ায় প্রয়োগ করা যায়। ঝান্ডুদা যাবেন লন্ডন। ছোকরা অফিসারের বেয়াড়াপনায় তাঁর গতি রুদ্ধ হয়েছিল। দুর্বোধ ছিল ছোকরা অফিসারটি। রসগোল্লার কৌটোটি ঝান্ডুদা লন্ডনে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। সেখান থেকে তিনি ছাড়িয়ে নেবেন। কৌটোয় মাদক পাচার হচ্ছে, এমনটা যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাতেও ছোকরা অফিসারের দায় থাকত না। কিন্তু তিনি কৌটো খুলিয়েই ছাড়বেন। এমন অনমনীয়তায় কিছুই নির্ণয় হচ্ছিল না। মুশকিল আসান হল রসগোল্লা। চুঙ্গিঘরের বড়কর্তা মুগ্ধ হয়েছিলেন। লাইনে দাঁড়ানো নানা দেশের যাত্রী রসগোল্লার স্বাদ পেতে তাঁদের ‘বদনকি যন্ত্রে’ রসগোল্লার নামে জয়ধ্বনি উঠেছিল। আসলে মুগ্ধতার সঙ্গীত। বাঙালিও তো এই রসেই মুগ্ধ। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, ছোকরা অফিসার তো রসে সিক্ত হননি? সেই জন্যই তো তাঁকে ‘গাড়ল’ গালাগাল শুনতে হয়েছিল। কৃষ্ণের কথা না শুনে তো কৌরবকুল ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল।
শশধর লিখিত এই পঙ্ক্তিগুলোর অর্থ কী? তিনি লিখেছেন, ‘তুমি বিনা প্রবাসে/ কেবা আর যাইতে সক্ষম জী’। বাঙালি রসগোল্লা ছাড়া থাকতে পারে না। তাই পাশের রাজ্যে গেলেও রসগোল্লার হাঁড়ি দুলিয়ে ট্রেনে ওঠে। মানে তখন উঠত। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের মতো। আবার এটাও মনে হয়, প্রবাসে অনাবাসী বাঙালির আক্ষেপ দূর করতে আধুনিকমনস্ক মিষ্টি ব্যবসায়ীরা রসগোল্লাকে টিনজাত করেছিলেন। সেই টিনের রসগোল্লাই লন্ডনে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঝান্ডুদা।
রসগোল্লার আবির্ভাব-সাল নিয়ে ‘পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন’। প্রণব রায়ের ‘বাংলার খাবার’ অনুযায়ী, তিনটি সাল মিলছে। ১৮৬৮ সালে বেনিয়াটোলার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের দিনু ময়রার পূর্বপুরুষ ব্রজ ময়রা হাই কোর্টের কাছাকাছি দোকানে নাকি প্রথম রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিলেন। অন্য মত, নদিয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের হারাধন ময়রা ১৮৪৬-৪৭ সালে প্রথম রসগোল্লা তৈরি করেন। বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লা আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। ব্রজ ময়রা আর হারাধন ময়রার আবিষ্কারকে ধরলে রসগোল্লার বয়স ১৫৬-১৫৮ বছর। শশধর বর্মণ স্তবটি লিখেছেন ১৯১৭ সালে। অর্থাৎ আবির্ভূত হওয়ার অর্ধশতকের মধ্যে রসগোল্লা বাঙালির মন-প্রাণ অধিকার করে নিয়েছিল। পিছনে ফেলে দিয়েছিল বহু মিষ্টিকে।
চার দশক পরেও রসগোল্লার সাম্রাজ্য এতটুকু টলেনি। বরং বেড়েছে। নিত্যনতুন রূপে তা বাঙালিকে মুগ্ধ করেছে এবং এখনও মুগ্ধ করে চলেছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘রসগোল্লা’ রসরচনাটির টিনের রসগোল্লা এরই উদাহরণ। রচনাটি ‘ধূপছায়া’ গ্রন্থের অন্তর্গত। ‘ধূপছায়া’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।
আলী সাহেব নিজেও রসগোল্লাকে দু’পঙ্ক্তির কাব্যাঞ্জলি দিয়েছিলেন লেখার শেষে। ‘রসগোল্লা’ রচনায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য, ‘রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে হায়!/ ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!’ এ যেন শশধর বর্মণ বর্ণিত রসগোল্লার গুণপনায় ‘বিমোহিত চরাচর’ পঙ্ক্তির ভাষ্য। স্তব-রচয়িতা শশধর মনে হয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। রসগোল্লা সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘অনাদি অক্ষয় অচ্যুত জী’!
কী অপূর্ব সত্য এই স্বাদ-দর্শন!
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)