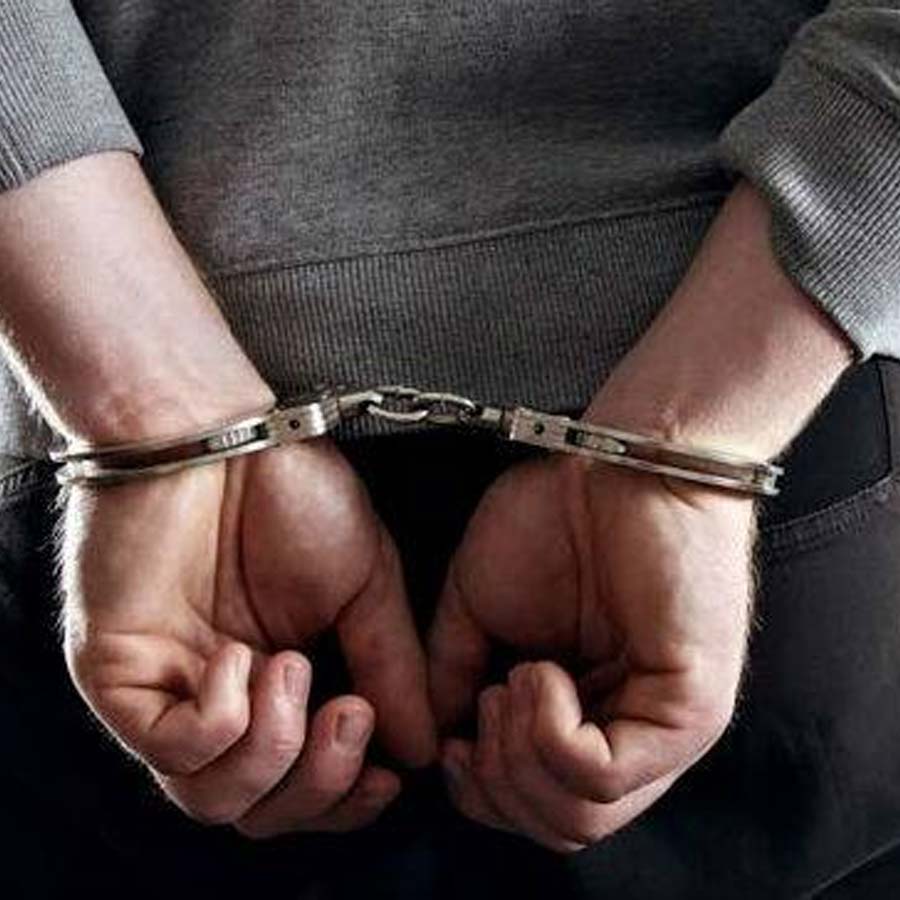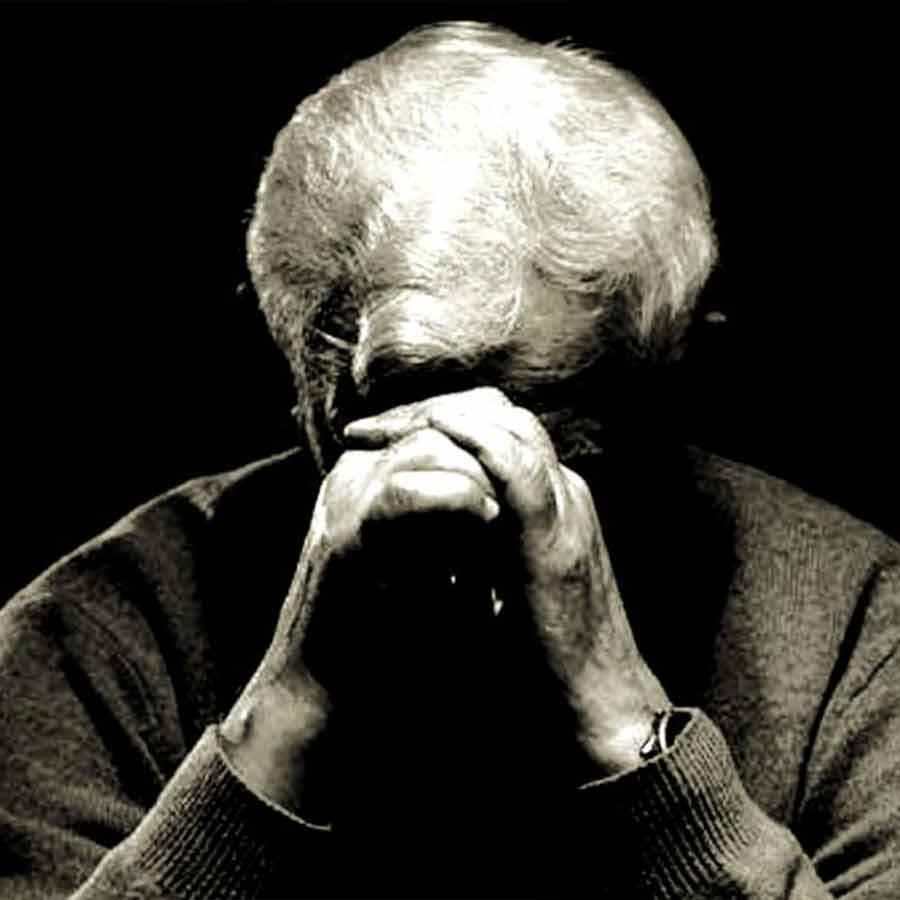সেমন্তী ঘোষের লেখা ‘দেবতার বঙ্গে অবতরণ’ (২-৪) প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা। কিছু বছর ধরে বাঙালির অবাঙালি সংস্কৃতিকে আপ্রাণ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা এই বঙ্গে রামনবমীর পালে আরও জোরে হাওয়া দিয়েছে। তার সঙ্গে ২০১৬ থেকে জুড়েছে আরএসএস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এ রাজ্যে রামকে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ছোটবেলায় রামনবমী কথাটি খুব বেশি করে শুনেছি বলে মনেই পড়ে না। এই সময়টা বাসন্তী পুজো, চড়কের মেলা, চৈত্র সংক্রান্তি, নববর্ষের আবহ থাকত সারা বাংলা জুড়ে। ২০১৯-এ এই রাজ্যে বিজেপির ভোট বাড়ায় গেরুয়া শিবির উল্লসিত হয়েছিল। তারই প্রতিদানে রামকে বাংলায় দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা জোরদার হয়েছে।
আজকের বাঙালি বোধ হয় ভুলে গিয়েছে, উত্তর ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে এ বঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতি কখনওই সে ভাবে মেলে না। এ বঙ্গে হিন্দু উৎসবের পাশাপাশি প্রতিবেশী মুসলিমদের পরবে সম্প্রীতির ছবি অতি পরিচিত ছিল। যদিও কিছু এলাকায় ভিতরে ভিতরে সংখ্যালঘুর প্রতি বিদ্বেষ যে তখনও ছিল, এ কথা সত্যি। তবে বাঙালি বিয়েতে যে দিন থেকে মেহেন্দি, সঙ্গীত-সহ উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস প্রকট হয়েছে, সে দিন থেকেই বোধ হয় আমরা বাঙালিরা, হিন্দুত্বের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলতাম তার থেকে সরে এসেছি। পোশাকে-আশাকে, ব্যবহারে, হিন্দি বাংলার মিশ্রণে এক খিচুড়ি ভাষায় বাঙালি এখন অভ্যস্ত। ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতে না পারলে মা-বাবাদের এখন গর্ববোধ হয়! ফলে দেশজোড়া হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের আস্ফালনে এই সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি মূল শিকড় পর্যন্ত চারিয়ে গেছে। আর বড় সমস্যা হল, বহু শিক্ষিত বাঙালি এই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন এবং বাঙালি সংস্কৃতির এই নিবন্ত দশাকে আধুনিকতার আখ্যা দিচ্ছেন। নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে হারিয়ে নব্য বাঙালি ঠিক কোন পথে চলছে, তা এখন সত্যিই বড় প্রশ্ন!
শুভ্রা চক্রবর্তী, কলেজ রোড, হাওড়া
বৃক্ষচ্ছায়া
মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গঠনের অগ্রণী সাংস্কৃতিক কান্ডারি সন্জীদা খাতুনের প্রয়াণ বিষয়ক প্রতিবেদন ‘প্রতিস্পর্ধার স্বর, বিদায় নিলেন বনস্পতি’ (২৬-৩) প্রসঙ্গে কিছু কথা। যখন সমগ্র উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন, যখন তাঁর মতো সাংস্কৃতিক যোদ্ধার খুব প্রয়োজন, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন বিকালে তিনি চলে গেলেন। কী আশ্চর্য সমাপতন! বড় অসময়ে এই যাওয়া। অপূরণীয় ক্ষতি হল দুই বাংলার অগণিত অ-সাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষের। ভারত ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সৌহার্দের সেতু রচনা করেছিলেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের গান সম্বল করে।
আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পথপ্রদর্শক থেকেছেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত সন্জীদা ধর্ম-বিযুক্ত ‘বাংলা নববর্ষ’ পালনকে সর্বজনীন উৎসবের চেহারা দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাংলাদেশ যখন পাক শাসনে, তখন শত বাধা সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালন করেছেন। নির্মাণ করেছেন ‘ছায়ানট’ নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র। ছায়ানটের অসংখ্য শাখা এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তিনিই বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রগানের চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। নিজে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলেন, তাই শান্তিনিকেতনের আদর্শে ছোটদের জন্য সৃষ্টিশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘নালন্দা’ তৈরি করে গিয়েছেন তিনি।
কেবল অনন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বা দক্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠক নন, সন্জীদা খাতুন এক জন মননশীল লেখকও। তাঁর লেখা বইগুলি দুই বাংলার সাহিত্যপ্রেমী পাঠককেই ঋদ্ধ করেছে। তাঁর লেখা বাংলা প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের সম্পদ এবং রবীন্দ্রচর্চার আকর স্বরূপ। দুই দেশ থেকেই বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন আর পেয়েছেন দুই বাংলার অসংখ্য মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। সংস্কৃতির বৃক্ষচ্ছায়া প্রদায়ী সন্জীদা খাতুনের অভাব আগামী দিনেও বাঙালি অনুভব করবে।
কৌশিক চিনা, মুন্সিরহাট, হাওড়া
বাংলা ক্যালেন্ডার
বাংলা, বাঙালিয়ানা ও নববর্ষ এই তিন পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু কোথায় যেন সেই বাঙালিয়ানাটাই উধাও। আমাদের বাংলা নববর্ষ কি আর আগের মতো আছে? মনে পড়ে যায়, আমাদের সময়ে নববর্ষ উদ্যাপনের ঘটাই ছিল আলাদা। চড়ক, গাজনের মেলায় লোকে লোকারণ্য আর বৈশাখ এলেই হালখাতা। দোকানে দোকানে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো, নতুন ক্যালেন্ডারের গন্ধ। নতুন পোশাকে বাঙালির আনাগোনা।
দুপুরে পাতে থাকত খাঁটি বাঙালিয়ানার সুবাস। শাক, ভাজাভুজি, শুক্তো, মাছের মাথা দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, মাছের ঝোল থেকে পায়েস, চাটনি মন ভরাত। চলত শুভেচ্ছা বিনিময়। বড়দের প্রণাম, বাড়ির কয়েক জন মিলে বসে রবিঠাকুরকে স্মরণ করা।
নববর্ষে বাংলা ক্যালেন্ডার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিনির্ভর বাংলায় পালাপার্বণ, তিথি-নক্ষত্র শুভাশুভ দিনক্ষণের উল্লেখ থাকায় বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদাই ছিল আলাদা। বলতে শোনা যেত, একটা বাংলা ক্যালেন্ডার দিয়ো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাংলা ক্যালেন্ডারও প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। বাংলা সাল-তারিখ কোথায়ই বা ব্যবহার হয় আজ? একমাত্র সংবাদপত্রেই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা সাল-তারিখ লেখা হয়। ইংরেজির মতো বাংলা সাল-মাস-তারিখ মনে থাকে ক’জনের? ক’জন বলতে পারেন বাংলা বারো মাসের নাম, পর পর? বর্তমানে বাংলা ক্যালেন্ডার দেওয়ালে শুধুই শোভা পায়, অনেক সময় পাতা ওল্টাতেও ভুলে যায় বাঙালি। ক্যালেন্ডার দেওয়ালে দোল খায়, প্রবীণদের মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে কতটা আগ্ৰহী?
সনৎ ঘোষ, খালোড়, বাগনান
আজি নববর্ষে
একটা বছর থেকে আর একটা বছরের দূরত্ব বারো মাসের। এই মাসগুলি অতিক্রমের লড়াইয়ে ব্যস্ত বহু মানুষের কাছে নববর্ষের দিনটি ক্যালেন্ডারে তারিখের বদল ছাড়া আর কিছুই না। তবুও বলব যে, নতুন বছরে শত মন্দের মধ্যেও ভাল থাকার ও ভাল রাখতে পারার একটা প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে জারি থাকুক। আগের বছরের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার জেদ থাকুক, কাউকে অকারণ অপমানে বিদ্ধ না করার ভাবনা থাকুক, চরম অসহায় মুহূর্তে বন্ধুর পাশে চুপ করে বসার জন্য দু’দণ্ড সময় থাকুক। ছলনায় ভরা এই দুনিয়াতে সৎ থাকার ইচ্ছাটা যেন কখনও হারিয়ে না যায়।
মানুষের ঔদ্ধত্য কমুক, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা বাড়ুক। হালখাতার সেই পুরনো সোনালি দিন আর আনন্দ ফিরে আসুক।
সঙ্গীতা ঘোষ, কলকাতা-৩২
পান্তাভাতে
ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং সেটা হয় প্রয়োজনের তাগিদেই। যেমন পান্তাভাত গরমকালের একটি অত্যন্ত উপযুক্ত সুস্বাদু খাদ্য। পান্তাভাত শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে, সেই কারণে গরমে এই পদ খেলে আরাম মিলবে। এ ছাড়াও শরীরে আয়রন, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে, ভিটামিন বি ১২-এর জোগান দেয়। প্রচণ্ড গরমে মিড-ডে মিলে শিশুদের পান্তাভাত ও ছোলার ছাতু মাখা পরিবেশন করলে ছোটরা সুস্থ থাকবে।
পার্থ প্রতিম মিত্র, ছোটনীলপুর, বর্ধমান
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)