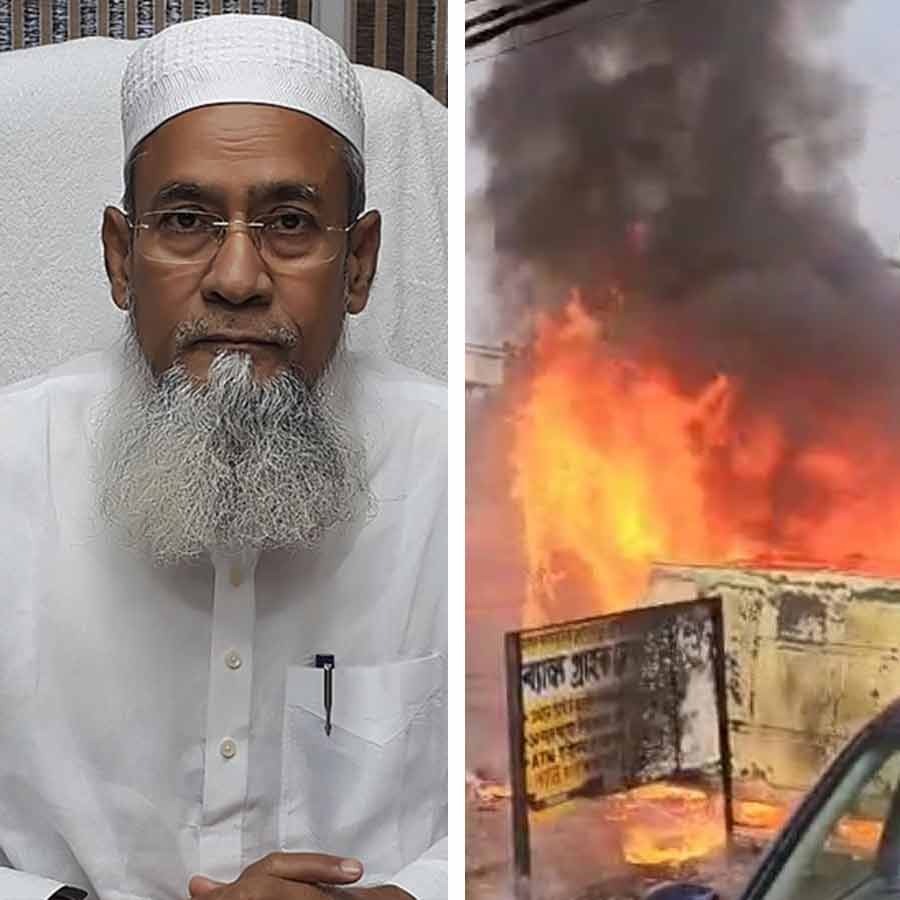হিন্দু কুলে নারায়ণ, মোমিন কুলে পির/ দুই কুলে পূজা খেয়ে হয়েছে জাহির— এই আদরের বক্রোক্তি ফৈজুল্লার পাঁচালি-তে আছে। বক্রোক্তি কথাটির সমর্থন ‘খেয়ে’ শব্দে মিলবে নিশ্চিত। তবে এই ধরনের প্রাচীন রসিকতা চলতি পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের গালে সপাটে চড় কষাতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত-সাধনার মরমি দলিল এই পাঁচালিতে আছে: ‘তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ।/ গুণ গাজী আপনি আসরে দেহ মন।।’ বাংলা ভাষায় রচিত ‘পির সাহিত্য’ তথাকথিত কৌলীন্য পায়নি, এলিট সমাজের কাছে আজও অপাঙ্ক্তেয়। পরকীয়া বিলাস, থ্রিলার আর ভৌতিক কাহিনিতে না মজে পড়শির আবহমান সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে মনোযোগ দিলে বরং চলমান অ-ধর্ম রাজনীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে এই পির সাহিত্য; যার প্রাণের কথা: ‘যেই আল্লা সেই ঈশ্বর এক কইরা জানি।/ ভাষা ভেদে ঈশ্বর ভেদ নাই যে আমি মানি।।’
পির শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। ফারসি এই শব্দটির ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু, তারই স্ত্রী-বাচক পিরানি। ওলাবিবি এমনই এক জন কাল্পনিক পিরানি। ওলাবিবি এবং ওলাদেবী (ওলাইচণ্ডী) নামান্তর মাত্র। ওলাওঠা রোগের থেকে নিস্তার পেতে হিন্দু আর মুসলমানের আরাধ্যা তিনি। হিন্দু ডাকে দেবী, মুসলমান ডাকে বিবি। কোথাও আবার তিনি বিবি-মা। তবে গৃহে পূজিতা নন। বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে, মূলত গ্রামাঞ্চলে ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। গাছের তলায় একটি অনুচ্চ আসনকে থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন: “ওলাবিবিকে হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত শ্রদ্ধা করেন, অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পীরগণকে যে ভাবে সাধারণ মানুষ মান্য করেন; হাজত, মানত বা শিন্নি প্রদান করেন, ওলাবিবিও অনুরূপ ভাবে সাধারণ মানুষের মানসিক অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ওলাবিবি তাই পিরানি বিশেষ।”
হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে এর মূর্তি একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো। মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবির ‘মূর্তি’ খানদানি ঘরের মুসলমান কিশোরী যেন। ওলাবিবিরা সাত বোন— আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহডবিবি, ঝেটুনেবিবি এবং ওলাবিবি নিজে। এই সাত বিবির প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্ত-মাতৃকার কথা, ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। এ ভাবেই সংস্কৃতি হাত বাড়ায় দু’জনের দিকে, ধর্ম তার সেতু হয়ে থাকে।
প্রায় পাঁচ দশক আগে রেলওয়ে কর্মচারী গিরীন্দ্রনাথ দাস তাঁর বহু পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার নির্যাস তুলে এনেছিলেন বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা বইটিতে। সেখানে তিনি বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত একত্রিশ জন ‘ঐতিহাসিক পির’-এর কথা লিখেছেন। ঐতিহাসিক কথাটির অর্থ— এঁরা বাস্তব পৃথিবীতে ছিলেন। এ ছাড়া বাঙালির ঘরে আজও পূজা পেয়ে চলেছেন আট জন কাল্পনিক পির-এর উল্লেখও আছে তাঁর গ্রন্থে। ওলাবিবির মতো খুঁড়িবিবি, বনবিবি, বিবি বরকতও কাল্পনিক পিরানি। আবার বাস্তবে ছিলেন এমন পিরানিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চম্পাবতী, ফাতেমা বিবি, রওশন বিবি।
চম্পাবতীর দরগায় রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারের সদস্য ধরণীমোহন রায় প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন শিন্নি দিতেন। বসিরহাটে ইছামতী নদীর তীরে রওশন বিবির সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পুণ্যস্থল। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে উরস উপলক্ষে মেলা বসে। আর পাশের কালী মন্দিরে একই সময়ে হয় কালী পূজা। পাশাপাশি দু’টি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই সে দিনও পর্যন্ত চোখে পড়ত মিলনমেলার আবহ। সেখানকারই কেন্দুয়া গ্রামে শীতকালে হত হিন্দু আর মুসলমানের বনভোজন উৎসব।
পাণ্ডুয়ার পির শাহ্ সুফির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্য-এর কবি রূপরাম চক্রবর্তী। চারঘাটের পির ঠাকুরবরের মাজার উপবীত (পৈতে) দিয়ে ঘেরা থাকত। এমনকি এখনও তাঁর নিত্য সেবায় বিল্বপত্র আবশ্যিক। শৈব সংস্কৃতির অনুসরণে পির সাহান্দি সাহেবের দরগায় গাজনের সময় ফুল দান করে সেই ফুলধোয়া জলকে পুণ্যবারি মনে করেন ভক্তবৃন্দ। ফুরফুরা শরিফের দাদাপির সাহেব ছিলেন হজরত মহম্মদের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিকির ৩১তম উত্তরপুরুষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ সখ্য। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও ছিল আন্তরিক পরিচয়। ঘুটিয়ারি শরিফের পির মোবারক বড়খাঁ গাজির একাধিক নাম প্রচলিত। তাঁকে নিয়ে রচিত নাটকে দেখা যায় পির গাজি পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণাপন্ন হচ্ছেন, এমনকি দেবীকে ‘মাসি’ সম্বোধন করে বলছেন: ‘নগর বসাতে সাধ/ উপায় তো দেখি না।/ স্বীকার না হলে মাসী/ ও চরণ তো ছাড়ব না।’ এ দিকে সাগর-মাসিও যে ‘বোনপো’-অন্তপ্রাণ, তার প্রমাণ এই নাটকের পরের সংলাপে: ‘বাপ গাজি! এর জন্য চিন্তা কি! উঠ, চল, আমি এর উপায় করে দেব।’ বস্তুত এই ধরনের নাটকগুলি এখনও বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কেবল অবসর যাপনের উপায় নয়, এগুলি ব্যতীত উরস, শীতলা পূজা, বনবিবি বা দক্ষিণরায়ের পূজা, মেলাগুলি অকল্পনীয়।
পিরের দরগায় প্রতি দিন বাতি জ্বালানো ও ধূপ দেওয়া, বাতাসা সহযোগে পিরের লুট, শিন্নি দেওয়া, সন্তান কামনায় ঢিল বাঁধার মতো ধারাবাহিক সংস্কার ও উদ্যাপন হাজার চেষ্টাতেও মুছে দেওয়া যাবে না। বারাসতের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে পির একদিল শাহের মাজার। প্রায় আট দশক আগে সেখানকার বিখ্যাত চিকিৎসক বসন্ত চট্টোপাধ্যায় কেবল সেই মাজার বাঁধিয়ে দেননি, প্রতি দিনের ধূপ-বাতি দেওয়া হত তাঁরই উদ্যোগে। যুক্ত-সাধনার নিবিড় শিকড় হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির আত্মার গভীরে প্রোথিত। নিজের ধর্ম পরিচয় ও ধর্ম চর্যার অন্তরালে মানুষের যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় তাকে রাজনৈতিক প্যাঁচ দিয়ে ঘুলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং ‘সবার উপরে রাজনীতি সত্য’ হয়ে ওঠার জবরদস্তি শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে জানে না মানুষ শেষ পর্যন্ত বোঝে ‘বিশ্বাসের ঐতিহ্য’কে।
সেই ঐতিহ্যে ধর্ম এবং সংস্কৃতি আসলে একই বৃন্তে দু’টি কুসুম। তাকে বৃন্তচ্যুত করা সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে কার্যত অসম্ভব।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)