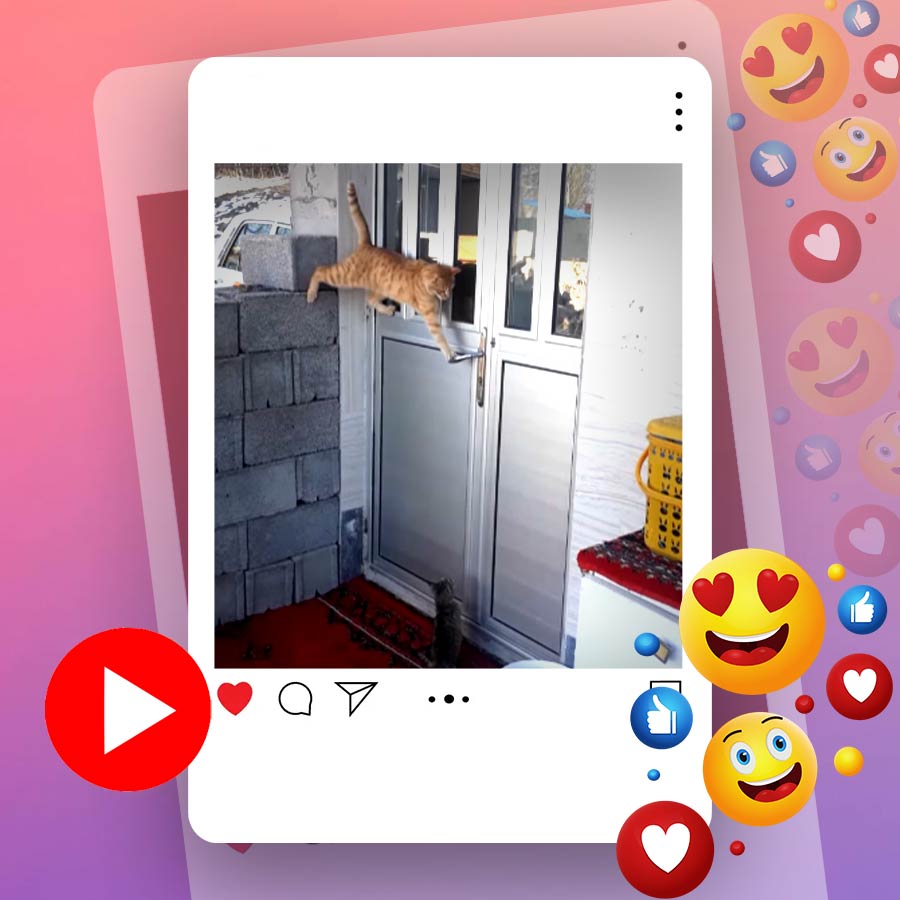উনিশ শতকের কলকাতা। ‘বাবু’র বাড়িতে গাজন ঘিরে তুমুল উন্মাদনা। কাওরা জাতিভুক্ত মূল সন্ন্যাসী কাদামাখা পায়ে, কানে বেলপাতা গুঁজে বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। সাদা ধপধপে ফরাসের উপর দিয়ে কাদামাখা পায়ে হেঁটে গেলেন। ‘বাবু’ তাঁকে প্রণামও করলেন। প্রণাম পেয়ে বাবুর মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন তথাকথিত ‘নিচু জাত’-এর বুড়ো মূল সন্ন্যাসী। হুতোম তাঁর ‘নক্সা’-য় লিখেছেন, “নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েছে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কত্তে হলো...।”
গাজনের সন্ন্যাসী হওয়া সব নিম্নবর্গের মানুষেরই বরাদ্দ ওই এক দিনের দেবত্ব, যে দিন উচ্চবর্ণের মানুষেরাও তাঁদের সামনে মাথা নোয়ান। কেউ কেউ বলতেই পারেন, গাজনের মূলে সমন্বয়ী ভাবনা আছে, সামাজিক মিশ্রণের ক্ষেত্র আছে। তাই বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার নিচু তলায় থাকা মানুষদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ক্ষমতাশালী মানুষের মেলবন্ধন তৈরি হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের চোখে এই প্রক্রিয়ার নাম আত্তীকরণ। যেখানে সামাজিক মেলবন্ধন বা সমন্বয়ী ভাবনার আড়ালে একটি সংস্কৃতি আর এক সংস্কৃতিকে ক্রমশ গিলে খায়। গাজনও তার ভিন্ন নয়।
বাংলায় গাজন মূলত দুই প্রকার। শিবের গাজন এবং ধর্মের গাজন। প্রথমটি হয় চৈত্র মাসে, সৌর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ ধর্মের বা ধর্মঠাকুরের গাজন হয় বৈশাখ মাসে চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। ধর্মঠাকুরের গাজন সম্ভবত প্রাচীনতর। আদি মধ্যযুগ থেকেই বাংলায় রাজাদের বিভিন্ন ভূমিদানের সূত্রে ব্রাহ্মণদের ভূস্বামী শ্রেণি হিসাবে উত্থান হয়েছিল। তবে শাস্ত্রীয় আচারে ব্রাহ্মণেরা কখনও কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাই ভূস্বামী শ্রেণির সঙ্গেই তৈরি হয়েছিল কৃষিজীবী শ্রেণি। প্রাক্-তুর্কি শাসনে মূলত নিম্নবর্গের এই কৃষিজীবী শ্রেণির আশ্রয় ছিল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ তোষণ এবং বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। সে সময় থেকেই নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে ধর্মঠাকুরের উত্থান।
আরও পরবর্তী সময়ে মুসলিম শাসকদের প্রভাব থেকে নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবীদের নিজের দিকে ধরে রাখতেই ধর্মঠাকুরকে নিজবৃত্তে নিয়ে আসা শুরু হয়। এই আত্তীকরণ পদ্ধতির অন্যতম উপায় ছিল মঙ্গলকাব্য। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন এবং সেনাপতি কালু ডোম, দু’জনকেই ধর্মঠাকুরের উপাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ র্যাল্ফ নিকোলাসের গবেষণাও দেখিয়েছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যেই ধর্ম বহু সময় বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। তবে বৈষ্ণব ধর্মের আঙিনা ছেড়ে ধর্মঠাকুর পরবর্তী সময়ে বাংলার শিবের সঙ্গেই জুড়ে গিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, এই শিব কিন্তু পৌরাণিক শিব নয়। বরং তিনি বাংলার গ্রামীণ গেরস্ত শিব। শিবের গাজন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই নিকোলাস দেখিয়েছেন, শিবের গাজন আসলে পৌরাণিক শিব, বাংলায় লোকায়ত শিব এবং ধর্মঠাকুরের সংমিশ্রণ— যিনি বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজেরই উপাস্য। গাজন আসলে ফসল কাটার আগে উর্বরতা বৃদ্ধিরই আরাধনা।
ধর্মের গাজন ক্রমশ শিবের গাজনে রূপান্তরিত। তবে মূল ধারক নিম্নবর্গরাই। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গের গাজনের উপরে নিকোলাসের গবেষণাই দেখায়, বামুন-কায়েতদের মতো উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিরা গাজন-চড়কের মূল উৎসবের বাইরেই থাকেন। তবে মন্দিরের ভিতরের যে ক্রিয়াকলাপ, তাতে উচ্চবর্ণের অধিকারই ‘শ্রেষ্ঠ’ হয়ে ওঠে। হুতোমের ‘নক্সা’-ও সেই কথাই বলে। তাই সন্ন্যাসীদের হাজারো মাথা ঝাঁকুনিতেও যখন শিবের মাথা থেকে ফুল-বেলপাতা পড়ছিল না, তখন ধরেবেঁধে সেই বাবুকে নিয়ে যেতে হয়। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পরে শিবের মাথার বেলপাতা নড়লে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধি সন্ন্যাসীরা কাঁটাডালের উপরে ঝাঁপ দেওয়া শুরু করেন। অর্থাৎ, মাসভর উপোস করে, সন্ন্যাস নিয়ে, কাঁটায় ঝাঁপ দিয়ে শারীরিক কষ্ট সইবে নিচুতলার লোকজন, তবে দেবতার মাথা থেকে ফুল না নড়লে সেই বাবুকেই যেতে হত। হুতোমের বিবরণে, বাবুর আধ ঘণ্টার আকুতির পরে শিবের মাথা থেকে বেলপাতা নড়েছিল।
একুশ শতকের বঙ্গেও গাজন, চড়ক ঘিরে বহু জায়গায় এই উঁচু-নিচু ভেদ রয়েছে। গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে ক্ষণিকের দেবত্বই বরাদ্দ আমাদের বহু সহ-নাগরিকের। কাঁটাঝাঁপ, আগুনঝাঁপের মতো বিষয়ে নিম্নবর্গের অগ্রাধিকার থাকলেও পুরোহিতের ভূমিকায় তাঁদের ভূমিকা নগণ্য। কিন্তু তার থেকেও গুরুতর সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে আসা নদিয়ার একটি ঘটনা। ওই জেলার এক শিবমন্দিরে সেই তল্লাটেরই কিছু মানুষের এত দিন প্রবেশাধিকার ছিল না। কারণ, তাঁরা তফসিলি জাতিভুক্ত। একই তল্লাটে থাকলেও শিবমন্দিরে ঢুকে পুজো দিতে পারতেন না তাঁরা। স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতারাও সেই বিধি টলাতে পারেননি (না কি চাননি?)। সংবাদে প্রকাশিত, তফসিলি জাতিভুক্ত শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্যও মন্দিরে ঢুকতে পারতেন না। মহামান্য হাই কোর্টের নির্দেশে শেষ অবধি পুলিশ-প্রশাসন নড়ে বসেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষও বাধা দিতে পারেননি। অবশেষে ওই মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়েছেন তফসিলি সমাজের মানুষেরা।
এই প্রথাই ফের প্রশ্ন তুলে দেয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চললেও আদতে তা তথাকথিত হিন্দু সমাজে কত দূর সমন্বয়সাধন করতে পেরেছে? না হলে নিম্নবর্গের উপাস্যকে টেনে নিলেও উপাসকদের প্রতি এই ভেদভাব কেন?
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)