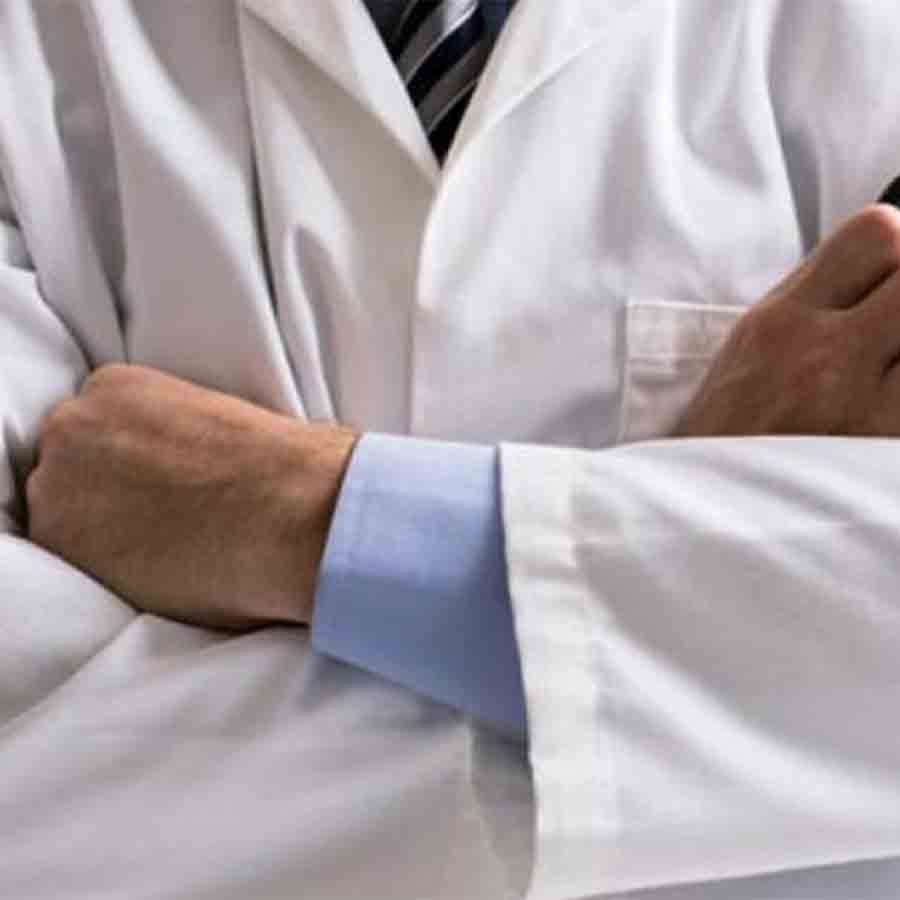য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’-এ মুদ্রিত একটি চিঠি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতেরো বছরের রবীন্দ্রনাথ তখন প্রথম বারের জন্যে বিলেতে। আছেন ডেভনশায়ারের এক শহরে। সেখানে মিস এইচ এবং মিস এন-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। দুই ইংরেজ-ললনার এক জন ছবি আঁকেন আর অন্য জন কবিতা লেখেন, নভেল পড়েন। বিকেলে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে মাঝে-মাঝেই তাঁরা এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। চার পাশের গাছপালা, পাহাড়, আকাশের একটা বিশেষ রং, সব কিছু সেই বিলেতি সুন্দরীদের প্রবল আকৃষ্ট করে, তাঁরা ‘শত মুখে’ সে সবের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। কিশোর রবির চোখে অবশ্য সে তেমন উল্লেখযোগ্য ঠেকে না, তিনি ‘বিশেষ সৌন্দর্য বড় একটা বুঝতে’ পারেন না, তাঁর ‘ভ্যাবাচ্যাকা লেগে’ যায়। কেবল সৌজন্যবোধের খাতিরে তাঁদের কথায় নীরবে সায় দেন। সঙ্গিনীদের এমন নিয়ত আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, এক দিন আগে থেকে কিছু একটা সৌন্দর্য দেখিয়ে ওঁদের ‘তাক’ লাগিয়ে দিতে হবে। ‘তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে’, এমন পণ করে রবীন্দ্রনাথ সে দিন পথে বেরিয়েছেন। চার দিকে গাছপালা ফুল পাহাড় সবই আছে, কিন্তু ‘একটা নতুন কিছু বের কোরতে হবে’।
চোখে পড়ল, ‘একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি কোরেছে, গাছ গুলোর ডাল পালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হোয়েচে। কোনটা গোল, কোনটা বা অষ্ট কোণ, কোনটা মন্দিরের চূড়োর মত। দেখে তো আমার তাক লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাকতে কিছু বলে বোলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়াতাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, “How beautiful!” Miss H-কে তার একটি ছবি নিতে অনুরোধ করলেম। Miss H ও Miss N ত একেবারে হেসে আকুল, তাঁরা বলে উঠলেন, “Oh, Mr. T, surely you are joking!”’ প্রত্যুত্তরে থতমত রবীন্দ্রনাথ যেন বড় রকমের ঠাট্টা করছেন, এমন ভান করে ওঁদের কথায় সায় দিলেন। সে দিন বিকেলে হতাশ রবীন্দ্রনাথ ‘অপ্রস্তুত হোয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাঙ্গালা কবিতা লিখতে’ বসেছেন। কবিতাটির শিরোনাম আমাদের জানা নেই, তবে সেই মুহূর্তে কবিতা যে তাঁর প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন, নির্দ্বিধায় বলা চলে। পরবর্তী কালে রচনাবলিতে বর্জিত এই অংশ আমাদের ভাবায়। রসিকতায় জড়ানো গল্পের নেপথ্যে রবীন্দ্রচিত্রকলার কোনও নির্দিষ্ট শৈলী কি ধরা রইল? আমরা দেখেছি, তাঁর চিত্ররচনার শুরু ‘আকারের মহাযাত্রা’য়, রঙের প্রবেশ সেখানে অনেক দেরিতে— উপরোক্ত ঘটনার আড়ালে কি লুকিয়ে আছে তার প্রচ্ছন্ন ইশারা?
প্রায় সত্তর বছর বয়সে ছবির জগতে ঢুকে পড়া রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালে এমনই মনে হয় আমাদের। রানী মহলানবিশকে জানিয়েছেন, “আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত— আজকাল সে আছে চোখ মেলে, রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা।” পাশাপাশি বলেন রেখা তাঁকে যেন ‘পেয়ে বসেচে’, তার মায়াজালে সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যহ তার নতুন নতুন ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারেন, “কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।” এ কোন রবীন্দ্রনাথ, যিনি আকাশ বাতাস থেকে ভেসে আসা সুর আর কথার পরিবর্তে রেখা এবং আকারের জয়োল্লাসে মেতে উঠতে চান?
এই রবীন্দ্রনাথ ছবির রবীন্দ্রনাথ। যিনি রক্তকরবী-র পাতায় বা পূরবী-র পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিতে গড়ে তুলেছেন একেবারে নতুন রকমের এক আকার। কবিতায় কাটাকুটির নকশা তৈরির অভ্যাস তাঁর বহু দিনের। শুরুর দিকে সে ছিল ‘আর্ট নুভো’ ঘেঁষা ডেকোরেটিভ অলঙ্করণ, সেখান থেকে সরে এখন এসেছে প্রিমিটিভ আর্টের ঢল। বিচিত্র সব জান্তব আকার দেখা দিচ্ছে কাটাকুটির অন্দরে, খোঁচাওয়ালা, কাঁটাওয়ালা চেহারা তাদের, কোথাও হাঁ-করা মুখগহ্বরে ধারালো দাঁতের সারি। কবিতার বর্জিত অক্ষর ঘিরে এদের আবির্ভাব, তথাকথিত সুন্দরের সঙ্গে যাদের কোনও সম্পর্ক নেই। লেখার পরতে পরতে রেখার ঘন বুনটে গড়া চাপ চাপ অন্ধকারের মতো তাদের শরীর, ধাতব পাতের মতো তীক্ষ্ণ, পেপার-কাটের মতো দ্বিমাত্রিক। পাণ্ডুলিপির আঁকিবুকি ছাড়িয়ে ছবি যখন সাদা পাতায় উঠে এসেছে, তখন সেই ছবিতেও রয়ে গিয়েছে পাণ্ডুলিপির ছায়াঘেরা পিছুটান। যেখানে রঙের ব্যবহার নিতান্ত কম, চিত্রপট ঘিরে আছে রেখা আর আকারের প্রতিমায়।
রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের এই সব ছবি মোনোক্রোম ঘেঁষা, রঙের বৈচিত্র সহসা চোখে পড়ে না। সে দিক থেকে দেখলে, রঙের উজ্জ্বল উপস্থিতি ১৯৩০-৩১ পেরিয়ে। এর অন্যতম কারণ, ফ্রান্স জার্মানি ইংল্যান্ড আমেরিকা ইত্যাদি দেশের নানা শহরে আয়োজিত প্রদর্শনীর সাফল্য চিত্রী হিসেবে তাঁকে প্রত্যয়ী করে তুলেছে। এই অধ্যায়ে শিল্পীর প্যালেট মোনোক্রোম থেকে সরে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। ক্রমে বিষয়ের দিক থেকেও বদল এসেছে ছবিতে, ‘জ়ুমরফিক’ ফর্মের পাশাপাশি এসেছে ‘ফিগারেটিভ’ কাজ। কখনও চিত্রপট ভরেছে নিসর্গের ছবি, ফুল বা আয়তচোখের নারীপ্রতিমায়। জীবনের প্রান্তে পৌঁছে প্রবল স্রোতের বেগে এমন ছবির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। জীবন জুড়ে রচিত গানের চেয়ে যে সংখ্যা অনেকটাই বেশি।
ছবির তারিখ মিলিয়ে দেখা যাবে, কখনও একটা সিটিং-এ আঁকা হয়েছে চার-পাঁচটা ছবি। একেবারে শেষবেলাতেও তার অন্যথা ঘটেনি। চকিতে মনে পড়বে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১ বৈশাখে পাঁচখানা ছবি এঁকেছেন। কোনওটা মানুষের অবয়ব, কোথাও সামনে ফিরে বা পাশ ফেরা মুখমণ্ডল, কোনওটা বা অন্ধকার গাছপালা। আশি বছর বয়স স্পর্শ করেও ভিতরের এই ‘ক্রিয়েটিভ আর্জ’কেই কি অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘ভলকানিক ইরাপশন’? আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গিরণের মতো এই চিত্রসম্ভারের মাধ্যম কি কালিকলম বা রংতুলির ঘনঘটায় সীমাবদ্ধ?
আমাদের চমকে দিয়ে দৃশ্যশিল্পের আধুনিক আঙ্গিকে তিনি রচনা করেছেন বেশ কয়েকটা ছাপাই ছবি। সাদামাঠা কাঠখোদাই নয়, ধাতব পাতের উপর তীক্ষ্ণ শলাকায় রেখার জাল বুনে রীতিমতো এচিং করেছেন। অবশ্য প্রিন্ট নেওয়া ইত্যাদি কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন মুকুল দে। সেই এচিং প্রিন্টের একটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছবির প্রথম অ্যালবাম ‘চিত্রলিপি’তে। সে ছবিতে ঘন অন্ধকারের বুকে তরঙ্গায়িত ঊর্মিমালার প্রান্তে উপবিষ্ট এক নারীমূর্তি, ছবির সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ-সহ এক ফালি কবিতা: ‘অসীম শূন্যে একা/ অবাক চক্ষু দূর রহস্য দেখা। The eyes seeking for the enigma of things/ explore the boundless nothing’।
সম্প্রতি শিল্পকলার অন্যতম আঙ্গিক হিসেবে দেখা দিয়েছে সেরামিক। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশো বছর আগে তাকেও স্পর্শ করতে ভোলেননি। ঘটের আকারযুক্ত একটি বড় সেরামিক-পাত্রের গায়ে অলঙ্কৃত নকশাতেও তাঁর নিজস্ব টিপছাপ অটুট। ১৯৩২-এর গোড়ায় খড়দহের বাড়িতে থাকাকালীন করেছিলেন এই ‘গ্লেজ়ড পটারি’।
কিন্তু ভাস্কর্য? না, ইচ্ছে থাকলেও ভাস্কর্য গড়া হয়নি রবীন্দ্রনাথের। ভিজে মাটির সংস্পর্শে অসুস্থ কবির ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রতিমা দেবীর সম্মতি ছিল না। তবে সিলিন্ড্রিক্যাল পাত্রের মতো একটা বাঁশের টুকরোর দু’পাশ ঘিরে এঁকেছেন পুরুষ ও নারীর অবয়ব। সে চিত্রিত কাজ প্রায় ভাস্কর্যের শামিল, দেখতে হয় চার দিক থেকে ঘুরে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রচিত্র-প্রদর্শনীতে এই সব কাজ বিশেষ করে দেখার সুযোগে রবীন্দ্রশিল্পভুবনের দিকে ফিরে তাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট: ভিসুয়াল আর্টের সব ক’টি দিকেই ছিল তাঁর আশ্চর্য আনাগোনা।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)