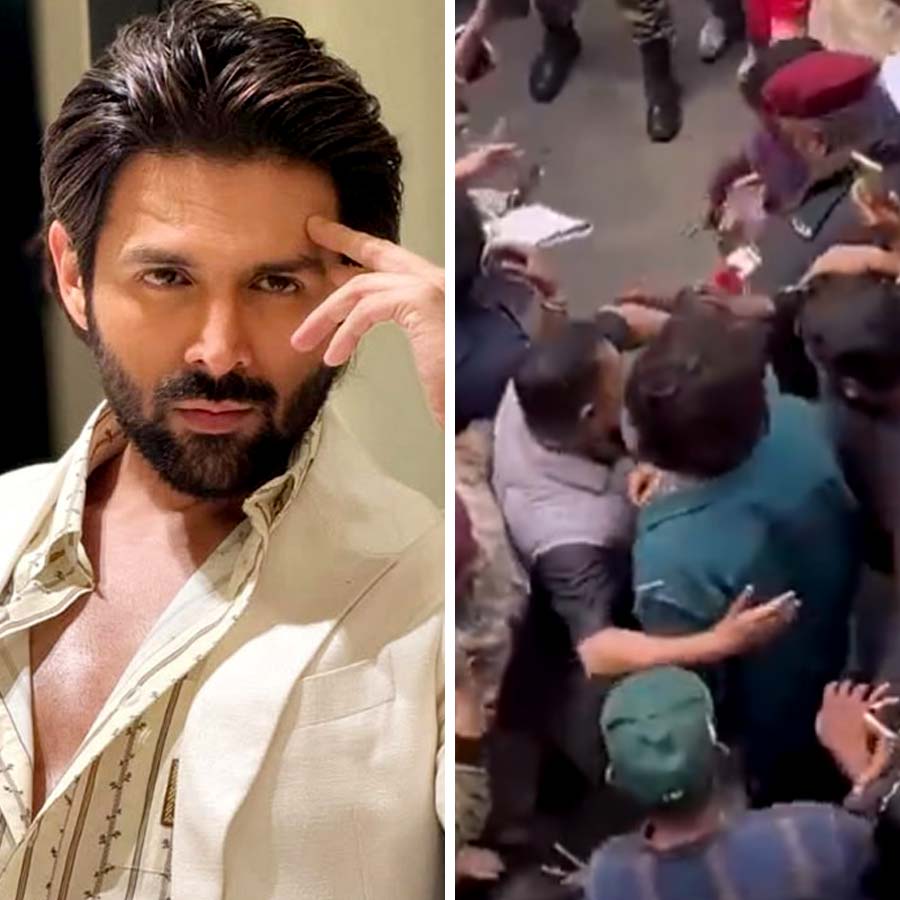সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজ়রি কাউন্সিল তাদের ‘ফাউন্ডেশনাল লিটরেসি ও নিউমেরেসি রিপোর্ট’-এ দেশের শিক্ষামানের যে চিত্র তুলে ধরেছে, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তবে তারা যে স্কোর-কার্ড প্রকাশ করেছে, তাতে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে সেরার স্বীকৃতি। যে যে সূচকের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন তা হল: শিক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষালাভের সুবিধা, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, সামগ্রিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং প্রাপ্ত শিক্ষার মান। প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের এই শিরোপা নিঃসন্দেহে গৌরবের। আরও একটি বিষয়ে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কৃতিত্বের দাবিদার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ‘ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ‘ড্রপআউট’-এর জাতীয় গড় ৩.৭% হলেও, এ রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে সেই হার শূন্য।
এই সাফল্যের মধ্যেও সম্প্রতি ‘অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট, রুরাল’ (এএসইআর) নামে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত মান সম্পর্কে এক অসরকারি সংস্থার করা সমীক্ষার যে ফল প্রকাশ্যে এসেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। দেখা যাচ্ছে, এখনও এ রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণির ৫.২% পড়ুয়ার বাংলার অক্ষরজ্ঞান নেই, ১৬.৪% অক্ষর পড়তে পারলেও শব্দ পড়তে জানে না। প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ১৪.৩% ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনে না, এমনকি তৃতীয় শ্রেণিতেও সংখ্যা চেনে না ৪.৪% পড়ুয়া। শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজে নিয়োজিত এই সংস্থা দেশ জুড়ে গ্রামীণ এলাকার ১৯টি ভাষার সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের পড়ুয়াদের (৫-১৬ বছর) নিয়ে সমীক্ষা করে এই ফল পেয়েছে।
ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতে অসামঞ্জস্য, শিক্ষা-বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার, প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, স্কুলের পরিকাঠামোগত দুর্বলতা-সহ বেশ কিছু ব্যাপার যে পঠনপাঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়া যে পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে শেখার তাগিদের অন্তরায়, এমন মতও শোনা গেছে একাধিক শিক্ষাবিদের মুখে। তাঁদের একাংশের মতে, দ্রুত বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুমনকে আকৃষ্ট করার উপযোগী পাঠ্যক্রম ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস পাঠদানের পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়া শিশুদের মধ্যে শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা কঠিন।
২০১৮-য় প্রকাশিত ‘প্রতীচী ও শিক্ষা আলোচনা’য় অনুরূপ বিতর্ক উঠে এসেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, “এক গোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল, শিশুরা যেহেতু বিনা পরীক্ষায় এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তাই তাদের লেখাপড়ার আগ্রহ থাকবে না। অন্য গোষ্ঠীর মূল বক্তব্য, যেহেতু শিশু নিজে নিজে শিখে উঠতে পারে না, তাই সে বিদ্যালয়ের সাহায্য নেয়। বিদ্যালয় শিশুকে শুধু বিদ্যাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে উচিত দিশা দেখায়। এটিই বিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব, বার্ষিক পরীক্ষার পদ্ধতির শিক্ষা পদ্ধতিতে এক চরম ফাঁকি হয়ে যাচ্ছিল। শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি বিকাশ ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছিল না... এই মূল্যায়ন পদ্ধতি বছরের শেষে ফেল করা ছাত্রকে এই বলে প্রতিপন্ন করছিল যে তার বুদ্ধিগত স্তর উপযুক্ত নয়।” প্রতিবেদনে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের স্থূলত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অমর্ত্য সেন।
সব শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে ‘রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯’ প্রণীত হয়। এই আইনে এক দিকে সকল শিশুর নিখরচায় শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকৃত হয়, প্রচলিত বার্ষিক মূল্যায়নের পরিবর্তে ‘কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কমপ্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন’ (সিসিই) বা ‘নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন’-এরও সুপারিশ করা হয়। ২০১৮-র ‘প্রতীচী ও শিক্ষা আলোচনা’ কিন্তু বলছে, রাজ্যের সব স্কুলে ‘সিসিই’ সমান ভাবে চর্চিত হচ্ছে না।
মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি শিশুর জ্ঞানার্জনে অনীহার একটি কারণ হয়তো, কিন্তু একমাত্র কারণ কি না তাও তর্কযোগ্য। মিড-ডে মিল, বিনামূল্যে বই-খাতা পোশাক জুতো শিক্ষা-সরঞ্জাম দিয়ে শিশুদের স্কুলমুখী করা গেলেও কেন শিক্ষালাভে আগ্রহী করা যাচ্ছে না, প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই সবচেয়ে জরুরি।
শিশুশিক্ষায় অগ্রণী দেশগুলোতে ভারতের তুলনায় শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ অনেক বেশি। শিশুদের মধ্যে শেখার আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যেও সেখানে চলছে নানা নিরীক্ষা। আনন্দময় পরিবেশ তৈরি, শিশুমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঠ্যক্রম রচনা, শিক্ষক-ছাত্রের আন্তরিক সম্পর্ক, পঠনপাঠনের সময় নির্ধারণে শিশুর স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া, এমন নানা বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। এ দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে ন্যস্ত, সেই শিক্ষকদের জন্য রয়েছে উচ্চ সম্মানী, উচ্চতর সামাজিক সম্মান। আমাদের দেশ ও রাজ্যের মতো তাঁদের ‘ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো’র দৃষ্টিতে দেখা হয় না। সে সব দেশে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি কঠিন ও স্বচ্ছ। এ রাজ্যে শিশুদের পড়াশোনায় আগ্রহী করে তুলতে হলে যেমন শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি ও পাঠ্যক্রম সংস্কার প্রয়োজন, তেমনই দরকার যথার্থ শিক্ষিত ও শিক্ষাব্রতী শিক্ষকও। দুর্নীতি সহায়ে চাকরি করতে আসা অযোগ্যদের দিয়ে এই প্রয়োজন মেটার নয়।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)