
মা-ঠাকুমার রান্নাঘর
রসিকজনা আজও ফিরে পেতে চান পাড়া ম-ম করা সেই সব রান্না! উপায়?

সুরবেক বিশ্বাস
বাড়িতে হঠাৎ কুটুম্ব। সাততাড়াতাড়ি ভারী, সুস্বাদু খাবার দিতে হবে। এ দিকে হেঁসেলে আনাজ বলতে শুধু পটল! কিন্তু তা দিয়েই বাজিমাত করে দিয়েছিলেন এক সাবেকি গৃহিণী!
চিংড়ি দিয়ে ডালনা খাওয়ার ভারী শখ কর্তার। তাতে গিন্নি আগেভাগে বলে দিয়েছিলেন, কেমন হবে সেই কুমড়োর শাঁস, তার খোসার রং। নইলে স্বাদ বরবাদ। সে কেমন?
মাংস কষানোর সময় হাঁড়িতে গোটা কয় আস্ত সুপারি ফেলে দিতেন এক রন্ধনপটিয়সী। রহস্যটা কী?
মা-ঠাকুমাদের হেঁসেলের গল্পে লুকিয়ে এমন অদ্ভুতুড়ে সব কাহিনি।
বছর কয়েক আগে পুজোর সময়ের কথা। বাড়িতে ভালমন্দ রান্না হবে।
একমাত্র ছেলেকে ডেকে তাঁর মা বলে দিলেন, ছোট সাইজের চেয়ে কিছুটা বড় এমন চিংড়ি লাগবে, যার মাথা ফেলা যাবে না।
তবে চিংড়ির গোটা শরীরের মতো মাথার খোলাটাও ফেলে দিতে হবে। চিংড়ির পোলাওয়ের স্বাদ অনেকটা নির্ভর করবে মাথার উপর।
ছেলে পড়লেন মহা সমস্যায়।
কী চিংড়ি কিনবেন?

জ্যান্ত হরিণা চিংড়িরও মাথা রাখা যায় না। চাপড়া চিংড়ির স্বাদ সব চেয়ে ভাল, তবে তার মাথাও ফেলে দিতে হয়। চামটে বা চামড়ে অনেকটাই ছোট, খোসা ও মাথাসুদ্ধ খাওয়াই নিয়ম।
অনেক ভেবে তিনি একেবারেই ছোট সাইজের টাটকা বাগদা চিংড়ি কিনলেন আর কাটালেন মায়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।
মাছ দেখে মা জননী মহা খুশি। গোবিন্দভোগ চালের পোলাও হল জম্পেশ। তেল, ঘি, মশলায় ভরপুর।
তবে চিনির সঙ্গে বেশ কিছুটা শুকনো লঙ্কাবাটা পড়ে বলে ওই পোলাওয়ের স্বাদ ঝাল-মিষ্টি মেশানো।
ছেলে অফিসে নিয়ে যেতে একেবারে সুপারহিট। এতটাই যে, আট মাস পরেও স্বাদ-গন্ধ ভুলতে না পারা সহকর্মীর প্রশ্ন, ‘‘চিংড়ির পোলাওটা জেঠিমা এখন আর রাঁধেন না বুঝি?’’
স্কুলজীবনে মেয়ে সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় ছিল মা অচলাদেবীর হাতে আলু-পটল-কুমড়ো দিয়ে চিংড়ি মাছের ডালনা।
হরিনা চিংড়ি দিলেও হবে, চাপড়া পড়লেও অসুবিধে নেই। কিন্তু ওই ডালনায় কুমড়ো দেওয়ার ব্যাপারে মা বড্ড খুঁতখুঁতে।
সুপ্রিয়ার মনে পড়ে, এক বার বাবা কমলা রঙের শাঁসওয়ালা কুমড়ো আনায় মা তুলকালাম বাঁধিয়েছিলেন।
ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, ‘‘আমি কি কুমড়োর ছক্কা রাঁধব যে এই কুমড়ো এনেছ? পই পই করে বলে দিলাম, কুমড়োর খোসা হবে কালচে সবুজ আর শাঁসের রং হবে সোনার মতো। না হলে চিংড়ি দিয়ে ডালনা হবে না।’’
রান্না নিয়ে এই ধরনের খুঁতখুঁতানির সে যুগ ছিল বড় সোনার সময়।
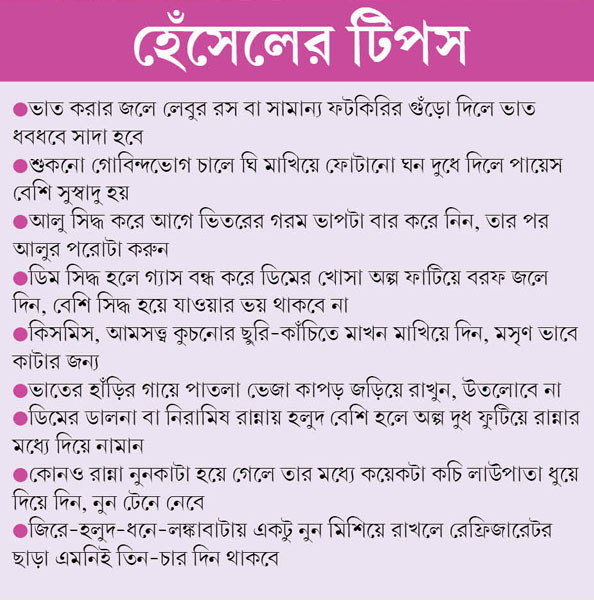
মা-ঠাকুমারা শুধু খুন্তি নাড়তেন না। তাঁরা অননুকরণীয় এক-একটি শিল্পের সৃষ্টি করতেন। সেই যে, লীলা মজুমদার বলেছিলেন না, রান্না বলতে ‘পৃথিবীর একটি সেরা শিল্প-কর্মের সাধনা’-কে বোঝায়! ঠিক তাই।
আর এই যে রন্ধন শিল্প, এ শুধু হেঁসেলের চার দেওয়ালের মধ্যেই যে আটকে থাকত, তাও নয়। শুরুয়াতটা হয়ে যেত বাজার থেকেই।
মানিকতলার অর্জুন বিশ্বাস গল্প করছিলেন। বলছিলেন, ছুটির দিনে শীতের বাজারে এক বার লোভনীয় ট্যাংরা পেয়ে কিনে নিয়েছিলেন প্রায় দেড় কেজি। কিন্তু তার সঙ্গে মুলো আনতে ভুলে গিয়েছেন বলে তাঁকে বাড়ির দরজা থেকে বাজারে ফিরতে হয়েছিল মায়ের আব্দারে।
এক সময় পাতলা স্নিগ্ধ ঝোল করতে হলে মা-ঠাকুমারা তার জন্য উপযুক্ত দু-আড়াই কেজির রুই মাছ আনতে বলতেন। কিন্তু দই পোনা কিংবা কালিয়ার জন্য হলে কিন্তু সেই মাছ নৈব নৈব চ। ওই সব ভারী পদের জন্য চাই বেশ ভারী ওজনের কাতলা।
বাড়িতে মোচার ঘণ্ট হলে সে দিন বাজার-কর্তার ওপর অবধারিত ফরমাশ বিচিকলার মোচা আনার।
আবার দেখুন, এ সব যেমন সত্যি, তেমনই হঠাৎ, কোনও প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে অতিথি এসে পড়লে সেখানেই কত রকমের যে পদ উদয় হত!
এমনই একটি কথা শোনা গেল ঢাকুরিয়ার ইন্দ্রাণী মল্লিকের কাছে। বাড়িতে হঠাৎ কুটুম্ব হাজির। একটু ভারী, অন্য রকম জলখাবার দিলে বাড়ির মান থাকে। কিন্তু গৃহিণী দেখলেন, ভাঁড়ার প্রায় শূন্য।
যখনকার কথা, তখন রেফ্রিজারেটর বাড়িতে বাড়িতে হাতে গোনা। এমনকী থাকলেও তাতে গোটা সপ্তাহের আনাজ ডাঁই করে রাখার চল ছিল না। ঝুড়িতে শুধু পটল আছে কিছু। আর থাকার মধ্যে চিঁড়ে-মুড়ি-খই এই সব। তাতেই মাথায় খেলে গেল আইডিয়া।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হল সুস্বাদু-সুগন্ধি চিঁড়ে-পটল। আসলে পটল দিয়ে চিঁড়ের পোলাও।
খোসা অল্প ছাড়িয়ে নিয়ে পটলের টুকরোগুলো সর্ষের তেলে হাল্কা করে নেড়ে নিলেন ইন্দ্রাণীর শাশুড়ি-মা অনিতাদেবী। আলাদা করে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে চিঁড়ে তুলে রাখলেন আলাদা করে। তার পর কড়ায় সর্ষের তেল ও গাওয়া ঘি একসঙ্গে গরম করে তার মধ্যে গরম মশলা-তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা-হলুদ বাটা-শুকনো লঙ্কা বাটা-নুন-চিনি ও কাজু-কিসমিস দিয়ে কষিয়ে পটলের সেই অল্প ভাজা টুকরোগুলো দিলেন ছেড়ে। শেষে ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে দিয়ে অল্প জল ঢেলে গা-মাখা অবস্থায় নামিয়ে দিলেন।
ইন্দ্রাণী বলছিলেন, এই ভাবে নাকি চাল-পটল কিংবা চাল-আলু-পটল করার রেওয়াজ একটা সময় অনেক বাড়িতেই ছিল। সেটা দুপুর বা রাতের খাবারের পদও হয়ে যেত। কিন্তু তার জায়গায় জলখাবার হিসেবে এই যে চিঁড়ে-পটল বানিয়ে দেওয়া হল, একেই বুঝি বলে রন্ধনশিল্পে ‘এস্থেটিক ইমপ্রোভাইজেশন’।
এই ‘ইনোভেশন’-এর ছোট্ট ছোট্ট ছোঁওয়া অতি সাধারণ সব খাবারকে চরম উপাদেয় করে দিত!
কৈশোরের গল্প বলছিলেন বিজয়গড়ের অতনু রাহা, ‘‘আমার যখন ইস্কুলবেলা, আমার মা আমাকে মাঝেমধ্যে প্রাতরাশে করে দিতেন গোলমরিচের গুঁড়ো ছেটানো বাটার টোস্ট আর ফিঙ্গার চিপস। এক দিন দেখি, ফিঙ্গার চিপসের রং খয়েরি-লাল, খেতেও অন্য দিনের তুলনায় বেশি সুস্বাদু।’’
কী ব্যাপার? না গরম তেলে মা প্রথমে বেশ কিছুটা চিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সে দিন, তার পর ভেজেছিলেন আলু, যার গায়ে অল্প অল্প খোসা ছিল। এবং ভাজাটা হয়েছিল ঢিমে আঁচে। ব্যস!
অতনু বলছিলেন, ‘‘আজকাল মাল্টিপ্লেক্সে খাবারের কাউন্টারে কিংবা মুরগি ভাজার জন্য প্রসিদ্ধ ফাস্ট ফুড চেন-এ ফ্রোজেন আলু দিয়ে তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুখে দিলে দুঃখও লাগে, হাসিও পায়। যাতে ধর তক্তা মার পেরেক গোছের ব্যাপার আছে, চটকদারি আছে, কিন্তু ওই মা-সুলভ যত্ন বা সৃষ্টিশীলতা কোথায় পাব! ফলে যা হবার তাই হয়।’’
মা-ঠাকুমাদের হেঁসেলের এই অদৃশ্য উপকরণের ব্যাপারটা ঠিক কী রকম, নিজের ঠাকুমার প্রসঙ্গে তার একটা অদ্ভুত উদাহরণ দিয়েছেন রন্ধন পটীয়সী শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর কথায়, ‘‘আমার ঠাকুমা তুলসীদাসী দেবী রান্নায় সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ছিলেন। তবে তাঁর উৎকর্ষ ছিল নিরামিষ রান্নাতে। রান্না করার সময়, বিশেষ করে দাদুর জন্য রাঁধার সময় ঠাকুমার কী রকম একটা পুজো করার মতো ভাব হত, সেই জন্যই বোধহয় রান্নার স্বাদ হত অত ভাল।’’
ভোজনশিল্পী বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে, ‘‘...আমার ঠাকুমার নিরামিষ রান্না— সে আবার অন্য জগৎ, মশাই, সেখানকার বাসিন্দারা ভারী বিনয়ী, ছেঁচকি ঘণ্ট শাক শুক্তো এই সব অনুজ্জ্বল নামে বিরাজ করে, কুমড়ো-বীচি লাউয়ের খোশার মতো ওঁচা জিনিশও সেখানে সম্মানিত। কিন্তু ঐ সব বিজ্ঞাপনহীন সৃষ্টি থেকে যা আস্বাদ বেরিয়ে আসে তা প্যারিসের সেরা রাঁধুনির কল্পনাতীত। যেমন রামধনুর সাতটাকে মিশিয়ে অসংখ্য রং বের ক’রে আনেন চিত্রশিল্পীরা, তেমনি মাত্র তিনটে-চারটে মোটা আস্বাদের মধ্যেই জিভের জন্য বিপুল বৈচিত্র্য রচনা করেন আমার মা-ঠাকুমারা, সেই তাঁদের স্টুডিওতে, যার সরঞ্জাম অত্যন্ত মামুলি, আর পেছনে অর্থবলও নেই।...এই ললিতকলা, জগতের সভ্যতায় বাঙালির বা বঙ্গনারীর এই বিশেষ অবদান...।’’ (উপন্যাস ‘গোলাপ কেন কালো’)
মা-ঠাকুমাদের যে রান্নাঘরকে স্টুডিও বলেছেন বুদ্ধদেব বসু, তার ক্যানভাস-তুলি-ইজেলও ছিল অন্য রকম। রন্ধন শিল্প মূর্ত হয়ে ওঠার পিছনে সে সবের অবদান কম নয়।
ঝকঝকে, নিকোনো রান্নাঘর ছিল মাটির। রান্না হত মাটির উনুনে, জ্বালানি ছিল কয়লার, কাঠকয়লার। পরবর্তী কালে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি গুলের (যাতে ধোঁয়া অপেক্ষাকৃত কম বেরোয়)।
তবে বাড়িতে অতিথির জন্য তরিবত করে মাছ-মাংস রাঁধতে হলে রান্নাঘরের যিনি রানি, তিনি চাইতেন গরাণ কাঠ। ওই জ্বালানিতে আমিষ রান্নার স্বাদ নাকি খুলত ভাল।
এ রকমও বাড়ি ছিল শহর কলকাতায়, যেখানে সুন্দরবন থেকে গরাণ কাঠ পৌঁছে দেওয়ার লোক ও ব্যবস্থা থাকত অনুষ্ঠানের আগের দিন।
কোনও কোনও উনুনের চুল্লি থাকত একাধিক। আঁচ কমে আসা নিভন্ত উনুনে দুধ জ্বাল দেওয়া হত। বেশি বেলায় রান্না হওয়া খাবার রান্না চাপিয়ে রাখা হত নিভন্ত উনুনের উপর, যাতে রাতে খাবার পাতে বেড়ে দেওয়ার সময়ে ওই পদ তাজা থাকে।
কিংবা উনুন যখন নিভু-নিভু, তখন তাতেই আলু, লাউ কিংবা পটলের খোসা ভাজা হত পোস্ত আর কাঁচালঙ্কা সহযোগে। গরম গরম ভাতের পাতে খেতে হত মুচমুচে।
এই কাঠ কিংবা কয়লার উনুনে রান্না যে শুধু সুস্বাদু হত, তা নয়, সেই রান্না নজর রাখত স্বাস্থ্যের দিকেও। ডাক্তার-ডায়েটেশিয়ানদের একাংশ স্বীকার করে নিচ্ছেন, এখনকার লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের চুল্লির আগুনে সরাসরি রুটি সেঁকে খাওয়ার পরিণামই কিন্তু মুঠো মুঠো ওমিপ্রাজল-প্যান্টোপ্রাজল-র্যাবিপ্রাজলের বড়ি গেলা। গ্যাসটিক-গ্যাসট্রাইটিস-আলসার-হাইপার অ্যাসিডিটি ঠেকাতে।
রোগীর পথ্য রাঁধার উনুন সে কালে কোনও কোনও বাড়িতে ছিল আলাদা!

রোগীর জন্য গলা ভাত, ডাল-সবজি সিদ্ধ, শিঙি-মাগুরের ঝোল কিংবা মাংসের স্টু হত ঘুঁটের জালে বা ঘুঁটের উনুনে। কারণ, রোগীর জন্য আদর্শ হল, ‘স্লো কুকিং’ বা ঢিমে আঁচে, ধীরে ধীরে রান্না। ঘুঁটের উনুনে ওই রান্না হয় সব চেয়ে ভাল।
আবার মা-ঠাকুমাদের কেউ কেউ এঁটো উনুনে অর্থাৎ যে উনুনে অন্যান্য রান্না হয়েছে, তাতেই দুধ জ্বাল দেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না।
ঘুঁটের আঁচের একটি উনুন থাকত শুধু দুধ জ্বাল দিতে। এমন উনুনেই লোহার কড়াই চাপিয়ে, কাঠের হাতা দিয়ে দুধ জ্বাল দিতেন মা- দিদিমা-কাকিমারা।
আস্তে আস্তে সেই দুধের উপর পড়ত সরের আস্তরণ, পরতে পরতে। সেই সর আলাদা করে তুলে রাখা হত। যা থেকে তৈরি হত অনির্বচনীয় স্বাদ ও গন্ধের ঘি।
তবে সব বাড়িতে আলাদা আলাদা উনুনের বিলাসিতা সম্ভব ছিল না। একটা উনুনেই হত সব রকম রান্না। সেটাই ছিল চ্যালেঞ্জ।
কারণ, কম সময়ে ভাল রান্না করতে হবে, একাধিক পদ পাতে বেড়ে দিতে হবে। আর ওই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়েই দক্ষতা ও নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিতেন সেকালের বঙ্গনারী।
যেমন, বেহালার রেণুকা বসু। তাঁর কন্যা, এ কালে নিজের পরিবারে রন্ধনে খ্যাতনামা রমা ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, তাঁর মা পাঁঠার মাংস রান্নার সময়ে হাঁড়িতে আস্ত সুপারি বেশ কয়েকটা ফেলে দিতেন। ফলে, মাংস সিদ্ধ হত তাড়াতাড়ি।
আবার ‘জ্বালানি খরচ সাশ্রয়’-এর ব্যাপারটাও বেশ মজার। মাংস কষানোর সময়ে হাঁড়ির ঢাকার উপর জলভর্তি একটা বড় পাত্র বসানো থাকত। কষানো হয়ে গেলে সেই গরম জলই মাংসে দেওয়া হত।
আজকালকার মতো আভেনের একটি চুল্লিতে মাংস কষানো হচ্ছে আর পাশের চুল্লিতে জল গরম হচ্ছে, এমন ব্যবস্থা কোথায়!
রেণুকা দেবী ইলিশ বা চিংড়ি সর্ষে বাটা, হলুদ, নুন, কাঁচালঙ্কা তেল দিয়ে মেখে টিফিন কৌটোয় ভরে তার মুখ বন্ধ করে ভাতের হাঁড়িতে দিয়ে দিতেন। ভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলিশ বা চিংড়ি ভাপাও হয়ে যেত। এর মধ্যে অন্য রকম কিছু নেই।
কিন্তু রেণুকা বসু নিজস্ব একটা কারিকুরি করতেন। কী সেটা?
টিফিন কৌটোয় আগে পেতে দিতেন ভাল করে ধোয়া পুঁইপাতা। সর্ষে মাখানো মাছ শুয়ে থাকত ওই বিছানায়। আবার মাছের গায়ের উপরেও বিছোনো থাকত পুঁইপাতার চাদর। তার পর টিফিন কৌটোর মুখ ঢাকা পড়ত।
এতে দু’টো কাজ একসঙ্গে হত। এক, পুঁইপাতার আবরণ কৌটোর গায়ে মাছকে লেগে যেতে দিত না। দুই, মাছের স্বাদ-গন্ধ-মশলায় মাখামাখি পুঁইপাতাও পরিণত হত সুখাদ্যে।
ভাতের মাড় গালার সময়ে টিফিন কৌটোটাকে বার করে নিতে হত। আবার ভাতের মাড় ফেলা হত বড় একটা পাত্রে। হিঞ্চে শাকের অনেকটা ডগা সুতো দিয়ে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হত গরম মাড়ের মধ্যে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হিঞ্চে শাক সিদ্ধ। যা কি না সর্ষের তেল, কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে মাখিয়ে প্রথম পাতে তেতো পদ হিসেবে খেতে দিতেন রেণুকা দেবী।
রমা ভট্টাচার্যের কথায়, ‘‘এখানে একসঙ্গে ভাত, হিঞ্চে শাক সিদ্ধ ও মাছের ভাপা তৈরি হচ্ছে। বেঁচে যাচ্ছে সময় ও কয়লার খরচ।’’
একই ভাবে ফুটন্ত গরম জলে সর্ষের তেল মাখিয়ে মুসুর ডাল ছাড়তেন রেণুকা দেবী। অল্প সময়ে সিদ্ধও হত, স্বাদও হত অনবদ্য।
এই ধরনের ‘স্কিল’-এর জন্যই হিন্দু গৃহিণীদের নিরামিষ রন্ধনশৈলী মুগ্ধ করেছে বুদ্ধদেব বসুকে।
তিনি লিখছেন, ‘‘...তাঁরা হাত পাকিয়েছেন একটি নতুন স্টাইলে, অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে। আমাদের যা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত, সেই কুমড়োর বিচি লাউয়ের খোশাকেও তাঁরা সুস্বাদু ক’রে তুলতে পারেন। তাঁদের ভাঁড়ারে স্থান পায় খিড়কি-পুকুরের শালুক-ডাঁটা, সবচেয়ে শস্তা বাজারের শাক, আর উঠোনের মাচার লাউপাতা আর কুমড়োফুল।’’
কুমড়োফুল, বকফুলের বড়া প্রসঙ্গেই বলা যায়, এখনকার মডিউলার কিচেনে যেমন বেসন ও কর্নফ্লাওয়ারের আধিক্য, মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের বড়া-ভাজা তৈরির বসন ও ভূষণ মূলত ছিল চালের গুঁড়ো, আতপ চালের গুঁড়ো, সঙ্গে ঈষৎ ছেটানো থাকত পোস্ত। যাতে বড়া হত মুচমুচে, খাস্তা।
গত তিরিশ বছর যাবৎ যাবতীয় আমিষ খাওয়া ও রান্না থেকে দূরে থাকা নবতিপর হিরণপ্রভা দাস সেই সনাতন পথের পথিক। তাঁর হাতে সর্ষেবাটা-নারকোল কোরানোর পুর ভরা ঝিঙে চালের গুঁড়ো মাখিয়েই ভাজা হয়। যাতে মিইয়ে না যায়, অল্প ঠান্ডা হলেও।
হিরণপ্রভার আমিষপ্রিয় নাতি-নাতনিরা তাঁর খিচুড়ির পরম ভক্ত। তাঁদেরই এক জন, রূপশ্রী দাসের কথায়, ‘‘দিদার খিচুড়ি অদ্ভুত। অমন খিচুড়ি কোথাও কখনও খাইনি।’’
বিভিন্ন পুজো উপলক্ষে প্রায় দশ কিলোমিটার উজিয়ে গড়িয়াহাটের হিন্দুস্থান রোডে মেয়ের বাড়িতে এসে এখনও খিচুড়ি রেঁধে যান তিনি। না হলে নাতি-নাতনিদের মন ভরে না।
দিদিমার রাঁধা এই খিচুড়ির স্বাদের কারণটা কি? রহস্য ফাঁস করছেন রূপশ্রী, ‘‘বাকি প্রায় সবাই খিচুড়ি রান্নার পর তাতে ঘি দেয়। আর আমার দিদা খিচুড়ির গোবিন্দভোগ চাল আর সোনামুগের ডালটাই আগে ঘিয়ে ভেজে নেন। ওটাই দিদা-স্পেশ্যাল।’’
রূপশ্রী তাঁর ঠাকুমা বিন্দুরানি রায়ের কাছ থেকে শেখা একটি বিশেষ পদ তৈরি করেন, যা কি না আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে সুপারহিট। তার নাম মাছের জলভাজা।
কাতলা মাছের পুরু পুরু পেটি নুন হলুদ মাখিয়ে হাল্কা ভেজে তুলে রাখতে হয়। তার পর নুন-হলুদ দিয়ে ঝিরিঝিরি করে কাটা পেঁয়াজ চটকে ও ফালি করা কাঁচালঙ্কা তেলে দিতে হবে। এখানে পেঁয়াজের সঙ্গে নুন-হলুদ চটকে দেওয়াটাই ‘টাচ’। নুন এমনি ছড়িয়ে দিলে রান্নাটা নুনকাটা হয়ে যাবে।
পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা কিছুক্ষণ সাঁতলানোর পর হাল্কা ভাজা মাছগুলো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ঢিমে আঁচে। একেবারে শুকনো শুকনো হয়ে গেলে মাছের জলভাজা তৈরি। কিন্তু রূপশ্রীর আক্ষেপ, ‘‘সবই দিই, খুব যত্ন করে রাঁধি, কিন্তু ঠাকুমার মতো কিছুতেই হতে চায় না।’’
এ নিয়ে আজকের অনেক রন্ধনপটিয়সী কিন্তু এক বাক্যে একটা মত অবশ্যই দেন।
তাঁরা বলেন, আসলে রান্নার উপকরণের সঙ্গে আর একটা বস্তু স্বাদের ফারাক গড়ে দিত। সেটা হল, বাসন-কোসন। পিতল আর লোহার ইয়া বড় বড় কড়াই, তেমনই লাগসই হাতা-খুন্তি। আর ছিল মাটির বাসন। লোহার কড়াইয়ে দুধ জাল দেওয়া হবে। পিতলের কড়াইয়ে ঘণ্ট বা ডালনা আর মাছ।
অর্ধশতকেরও বেশি আগে চট্টগ্রামের কনকলতা ভট্টাচার্য স্টেশন মাস্টার স্বামীর চাকরির সূত্রে অসমের তিনসুকিয়ায় গিয়ে সংসার পাতেন। লোহার কড়াইয়ে কষানোর পর তিনি মাংস ঢেলে দিতেন মাটির হাঁড়িতে। বাকি রান্নাটুকু ওই পাত্রেই হত। গন্ধ পেয়ে জিভের জল ফেলত গোটা পাড়া। এমন সব দেবভোগ্য খাবার খাওয়া হত কাঁসার থালা-বাটিতে। কনকলতা দেবী সেই সব বাসন মাজতেন ঘুঁটের উনুনের ছাই দিয়ে।
এক বার কনকলতার ছোট জা এসেছেন মেহের কালীবাড়ি স্টেশন থেকে। বাড়িতে অতিথি সমাগম হবে, সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে।
যাঁরা আসবেন, তাঁরা সব রেলের কর্তা। তাক লাগিয়ে দেওয়া হল নারকোলের মিষ্টি করে। এক-একটা মিষ্টি এক-একটা গলদা চিংড়ি। যার চোখ তৈরি হয়েছিল এলাচ দানা দিয়ে।
সেই মিষ্টি বানানো অবশ্য সহজ ছিল না। পাক্কা এক রাতের প্রস্তুতি। প্রথমে মালা থেকে নারকোলের শাঁস ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে রাতভর ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল জলে।
সকালে জল থেকে উঠিয়ে নারকোলের টুকরোগুলোর পিছনে লেগে থাকা ছালও তুলে ফেলা গেল সহজে, সারা রাত জলে ভিজেছে বলে।
তার পর নরম শাঁস জাতিতে সুপারি কুচোনোর মতো ঝিরি ঝিরি করে কাটা হল। এর পর কড়াতে চিনি দিয়ে পাক। কিন্তু এতটুকু লাল হলে বারোটা বেজে যাবে।
পাকের পরেও ওই নারকোলের ছাঁচকে রাখতে হবে দুধসাদা। তবেই না কেরামতি।
আর চিনির পাক দেওয়া ওই নারকোলের ঝিরি দিয়েই তৈরি হল গলদা চিংড়ি। অতিথিরা শুধু ওই মিষ্টিতেই মাত হয়ে গেলেন।
‘‘সেই দুপুরে আরও একটা অদ্ভুত পদ হয়েছিল আমাদের বাড়িতে,’’ স্মৃতিচারণা করছেন কনকলতা ভট্টাচার্য়ের বড় মেয়ে, সত্তর ছুঁই ছুঁই অনিতা দেবী।
কী সেটা? তিনি বলেন, ‘‘কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের মুড়িঘণ্ট তো সবাই করে। কিন্তু আমার মা সে দিন করেছিলেন ইলিশের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট। তবে ইলিশের মাথাতেও অসংখ্য সরু সরু কাঁটা থাকে। সেই কাঁটা তো মুড়িঘণ্টে পড়লে চলবে না। তাই, আমাকে একটা একটা করে কাঁটা বেছে ফেলে দিতে হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার ধৈর্যের পরীক্ষা। মুড়িঘণ্ট রান্না হয়েছিল শুধু মুড়োর বড় বড় কাঁটা আর ইলিশের তেল দিয়ে।’’
মা-ঠাকুমাদের হেঁসেলে ধৈর্য ছিল ভাল রান্নার অন্যতম অপরিহার্য মশলা। এখন সেই অসীম ধৈর্য কে দেখাবেন? দেখানো কি আদৌ সম্ভব?
বছর কুড়ি আগে, ভাইফোঁটার দিন গড়িয়াহাটের এক চিনে রেস্তোরাঁয় দেখেছিলাম, এক মধ্যবয়স্ক বোন বা দিদি তাঁর ভাই বা দাদাদের খাওয়াচ্ছেন।
ওয়েটার একটার পর একটা পদ এনে টেবিলে রাখছেন, আর বড় চামচে করে সে সব ভাইয়েদের পাতে দিচ্ছেন বোন। ভাইয়েরা সোনামুখ করে খেয়ে নিচ্ছেন।
মা-ঠাকুমার হেঁসেলের বিদায়ঘণ্টার ধ্বনি সে দিনই প্রথম কানে বেজেছিল কি? হবেও বা!
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy








