ইতিমধ্যে অনেকেই ‘অ্যাডোলেসেন্স’ দেখে ফেলেছেন। এবং এই নিয়ে প্রচুর লেখালিখি, আলোচনাও চলছে। কিন্তু সিরিজ়ের যে দিকটি নিয়ে এই প্রবন্ধ, সেটি নিয়ে ততটা আলোচনা এখনও পর্যন্ত দেখিনি।
বিশদ আলোচনার আগে আমি প্রথমেই সিরিজ়ের নির্মাতাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তৃতীয় পর্বটিতে (চার পর্বের ওয়েব সিরিজ়) এক জন মনোবিদের সংলাপ প্রায় যথাযথ ভাবে তুলে ধরার জন্য। কারণ, এটি প্রায় বিরল। অন্যান্য বিনোদনমূলক ছবি বা সিরিজ়ের তুলনায় ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর তৃতীয় পর্ব অনেক বেশি বাস্তবমুখী। সংশোধনাগারের অন্দরে সহপাঠীকে খুনে অভিযুক্ত কিশোর জেমির সঙ্গে যখন কথোপকথনে বসেন মনোবিদ, তখন তাঁর দিকটিও দেখতে পাওয়া যায়। মনোবিদের মনের অবস্থা, তাঁর ভাবনা, তাঁর অভিজ্ঞতা সাধারণত এ ভাবে দেখা যায় না পর্দায়। ‘দীপ জ্বেলে যাই’-এর আমল থেকে ‘ডিয়ার জ়িন্দগি’ পর্যন্ত দেখেছি, মনোবিদের সঙ্গে তাঁর কাছে দেখাতে আসা ব্যক্তির সম্পর্কের প্রকাশ বিশেষ বাস্তবরূপী হয় না। কখনও মনোবিদের কাছে এসে এক জন তাঁর প্রেমে পড়ছেন! কখনও মনোবিদই মানসিক রোগী হয়ে উঠছেন। এতটা সরলীকরণ করার মতো নয় কিন্তু বিষয়টি। এক জন মনোবিদের কাছে যিনি আসেন, দু’জনের সংলাপকে নিয়ে নানা ‘ফ্যান্টাসি’র ফসল আমরা দেখেছি। কিন্তু বাস্তব চিত্র আমরা খুব একটা দেখিনি।
আরও পড়ুন:
থেরাপি চলাকালীন এক জন মনোবিদের মনের উপরেও যে অভিঘাত আসতে পারে, ‘অ্যাডোলেসেন্স’ তার একটা নির্দিষ্ট আন্দাজ দিল। মনোবিদ হিসাবে আমার কাছে এই বিষয়টার অবশ্যই একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। যাঁরা মনের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের মনের উপর তৈরি হওয়া অভিঘাতের কথা, তাঁদের মনের যত্নের প্রয়োজনীয়তার কথা সেই অর্থে খুব বেশি শিল্পমাধ্যম, পারিপার্শ্বিক সংলাপে, সামাজিক পরিসরে তেমন ভাবে উঠে আসতে দেখি না। বরং উল্টোটাই দেখি। কোনও মনোবিদ হয়তো জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন বা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন— তখন প্রথমেই তাঁকে শুনতে হয়, ‘‘আপনি তো এক জন মনোবিদ। আপনার মনের অবস্থা কেন এ রকম!’’ যেন দাঁতের চিকিৎসকদের দাঁতে ব্যথা হয় না! কার্ডিয়োলজিস্টেরা যেন হৃদ়্রোগে আক্রান্ত হন না! কিন্তু মনোবিদদের অনেক বেশি ‘মেন্টাল হেল্থ শেমিং’-এর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।
এক জন মনোবিদের ক্ষেত্রেও মনের যত্ন যে গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করে ‘অ্যাডোলেসেন্স’ সিরিজ়ের তৃতীয় পর্বটি। সেখানে ওই কিশোর যেমন বহু সময়ে মনোবিদের মনে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরির মতো পরিসর সৃষ্টি করছে। কখনও তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে, কখনও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করছে। এমনকি, কখনও ব্যক্তিগত প্রশ্নে তাঁকে অনেক বেশি লিপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুসংহত ভাবে তিনি সম্পূর্ণ সেশনটি শেষ করেন এবং তার পর ভেঙে পড়েন। এই পর্বটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এমন অনেক মুহূর্তের অভিঘাতের আখ্যান অকথিত, অপ্রকাশিত আমাদের অনেকের মনের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। থেকে যায়। এই আখ্যান নিয়ে আলোচনা থেরাপির প্রাথমিক নীতির বিরোধী। এথিক্সের বাইরে। ফলত এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় নিজেকেই নিজের মনের সঙ্গে আসতে হয়।
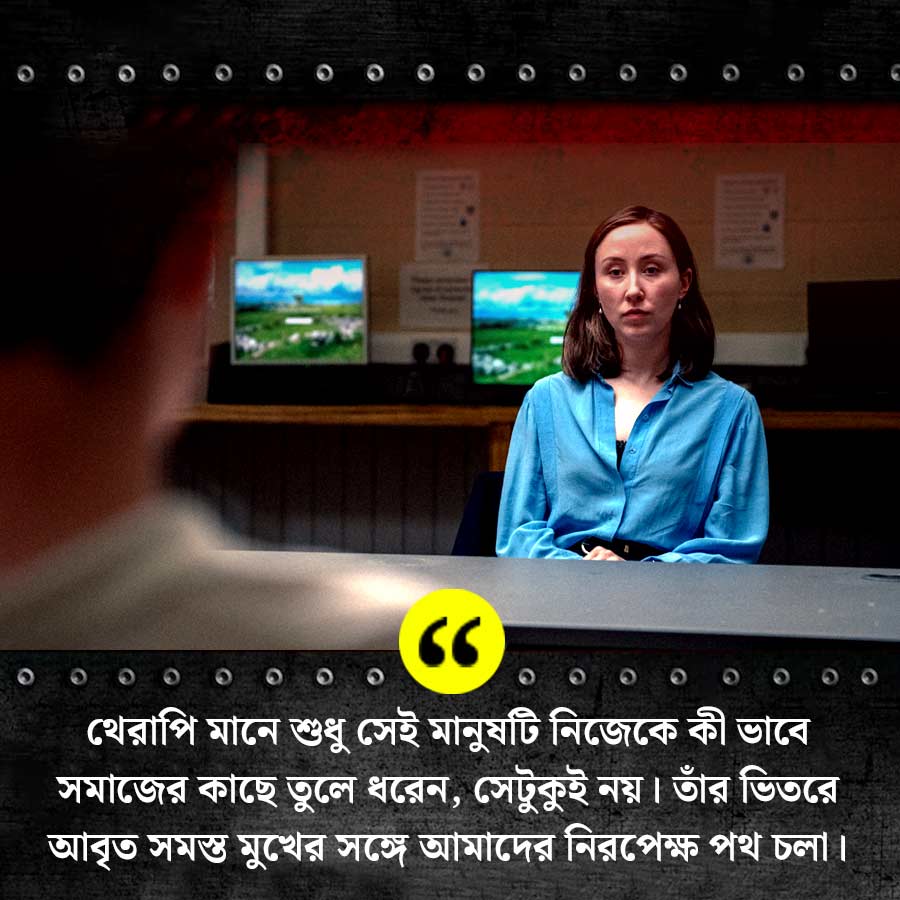
ছবি: সংগৃহীত।
যত ক্ষণ থেরাপি সেশন চলে, যে মানুষটি আমাদের কাছে এসেছেন, তাঁর দগদগে আবেগের গহীনতম ঘর আমাদের ঠিকানা হয়ে ওঠে। এমনও হতে পারে, মনোবিদ নিজে যে সঙ্কট দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবনে যে বিপর্যয় চলছে, উল্টো দিকের মানুষটিও তাঁর সংলাপে একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন।
থেরাপিও কিন্তু কখনও কখনও মনোবিদের জন্য ‘ট্রিগার’-এর পরিসর তৈরি করতে পারে। ওই মুহূর্তে যা যা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়, যে আবেগের ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটা পারস্পরিক চলন তৈরি হয়, তা নিয়ে কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোনও পেশার ক্ষেত্রে, কোনও ব্যক্তি তাঁর আবেগ নিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কারও সঙ্গে মতানৈক্য হলে, তিনি বাড়ি ফিরে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পেশায় সেটি সর্বৈব ভাবে পরিত্যাজ্য। একটা পেশাগত একাকিত্ব রয়েছে। সেশনের পর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পথ চলা একান্তই অন্তরের। নিজের সঙ্গে।
সংশোধনাগারের ভিতর এক জন নাবালকের সঙ্গে কথা। সেখানে মনোবিদের কথার মাধ্যমে সত্য অন্বেষণের প্রয়াস রয়েছে। তিনি বলছেন, ‘‘আমি আইনজীবী নই, পুলিশের কেউ নই। আমি শুধু তোমার আখ্যানটা শুনতে চাই।’’ কোথাও কোথাও তিনি বুঝতে পারছেন নির্দিষ্ট একটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ছেলেটি রেগে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খুব শান্ত ভাবে একই প্রশ্ন বার বার সামনে আনছেন। এই প্রশিক্ষণ কিন্তু আমাদেরও দেওয়া হয়। কোনও মতপার্থক্য হলে, উল্টো দিকে বসে থাকা মানুষটি উত্তেজিত হলে, তাঁর মধ্যে জন্ম নেওয়া সব রকমের কঠিন আবেগের সঙ্গেও আমাকে পথ চলতে হবে। এবং সেই আবেগকে ধারণ করতে হবে। কারণ, থেরাপি মানে শুধু সেই মানুষটি নিজেকে কী ভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরেন, সেটুকুই নয়। তাঁর ভিতরে আবৃত সমস্ত মুখের সঙ্গে আমাদের নিরপেক্ষ পথ চলা। যেমন এই সিরিজ়ে, কিশোরটি মনোবিদকে এক সময়ে ‘এলিট’ বলে আক্রমণ করছে। অর্থাৎ, তার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, সে সমাজের কোন শ্রেণির মানুষকে কোন আঙ্গিক থেকে দেখে। আমরাও দেখেছি, থেরাপি যখন একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছোয়, তখন নিঃসঙ্কোচ আবেগের প্রকাশ সেখানে আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নিঃসঙ্কোচ আবেগের যথাযথ মৌখিক বহিঃপ্রকাশের পরিসর তৈরি করতে পারাটাই থেরাপির ক্ষেত্রে কাম্য।
থেরাপিতে দু’জনের শারীরিক স্পর্শের ক্ষেত্রে নিষেধ রয়েছে। যেমন, হয়তো তিনি আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁকে বলপূর্বক নয়, বরং শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, ‘আমি আপনার কথা শুনছি’। প্রতিটি আবেগ যেন শব্দের মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, সেই প্রয়াসও নিরন্তর চলতে থাকে। পাশাপাশি, আমাদের নিজের আবেগের উপরেও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

‘অ্যাডোলেসেন্স’ সিরিজ়ের তৃতীয় পর্বের একটি দৃশ্যে এরিন ডোহার্টি (বাঁ দিকে) এবং ওয়েন কুপার। ছবি: সংগৃহীত।
সাধারণ থেরাপি সেশন এবং সংশোধনাগারে অপরাধীর থেরাপি সেশনের পার্থক্য থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। সংশোধনাগারে কাজ করার সরাসরি অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই এখানে যে থেরাপির নিয়ম দেখানো হয়েছে, তা হয়তো আমরা যে পরিসরে থেরাপি করি, তার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে না। যেমন ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এ তিনটে সেশনের পরেই জেমি নামক ওই কিশোর অবাক প্রশ্ন করে মনোবিদকে, ‘‘আজকেই কী করে শেষ হয়ে গেল?’’ হতে পারে, আদালতের নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই থেরাপি শেষ করতে হল। সেইমতোই মনোবিদ সেশনের পরিকল্পনা করেছেন। এমনতিতে আমরা কিন্তু কাউকে বলতে পারি না, ‘‘আপনি আর কাল থেকে আসবেন না।’’ সেশনের সমাপ্তি ঘটে মনোবিদ ও মনোরোগীর পারস্পরিক সম্মতিতে। সেখানেও যেন কোনও সিদ্ধান্ত একে অপরের উপরে চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সে দিকটা খেয়াল রাখতে হয়।
আমাদের শেখানো হয়, মনোবিদ কোনও সেশনে বসলে তখন তাঁর শুধুই দুটো কান এবং নিজস্ব বোধবুদ্ধি ছাড়া আর কোনও পরিচয় থাকতে পারে না। এমনকি, যখন কোনও প্রশ্নও রাখা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য ওই মানুষটিকে আর একটু ভাল করে বোঝা, তাঁর আরাম। কোনটা নিয়ে আলোচনা এগোলে আমার কৌতূহল প্রশমিত হবে বা নিজের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে, সেটি কিন্তু থেরাপির সংলাপের অংশ হওয়া কখনওই কাম্য নয়। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক, আমার কাছে কোনও তারকা ক্লায়েন্ট তাঁর নতুন প্রেমের আখ্যান শোনালেন। তাঁকে আমি চিনি বলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ওই ব্যক্তি কার সঙ্গে প্রেম করছেন। হতে পারে, যাঁর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন, তাঁকেও আমি চিনি। কিন্তু প্রশিক্ষণ অনুযায়ী এই প্রশ্নটা আমার জিজ্ঞাসা করার কথা নয়। তিনি মনে করলে সেই পাত্র বা পাত্রীর পরিচয় আমাকে জানাতে পারেন। আবার না-ও পারেন। কিন্তু সেটা জানার পরেও যেন আমার মনের মধ্যে কোনও আবেগের বিচলন না ঘটে, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।
আরও পড়ুন:
ওটিটি-র ওই সিরিজ়ে কি সবটাই তেমন দেখানো হল? তা ঠিক নয়। অন্য সব ছবি-সিরিজ়ে যেমন চিত্রনাট্যের স্বার্থে নানা রকম সংযোজন ঘটে, এখানেও ঘটেছে। যেমন এখানে মনোবিদ জেমির সঙ্গে দেখা করতে এলেন হট চকোলেট এবং স্যান্ডউইচ নিয়ে। এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা না। আমার বহু ক্লায়েন্টের কাছে শুনেছি, আরও অনেকেই নাকি মনোবিদের সঙ্গে কফি খেতে যান বা সেশনের বাইরেও দেখা করেন। সেটা কিন্তু আদতে হওয়ার কথা নয়। যদি কোনও মনোবিদ ক্যাফেতে ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং সেখানে থেরাপি চলাকালীন মনোবিদের পরিচিত কেউ উপস্থিত হন, সেই দু’টি মানুষের কথোপকথনের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কিন্তু মনোবিদ সম্পর্কেও এমন অনেক তথ্য পেতে পারেন যা থেরাপির পরিপন্থী। ক্লায়েন্টের কাছে থেরাপিস্ট একটি ফাঁকা স্লেটের মতো হওয়াই ভাল, যাতে ক্লায়েন্টের সমস্ত আবেগ সেই প্রতিফলকে ফুটে উঠতে পারে।
এক জন মনোবিদেরও কিন্তু দীর্ঘ সময় পর অন্য এক জন সিনিয়র মনোবিদের সঙ্গে আদানপ্রদানের প্রয়োজন হতে পারে। বিষয়টাকে ‘সুপারভিশন’ বলা হয়। আমাদের দেশে সেই পরিসর একটি বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের অন্তর্গত। কিন্তু যখন কেউ বহু দিন পেশায় যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের জন্য এমন বৃত্ত তৈরি হওয়া বা সুপারভিশনের নির্দিষ্ট পরিসর সুসংহত ভাবে তৈরি হওয়ার এখনও অনেক প্রয়োজন রয়ে যাচ্ছে। যাঁরা দীর্ঘ দিন এই পেশায় রয়েছেন, তাঁদের মানসিক ক্ষরণের শুশ্রূষার যথাযথ পরিবেশ তৈরি হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে সুজিত সরকার পরিচালিত ‘আই ওয়ান্ট টু টক’ ছবিতে অভিষেক বচ্চনের নার্সের আত্মহত্যার ঘটনাটি মনে পড়ছে। তিনি মনোবিদ ছিলেন না। কিন্তু রোগীর মানসিক শুশ্রূষার সংলাপে সংযুক্ত ছিলেন। আসলে এক জন ‘কেয়ার গিভার’ দিনের শেষে কোথায় ফিরছেন বা কেমন আছেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে তিনি ডাক্তার হোন, নার্স হোন অথবা মনোবিদ। যে পেশা অন্যের যন্ত্রণাকে প্রতিনিয়ত বহন করে, সে পেশায় নিজের ভার নামিয়ে রাখার ঘরটুকুর যত্ন বড় জরুরি।
থেরাপি নিয়ে আমাদের মনোভঙ্গিতে অবশ্যই বদল এসেছে। স্টিগমাও আগের থেকে কমেছে। কিন্তু থেরাপির সেশনে আদতে ঠিক কী হয়, তা নিয়ে এখনও অনেক ভুল ধারণা রয়ে গিয়েছে। আর মনোবিদের মনের উপর কী প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে কোনও ধারণাই কি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমরা? ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর এই তৃতীয় পর্বটি সেই না-হাঁটা পথে পা বাড়াল।
(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অনুলিখিত)












