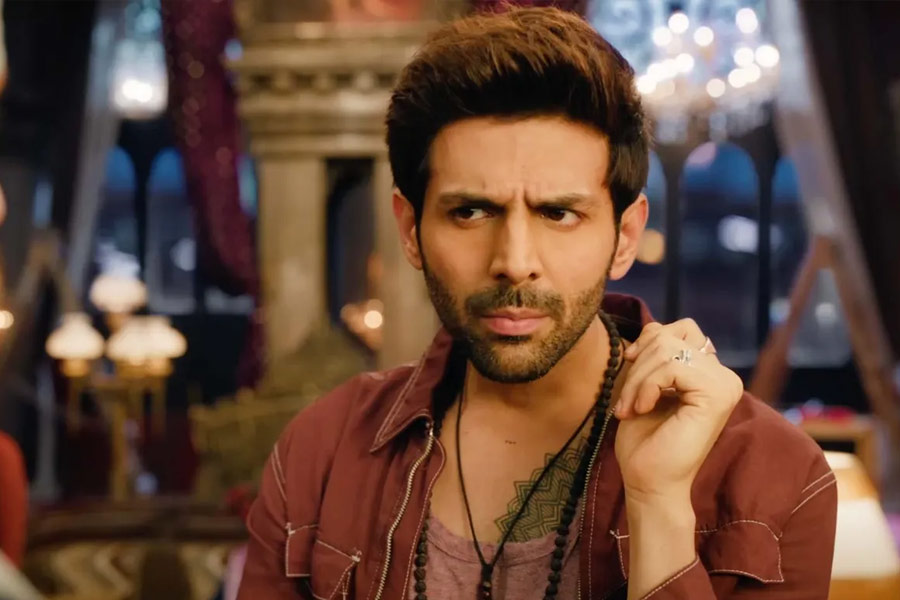পুজো হোক, কিন্তু সুকুমার কই
জাত বিজাতের নানান ফ্যাচাং দূর করে দিই ঘিচি ঘিচিতাং দুপুরবেলায় পাত পেড়ে তাই, ভাগ করে ভোগ খাচ্ছি সবাই আসুন সবার নিমন্ত্রণ। পুজো আসছে। বিভেদ ভুলে আনন্দযজ্ঞে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন মিলন মুখোপাধ্যায়।জাত বিজাতের নানান ফ্যাচাং দূর করে দিই ঘিচি ঘিচিতাং দুপুরবেলায় পাত পেড়ে তাই, ভাগ করে ভোগ খাচ্ছি সবাই আসুন সবার নিমন্ত্রণ। পুজো আসছে। বিভেদ ভুলে আনন্দযজ্ঞে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন মিলন মুখোপাধ্যায়।

শিশুকাল থেকে শুনে আসছি নানান বাদ্যযন্ত্র। কত রকমের শব্দ। বাঁশি, সানাই, ওবো, বেহালা, একতারা, বাংলা ঢোল, ঢোলক, সেতার, সরোদ, তবলা, পাখোয়াজ আরও হাজার রকমের। সারা বছর ধরে শুনি। অথচ একটি বাদ্য-যন্ত্র শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা। গ্রামে-গঞ্জে, বরিশাল, কলসকাঠি, কলকাতার শহরতলিতে থাকলে, মাঠে মাঠে কাশবনের ঢেউ, শিউলি গাছের চৌহদ্দিতে ‘ম’ ‘ম’ সুগন্ধ পাওয়া যেত। এখন এই দূরবাসে আকাশ-ভরা থমথমে মেঘ, ছিটেফোঁটা বৃষ্টির ছাঁট বা ঝমঝমাঝম। দূরাগত সেই বাদ্যের শব্দ শোনা যায় না। হৃৎপিণ্ড ধক ধক শব্দে তাসা-পার্টির বাজনা শুনি গণপতি পুজোর সময়। ব্যস।
কুর-কুর নাকুড়-নাকুড় শব্দে আমাদের বাংলার ঢাকের শব্দ শ্রবণে আসে না। পুজোর ক’দিন মণ্ডপের কাছাকাছি পৌঁছালে, তবে নানান শব্দকল্পদ্রুমের বাজারি চিৎকার থেকে কান-খাড়া করে শুনলে অতি ক্ষীণ শব্দ কানে আসে, সেই ঢাকের। হায় মুম্বই। এমন কৃপণ-শব্দের সঙ্গে কল্পনা করুন, শেয়ালদা থেকে লালবাজার অবধি সারা বউবাজার স্ট্রিটের ফুটপাথে সার বেঁধে, ভিড় করে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছেন হরেক গ্রামগঞ্জ থেকে আসা ঢাকিরা। ওই ফুটেই দুলে দুলে, নেচে নেচে ঢাকের পালক নাচিয়ে নাচিয়ে বাজাচ্ছেন বিভিন্ন ঢাকের বোলে। যেন সব্বাই বলছে, ‘বায়না করে, যাও বাবুরা’। যেন, বলছে,
ঠাকুর আসবে কতক্ষণ
ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ
ঠাকুর যাবে বিসর্জন।
আর, সঙ্গে ওদের জুড়িদার কাঁসর এক ঘেয়ে বিভিন্ন তালে বলে চলেছে,
ক্যান-ক্যান-ক্যান-ক্যান?
আসবে যাবে শরৎকালে
শিউলি ফুলের সাত সকালে
পল্লি-পাড়ার ঘুম ভাঙাতে
মানবজমির মন রাঙাতে
বারো মাসেরই পার্বণ।
ঠাকুর আসবে কতক্ষণ...
সদলবলে আসবে ঠাকুর
ঢাকের কাঠির নাকুড়-নাকুড়,
‘চান্দাটি দিন’ গিজতা ঘিচাং
সার্বজনীন বিশাল মাচান
বেঁধে প্রতিমা দর্শন
ঠাকুর আসবে কতক্ষণ...
বিজয়িনীর পুজার আসর
নাটক-গগন বা ঘণ্টা কাঁসর
জগৎজুড়ে বঙ্গবাসী
সবাই ঠাকুর ভালোবাসি,
হরেক রকম ভাষার ভাষী
সবার মুখে ফুটলো হাসি
হাসির ভাষায় তফাত কম
ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ...
জাত বিজাতের নানান ফ্যাচাং
দূর করে দিই ঘিচি ঘিচিতাং
দুপুরবেলায় পাত পেড়ে তাই,
ভাগ করে ভোগ খাচ্ছি সবাই
আসুন সবার নিমন্ত্রণ।
ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ...
নতুন বধূ ও বুড়ি-মা
সিঁদুর আলো ও খুড়ি-মা
দশভুজার যাবার সময়
নাও চেয়ে নাও শান্তি অভয়
ভাসাই সাগরে দর্পণ।
ঠাকুর যাবে বিসর্জন...
বুকের মধ্যে ভক্তি দিও
প্রতিবাদের শক্তি দিও
ন্যায় অন্যায় চিনিয়ে দিও
ভালবাসায় বিকিয়ে দিও
সবাই আত্মীয়-স্বজন।
ঠাকুর যাবে বিসর্জন...
আসছে বছর তাড়াতাড়ি
আসতে হবে নইলে, আড়ি
তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে
ভাই-বন্ধুর বুক জুড়িয়ে
হৃদয়ে লেপেছি চন্দন
ঠাকুর যাবে বিসর্জন...
ঠাকুর আসবে কতক্ষণ
ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ
ঠাকুর যাবে বিসর্জন
কাঁসর ক্যান-ক্যান-ক্যান-ক্যান.....।
পুজোয় ঢাকের ডাকের ছড়া লিখতে লিখতে নানান চরিত্রেরা মগজের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ঢাকের বোলের শব্দের মধ্যে একজনই ছড়াকার সঠিক বের করতে পারতেন তার বাংলা ভাষায় তর্জমা-টাইপ। ছন্দ-মিল ইত্যাদি মিলিয়ে বোলের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত। ছোটবেলার সঙ্গি “আবোল-তাবোলে”র সৃষ্টিকার সুকুমার রায়, তাঁর কথা মনে হল কারণ, এই পুজো-উৎসবের মরশুম সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি পার্থিব জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। আর কোথায় বুকে ব্যথা বাজে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এই মাসের, বলতে গেলে, এই সপ্তাহের ১৯ তারিখ প্রথম বই হিসাবে “আবোল-তাবোল” বেরিয়েছিল। আর, তার আগে ১০ সেপ্টেম্বর ‘হিজিবিজিবিজে’র স্রষ্টা চলে গেছেন।

উৎসবের মরশুমে বরং আনন্দ খুঁজি আমরা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, যেখানে ঢাকের বোলের মানে খোঁজা যায়।...
বগ-বগ টগবগ করে ভাত ফোটে, দুধ ফোটে, পট-পটাস করে পটকা ফোটে। কিন্তু ফুল ফোটার শব্দ কী রকম, কেউ শুনেছেন? ফুল ফোটারও শব্দ হয়, আমরা শুনিনি, জানি না। একজনই শুধু জানতেন। শুধু তাই নয়, ছল-ছলাৎ শব্দে জলে নৌকো বয়, ঝড়-ঝঞ্ঝার শব্দ বয় সোঁ সোঁ করে। কিন্তু ফুলের গন্ধ ফোটার শব্দ কেউ শোনেনি কী রকম? একজন শুনেছেন। সারা পৃথিবীতে স্রেফ একজনই এ সবের শব্দ শুনেছেন, জানেন। তাই, ছড়ার অক্ষরে অক্ষরে সেই ধ্বনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন আজ থেকে একশো বছর আগে
ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা
ফুল ফোটে? তাই বল। আমি ভাবি পটকা!
শাঁই শাঁই পন পন, ভয়ে কান বন্ধ
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?
আবার, আরও কান পেতে মন দিয়ে শুনে সেই ছড়াকার জানিয়েছেন,
হুড়মুড় ধুপধাপ ওকি শুনি বাইরে!
দেখছো না হিম পড়ে যেও নাকো বাইরে।
আরও আছে। জলে কলসি ডোবার মত শব্দ গব গব গবাস করে চাঁদ ডুবে যাবারও শব্দ হয়। যেমন হাত কাটে, পা কাটে, কাটে কাঠ করাত দিয়ে কাঁচ ভাঙার পার্থিব বস্তু ভাঙার মতোই খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাতে কাটে এই রে।
দুড় দাঁড় চুরমার ঘুম ভাঙে কই রে!
এমনি আরও কত আজগুবি কাণ্ডের খাতা-কলমের মাধ্যমে আমাদের দিয়ে গেছেন ছড়াকার সুকুমার রায়। যাঁর সন্তান সত্যজিৎ রায় রেখে গেছেন আমাদের জন্যে অসাধারণ দৃশ্যকল্পময় চলচ্চিত্র এবং যাঁর সুযোগ্য পিতৃদেব উপেন্দ্রকিশোর রায়, যাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর লেখায়, গানে, ছবিতে আর মুদ্রণের কাজে ছড়িয়ে রয়েছে।
এহেন প্রতিভাবান পিতার সান্নিধ্যে মানুষ হয়ে ছিলেন সুকুমার। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ‘মুকুল’ পত্রিকায় দুটি বাক্য রচনা ছাড়া ছাত্রাবস্থায় সুকুমার রায়ের সাহিত্য রচনার কোনও নজির পাওয়া যায় না।
প্রতিভাবান সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তার মানে, আজ থেকে শোয়া শ’ বছরের একটু আগে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, এমন শক্তিশালী, চিন্তাশীল, আজগুবি কল্পনাপ্রবণ লেখক বা ছড়াকার আর দ্বিতীয় কোনও নাম অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর জন্মের আগেও নয়, পরেও নয়। অন্তত বাংলাভাষায়। অথচ, আজকের প্রজন্মের ক’জন তাঁর নাম জানেন? ক’জন তাঁর লেখা পড়েছেন। কিছু শিশু বা বালককে সুকুমার-প্রেমিক অভিভাবকরা হয়তো আবোল-তাবোলের দু’একটি ছড়া মুখস্থ করিয়েছেন এবং তাঁরা সেই ছড়াটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাখিপড়ার মতো আবৃত্তি (এই মুম্বইয়ের বেশির ভাগ বাঙালির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছি, উক্ত ‘আবৃত্তি’ শব্দটাকে অম্লান বদনে উচ্চারণ করেন ‘আব্বৃত্তি’!!) করে উগরে দেয়।
এ তো গেল এই প্রজন্মের কথা। অথচ, যাঁরা যৌবনে বা মধ্য বয়সের সময় সাঁতরাচ্ছেন, তাঁদের কাছে একটি প্রশ্ন। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জতীয় মনীষীদের জন্মদিনটি আমরা সাধারণত ভুলি না। এত সব বাঙালি কবি, সাহিত্যিক, ঋষি, মুনি, মনীষীদের শতবর্ষ, সার্ধ-শতবর্ষ বা দ্বি-শতবর্ষ বেশ ঘটা করে উদ্যাপন করি। সামগ্রিক ভাবে না হলেও ছোট ছোট দলে, গোষ্ঠীতে বা পাড়ায়-পাড়ায়। অথচ বাঙালিদের গর্ব ‘বাংলা’ ভাষায় একমাত্র আজগুবি কল্পনার একমেবাদ্বিতীয়ম সাহিত্যিক-শিল্পী-ছড়াকারের জন্মের ১২৫টি বছর সম্পূর্ণ হল সম্প্রতি এবং আমরা কেউ তাঁর জন্মদিনটি মনে রাখলুম না।
‘বাংলা’য় বলেই কি? কারণ, একই ধরনের আজগুবি (ননসেন্স) বিলিতি সাহিত্যকলাকার জন্মেছিলেন ঠিক দুশো বছর আগে। এডওয়ার্ড লিয়ার। ননসেন্স সাহিত্য যেখানে ঘোড়ার ডিমও তোড়ায় বাঁধা পড়েঅসম্ভব সম্ভবের সেই রাজ্যের দুই দিকপাল। একজন ইংরিজি ভাষায় লেখার জন্যে বিশ্বখ্যাত, অন্য জন আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় লিখেছেন বলেই বঙ্গভূমের বাইরে প্রায় অজানা, অচেনা। কী দুর্ভাগ্য? তাই বলে আমরা কেন ভুলে যাব? না, ভুলতে চাই না বলেই এই লেখাটি। যাতে অমন মানুষকে আমরা, অন্তত বাঙালিরা সহজে বিস্মৃত না হই। অমন প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও বিচিত্রমুখীনতা মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুন।
১৮৮৭ থেকে ১৯২৩।
ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সুকুমার রায় কত দিকে যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুমুখী ভাবনা ও কাজ। কী প্রচুর প্রাণশক্তি, উদ্যম ও উদ্যোগ। কলেজ ছাড়ার কিছু দিনের মধ্যেই ‘ননসেন্স ক্লাব’-এর প্রতিষ্ঠা। সুকুমার-সাহিত্যের মূল ধারাটি কোন দিকে প্রবাহিত হবে, তার প্রথম ইঙ্গিত এই ক্লাবের নামকরণের মধ্যেই পাওয়া যায়। (প্রসঙ্গত, পরবর্তী কালে বহু যুগের পর সম্পাদক-লেখক দীপ্তেন সান্যালের পত্রিকা ‘অচলপত্রে’ হয়তো এরই অনুসরণ করেছে।) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে এ হেন ক্লাবের জন্য লেখা ছয়টি নাটক‘ঝালাপালা’ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ এবং পরের ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’-র পাতায় সুকুমারের হাস্যরসের প্রথম পরশ পাওয়া যায়। দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশি সার্থক ও উপভোগ্য। মুম্বইয়ের বিখ্যাত সংস্থা ‘সাহানা’র প্রযোজনায় উদয়ন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় এই নাটকটি কিছু দিন আগে এই সুদূর পশ্চিমের শহরে যথেষ্ট সুনাম করেছিল। কিন্তু প্রথমটিতেও মৌলিক পরিচয় যে একেবারেই নেই, তা নয়। ভাষাকে অবলম্বন করে হাস্যরসের সৃষ্টি সুকুমার-সাহিত্যের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। ‘ঝালাপালায়’ যেমন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। পাঠশালার ছাত্র চেষ্টা করে তার পণ্ডিতমশাইকে ইংরিজি কথার মানে জিজ্ঞেস করছে

কেষ্টা, ‘আই গো আপ, ইউ গো ডাউন’ মানে কি? পণ্ডিত‘আই’‘আই’ কিনা চক্ষু, ‘গো’ গয়ে ওকারে গো।
গৌ গাবৌ গাবঃ ইত্যসরঃ । ‘আপ’ কিনা আপঃ সলিলাং বারি, অর্থাৎ জল। গরুর চক্ষে জল। অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে।
কেন কান্দিতেছে? না, ‘উই গো ডাউন’। কিনা, ‘উই’ অর্থাৎ যাকে বলে উই পোকা‘গো ডাউন’ অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামখানায় উই ধরে আর কিছু রাখল না। তাই না দেখে, ‘আই গো আপ’গরু কেবলই কান্দিতেছে।
‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকে রামায়ণের অমন মহাকাব্যের জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে চরিত্রদের আধুনিক করেছিলেন সুকুমার একশো বছর আগে। পুঁইশাক চচ্চড়ি বাইগেট কোম্পানি, হোমিওপ্যাথি, ব্যায়ামবীর স্যান্ডো, রেকারিং ডেসিম্যাল ইত্যাদিও অনায়াসে স্থান পেয়ে গেছে এই নাটকে। এমনকী এ হেন ‘রামায়ণ’এ হনুমান বাতাসা খায়, যমদূতের মাইনে বাকি পড়ে, সুগ্রীব জখম পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধে, বিভীষণের দাড়ির গন্ধ জাম্বুবানের বিরক্তি উদ্রেক করে। সহজ সুরে, সহজ ছন্দে রচিত গানগুলিও নাটকের কাব্যরস চমৎকার ভাবে ছড়িয়ে দেয় দর্শক-শ্রোতার মধ্যে।
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র সুদর্শন, উজ্জ্বল, আনন্দময়, সুভদ্র মানুষটি স্বল্প আয়ুষ্কালে বহুমুখী চর্চায় প্রতিভা ও স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন সেই সময় বিজ্ঞান, ফোটোগ্রাফি, মুদ্রণ প্রযুক্তি, সন্দেশ-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা, ‘ননসেন্স’ ক্লাব, ‘সন্ডা’ ক্লাব (সানডে ক্লাবের ভাষান্তরে) চালনা, সঙ্গীত রচনা, আপন কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তার ‘ইলাস্ট্রেশন’ এমন বহুমুখী প্রতিভাধর আর তো কাউকে তেমন খুঁজে পাই না। এছাড়াও, প্রবন্ধে, গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, শিশু-সাহিত্যে এক ডজনেরও বেশ বইয়ের রচয়িতা।
পিতা উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘আবোল-তাবোলে’ প্রকাশিত (১৯১৪) প্রথম ছড়া ‘খিচুড়ি’তেই সর্ব প্রথম সুকুমার সাহিত্যের বিচিত্র উদ্ভট প্রাণীর আবির্ভাব। এখানে প্রাণীর জন্ম হয়েছে স্রেফ বাংলাভাষার কারসাজিতে—
“হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু, কেমনে তা জানি না।”....
এই উদ্ভট খেয়ালি নিয়মেই লেখকের কলমে এবং কল্পনায় জন্ম নিল বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাশিম। শুধু নামকরণেই শেষ নয়। এ হেন সব উদ্ভট-আজগুবি প্রাণীদের দেখতে কেমন, তারও নমুনা সব স্বহস্তে এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল। বিলেতের আজগুবি কবি এডওয়ার্ড লিয়ারের সঙ্গে কিছু লোক সুকুমারের লেখার তুলনা করেছিল বটে, কিন্তু ইংরিজিতে যে সব আজগুবি প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, তাদের কাউকেই আমাদের পরিচিত চেনা-জানা গণ্ডীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, ডং, জাম্বলি, পব্ল, কাঙ্গল-ওয়াঙ্গল।
আমাদের ‘হুকোমুখোর’ বাস কিন্তু বাংলাদেশে। শুধু তাই নয়,
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার
আর তাই কেহ নাই এ ছাড়া।
ঠিক তেমনই ট্যাঁশগরুকে অনায়াসে দেখা যায় হারুদের আপিসে। কিম্ভুত কেঁদে মরে ‘মাঠপাড়ে গাটপাড়ে’। কুমড়োপটাশও নিশ্চয়ই শহরের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেন। নইলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের শহরবাসীদের এতটা সতর্ক থাকার প্রয়োজন হত না। একমাত্র রামগরুড়ই দেখি সঙ্গত কারণেই নিরিবিলি পরিবেশ বেছে নিয়েছেন। সেও কোনও রূপকথার রাজ্যে নয়, ঠিক বাস্তব রাজ্যও বলা যাবে না। আসলে এটি কবির একটি নিজস্ব জগৎ। এই জগতের সৃষ্টিই হল সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
পুত্র সত্যজিৎ রায়ের মতে, ‘সন্দেশ’এ প্রকাশিত ছোটগল্প ‘দ্রিঘাংচু’ই তাঁর পিতার শ্রেষ্ঠ রচনা কয়েকটির মধ্যে অন্যতম। সহসা এক রাজসভায় একটি দাঁড়কাক প্রবেশ করে, গম্ভীর কণ্ঠে ‘কর’ শব্দটি উচ্চারণ করার ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাই নিয়েই গল্প। গল্পের শেষে রাজামশাইকে রাজপ্রাসাদের সেই ছাদে সেই দাঁড়কাকের সামনে দাঁড়িয়ে চার লাইনের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। মন্ত্রটির একটি দশ লাইনের সংস্করণ সুকুমার তাঁর নাটক ‘শব্দকল্পদ্রুম’-এ বৃহস্পতি মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, মন্ত্রটি হল—
হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দীভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানামামা
চিনে বাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসানে উড়ে মলি
ধর্মতলা কর্মখালি।
খাঁটি ননসেন্সের চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া ভার। কোথায় যে এর সার্থকতা, এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সামান্য অদলবদল করলেই, কেন যে এর অঙ্গহানি হতে বাধ্য, তা বলা খুব কঠিন। এর অনুকরণ চলে না, বিশ্লেষণ চলে না। জিনিয়াস ছাড়া এর উদ্ভাবন সম্ভব নয়। এই ‘খেয়াল রস’ কিন্তু ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের নবরসের অন্তর্গত হয়। সুকুমার রায় উদ্ভাবিত এটিকে দশ (সুকুমারের কায়দায়) বা ‘সাড়ে নবরসের’ মধ্যে ফেললে কেউ আপত্তি করবেন না। আলঙ্কারিক ছন্দ ও শব্দসম্ভারের তুলনা নেই। তবে হ্যাঁ, এ হেন রসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অনামী ভাবুকের গ্রাম ছড়ায়। যেমন—
আইকম্ বাইকম্ তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি
রেলরুম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।
তবে খাঁটি সাহিত্যিক যে ভাবে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে উদ্ভট হাস্যরস পরিবেশন করেন, তার কোনও লক্ষণ কোনও গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যাবে না।
তাই সুকুমারের হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের মতো একদিন এসেছিল একের পর এক ফুল ফোটার চমকে। কিন্তু আপন সৃষ্ট সেই খেয়ালি স্রোতে ভাসতে ভাসতেই কখন ঘনিয়ে এসেছিল ঘুমের ঘোর নিতান্ত ক্ষণজন্মার মতোই, অসময়ে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে ক’দিনের কালাজ্বরে গানের পালা সাঙ্গ করে চলে গিয়েছিল তরুণ সুকুমার।
“আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।
জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনও রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আসুন, তাঁর এই ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা নতুন করে আরবার সুকুমার রায় পড়ি শিশুর মতো লাগামছাড়া হেসে।
ছবি: দেবাশিস ভাদুড়ি।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy