
গড়ে তুলি বাঙালির ‘জাতীয়’ বা ‘ন্যাশনাল’ ইতিহাস ও সংস্কারের উদ্যোগ
বঙ্গীয় আধুনিকতার যে ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্ব ব্রাহ্ম সমাজের আনুকূল্যে চলে আসছিল, অর্থাৎ রামমোহন এলেন আর আলো এল— সেটি খারিজের উৎকণ্ঠা যেন দেখি বঙ্কিমের ইতিহাস-ব্যাখ্যায়।পাশ্চাত্য অর্থে ‘ইতিহাস’ নামক ভাষার ও হেতু-পরম্পরার এক বিশেষ রীতি মেনে গড়া বৃত্তান্তটি বাঙালির নেই... লিখছেন স্বপন চক্রবর্তী

স্বপন চক্রবর্তী
বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, বাঙালির ইতিহাস নেই এমন নয়, অথচ আমরা নানা অতিকথা গিলে আর পরের মুখে ঝাল খেয়ে সেই অতীতের কথা ভুলে গিয়েছি। বখতিয়ার খিলজি সতেরো জন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে নিয়ে তামাম বাংলা জিতে নিলেন, মিনহাজউদ্দিনের এই ‘উপন্যাস’ নিছকই গল্পকথা। একে বাংলার ‘ইতিহাস’ বলতে অস্বীকার করেন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮০ সালের এক প্রবন্ধে। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ নামের সেই প্রবন্ধে বঙ্কিম চেয়েছিলেন ‘প্রমাণ’: গৌরবের প্রমাণ, অগৌরবেরও। বাংলার অতীত থাকলেও ‘ইতিহাস’ নেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য অর্থে ‘ইতিহাস’ নামক ভাষার ও হেতু-পরম্পরার এক বিশেষ রীতি মেনে গড়া বৃত্তান্তটি বাঙালির নেই। বাঙালির ইতিহাস লিখতে হবে। ‘যে বাঙালি, তাহাকেই লিখিতে হইবে।’
একই কথা বলবেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি বাংলা ভাষায় ইতিহাস সম্পর্কিত প্রথম সাময়িকপত্র ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ প্রকাশ করেন ১৮৯৮ সালে। পত্রিকাটি চলে ১৯১১-’১২ সাল অবধি। বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু পরেই স্বদেশি আবেগের আবহে ঐতিহাসিক গবেষণার ‘বৈজ্ঞনিক’ রীতি স্থির করে জাতিসত্তা নির্মাণের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। বাঙালির ইতিহাস নেই। ‘বাঙ্গালী নিজে চেষ্টা না করিলে সে ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না।’ ১৯০৭ সালে লেখা ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ নামের প্রবন্ধ থেকে বাক্যটি উদ্ধার করলাম। সেখানে অক্ষয়কুমার আরও বলছেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বাংলার সংস্রব থাকলেও ‘বাঙ্গালাদেশের বিশেষত্বের অভাব নাই’। আধুনিক রীতিতে ইতিহাস লেখার আয়োজনে বঙ্গদেশ যে আর সব প্রদেশ থেকে খানিক পিছিয়ে আছে, এ কথাও তিনি বলেছেন অন্যত্র।
অদ্ভুত চক্রক। ইতিহাস রচনা করবে ‘বাঙালি’ নামক জাতি, আবার সেই ইতিহাসজাত বাঙালি লিখবে ‘ইতিহাস’ নামক বয়ান। এই চক্রে ঘুরে হয়রান হয়েছিল উনিশ শতকের বাঙালির নিজ জাতিপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা। হিন্দু কলেজের কালাপাহাড়ির কাল পেরোবার পর এই বৃত্তাকার কক্ষপথটি স্পষ্ট হয়। আমরা পরাধীন, বিশ্বজনীন আধুনিকতার দরবারে আমরা কোণঠাসা। তবে এ বার ঘরে ফিরি, গড়ে তুলি বাঙালির ‘জাতীয়’ বা ‘ন্যাশনাল’ ইতিহাস ও সংস্কারের উদ্যোগ— এই জিনিস একেবারে স্বদেশি পর্ব পর্যন্ত ছিল, সন্দেহ নেই। তার চাইতেও জরুরি কথা, পশ্চিমের ধারায় শিক্ষিত বাঙালির পরের প্রজন্ম বিজেতাদের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে এক অন্তর্ঘাতী সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল। নিউটনের মেধা, শেক্সপিয়র ও বায়রনের কাব্যরস এবং ছাপাকলের উত্তেজনা বঙ্গদেশের আঙিনায় আছড়ে পড়েছিল প্রায় একই মুহূর্তে। কথাটা অনেকেই খেয়াল রাখেন না। ‘আধুনিক’ বাঙালি হওয়া মানে কেবল জাতীয় খোলে গুটিয়ে যাওয়া নয়, বরঞ্চ তা পাশ্চাত্য ইতিহাসের সদৃশ বয়ানের চাইতে এগিয়ে— এটা প্রমাণের তাগিদ অনুভব করেছিলেন বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেক চিন্তক, তাঁদের দেশীয় কুসংস্কারের সমালোচনা যতই তীব্র হোক না কেন।
বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই ধরা যাক। তিনি মনে করতেন বঙ্গদেশে এক বৌদ্ধিক আলোড়ন হয়েছিল বটে। তবে সেটি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে নয়, চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন যে, তুলনায় তাঁর কালের বাঙালি ছিল প্রান্তিক, নিজেদের ইতিহাস জানতে পর্যন্ত শাসকদের মুখাপেক্ষী, সৃষ্টি-জ্ঞানে-কর্মে আত্মবিস্মৃত এক জাতি। লেখাটিতে তিনি যে ঐতিহাসিক মডেলটির প্রসঙ্গ পাড়ছেন সেটি কিন্ত ইউরোপীয় রেনেসেন্সের। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতরা এলেন ইতালি ও পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে, আরম্ভ হল নতুন করে গ্রিক-লাতিন ভাষার তালিম, ধ্রুপদি ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার-সম্পাদনা-মুদ্রণ-তর্জমা, ধ্রুপদি ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির সমবায়ে শিক্ষা ও সভ্যতার সৃষ্টি-নির্মাণ-সংস্কার— এই গণপাঠ্য ভাষ্যের আদলে তিনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ‘Renaissance’ ব্যাখ্যা করলেন, প্রয়োগ করলেন ইংরেজিতে শব্দটিও লাতিন হরফে। ইউরোপে পেত্রার্কা, গালিলেও, লুথার, বেকনরা যা করেছেন তার তুলনা তাঁর কালের বঙ্গদেশ নয়। ‘আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যোচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।’ রূপ-সনাতন আদতে কর্নাটকের লোক কি না, তাঁদের পূর্বসূরিদের ভাষা তেলুগু ছিল কি না, এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তখন তাঁরা চৈতন্য-পরিকর, যদিও মহাপ্রভুর শিষ্যেরা সকলে বঙ্গভাষী ছিলেন না। বঙ্কিম এর পর রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, রঘুনন্দনের মতো দার্শনিক ও স্মৃতিকারদের, এবং চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরগামী কবিদের নাম করেছেন। বিদ্যাপতিও আছেন ফর্দে, তাঁর বাঙালিয়ানা নিয়ে বোধহয় তখন সংশয় কম ছিল।

বঙ্গদেশে যে এক কালান্তরের পর্ব চলছে, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই জানতেন। না জানলে তিনি চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের আপত্তি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য রীতিতে উপন্যাস লিখতেন না, তাও প্রথমটি ইংরেজিতে। না জানলে তিনি মধুসূদন-দীনবন্ধুর গুণের কদর করতেন না, শিক্ষিত পাঠকসাধারণের রুচি সংশোধনের স্বার্থে ‘বঙ্গদর্শন’ কাগজের মারফত সৎ সাহিত্যের নিরিখ তৈরি করতে সচেষ্ট হতেন না, কৃষ্ণ থেকে কঁত পর্যন্ত নানা মনীষীর থেকে রসদ জড়ো করে প্রাচীন সভ্যতাচ্যুত অথচ নতুন করে সচেতন হয়ে ওঠা এক জাতির লক্ষ্য নির্ণয়ে এত মেধা খাটাতেন না। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধে বাঙালির ইতিহাস রচনার ম্যানিফেস্টোও লিখতেন না তিনি। কিন্তু বঙ্গীয় আধুনিকতার যে ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্ব ব্রাহ্ম সমাজের আনুকূল্যে চলে আসছিল, অর্থাৎ রামমোহন রায় এলেন আর আলো এল— ক্রমে নয়, অতর্কিতে, সেটি খারিজ করার উৎকণ্ঠা যেন দেখি বঙ্কিমের ইতিহাস-ব্যাখ্যায়। পুরাণেতিহাস এবং তার সাকার উপাস্যকে অযৌক্তিক বলে মানলেও হিন্দু ‘লোকবিশ্বাসের...গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি’ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তিনি বহু বার, যেমন ১৮৭৫ সালের ‘ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কী বলে’ লেখাটিতে। যাঁরা বঙ্কিমের ‘লোকশিক্ষা’ প্রবন্ধটি পড়েছেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন রামমোহনের ব্যর্থ চেলাদের সঙ্গে মহাপ্রভুর সফল ধর্মপ্রচারের জোরালো, হয়তো-বা অস্বস্তিকর তুলনার কথা। ১৯০৫ সালে ছাপা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ বইতে ‘সমাজের কথা’ পড়লেও স্পষ্ট হয় যে, রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা রামমোহনের অনুরাগী তাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ গরজ ছিল। গরজ ছিল প্রমাণ করার যে, কোনও স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না রামমোহন। তন্ত্রশাস্ত্রেই রয়েছে ব্রাহ্ম মতের উৎস— এমনটাই বলতে চেয়েছেন ভূদেব। ‘ফলকথা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রাজা রামমোহন রায় নিজে একটী নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিবেন এরূপ অভিমানে সম্বন্ধ হয়েন নাই।’
আরও পড়ুন: বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব না বুঝিয়ে মানুষকে তাঁর কথা সরল ভাবেই বোঝানো যেত
কিন্তু ইতিহাসের কথাই যখন হচ্ছে, তখন খটকা লাগে ভেবে যে, কেন উনিশ শতকে পৌঁছে জাতিপরিচয় নিয়ে এতটা উদ্বেগ ও আগ্রহ বোধ করল বাঙালি? এমনকি, যার মাতৃভাষা বাংলা সেই বাঙালি, এমন সংজ্ঞার্থের প্রস্তাব কেন করতে হল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে ১৯০৭ সালে ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ প্রবন্ধে? সেই শশাঙ্ক থেকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অবধি বাংলার প্রতাপের কথা তো পড়ি ইতিহাসে, পালরাজাদের সময়ে বাংলার নৃপতিরা সাম্রাজ্য পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার সুতি, রেশম আর আফিম তো মোগল আমলের শেষ দিকেও ছিল আর্থিক বৈভব ও রাজনৈতিক বিবাদের হেতু। বলতে পারেন, স্বদেশি আন্দোলনের তাগিদ ছিল এমন শিকড় এবং সংহতির সন্ধানের নেপথ্যে। কিন্তু তাতে তো সব কথা বলা হল না। বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন ঢের আগে থেকে। ও দিকে হিন্দু মেলা প্রথম বসিয়েছিলেন ডিরোজিওর এককালের শিষ্য রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৭ সালে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে মিলে।
বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রই ঠিক ধরেছিলেন। বাঙালির জাতিপরিচয়ের সঙ্কট ছিল পরতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। মহাপ্রভুর সময়ে বাঙালি পরাধীন সে অর্থে ছিল না, যে অর্থে সে ছিল কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনে। রাজার যদি হয় পরদেশে বাস, তবেই আসল ‘পরতন্ত্র’। তুর্কি-পাঠান-মোগলরা ছিল বাংলার শাসকদের— তাদের জাতিপরিচয় যাই হোক, অধিরাজ। বিদ্রোহ না করলে নবাব-সুলতানদের কালে বাংলা ছিল কার্যত স্বশাসিত। ‘লিবার্টি’ মানে স্বাধীনতা, ‘ইন্ডিপেন্ডেন্স’-এর অর্থ স্বতন্ত্রতা। বাঙালি বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে এক পরতন্ত্র কারণ ‘ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই’। ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা’ প্রবন্ধে বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র: ‘যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনরূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।’ যতই ‘লিবার্টি’র কথা বলুন ডিরোজিও ও রামমোহনের শিষ্যেরা, আসল সমস্যা রাজনৈতিক পরতন্ত্র। মনে রাখতে হবে, হিন্দু মেলার এক দশক আগেই মহাবিদ্রোহ, যে বিদ্রোহ ছিল নব্যবাঙালির সমর্থন বঞ্চিত। এবং মহাবিদ্রোহের পরের বছরই ঘটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অবিভক্ত ভারতের অন্তর্ভুক্তি।
চৈতন্যদেবের সময়কে বাংলায় শিক্ষা-সংস্কৃতির এক নবজন্মের (বা নবায়নের বা নবজাগরণের— renaissance শব্দের একাধিক অর্থ) কাল বলে শনাক্ত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই আলোড়নের প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রসঙ্গ তোলেন, স্মরণ করেন পেত্রার্কার কথা। নেপাল থেকে ‘ডাকার্ণব’ সহ বিভিন্ন দোহাকোষ এবং চর্যার পুঁথি এনে সম্পাদনা করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী, বঙ্কিমের মতো তাঁরও বাড়ি ছিল নৈহাটিতে। বঙ্গদেশে দীনেশচন্দ্র সেন ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতো তিনি ছিলেন ইউরোপীয় অর্থে ‘হিউম্যানিস্ট’— মানবিকীবিদ্যার মৌল রসদ হিসাবে যাঁরা পুথি-পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন, এ গোত্রের বিদ্বান। তাঁর কি সায় থাকত বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তে?
সম্পূর্ণত হয়তো নয়। হরপ্রসাদ চেয়েছিলেন ইংরেজ শাসনে বাংলার বিদ্যাচর্চায় যে অনুকূল বায়ু বইছে তার সদ্ব্যবহার করতে। ১৮৮৬ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এক ভাষণে তিনি ইউরোপীয় রেনেসেন্সের তুলনা করেন তাঁর নিজের কালের বঙ্গদেশের সঙ্গে, চৈতন্যদেবের সময়ের সঙ্গে নয়। তখন ইউরোপে ‘গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল মাত্র’। অন্য দিকে এখন বাংলায় ‘কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি’। এই বলে তিনি পুরনো বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য, ইংরেজি, মায় ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় সাহিত্যকে বাঙালির বিস্তৃত পাঠ ও চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে দেখাতে চাইলেন। ‘এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে?’ এর বিশ বছরের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে এক সংগ্রহশালায় বাঙালির জাতিপরিচয়ের যাবতীয় স্মারক একত্র করার চেষ্টা হবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো কর্মঠ মানুষের নেতৃত্বে। অথচ হরপ্রসাদ চাইছেন এক ব্যাপক বিশ্বজনীন পরিচয়। পরিষদের রজতবর্ষ পূর্তিতে সচিব রামেন্দ্রসুন্দর জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা এশিয়াটিক সোসাইটির আদলে গড়া এক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁদের কাজের পরিসর তুলনায় ছোট। তাঁদের ক্ষেত্র বঙ্গদেশ, এশিয়া মহাদেশ নয়। এর সঙ্গে হরপ্রসাদের উচ্চাভিলাষের তুলনা করুন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং হরপ্রসাদের প্রস্তাব এক হিসাবে পরস্পরের সম্পূরক। দু’জনেই চাইছেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের বিস্তার, এক আধুনিক বিশ্বজনিনতা। বঙ্কিমচন্দ্রে তার ঐতিহাসিক প্রতিরূপ এক স্বাধীন অতীতে, হরপ্রসাদের বিচারে তার আসন্ন সুযোগ পরাধীন বঙ্গদেশে। বাঙালির জাতিপরিচয়ের সঙ্কট রয়েছে এই দুই প্রস্তাবের আপাতবিরোধে।
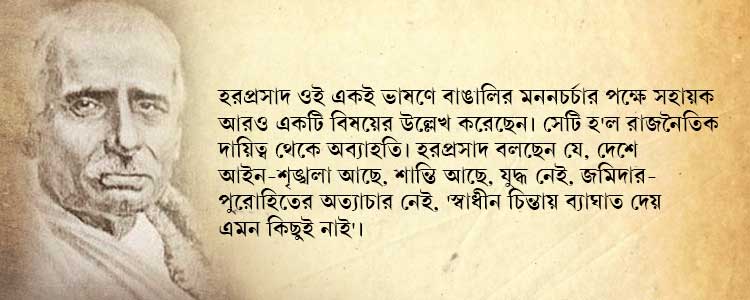
মনন ও সৃষ্টির ‘স্বাধীনতা’র খাতিরে হরপ্রসাদ রাজনৈতিক ‘পরতন্ত্র’ মেনে নিতে কি রাজি ছিলেন? তেমনই তো মনে হয়। হরপ্রসাদ ওই একই ভাষণে বাঙালির মননচর্চার পক্ষে সহায়ক আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেটি হ’ল রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। হরপ্রসাদ বলছেন যে, দেশে আইনশৃঙ্খলা আছে, শান্তি আছে, যুদ্ধ নেই, জমিদার-পুরোহিতের অত্যাচার নেই, ‘স্বাধীন চিন্তায় ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই’। ‘স্বাধীন’ শব্দের এই প্রয়োগ খেয়াল করার মতো। হরপ্রসাদের রাজনৈতিক অভিপ্রায় অথবা অভিপ্রায়হীনতা ফাঁস করে দেয় তার পরের বাক্যটিতে আবার ‘স্বাধীন’ শব্দের ব্যবহার: ‘স্বাধীন দেশে, দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচারকার্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙালির অদৃষ্টে এ-সকল কার্যের জন্য ইংরেজ আছেন।’ কথাটার মধ্যে শ্লেষটুকু মেনে নিলেও ঠিক কাদের পক্ষে দেশীয় রেনেসেন্সের বায়ু অনুকূল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। রোজগারের দায়িত্বের কথা তো নেই, অন্তত সরাসরি নেই। ধরে নিচ্ছি পরতন্ত্রে লাভ আছে যাদের, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে যারা ধনী অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষান্তে চাকরি যাদের জুটবেই, তাদের কথা ভেবেই লেখা কথাগুলি। রবীন্দ্রনাথ থেকে সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বিদ্যাসাগর থেকে সমর সেন— অনেকেই এমন নিশ্চেষ্ট বাঙালিয়ানা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। মুড়ি-মিছরি এক করে ফেললেও এবং রাষ্ট্রসর্বস্ব অতিশয়তার বিকল্পের কাছে মনন সঁপে দিলেও বাংলার নবজাগরণের অনেক মহারথীর শ্রেণি-অবস্থান সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙালি নকশালপন্থীদের বিশ্লেষণ অনেকাংশে ঠিক ছিল, এ কথা অসংকোচে স্বীকার করে নেওয়ার সময় হয়েছে।
বাংলার সংস্কৃতির তথাকথিত নবোন্মেষের পর্বের সীমাবদ্ধতার কথা আজ সকলেরই জানা। মুসলমানদের অবদান তখন ছিল বিরল। কারণ হিন্দুরা তখন ছিল, রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষের ভাষায়, ভিন্ন নয়, ‘বিরুদ্ধ’। জাতপাত, বর্ণভেদ ছিল ঘৃণ্য পর্যায়ের, আজও আছে এখানে-সেখানে প্রগতিপন্থার ফ্যাশনদস্তুর মূঢ় পুরোভাগে। স্ত্রীশিক্ষা এগিয়েছিল ঠিক, নারীর স্বাধিকার কিন্তু তেমন বলার মতো বাড়েনি। একসময়ে ধর্মসম্প্রদায়ের ছুরি চালিয়ে বঙ্গদেশ দু-ভাগ করা হয়, আবার ভাষা-সংস্কৃতির শক্তিতে বাংলাদেশ ছিনিয়ে আনে রাজনৈতিক পরতন্ত্র থেকে মুক্তি। ভারতবর্ষ থেকে ‘স্বতন্ত্রতা’র জন্য এককালে সংগ্রাম চালিয়েছিল যে বাঙালি মুসলমান, সে এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করার অসম্ভব ক্লেশে ব্যস্ত।
কিন্তু এ সব ঐতিহাসিক কূটাভাসের গভীরেও রয়েছে বাঙালির জাতিপরিচয় নিয়ে সেই আপাতবিরোধী অথচ সম্পূরক অবস্থান যা আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের মতামতের তুলনা করলে দেখতে পাব। আধুনিক বাঙালির কৃতিত্ব খর্ব করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে হিন্দু বাঙালি এক স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নির্মাণে ব্যর্থ হয়, কারণ তেমন স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা হিন্দু বাঙালির মধ্যে ছিল ঈষৎ দূর্বল। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের নামের তালিকা সাজিয়ে সহজাত মেধার সাক্ষ্য পেশ করা যায়, জাতীয়তা নির্মাণের সাফল্য দাবি করা যায় না। যে মেধা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরতন্ত্রের সুবাদে ‘স্বাধীন’ হয়ে তৃপ্ত, সেই মেধা রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থার নেতৃত্ব কাঁধে নিতে সতত পরান্মুখ। এ বিষয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পর্যবেক্ষণকে অভ্রান্ত বলেই মনে করি। ‘বাঙালীত্বের স্বরূপ’ নামে এক প্রবন্ধ তিনি লেখেন ১৯৩২ সালে। কবেকার সেই লেখায় এই ধীমান অথচ অপ্রিয়ভাষী লেখক বলেছিলেন: ‘যে অনুকরণশীলতা বাঙালী মনের একটা সনাতন ধর্ম, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর কীর্তি তাহার একটি নূতন প্রয়োগ মাত্র।...বাঙালীত্বের স্বরূপ একটা সর্বতোমুখী ব্যর্থতার তীব্র অনুভূতি বই আর কিছুই নয় তো।’ কথাটা ভেবে দেখলে আমরা ভাল করব।
লেখক: শিক্ষাবিদ
অলঙ্করণ: তিয়াসা দাস
-

কোহলিকে চিনতেই পারছেন না লাবুশেন, ৬ বছর আগের বিরাটকে খুঁজছেন অসি ক্রিকেটার
-

বয়সের ছাপ এড়াতে চান? ৮ উপকরণে তৈরি মাস্কটি মেখে দেখুন, টানটান হবে ত্বক
-

স্টেশনে পরিত্যক্ত স্যুটকেস ঘিরে আতঙ্ক, খুলতেই বৃদ্ধার দেহ! খুনের সঙ্গে জড়িতে সন্দেহে আটক দুই
-

হিরে-জহরত, মণিমুক্তো কিচ্ছু নেই, বদলে রয়েছে এক আঁটি শাক! জানেন সে ব্যাগের দাম কত?
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy







