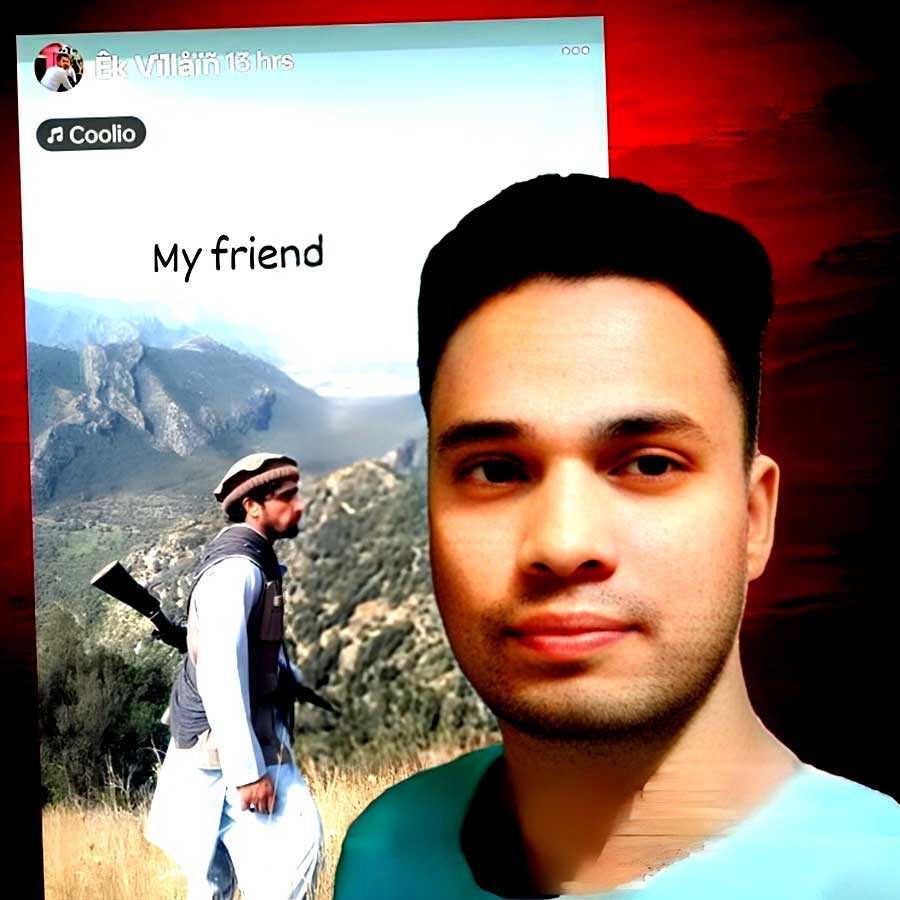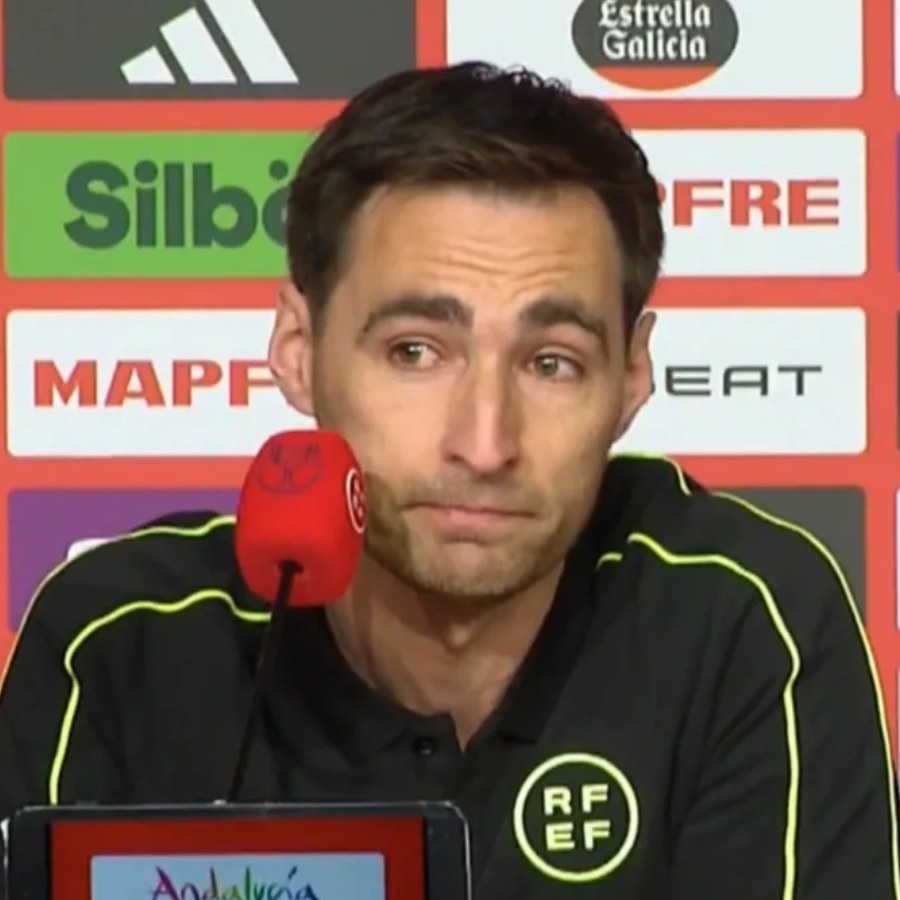অতি দর্পে অতি ক্ষতি, তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের এক্তিয়ার বিষয়ে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়টি তা স্পষ্ট করে দিল। অধিকারের সীমা জোর করে বাড়াতে চাইলে যেটুকু আছে, তা-ও চলে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে রাজ্যপাল কেবলই কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানসম্মত প্রতিনিধি, সংবিধান মোতাবেকই তাঁর ভূমিকা অতি সীমিত, ক্ষমতা অতি সামান্য। অথচ নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রথম থেকেই এই নীতি অমান্য করে আসছে। গত এগারো বছরে বিভিন্ন রাজ্যে— নির্দিষ্ট ভাবে বললে— বিভিন্ন বিরোধীশাসিত রাজ্যে, রাজ্যপাল পদটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে ‘ব্যবহার’ করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবির বিপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায় তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি এক মাইলফলক হয়ে রইল। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করল। সে রাজ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া দশটি বিল রাজ্যপাল স্বাক্ষর না করে আটকে রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক রায় বেরোনোর পরেই তামিলনাড়ু বিধানসভা সেগুলি আইন হিসাবে বলবৎ করেছে, রাজ্যপালের সই ছাড়াই। সংবিধান সূচনার পঁচাত্তরতম বছরে সংবিধানের এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য করা যায় এই ঘটনাকে।
ঐতিহাসিক হলেও বিষয়টি অভূতপূর্ব নয়। বিধানসভার বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা আর লোকসভার বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা যে-হেতু তুলনীয়, সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছে এ দেশের ‘শৈশব’কালেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, এবং সেই সঙ্কটেরও এমন মীমাংসাই হয়েছিল। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্বে হিন্দু কোড বিল উত্থাপিত হতে তীব্র মতসংঘর্ষ তৈরি হয়, রক্ষণশীল সাংসদরা যথাসাধ্য বিলটিকে আটকে দিতে উদ্যত হন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বিলটিতে স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নেন। তদানীন্তন অ্যাটর্নি-জেনারেল সেতলবাদ তখন স্মরণ করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজা বা রানির মতো— আক্ষরিক ভাবেই নেহাত প্রতীকী। জননির্বাচিত প্রতিনিধিসভা দ্বারা সম্মত কোনও প্রস্তাব আটকে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই, কেবল প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকারটুকু আছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও স্পষ্ট, কেননা রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শটি সংবিধানে অন্বিত হয়েছিল। মহামান্য বিচারপতিরা মনে করিয়ে দিলেন, কেবল স্বাক্ষরদানটুকুই নয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বাক্ষরদানও প্রত্যাশিত। রাজ্যের পাশ-করা বিলের ক্ষেত্রে যদি রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির মত না থাকে, তা হলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে, কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিল ফেলে রাখা যাবে না।
সর্বোচ্চ আদালতেরই নির্দেশক্রমে, এই রায়ের একটি করে কপি প্রতিটি রাজ্যের হাই কোর্ট এবং রাজ্যপালের অফিসে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তামিলনাডুর মতোই, এখানেও ২০২৪ ও ২০২৫ সালে পাশ হওয়া কয়েকটি বিল আটকে আছে রাজ্যপালের সই-প্রত্যাশায়, যা রাজ্যপাল নাকি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিবেচনার জন্য আলাদা করে রেখেছেন। তালিকায় আছে বিতর্কিত ‘অপরাজিতা বিল’, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে বেশি অধিকার প্রদানের বিলও। প্রসঙ্গত তামিলনাড়ুর যে ক’টি বিল নিয়ে সঙ্কট ছিল, তার মধ্যে ন’টি শিক্ষা-সংক্রান্ত: বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের অধিকার সংক্রান্ত। ধরে নেওয়া যায়, সেই রাজ্যের পর পশ্চিমবঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্যপালের হাত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই চলে যাবে। গত কয়েক বছরের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে লাগাতার অচলাবস্থার পর হয়তো মীমাংসায় আসা সম্ভব হবে। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্র বনাম রাজ্য দ্বন্দ্বের সুরাহা হলেও তা রাজ্যের পক্ষে একটা প্রাপ্তি, সন্দেহ নেই।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)