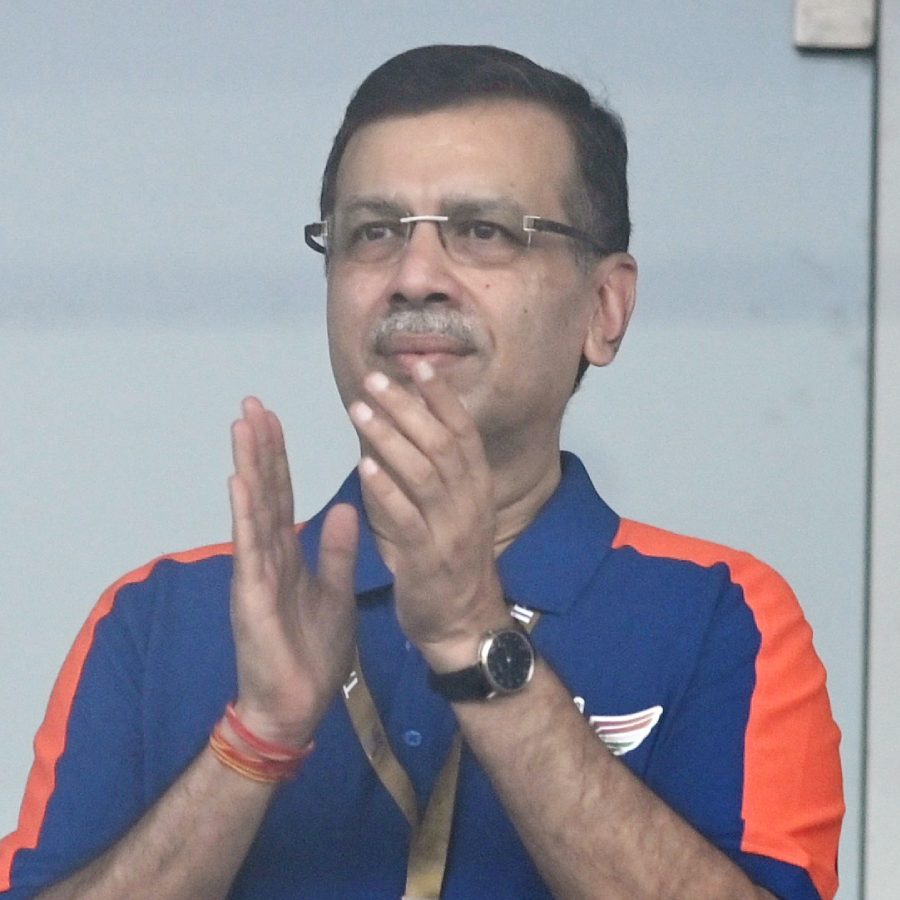‘মা ফলেষু কদাচন?’ (২৪-১) শীর্ষক প্রবন্ধে অশোক কুমার লাহিড়ী বৃক্ষরোপণের পরবর্তী সঠিক পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উপায় ও প্রয়োজনীয়তার কথা যথার্থ আলোচনা করেছেন। বর্তমান পরিমণ্ডলে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি পালন অত্যন্ত প্রশংসনীয় এ কথা অনস্বীকার্য। শুধু ভূমিক্ষয় রোধ নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ ও আবহাওয়ার সমতা বজায় রাখার জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তবে শুধু সরকারি উদ্যোগে নয়, প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও কর্তব্য পালনে সচেতন হতে হবে। কত গাছ লাগানো হয়েছে সে পরিসংখ্যানের চেয়ে অধিক জরুরি কতগুলো গাছ বেঁচে আছে বা থাকল, তার পরিসংখ্যান। সরকারি কর্মসূচিতে টাকা ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগানোর পর যদি কয়েকশো বা হাজার গাছ বেঁচে থাকে, তা হলে সে কর্মসূচি যথাযথ পালন হয়নি বলেই বিবেচিত হবে।
অবশ্যই যথেচ্ছ অরণ্য বিনাশ যাতে না হয় তার জন্য সরকারি নজরদারির সঙ্গে নাগরিক সচেতনতাও বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের কথা যথার্থ যে, মানবশিশু জন্মানোর পরে পদে পদে তার লালন-পালনের জন্য যেমন যত্ন নেওয়া হয়, বৃক্ষরোপণের পর চারাগাছগুলোর প্রতি তেমনই যত্নবান হওয়া উচিত। গ্রহণ করা হোক এমন অঙ্গীকার যে, পরিবারে একটি শিশুর জন্মানোর সঙ্গে তার অভিভাবকের উদ্যোগে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বা রাস্তার পাশে বা কোনও সরকারি জায়গায় একটি বৃক্ষরোপণ করা হবে, যার লালন-পালনের দায়িত্ব পরিবারের লোকেরাই নেবেন। তা হলে বোধ হয় সেই শিশুর বৃদ্ধির পাশাপাশি সেই বৃক্ষেরও যথার্থ যত্ন হবে। প্রবন্ধকার এখানেও সঠিক কথা ব্যক্ত করে উপমা টেনেছেন যে, সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয়ভবন, হাসপাতালভবন বা রাস্তা সংস্কার বা পুকুরপাড় বাঁধানোর মতো সামাজিক প্রকল্পের সাফল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদাসীন না হয়ে কড়া পর্যবেক্ষণের যেমন প্রয়োজন, বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রেও তেমনটা হওয়া উচিত। এনএমসিজি দ্বারা এ দেশের প্রধানতম নদী গঙ্গার সুরক্ষায় যে বিস্তৃত প্রকল্প ‘নমামি গঙ্গে’ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে অন্যতম কাজ গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন করা। তাতে নদীর স্বাভাবিক চরিত্র বজায় থাকবে। অবশ্য এমন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি বিভাগ বিশেষ করে বন দফতরকে তৎপর হওয়ার সঙ্গে কড়া নজরদারি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। না হলে ব্রিটেনের টেমস বা চিনের ইয়াংসি নদীর মতো গঙ্গা নদীর পুনরুজ্জীবন দেখা আমাদের অধরাই থেকে যাবে।
স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০
চারাগাছের মৃত্যু
অশোক কুমার লাহিড়ী তাঁর ‘মা ফলেষু কদাচন?’ প্রবন্ধে ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের আর এক বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ ও তার ব্যর্থতার ঘটনাটির উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্য জুড়ে রাস্তার দু’ধারে প্রচুর নারকেল গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল একশো দিনের কাজের মাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই তার পরের বছরে একটি নারকেল গাছকেও জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি! এর দু’টি কারণ। প্রথমত, নারকেল গাছ পথ-পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ হওয়ার উপযুক্ত নয়। শৈশব, কৈশোরে সেটি দু’পাশে পাতা বিস্তার করে, যা যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। অন্য দিকে, বড় হওয়ার পর তা থেকে ফল, শুকনো পাতা পড়ে পথচারীদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, কেবল নারকেল গাছকেই কেন ওই প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তা এক বিস্ময়। দ্বিতীয়ত, পরিচর্যা ও সংস্কারের অভাব। একটি গাছ রোপণের পর তাকে বেড়া দিয়ে না ঘিরলে এবং নিয়মিত জল, সার না দিলে তা বেড়ে ওঠে না। সেই প্রকল্পে তা-ই ঘটেছিল। মাঝখান থেকে গাছের চারা সরবরাহকারী এজেন্সির যে বিপুল লাভ হয়েছিল, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নেই।
পার্থ পাল, মৌবেশিয়া, হুগলি
অতিসরলীকরণ
‘দাপটের ভাষা’ (২৪-১) সম্পাদকীয় থেকে জানলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর চেয়ারম্যান এম জগদেশ কুমার কলকাতায় এসে গবেষণা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অনুদান বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন সব শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, যা শ্রুতিমধুর মনে হয়নি। চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাতে যুক্ত থাকার সুবাদে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আগেও এসেছে। সেই সূত্রেই দু’-চার কথা বলার চেষ্টা।
গবেষণা প্রকল্পের অনুদান নেওয়ার আগে তার প্রস্তাব (রিসার্চ প্রোপোজ়াল) বানিয়ে পাঠাতে হয় অনুদান প্রদানকারী সংস্থাকে। চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ এমন অনুদান দিয়ে থাকে। এই প্রস্তাবকে যথেষ্ট গুণগত মানদণ্ড পার হতে হয় অনুদান পাওয়ার আগে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন অনেক বেশি জোর দেওয়া হয় এমন গবেষণাতে, যেখানে মূল উদ্দেশ্য খুঁজে বার করা নতুন চিকিৎসা, বা নতুন ওষুধটি রোগীর জীবনে কী প্রভাব ফেলবে। একে বলা হয় ‘পেশেন্ট-সেন্টারড আউটকাম’। সহজে বলতে গেলে— একটি নতুন ওষুধ হাঁপানির রোগীর রক্তের কোনও একটি পরীক্ষাতে ভাল ফল দিল, প্রদাহজনিত বায়ো মার্কার কমিয়ে দিল। কিন্তু সেটি প্রত্যক্ষ ভাবে রোগীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। বহু রোগীর কিছু আসে যায় না রক্তের পরীক্ষাতে কী এল সেটা জেনে, যদি তাঁর সমস্যাটি না কমে। অথচ, যদি দেখা যায় নতুন ওষুধটি রোগীর মাসে যত বার ইনহেলার নিতে হচ্ছে, সেটির সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারছে, তাঁর শ্বাসকষ্টের মাত্রা কমে যাচ্ছে— স্বাভাবিক ভাবেই সেটি অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। কেউ তর্ক করতেই পারেন, নতুন ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে রক্তে একটি বিশেষ প্রদাহজনিত বায়ো মার্কার কমিয়ে দিতে পারা মৌলিক, স্বতন্ত্র গবেষণা। অবশ্যই। তবে সেই গবেষণা বাস্তব জীবনে কী ভাবে প্রভাব ফেলবে, তার কিছু রূপরেখা থাকা জরুরি। মৌলিক গবেষণাই পরবর্তী কালে বৃহত্তর গবেষণার পথ খুলে দেবে এবং এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, যাঁরা অনুদান দেওয়ার নিয়ম নির্ধারক, তাঁদের কিছু মানুষ অবশ্যই একটি গবেষণা অনুদানের জন্যে প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় এই সমস্ত কিছু খেয়াল করে দেখেন, দেখতে চান, এবং দেখার মতো যোগ্যতা রাখেন।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা, গবেষণাপত্রের মূল্যায়নের মাপকাঠিতে স্বচ্ছতা আশা করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একই সঙ্গে সেই গবেষণার ফল দেশের বর্তমান নানা সমস্যাকে কী ভাবে সমাধান করবে, জানতে চাওয়াটা ভুল নয়। এমন গবেষণা যাতে পরিবেশ দূষণ, ক্যানসার, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যার সমাধান হবে— সেগুলির অবশ্যই বেশি প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সেটা করতে চাওয়া মানেই জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষের বদলে ঝকঝকে ‘প্রেজ়েন্টেশন’কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, না ব্যবসায়িক ফয়দা দেখা, এমনটি ভাবা হয়তো অতিসরলীকরণ।
সুমিত রায়, চৌধুরী ডিপার্টমেন্ট অব নিউরো-অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার, এমস, নয়া দিল্লি
ঘোলা জল
কলকাতার বালিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘ দিন ধরে পাইপলাইনে ঘোলা জল আসছে। সেই জলে মিহিবালি, কাঁকর পর্যন্ত থাকে। ঘোলা জলের জন্য বাড়ির নিজস্ব পাইপলাইনের ভিতর সরু হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পাম্পের ক্ষতি হয়। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা চলতে থাকলেও পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। অথচ, এই অঞ্চল থেকে তারা মোটা টাকা কর হিসেবে আদায় করে।
অরুণ কুমার সেন, কলকাতা-১৯
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)