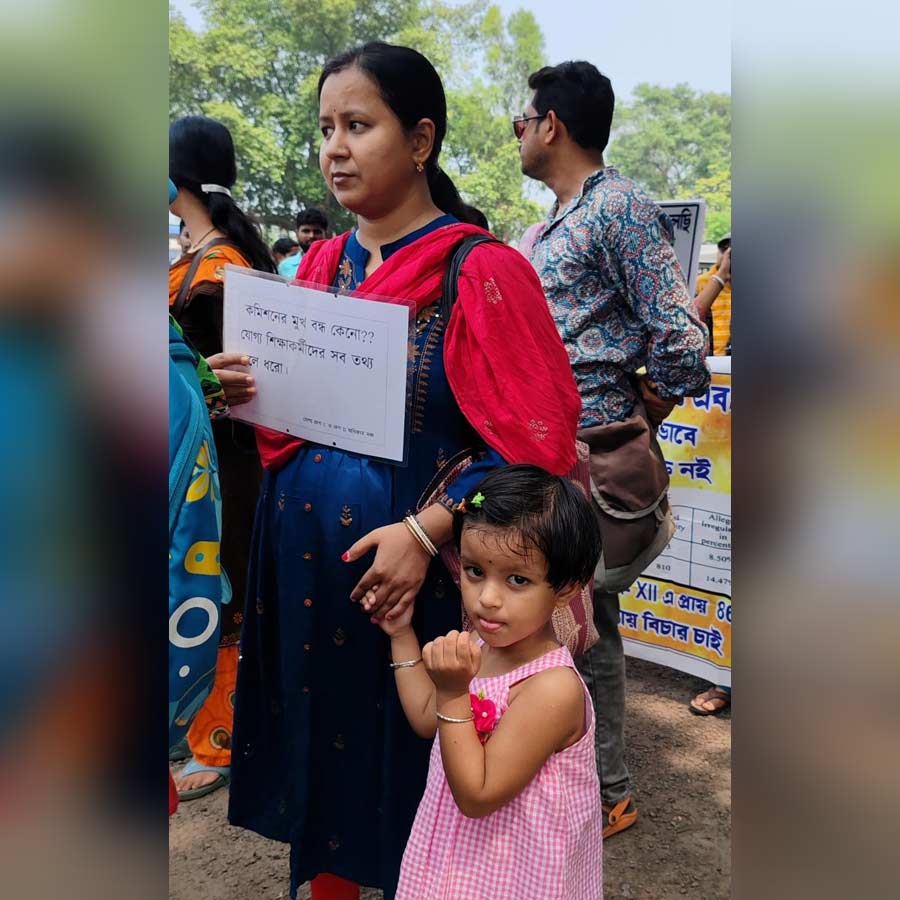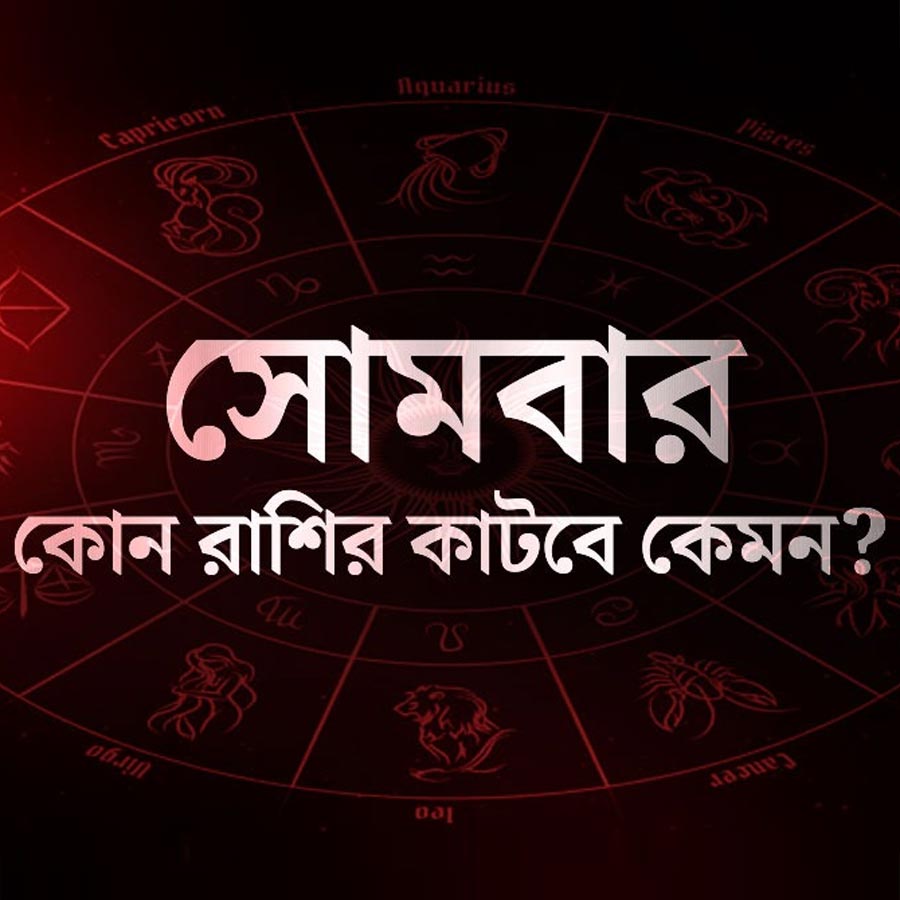আদিত্য ঘোষের ‘২০২৪: শেষ সতর্কবার্তা’ (৪-৩) শীর্ষক সময়োপযোগী প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বোঝা যাচ্ছে গরমের দাপট বাড়ছে, যার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ বা বিশ্ব উষ্ণায়নকে দায়ী করছেন। তথ্য বলছে, ২০২৪ ছিল ইতিহাসের উষ্ণতম বছর। ওয়াকিবহাল মাত্রেই জানেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো কিছু গ্যাস তাপশক্তি ধরে রাখে। আর ওই গ্যাসগুলির মাত্রা বৃদ্ধি মানে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। কয়লা এবং পেট্রলিয়ামের মতো জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো হলে ওই গ্যাসগুলির (যারা গ্রিনহাউস গ্যাস নামেও পরিচিত) নিঃসরণ বাড়ে। তবুও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে, কলকারখানা ও যানবাহন চালাতে এখনও যথেচ্ছ জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো হয়। অথচ, বহু বছর আগেই পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌরশক্তি-বায়ুশক্তি প্রভৃতি বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এদের ব্যবহারে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এটাই যে, সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে অতি দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁরা দ্রুত ও বেশি মুনাফার জন্য বিকল্প শক্তির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছেন। ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যাচ্ছেন, এ-হেন আত্মঘাতী নীতির কারণে সারা পৃথিবীর মানুষকে খেসারত দিতে হচ্ছে। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মানুষ-সহ জীবকুলের বিনাশের।
১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) তৈরি হয়েছিল বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। ধারাবাহিক ভাবে আইপিসিসি প্রতিটি রিপোর্টে পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সতর্ক করে চলেছে। কিন্তু আমেরিকা-সহ শিল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার শিল্প ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণে বল্গাহীন ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজ়িলের রিয়ো ডি জেনিরো শহরের সম্মেলন, যা ‘আর্থ সামিট’ নামেও পরিচিত, পরিবেশ এবং উন্নয়নের নতুন আন্তর্জাতিক নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো সম্মেলনেও যোগদানকারী দেশগুলি স্বাক্ষর করেছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ওই ঘোষণাপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। উল্টে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে— এই অভিযোগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের বেপরোয়া কাজকর্ম হয়তো এক দিন বন্ধ হবে, কিন্তু তখন কেউ হয়তো এই গ্রহে বেঁচে থাকবে না। ২০২৪ সাল সেই ইঙ্গিত দিয়ে গেল।
কৌশিক চিনা, মুন্সিরহাট, হাওড়া
পদক্ষেপ জরুরি
আদিত্য ঘোষের ‘২০২৪: শেষ সতর্কবার্তা’ শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালটি পৃথিবীর উষ্ণতম দশক হিসেবে চিহ্নিত। অনুমান করা হয়েছিল ২০৩০ সালের আগে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বিপদসীমা অতিক্রম করবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সেই সীমা ২০২৪-এই অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, যাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে ‘ক্লাইমেট ব্রেকডাউন’। জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক সমস্যা। সেই কারণে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। কিন্তু দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে যে দেশগুলিতে, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় উদাসীনতা যথেষ্ট। বরং জলবায়ু নীতিগুলো থেকে সরে থাকার আগ্রহ বেশি। সমীক্ষা বলছে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব যে দেশগুলিতে সর্বাধিক হবে, তার অন্যতম ভারত। তা হলে আমরা নিষ্ক্রিয় কেন? ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, তাপপ্রবাহ ও তুষারপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানীয় জল ও খাদ্যসঙ্কট প্রভৃতি মোকাবিলায় অবশ্যই সরকারি ভাবে দ্রুত পদক্ষেপ করা জরুরি। পাশাপাশি অরণ্য ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন, জীবাশ্ম-জ্বালানি (কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) পোড়ানোতে নিয়ন্ত্রণ দরকার। সবার আগে দরকার মানব সচেতনতা বৃদ্ধি। সঙ্গে গাড়ি ও কলকারখানার কারণে প্রবল বায়ুদূষণ রোধ, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার, জলাভূমি সংরক্ষণ ও উপকূলীয় অঞ্চল সংরক্ষণের মতো কাজে এই মুহূর্তে সরকারি তৎপরতা না বাড়ালে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে ক্ষতি অপূরণীয়।
স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০
রাজনীতির শিক্ষা
সুকান্ত চৌধুরীর ‘নতুন করে ভাবা’ (১৯-৩) শীর্ষক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতা জানাতে চাই। এক জন প্রবাসী হিসেবে স্কুলজীবন শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য এই শহরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রবেশ করে দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের মুখে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কিছু ছেলেমেয়ে থাকত যাদের কাজ ছিল আমাদের মতো নতুন আগত গ্রাম-মফস্সলের ছেলেমেয়েদের রাজনৈতিক কথাবার্তায় ভুলিয়ে তাদের নিজেদের ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করা। কোনও রকমে নানা অজুহাত দিয়ে নিত্যদিনের এই থেরাপি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু ক্রমশ উপলব্ধি করলাম যে, সর্বত্রই আড়ালে-আবডালে রাজনীতি হাতছানি দিচ্ছে ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে কী ভাবে নিজেদের দলে টানা যায়। কোনও না কোনও মতাদর্শে বাধ্য হয়ে ঘাড় কাত করতেই হবে।
বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিয়ে যে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা অত্যন্ত লোভনীয় এবং বিপজ্জনক। এই অনাবশ্যক ব্যবস্থাকে বন্ধ করার জন্যে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। যেমন— প্রথমত, শিক্ষাঙ্গন বিদ্যালাভের স্থান। সেখানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়া-সহ কোনও অভিযোগ জানানোর থাকলে তা উপাচার্য বা সমগোত্রীয় আধিকারিকের হাতে না দিয়ে নির্দিষ্ট কোনও বাক্সে রেখে আসা দরকার, যেটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাঙ্গনের বিশিষ্ট দু’জন মনোনীত শিক্ষাবিদ দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। এর ফলে ‘ঘেরাও’ নামক অসাংবিধানিক অব্যবস্থা থেকে শিক্ষকরা নিষ্কৃতি পাবেন। তৃতীয়ত, সেই কংগ্রেস আমল থেকে শুরু হওয়া এবং পরবর্তী কালে যুক্তফ্রন্ট ও তার পরে বামফ্রন্ট এবং বর্তমানে তৃণমূল সরকারের দলের নেতাদের প্ররোচনায় তুচ্ছ দাবি নিয়ে পড়াশোনা শিকেয় তুলে শিক্ষাঙ্গনকে দূষিত করার অভিসন্ধি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।
চতুর্থত, ছাত্রছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেই রাজনীতির পাঠ নেবে— এই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্র পড়াশোনার জায়গা। সেখানে রাজনীতি কেন আসবে? ভারতের বহু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির প্রবেশাধিকার নেই। সে ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়া মেটাতে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করেন না? তা হলে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন এ ভাবে রাজনৈতিক গুন্ডামির জায়গা করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হবে? পঞ্চমত, শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে। তাঁরা অবশ্যই কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা তাঁদের শোভা পায় না।
সারা দেশের যুব সমাজের যে অধোগতি লক্ষ করা যাচ্ছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না। অবিলম্বে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করতে না পারলে দেশের কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর নয়।
সুব্রত সেন গুপ্ত, কলকাতা-১০৪
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)