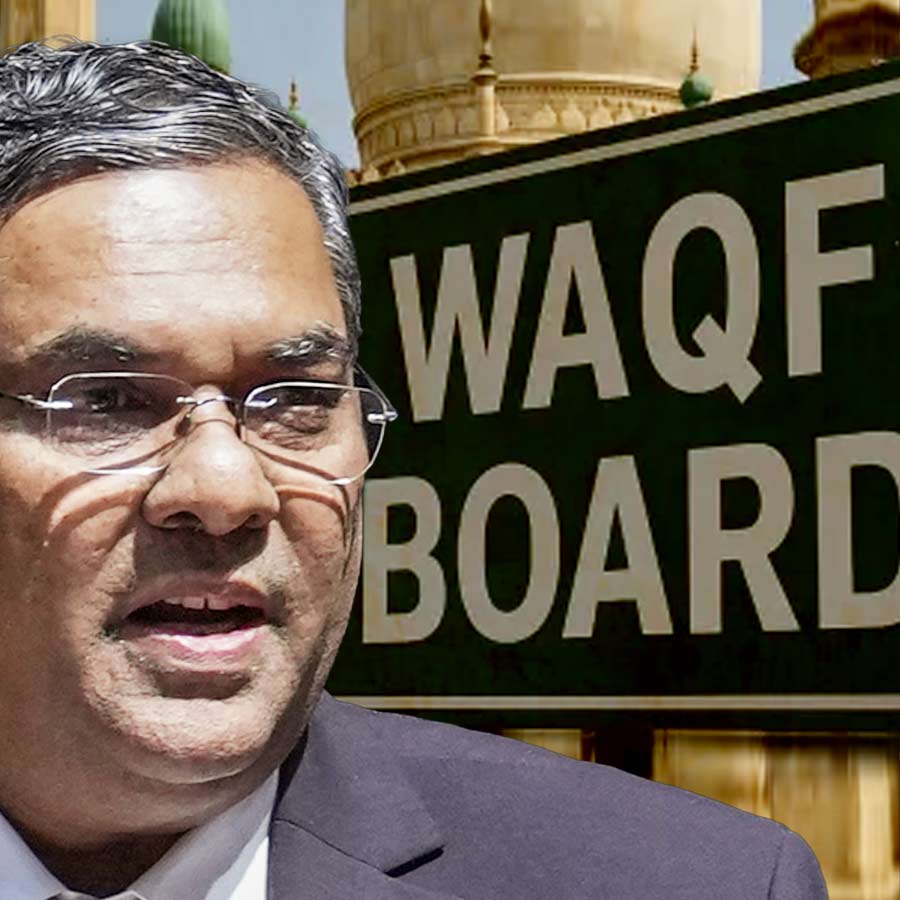জনগণ প্রশ্ন তোলে, তারকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রচারমাধ্যমে এত কাটাছেঁড়া কেন! কিন্তু সত্যিটা হল, এই সব ঘটনার দর্শক ও পাঠক আদৌ কম নয়। মনোবিজ্ঞান সিলমোহর দিয়েছে, আমজনতা খুব ভালবাসে বিতর্ক ও নাটকীয়তা। তাই এই সব ঘটনা গণস্মৃতিতে দীর্ঘকালীন ছাপ রেখে যায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অভিশংসনের কারণ, শিশুদের সঙ্গে জনপ্রিয় পপ-তারকার অদ্ভুত বন্ধুত্বের ইচ্ছা, যুবরানির রোজনামচা— সবই আজও মনে রেখেছেন মানুষ। বহুচর্চিত ঘটনাগুলি বাদ রেখে এই বইয়ে বিশ্বকে চমকে দেওয়া ৪১টি বিতর্কের বিবরণ একত্র করেছেন লেখক। বইটি নিয়ে ‘প্রাপ্তবয়স্ক কৌতূহল’ জন্মাতেই পারে, কিন্তু তা যে সুবিচার হবে না, তার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে ভূমিকায়: “সমাজের চোখে ব্যতিক্রমী বহু ঘটনাই শুরুতে কেচ্ছা হিসেবে চিহ্নিত হয়, যুগান্তরে তারই নাম হয়ে যায় ইতিহাস।” ইতিহাসের খাতিরেই জনপ্রিয় চরিত্রের ভাল কাজের সঙ্গে তাঁর তথাকথিত মন্দ কাজের দিকটাও ছোঁয়ার চেষ্টা। বিজ্ঞান, সিনেমা, সাহিত্য, রাজনীতি, খেলা— বিবিধ বিষয়ে সাবলীল ও স্বাদু কলমচারণায় লেখক তুলে এনেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ব্যভিচার, রাজপুত্রের দুর্নাম, অলিম্পিক্সের গেমস ভিলেজে অ্যাথলিটদের বন্ধনহীন জীবন, ধর্মগুরুর আশ্রমের লুকানো কাহিনি। বিবরণের বেশিটাই নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা, প্রতারণা ঘিরে। পাশাপাশি ওজনে বেশ হালকা— প্রকাশনার জালিয়াতি, আর্থিক তছরুপ, রাষ্ট্রনায়কের কুম্ভীলকবৃত্তি, চাঁদে মানুষ পাঠানো ইত্যাদি শরীরগন্ধরহিত কাণ্ডকারখানা। অথচ সেগুলি নিয়েও কথা-কাহিনি আর একটু জমলে আকর্ষণ ফিকে হত না।
কেচ্ছা
সুস্নাত চৌধুরী
৩৫০.০০
সপ্তর্ষি
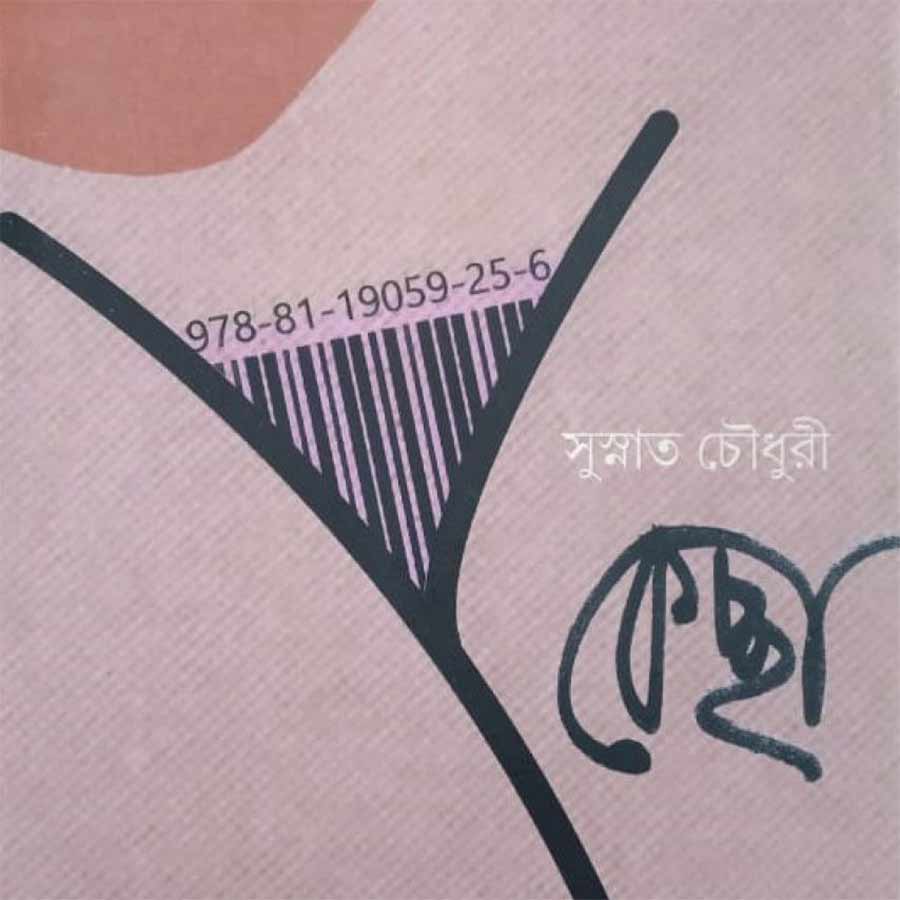
শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে উইলিয়াম কেরীর বিচিত্র কর্মোদ্যোগ বঙ্গসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শুরুর দিনগুলির সংগ্রাম অনেকটাই থেকে যায় নজরের আড়ালে। আর্থিক সঙ্কট ও ব্যক্তিগত জীবন নানা বাধা কাটিয়ে তিনি ছাপাখানা, কাগজকল-সহ শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষালয়, ছাত্রাবাস ও নারীশিক্ষার প্রসারে জেনানা-মিশন স্থাপন করেন। মিশনারি হিসাবে বাইবেল অনুবাদ-সহ ধর্ম সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাজের পরিধির অনেকটা জুড়ে থেকেছে। কিন্তু প্রকাশনার এই কাজের মধ্যেই নিঃশব্দে মাথা তুলতে শুরু করেছে বাংলা গদ্যসাহিত্যের অঙ্কুর। এমনকি বাংলা ভাষায় প্রথম গোয়েন্দাগল্পের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে তাঁর ইতিহাসমালা সঙ্কলনে। অন্য দিকে শ্রীরামপুরে তাঁর ব্যক্তিগত বাগানে কেরী বীজ বুনলেন বাংলায় উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার। হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী হিসাবে সেই শখ ছড়িয়ে দিলেন মানুষের মধ্যে।
কেরী ও বঙ্গ সংস্কৃতি
সম্পা: সুরঞ্জন মিদ্দে
৭৫০.০০
নান্দনিক
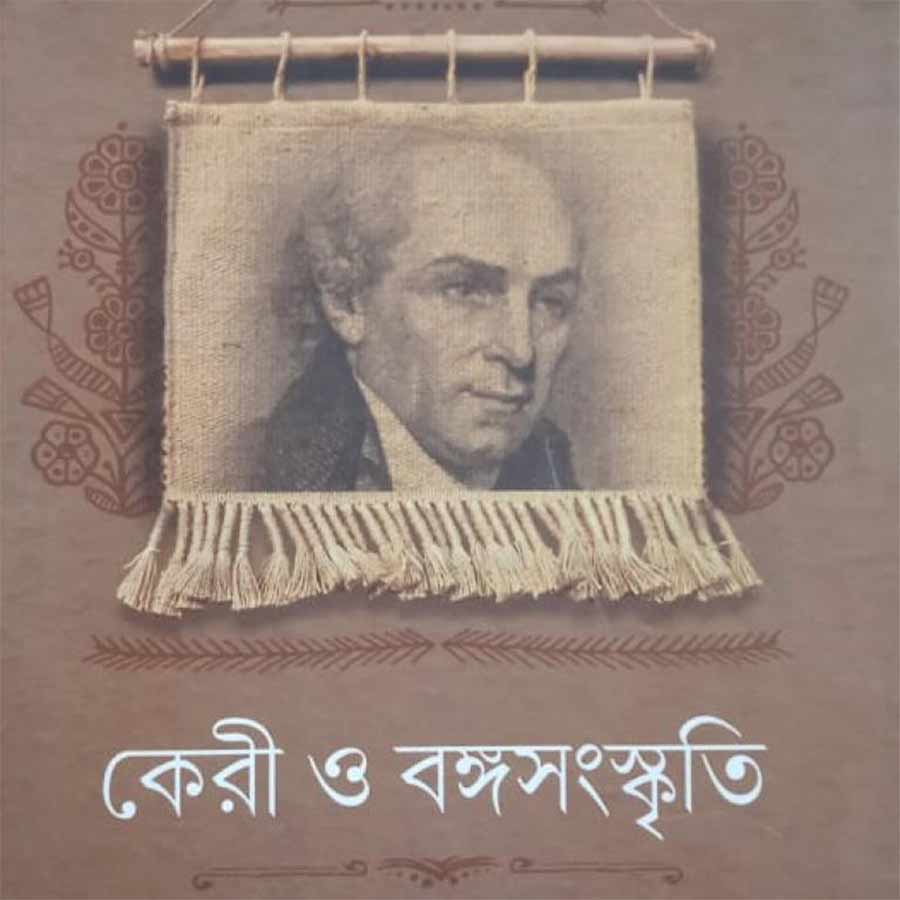
বঙ্গসংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবের মূল্যায়নে ফুটে উঠবে নানা ভাষ্য, স্বাভাবিক। সেই বহুস্বরকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে, দুই মলাটে দুই বাংলার প্রাবন্ধিকদের অভিমত। লেখক তালিকায় রয়েছেন সজনীকান্ত দাস, গোপাল হালদার, সুকুমার সেন, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ফাদার দাতিয়েন, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাজমা ইয়াসমিন প্রমুখ। তাঁরা আলো ফেলেছেন কেরীর কাজ ও সমসময়ের উপর। শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত পুস্তক তালিকা ও কেরীর জীবনপঞ্জি মূল্যবান সংযোজন।
মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সময় আধুনিকতা
সম্পা: মানবেন্দ্র সাহা
৪৪৯.০০
পালক
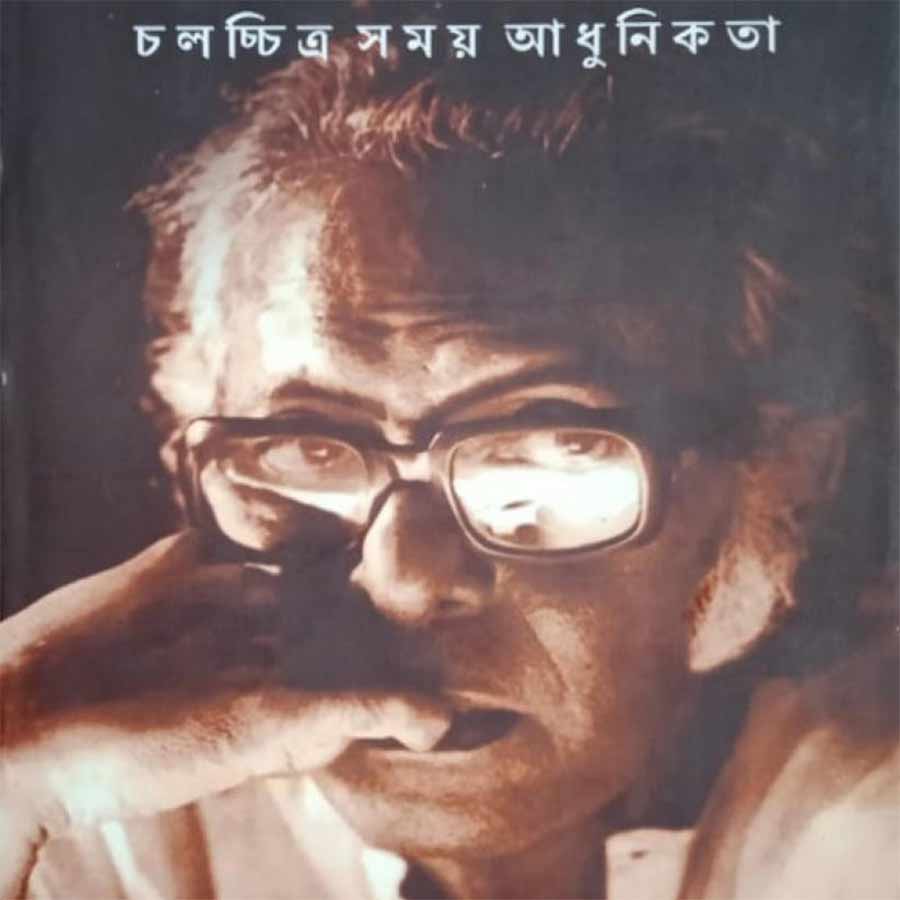
ছবির বিষয়বস্তু সে দেশের মাটিতে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা খেয়াল রাখতেন মৃণাল সেন: নিজের ছবি করার সময়, অন্য পরিচালকের ছবি দেখার সময়ও। কোনও ছবি বাস্তবতার প্রতি কতটা অনুসন্ধিৎসু, স্বদেশের প্রতি কতখানি আন্তরিক ভাবে বিশ্বস্ত, তা নিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের ছবিতে সেখানকার মানুষ, তাঁদের আচরণ, মানবিক সম্পর্ক ও আবেগ, সর্বোপরি সব কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত একটা ভূখণ্ড কোনও নতুন জটিলতার জন্ম দিচ্ছে কি না, সজাগ থাকতেন। তা নিয়ে যেমন তর্কে জড়াতেন, তেমনই জরুরি কথা উচ্চারণে পিছপা হতেন না। এক বার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, “তৃতীয় বিশ্বের ছবিনির্মাতা পশ্চিমি দর্শকদের ভিড় টানতে তার ছবিতে বাইরের দুনিয়ার কিছু বিষয় নিয়ে আসছে। এইভাবে সে এমন ছবি বানাচ্ছে... সেগুলোর সঙ্গে বাস্তবতার সম্বন্ধ নাও মিলতে পারে।” এমন আরও একটি কথোপকথন রাজীব মেহরোত্রার সঙ্গে। শ্যামল ভট্টাচার্য ও বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্যের অনুবাদে এই দু’টি ইংরেজি সাক্ষাৎকার বইটির পাঠ-প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে। বিশিষ্টদের রচনায় মৃণাল সেনের সামগ্রিক চলচ্চিত্রকর্মের আলোচনা, কিছু তাঁর নির্দিষ্ট ছবি সংক্রান্ত। ছবি তৈরির পিছনে মৃণাল সেনের দায়বদ্ধতা ও শিল্পরীতি বুঝতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)