কুষ্ঠ বা হ্যানসেন রোগ পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাধিগুলির মধ্যে অন্যতম, যাকে আজকেও সমগ্র বিশ্ব থেকে নির্মূল করা যায়নি। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কেবল শারীরিক যন্ত্রণাই নয়, মানসিক ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়। প্রাচীন শাম্বপুরাণে— যাকে ভিত্তি করে সমরেশ বসু লিখেছিলেন শাম্ব উপন্যাস— উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব ঋষি দুর্বাসার সাপে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সূর্যের উপাসনা করে তা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ‘কুষ্ঠ-রোগীর বউ’-এ চিত্রিত রোগীর সীমাহীন মানসিক যন্ত্রণা।
১৮৭০-এর দশকের প্রথম জনগণনা থেকে জানা যায়, ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সম্ভবত ৯৯ হাজার ৭৩ জন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। এই সংখ্যা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, রোগীদের প্রাত্যহিক জীবন ইত্যাদির যে ক্রমবিবর্তন হয়েছিল তার ইতিহাস যা আজও প্রাসঙ্গিক, তা অনেকটাই অজানা। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা সম্ভব সমাজ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দেশীয় চিকিৎসা, ধর্মীয় সংগঠন এই সব কিছুর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক; যাদের প্রভাব উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও বজায় থেকেছে।
এম্পায়ার অ্যান্ড লেপ্রসি ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল
অপলক দাস
১২৯৫.০০
রাটলেজ
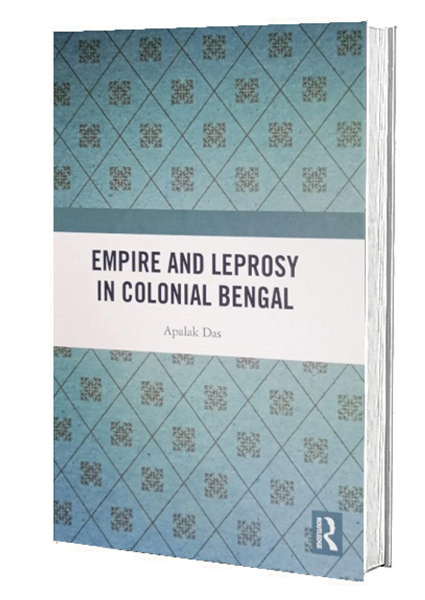
জেন বাকিংহামের গ্রন্থ লেপ্রসি ইন কলোনিয়াল সাউথ ইন্ডিয়া: মেডিসিন অ্যান্ড কনফাইনমেন্ট এবং অন্যদের লেখা অল্পসংখ্যক প্রবন্ধ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও, এই বিষয়ে বাংলার উপরে লেখা পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থের অভাব ছিল। অপলক দাসের লেখা আলোচ্য গ্রন্থটি এই অভাব পূরণ করেছে। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থার জটিলতা, রোগীদের পৃথকীকরণ, ভবঘুরেমি, পুর আইন, অধঃপতন, অধঃপতিত বিষয়ক ধারণা— নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।
ঔপনিবেশিক বাংলায় সরকার প্রস্তাবিত ১৮৮৯-এর ‘লেপার বিল’ নিয়ে বিতর্ক থেকে শুরু করে, ১৮৯০-৯১’এর ‘লেপ্রসি কমিশন’ এবং ১৮৯৮-এর ‘লেপ্রসি অ্যাক্ট’ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে যে-হেতু কলেরা, স্মলপক্স, ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি মহামারির মতো সেনাবাহিনী, অসামরিক ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কুষ্ঠ রোগ বিশেষ সমস্যা তৈরি করেনি, তাই রাজশক্তির নীতি অন্তত ১৯২০ পর্যন্ত যতটা না কুষ্ঠ রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার প্রয়াসে সচেষ্ট থেকেছে, তার থেকে বেশি তা মনোযোগী ছিল কুষ্ঠ রোগীদের সমাজ থেকে দূরে স্বতন্ত্র ভাবে নজরদারির আওতায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে।
কুষ্ঠ রোগ যে কত দূর সংক্রামক, এই বিষয়টি নিয়েও খুব সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। উনিশ শতকের কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ইত্যাদি নানা শহরে কুষ্ঠ রোগীর আশ্রয়স্থল বা ‘অ্যাসাইলাম’ তৈরি করা হয়েছিল। সরকারি অনুদান, ব্যক্তিবিশেষের বদান্যতা এবং বিশেষ করে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল।
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় ১৮৭৪ থেকে ‘মিশন টু লেপারস’ এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগ আলোচিত হয়েছে। ১৮৭৪-এ ওয়েলেসলি বেলি প্রতিষ্ঠা করেন ‘দ্য মিশন টু লেপারস’, যার নাম পরে পাল্টে হয়েছিল ‘দ্য লেপ্রসি মিশন’।
পুরুলিয়ায় স্থাপিত, কুষ্ঠ রোগীদের সর্ববৃহৎ আশ্রয়স্থলটি এমটিএল-এর আর্থিক সহায়তা লাভ করেছিল। আসানসোল, রানিগঞ্জ, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় খ্রিস্টান মিশনারিরা স্থাপন করেছিলেন আরও নানা অ্যাসাইলাম। ভারতবর্ষের উচ্চবর্গের দানশীল মানুষজন এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও যোগীন্দ্রনাথ বসু স্থাপন করেন দেওঘরের রাজকুমারী লেপার অ্যাসাইলাম। ভাগলপুরের অ্যাসাইলাম নির্মিত হয়েছিল রায়বাহাদুর শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতা ও উৎসাহে।
লেখক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে দেখিয়েছেন, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি অ্যাসাইলাম, যেমন গোবরার আলবার্ট ভিক্টর লেপার অ্যাসাইলাম ও মিশনারিদের পরিচালিত আশ্রয়স্থলগুলির মধ্যে কী রকম সাদৃশ্য বা অমিল ছিল। কোথাও কোথাও ভারতীয় এবং ইউরোপীয় রোগীদের পৃথক ভাবে রাখার ব্যবস্থা হত। অনেক জায়গায় মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের স্বতন্ত্র ভাবে থাকার ব্যবস্থা ছিল, যদিও সর্বত্র নিয়মকানুন একই রকম ছিল না।
পশ্চিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জীবাণু তত্ত্ব, গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবে ট্রপিক্যাল মেডিসিন সংক্রান্ত গবেষণা উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশেষত বিশ শতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার বিষয়টি কী চেহারা নিয়েছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বায়োমেডিসিন বা অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন ভারতে এসেছিল ইউরোপীয় শাসকদের হাত ধরে। তবে বহু দিন পর্যন্ত কুষ্ঠ ও অন্যান্য ব্যাধির চিকিৎসায় পশ্চিমি শাসক ও চিকিৎসকরা ভারতের দেশজ পদ্ধতি কাজে লাগাতেন। কুষ্ঠের চিকিৎসা হিসেবে নিমপাতার সাহায্যে বাহ্যিক মাসাজ, দস্তা তামা পারদ আর্সেনিক প্রয়োগের প্রচলন ছিল।
বিশ শতকের প্রথম দিকে স্থাপিত ‘ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন’-এর লেপ্রসি বিভাগ কী ধরনের গবেষণা পরিচালনা করছিল, লেখক তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯১৫ নাগাদ লেয়োনার্ড রজার্স চালমুগরা গাছের বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল ব্যবহার করে কুষ্ঠরোগ উপশমের উপায় বার করেছিলেন। লেখকের মতে, ১৯২০-র দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিএসটিএম-এর লেপ্রসি বিভাগ যে ধরনের গবেষণা প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছিল, তা উপনিবেশ ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার একচ্ছত্র আধিপত্যকে জোরদার করলেও এ কথা মনে রাখা দরকার, ঔপনিবেশিক আমলে একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের মেডিক্যাল রিসার্চ হয়েছিল, ১৯৫৫-র ‘ন্যাশনাল লেপ্রসি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম’-এ তা চূড়ান্ত পরিণতি অর্জন করে।
চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় বাংলা পত্রপত্রিকা, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ইত্যাদিতে প্রকাশিত কুষ্ঠ বিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তব্য। এগুলি বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন, বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকরা কী ভাবে ও কত দূর কুষ্ঠ ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক ভবঘুরে প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষকে সমাজের জন্য বিপজ্জনক বলে মত প্রকাশ করেছিলেন; এই রোগ নিরাময়ের বিষয়টিই বা কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিল। ভেষজ ওষুধ তৈরি ও তার বিপণনের কথাও আলোচনা করেছেন লেখক। উপসংহারে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কুষ্ঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে লেখা এই গবেষণাগ্রন্থ নিঃসন্দেহে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক পর্বের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ব্রিটিশ ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু দিন পর্যন্ত প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সংক্রামক রোগ, মহামারি, অতিমারির ইতিহাস, জনস্বাস্থ্য, ভারতীয়দের শরীরের ঔপনিবেশিকীকরণ, মহিলাদের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে কেউ কেউ অন্য ধরনের বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছেন— যেমন, এমন কিছু ব্যাধির ইতিহাস যা অতীতে মহামারি হিসেবে দেখা না দিলেও যার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থটি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)







