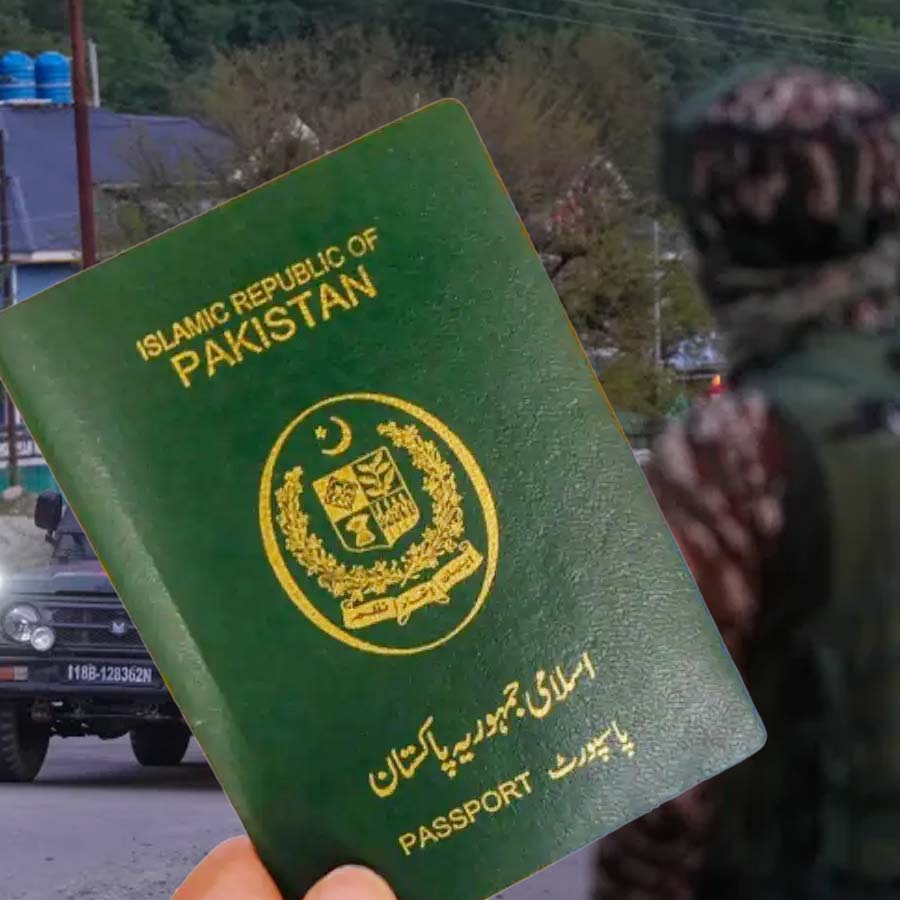জামাইষষ্ঠী জামাইসর্বস্ব রীতি। উৎস, তাৎপর্য এবং আভিধানিক অর্থেও এর সমর্থন মিলবে। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, নাম যা-ই হোক না কেন, এ রীতিতে আসলে শ্বশুরবাড়িরই প্রাধান্য। আর রীতিটা খাওয়াদাওয়া সর্বস্ব। জামাইষষ্ঠী-তে কী হয়? ‘চলন্তিকা’ বলছে, ‘জামাইকে তত্ত্ব দেওয়া ও নিমন্ত্রণ করা হয়’। সুবলচন্দ্র মিত্র জানাচ্ছেন, ‘দেশাচার মতে জামাইকে অর্চনা করা হয়’। নিমন্ত্রণ আর অর্চনা করার স্থান কোথায়? শ্বশুরবাড়ি। নিমন্ত্রণ করলে আপ্যায়ন করতে হয়। আপ্যায়নে খাওয়াদাওয়া থাকবেই। অর্চনা করলে ভোগেরও ব্যবস্থা করতে হয়। দেবদেবীর পূজার্চনায় তা-ই রীতি। জামাইদেবতার অর্চনায় ‘জামাইভোগ’ থাকে স্বাভাবিক ভাবেই।
জামাইভোগের আয়োজনের স্বাভাবিকতায় এখন বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়। ‘আসছে জামাইষষ্ঠী, ফলের বাজার আগুন’, ‘ষষ্ঠী আগে, জামাইয়ের পাতে এ বার পড়বে না লিচু’ বা ‘ঊর্ধ্বমুখী পাঁঠার মাংস, শ্বশুরের পকেট হালকা’ জাতীয় খবর দেখা যায় তিথি পালনের আগে। বোঝাই যায়, জামাইভোগে এলাহি আয়োজন হয়।
কেমন এলাহি? পরশুরামের একটি লেখায় তার সামান্য বর্ণনা মেলে। তাঁর ‘জামাইষষ্ঠী’ শীর্ষক লেখাটি অসমাপ্ত। কিন্তু পরশুরামীয় ভিয়েনের উত্তম উদাহরণ। এ লেখায় জামাই মহাবীর প্রসাদ চৌধুরী। নামটি অবাঙালি হলেও জামাই কিন্তু বাঙালি। তবে প্রবাসী বাঙালি। গোরখপুরে মহাবীর প্রসাদের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ বাস করতেন। কলকাতার হ্যারিসন রোডে তাদের পৈতৃক কাপড়ের ব্যবসা। মহাবীর বিয়ে করে চন্দননগরের বনেদি বংশের সন্তান যদুগোপালের মেয়ে ফুল্লরাকে। যদুগোপালের অবস্থা মন্দ হয়েছে। কিন্তু আগের বড়লোকি চাল বদলাতে পারেননি। ফলে দেনা বাড়ে। এ দিকে আড়ম্বরে জামাইষষ্ঠীও করে সে। কলকাতা থেকে দু’জন বাবুর্চি আনিয়ে পাঁচ জামাইয়ের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করে। আর নিয়ে যায় এক গাড়ি আইসক্রিম।
আয়োজন এলাহি। কিন্তু জামাই কি সহজে জামাইভোগের নাগাল পায়? এখন ছোট পরিবার। তাই জামাইভোগ সহজ। কিন্তু এক সময়ে ভোগের আগে বড় দুর্ভোগ পোহাতে হত জামাইদের। দীনবন্ধু মিত্রের কবিতায় দুর্ভোগের বর্ণনা আছে। ‘জামাই বারিক’ প্রহসনের লেখক জামাইষষ্ঠী নিয়ে দু’খানি কবিতা লিখেছিলেন। ‘জামাই-ষষ্ঠী (প্রথম বারের)’ এবং ‘জামাইষষ্ঠী (দ্বিতীয় বারের)’। দু’বারেই নানা দুর্ভোগ।
প্রথম বার জামাইষষ্ঠী করতে চলেছে জামাই। পরিপাটি বেশভূষা, “পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।/ কামিজ পীরণ পেংগি কত গায় দিল।” ধনহীন জামাইরাও “সুবেশে শ্বশুরবাড়ী বাড়াইতে মান/ বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান।” তার পর শ্বশুরবাড়ি। অভ্যর্থনা পর্বের পরে উপবেশন। মেয়েরা ভাঁটাগুলির উপরে পিঁড়ে পেতে বসতে দিল। জামাই বসতেই সে পিঁড়ে টলমল করে চলমান। শ্যালিকা ও মেয়ের দল হাসতে হাসতে বলে উঠল, “ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ।” রাম ঠকান ঠকে জামাই চুপ। তখন আবার বোবা জামাই বলে খোঁটা। এর পর খাওয়াদাওয়ার পালা। সেখানেও চাতুরি। জামাইয়ের জন্য তৈরি হয়েছে কাপড় ভরা ক্ষীরছাঁচ। চিনির বদলে দেওয়া হল ঘুণ। চালের পিটুলি দিয়ে তৈরি হল চন্দ্রপুলি। নুন হল গুঁড়ো চুন। এ নুন মুখে দিলেই ‘জিভ জ্বলে ফায়ার’ হয়ে যাবে। এমন দুর্ভোগ সহ্যের পরে জামাইভোগ, ‘অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন’। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন হয়তো সত্যি বা বাড়াবাড়ি। তবে যদুগোপাল যদি কলকাতা থেকে চন্দননগরে দু’জন বাবুর্চি ভাড়া করে নিয়ে যেতে পারেন, তা হলে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর অসম্ভব কী!
এ বার ‘জামাই-ষষ্ঠী (দ্বিতীয় বারের)’। নতুন জামাইয়ের কাছে, ‘ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান’। ষষ্ঠীর পিত্রালয়ে আবার সেই ঠকানোর ধারাবাহিকতা। মেয়ের দল এগিয়ে দিল ঢাকনি দেওয়া জলের গ্লাস। কিন্তু সে গ্লাসে জল নেই। জামাইয়ের জন্য কলাগাছের গোড়া কেটে তৈরি হয়েছে ডাব। বিচুলির জল দিয়ে তৈরি মিছরির পানা। তেলাকুচো ফল কেটে তা শশার রূপ দেওয়া হয়েছে। তেঁতুলের বীজ বেটে হয়েছে ক্ষীরছাঁচ। শেষে পিপুলের পাতা দিয়ে সাজা পান এগিয়ে দেওয়া হল জামাইয়ের দিকে। এ সব জলযোগ পর্বের জামাই-আদর এবং জামাইভোগ। এর পর ভোজনায়োজন। সেখানেও আর এক প্রস্ত দুর্ভোগ। পাতের পাশে বাটির দুধ আসলে চালের পিটুলি গোলা। সন্দেহ যাতে না হয় সে জন্য পিটুলির উপরে ছড়িয়ে দেওয়া আসল দুধের সর। মোম গলিয়ে হয়েছে ঘি। ‘জামাই ব্যাটা খাবি কী’! প্রচলিত ছড়ায় আছে, “ধানের ভেতর পোকা জামাইবাবু বোকা।” এই ছড়া বোধহয় শ্বশুরবাড়িতে জামাই ঠকানোর নানা উদাহরণ দেখে-শুনে কোনও স্বভাবকবি বানিয়েছিলেন।
দুর্ভোগের আরও রকমফের আছে। উদাহরণ আবার পরশুরাম থেকে। ‘জামাইবাবু ও বৌমা’ কবিতা। যে কবিতার শিরোনামের নীচে কবি স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন, ‘ন্যাকা ন্যাকা সুরে পড়িতে হইবে’। একটা বিষয় বলে রাখা ভাল। এই কবিতার জামাইয়ের শ্বশুরালয়ে যাত্রা কিন্তু জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে নয়। প্রথম বার গমন। ‘দূর দেশে’ শ্বশুরবাড়ি। জামাইয়ের মন আনচান কখন পৌঁছবে— “আর কত দেরি? আর যে সহে না/ ধড়ে প্রাণ আর থাকিতে চাহে না।” এর আগে এক কাণ্ড ঘটিয়েছে জামাই। বক্সার স্টেশনে ট্রেন থামতে এক হোটেলে খেয়েছে। গরম ভাত আর মাটন কারি। হাতে মাংসের কারির হলুদের দাগ। ধুয়েও যায়নি। বুকে বাহারি রুমাল গোঁজা আছে বটে। তবুও জামাই পড়েছে দ্বিধায়, “কোন প্রাণে হাত মুছি গো তাহায়?/ শালা-শালী দেখে কি ভাবিবে হায়!”
এর পর শ্বশুরবাড়ি। খেতে দেওয়া হয়েছে জামাইকে। ঘিরে ধরেছে শালির দল। জামাই এত লোকের সামনে সঙ্কুচিত। সে খুব যত্ন করে সাবধানে শরবতে লেবু টেপে। পাছে লেবু ফসকে শালিদের গায়ে পড়ে। শুধু শালিদের নয়, ‘ডিডি মেট্রো’-পূর্ববর্তী যুগে গ্রামাঞ্চলে বহু কৌতূহলী নজরের সামনে জামাইদের অস্বস্তিতে পড়তে হত। পাড়ার নতুন জামাই হলে তো কথাই নেই। জামাইষষ্ঠীর দিন রাস্তায় বহু পড়শির জোড়া জোড়া চোখ জামাইয়ের পোশাক থেকে হাতে মিষ্টির হাঁড়ি বা বাক্স পর্যন্ত মেপে নিত।
এই যে আয়োজন, জামাইকে নিয়ে এত আগ্রহ, তা কিন্তু বজায় থাকে না পরে। দীনবন্ধু মিত্র এবং পরশুরাম দু’জনেই পুরনো জামাইদের দুঃখ নিয়ে কাব্য করেছেন। দীনবন্ধুর পুরনো জামাইরা দু’-তিন ছেলের বাপ। তারাও ষষ্ঠীতে যাবে বলে খেপে উঠেছে। কিন্তু একটা অজুহাতও খাড়া করছে। বাটা নিতে, অর্থাৎ পাওনা বুঝতে, তারা শ্বশুরবাড়ি যাবে না। যাবে ছেলেকে দেখতে। হয়তো ছেলেকে নিয়ে স্ত্রী ষষ্ঠীর আগেভাগেই শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছিল। দীনবন্ধু এইটুকু লিখেই চলে গিয়েছেন নতুন জামাইয়ের গুণকীর্তনে। তাঁর সংশয় ছিল, “পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।/ নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে।” পরশুরাম পুরনো জামাইদের বিষয়ে আরও নির্মম। দীনবন্ধু তবু ইঙ্গিত দিয়েছেন, ছেলেকে দেখার অজুহাতে গেলেও পুরনো জামাই বাটা পায়। কিন্তু পরশুরামের স্পষ্ট কথা, পুরনো জামাইয়ের জন্য রোজ রোজ আর আসে না পাঁঠা। পাতে পড়ে সজনের ডাঁটা।
শাশুড়ি, শালী, শেলেজরা জামাইয়ের সামনে জামাইভোগে কী সাজিয়ে দিতেন? পাঠ, পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা বলছে, জামাইয়ের পাতের পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কাতলা-কোপ্তা-কালিয়া-কচি পাঁঠা-কাটলেট, সময় যাকে প্রাধান্য দিয়েছে সে-ই জামাইয়ের পাত আলোকিত করেছে। অথবা অনেকে মিলে। পরশুরাম ঘেঁটে মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে, পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট, মাছের বড় মুড়ো, পাঁঠার মাংস আর পুরনো জামাইয়ের জন্য কাঁকড়ার দাঁড়া। দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় ‘অন্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন’ এবং চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র কথা আছে। কিন্তু উদাহরণ নেই।
জামাইষষ্ঠীতে ফলের ভরা মরসুম। ফলে শেষ পাত ফলাও করে ফল। আম থাকে। ষষ্ঠী একটু পিছিয়ে থাকলে লিচুও। দীনবন্ধু মিত্র আম আর মধুফলের উল্লেখ করেছেন। মধুফল কোনগুলো? জানা নেই।
বাঙালির ভূরিভোজ মধুর করে তোলে মিষ্টি। বাংলায় মিষ্টির বৈচিত্র সর্বজনবিদিত। কিন্তু জামাইষষ্ঠী নিয়ে তিন-তিনটি লেখায় মিষ্টির তেমন বৈচিত্র মিলল না। পরশুরামের লেখায় মেলে, রাবড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ। দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় ক্ষীরছাঁচ, চন্দ্রপুলির উল্লেখ। পুরনো লেখায় জামাইষষ্ঠীর মিষ্টির বৈচিত্রহীনতায় দুঃখের কিছু নেই। বরং বাঙালির গর্ব করা উচিত। কারণ দুনিয়ায় বাঙালিই একমাত্র জাতি যে জামাইয়ের জন্য বিশেষ মিষ্টি তৈরি করিয়েছিল। কাহিনিটা খুবই জনপ্রিয়। তেলিনিপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়দের গিন্নিমা সূর্য মোদককে বরাত দিয়েছিলেন জামাই ঠকানো মিষ্টির। সূর্য মোদক তৈরি করলেন জলভরা তালশাঁস সন্দেশ। নতুন জামাই কামড় দিতেই সন্দেশের ভিতরের জলীয় অংশ পড়ল পাঞ্জাবিতে। দেখে জমিদার বাড়ির মেয়েমহলে হাসির রোল।
দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল বটে জামাইকে। কিন্তু বাঙালি পেল সত্যিকারের ‘জামাইভোগ’। সূর্য মোদকের এই জলভরা তালশাঁস ছাড়া আর কোন মিষ্টিই বা এই শিরোপা পেতে পারে!
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)