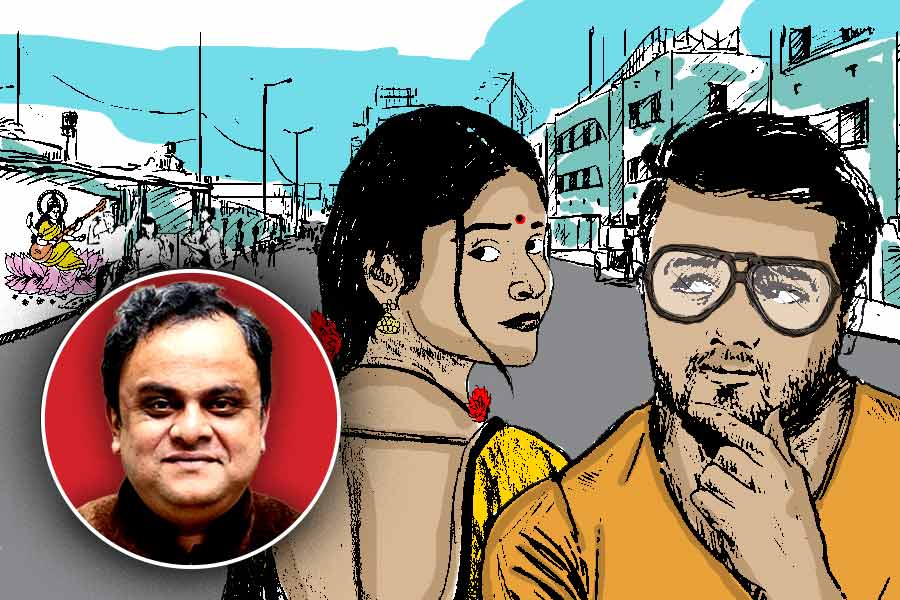বাংলার গতিপথ এখন অন্য দিকে
ছিল বিপুল দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ। ছিল নিরক্ষরতা। ছিল যুক্তিহীন রাজনৈতিক একগুঁয়েমি, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন ও গণহত্যা। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে আমরা সেই সব দৈত্যকে বোতলবন্দি করতে পেরেছিলাম। আবার সেই লজ্জা আমাদের সামনে। আজ দ্বিতীয় পর্ব।
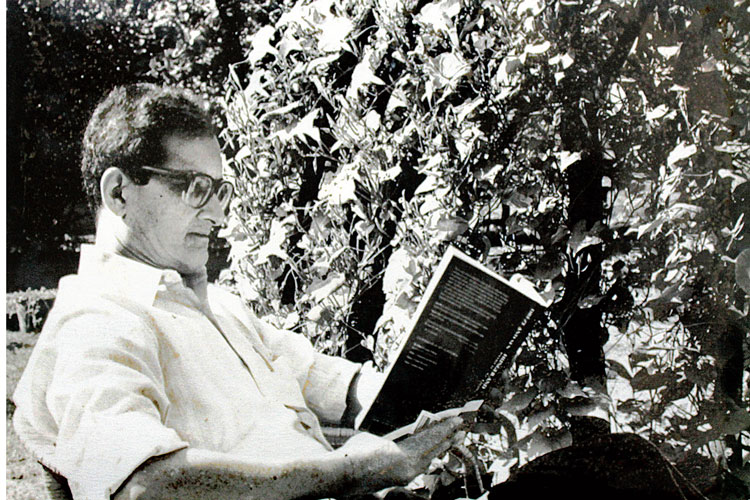
নিমগ্ন: কেমব্রিজে গাছের ছায়ায় বই পড়া।ছবি শান্তিনিকেতনে ‘প্রতীচী’ বাড়ির সৌজন্যে
অমর্ত্য সেন
যাদবপুরের কাজ এবং ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশা আমার খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত কলেজ স্ট্রিট ও কফি হাউসে ঢুঁ মারাটাও চলছিল। আমি প্রেসিডেন্সি ছেড়েছি ১৯৫৩ সালে, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ তাঁর পূর্বসূরি জোসেফ স্তালিনের নানা অপকর্ম লোকসমক্ষে তুলে ধরার অনেক আগে। কিন্তু এমনকি সেই ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকেও বিশ্ব ঘটনাপঞ্জির বিচক্ষণ পাঠকের পক্ষে স্তালিনের নেতৃত্বে ঘটা ‘বহিষ্কার’ (পার্জ) ও ‘বিচার’ (ট্রায়াল)-এর ঘটনাগুলোর আসল রূপটা আঁচ করতে না পারার কারণ ছিল না। এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে লোককে যে নির্মম সাজা দেওয়া হত, তাতে বড় রকমের অবিচার হচ্ছে— এ-রকম চিন্তা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় এই বিষয়গুলো প্রায়ই আমাদের আলোচনায় উঠে আসত, এবং কখনও কখনও এমন হত যে, আমার সব বন্ধুরা এক দিকে আর আমি অন্য দিকে। এক দিকে ছিল দক্ষিণপন্থীরা, যারা মনে করত মার্ক্সের কথা আগাগোড়াই ভুল (আমার চোখে এই ধারণায় ছিল বড় রকমের ভ্রান্তি)। আর অন্য দিকে ছিল ‘প্রকৃত বামপন্থী’রা, যারা মনে করত রাশিয়াতে কোনও অন্যায় অত্যাচার ঘটেনি, যা ঘটেছে তা হল ‘জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা’র প্রয়োগ (এই ধারণাকে আমি অপার বালখিল্যতা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে করতে পারিনি)। এই দুইয়ের মাঝে আমাদের অবস্থানটা ছিল বেশ কঠিন। এই অবস্থাতেই আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, অন্যরা আমার সঙ্গে সহমত হলে সেটা আমার পক্ষে যত আনন্দদায়কই হোক, অন্যদের সহমতির ওপর কম নির্ভরশীল হওয়াই ভাল।
এবং, এটা রাজনীতি বিষয়ে চিন্তাভাবনার কোনও ভাল পথ হতে পারে না। রাজনীতিতে গোষ্ঠীর ভূমিকা— শুধু ব্যক্তির নয়— গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা এবং সমালোচনামূলক— এমনকি ঘোর বিরোধী— যুক্তির জন্যও পরিসর থাকা দরকার। সামাজিক সত্তা এবং ব্যক্তিগত যুক্তির এই সংমিশ্রণ আমার কাছে বরাবরই খুব মূল্যবান বোধ হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে কলকাতায়— যাদবপুরে ও কলেজ স্ট্রিটে— আমার অভিজ্ঞতা এই সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তাকে সমানে তুলে ধরেছে। ঘটনাক্রমে, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম বই ‘কালেক্টিভ চয়েস অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার’-এর প্রথম পাতাতেই আমি কার্ল মার্ক্স-এর ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট (১৮৪৪) থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করি: ‘‘সর্বাগ্রে যেটাকে পরিহার করা দরকার তা হল— ‘সমাজ’কে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।’’ ১৯৫০-এর দশকে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বঞ্চনাগুলো একটা বড় এবং সাহসী পথ পরিবর্তন দাবি করছিল, অথচ সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনটা আসছিল খুব ধীর গতিতে। সেই সময়ে এই চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ছিল খুব বেশি। তেমনই, আজ যখন বাঙালি সমাজকে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন এই চিন্তা আমাদের কাছে আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৮
এ বার ক্ষান্ত দেওয়া দরকার। ১৯৫১ সালে যখন কলকাতায় পড়তে আসি সেই সময়টা ছিল ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির খুব কাছাকাছি। ব্রিটিশ শাসনে ঘটা বিভিন্ন ট্র্যাজেডি এই রাজত্বের শেষ পাদে বিশেষ ভাবে চোখের সামনে উঠে এসেছিল। আমরা ভারতবর্ষে কোন ধরনের পরিবর্তন চাই, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তায় এই সঙ্কটগুলি খুবই প্রভাব ফেলেছিল।
এগুলোর মধ্যে দুটো মহাবিপর্যয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি এড়ানো সম্ভব নয়। দেশে বিপুল দারিদ্র ছিল, এবং এই দারিদ্র মাঝে মাঝেই বিরাট দুর্ভিক্ষের আকার নিত, যাতে অগণন লোকে অনাহার ও অন্যান্য বঞ্চনার কারণে মারা যেত। বাংলায় কুড়ি থেকে তিরিশ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়েছিল পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০ সাল) মন্বন্তর। ১৯৪৩-এর সেই দুর্ভিক্ষ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ছেলেবেলায়। ছবি শান্তিনিকেতনে ‘প্রতীচী’ বাড়ির সৌজন্যে
অ্যাডাম স্মিথ ও ইউরোপের অন্য অনেক পুরোধা অর্থশাস্ত্রীর বর্ণনায় পাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের, সমৃদ্ধি ছিল চোখধাঁধানো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তিলগ্নে ভারত হয়ে উঠল পৃথিবীতে দারিদ্রের মূর্তিমান উদাহরণ। এমন অবস্থায় আর্থনীতিক উন্নতির প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। দারিদ্রের পাশাপাশি ছিল সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা। প্রাক-আধুনিক বিশ্বে এটা কোনও নতুন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু বিশ্ব জুড়ে— ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, এবং অন্য নানা দেশে— যখন বিদ্যালয় শিক্ষায় বিপুল অগ্রগতি ঘটে চলেছিল, তখন ভারতে সেটা ঘটেনি সাম্রাজ্যবাদের কারণে। ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র দশ শতাংশের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের চোখে শিক্ষার এই বিরাট অভাবই ছিল ভারতের এগিয়ে যাওয়ার পথে সর্বক্ষেত্রেই সর্ববৃহৎ বাধা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত ছিলাম, কিন্তু কফি হাউসের সেই আড্ডায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিরোধিতার চড়া সুর আমাকে বিস্মিত করে।
এই সমস্যার মোকাবিলায় আমাদের সাফল্যকে মিশ্রই বলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালই সাফল্য এসেছে। (এ ক্ষেত্রে বামপন্থীদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।) কিন্তু পাশাপাশি, কলকারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পিছনে নানা কারণগুলোর সব ক’টিই যুক্ত ছিল বিভিন্ন নীতির যুক্তিহীন প্রয়োগের সঙ্গে। এই নীতিগুলোর মূলে আবার ছিল গঠনমূলক চিন্তা বিসর্জন দিয়ে কাজ পণ্ড করা এবং গোঁয়ার্তুমির আনন্দে মশগুল থাকার মানসিকতা।
সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব তখন ভয়ানক। এই দ্বিতীয় বিপর্যয়টাও ছিল বিরাট। বঙ্গদেশ তথা ভারত জুড়েই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়— আমার মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের চোখে এই সহযোগ ‘হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা’ হিসেবে ধরা দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার আগের সময়টিতে দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসার ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। যুক্তির ধার না ধারা রাজনৈতিক একগুঁয়েমি অতীত থেকে চলে আসা জাতীয়তা, ভাষা, স্থানিকতা, বিশ্বাস এবং অন্যান্য হাজার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে— বিশেষত পরস্পর-বৈরী হিন্দু-মুসলমানে— আড়াআড়ি ভাগ করে ফেলল। স্বাধীনতার সময়ে সারা রাত জুড়ে শোনা যেত, হত্যার— বস্তুত গণহত্যার— আর্তনাদ, হিন্দু ও মুসলমানের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার। সেই স্মৃতি আমার মন থেকে যাওয়া সম্ভব নয়।
দেশভাগ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কালে হিন্দু রাজনীতি ও মুসলমান রাজনীতি, দুইয়েরই এটাই ছিল স্বরূপ। আমি যখন কলকাতায় আসি তখন এ-শহর সেই সেই বীভৎস ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলছিল— কিন্তু জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে ছিল সদ্য ঘটা হত্যার নানা চিহ্ন, সকলেই যার কথা জানতেন। ১৯৫০-এর দশকে আমরা সেই দানবকে, সাময়িক ভাবে হলেও, বোতলবন্দি করে ফেলতে পেরেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যা পরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম দেয়। কাজি নজরুল ইসলাম দেখে খুশি হতেন যে, তাঁর বিখ্যাত কবিতার ‘কাণ্ডারী’ নিজের দায়িত্বটা ভালমতোই পালন করে চলেছিলেন।
সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িক চিন্তার পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার গতিপথ বেশ কিছুটা অন্য দিকে ঘুরে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ যদি তার অ-সাম্প্রদায়িক বাঙালি পরিচিতি (রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচিতি) ধরে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকে, তবে কেন এবং কী ভাবে এমনটা হল তা নিয়ে গভীর এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ করা দরকার। কিছু লোক যদি তাঁদের ধর্মীয় বা অন্যান্য সম্প্রদায়গত পরিচিতির কারণে শঙ্কার সম্মুখীন হন, এবং অবাধে চলাফেরা করতে ভয় পান, তা হলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কী কারণে তা ঘটেছে? আমাদের এই গর্বের শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় এতটা অক্ষমতা এসেছে কী কারণে? প্রশ্নটার উত্তর জানা গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে এই লজ্জাকর সমস্যাটির সমাধানও একান্ত জরুরি। (সমাপ্ত)
৫ জুলাই ২০১৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ‘ক্যালকাটা আফটার ইন্ডিপেনডেন্স: আ পার্সোনাল মেমোয়ার’-এর অনুবাদ
-

মেয়েদের লক্ষ্মীমন্ত হতে বলা হয়, যাতে সব সহ্য করে নেয়, সরস্বতীমন্ত হতে শেখায় না: অপরাজিতা
-

অমিতাভের যুগে সরস্বতী পুজো ছিল মেয়েদের দেখে ‘আওয়াজ’ দেওয়ার, আমির আসার পর বদলে গেল!
-

রাতের চশমা পরেননি চপারের পাইলট? তাই ধাক্কা বিমানে? ওয়াশিংটনে ব্ল্যাকবক্স থেকে উঠছে প্রশ্ন
-

অরণ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়লেও রইল প্রশ্ন
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy