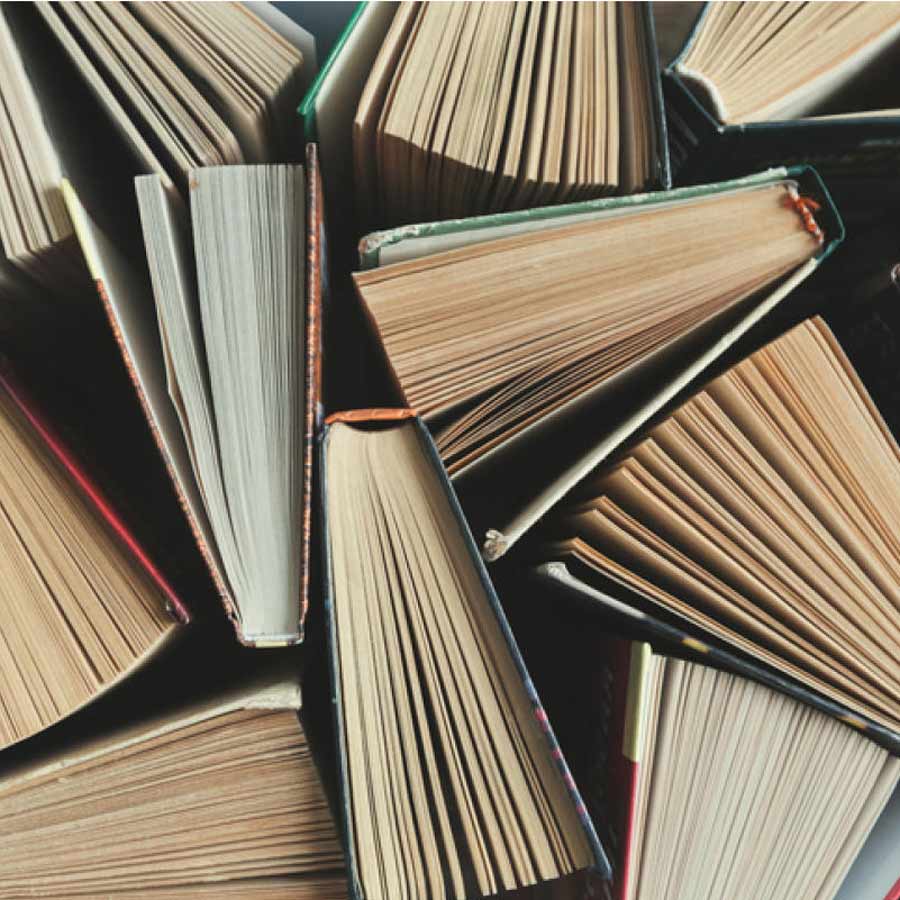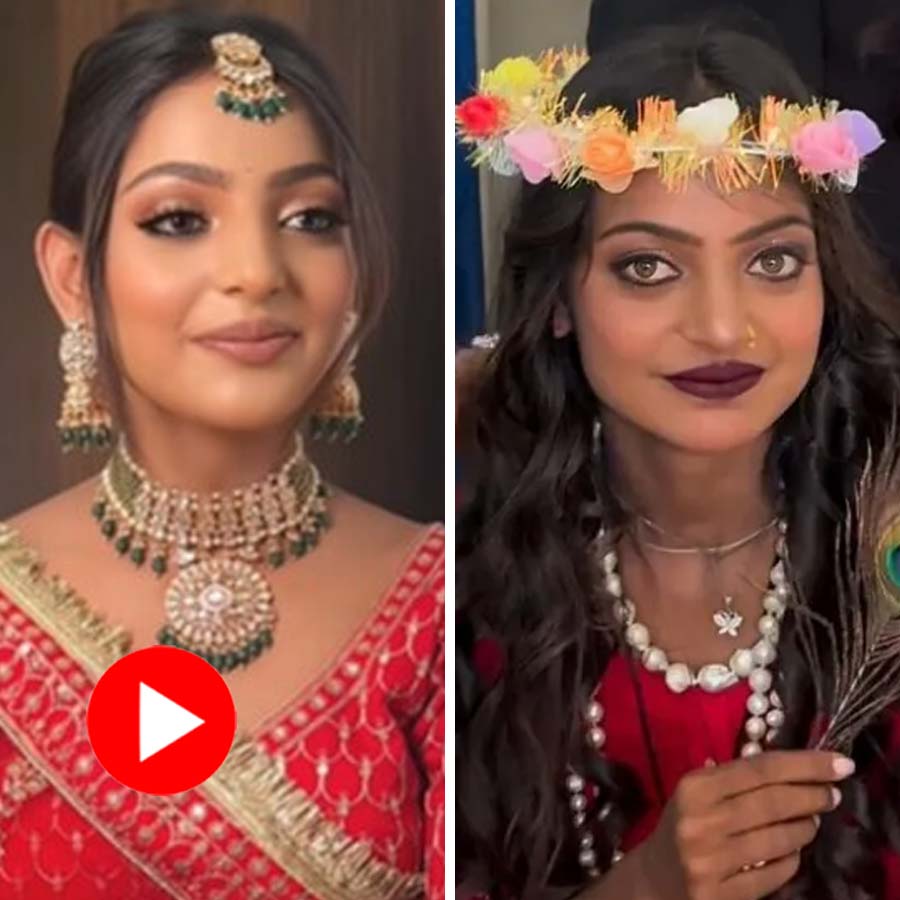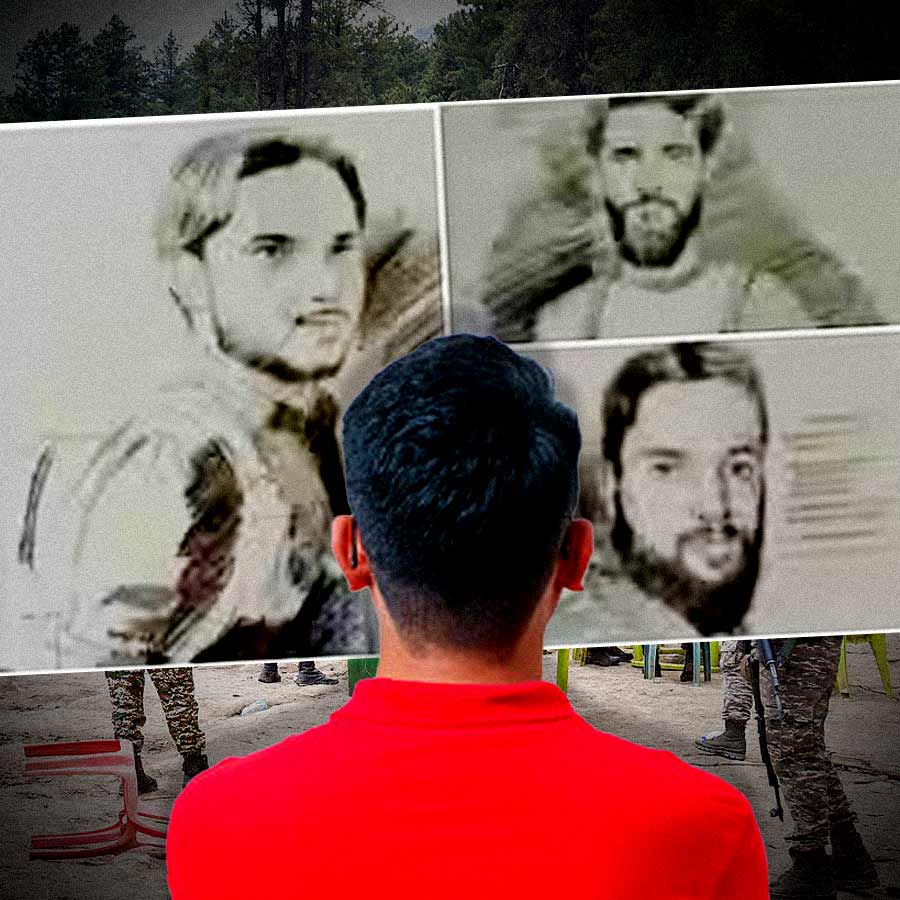বিতস্তা ঘোষালের প্রবন্ধ “অনুবাদে ‘বিশ্বসাথে যোগ’” (১৪-৩) প্রসঙ্গে এই চিঠি। অন্য ভাষায় রচিত একটি উপন্যাসকে ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষায় অনূদিত করে ট্রান্সক্রিয়েশন বা স্থানান্তর-এর পর্যায়ে নিয়ে আসেন অনুবাদক। লেখক অথবা লেখিকার চেয়ে অনুবাদকের মুনশিয়ানা এবং কৃতিত্ব কোনও অংশে কম নয়। অনুবাদকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক হতে হয় অনুভূতি, সংবেদনশীলতার পর্যায়ে। দু’জনের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, জগৎ একই রকম হলে ভাল। অনেক সময় লেখক যখন লেখেন তাঁর অবচেতনে অনেক কিছু থাকে, সেই দৃশ্য-পরিস্থিতি-পরিবেশ অনুবাদককে সচেতন ভাবে বুঝে নিতে হয়। লেখকের কাজ বা ভাবনা আবার অন্য একটি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করছে, সেখানেও সেটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব উপস্থিতি ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আছে। ভাষা শুধু গল্পের বাহক নয়, ভাষার নিঃশ্বাসও উপন্যাস ও গল্পের পরতে পরতে মিশে থাকে।
অরুণাভ সিংহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বটেই, এ কালের বহু সাহিত্যিকের লেখা অনুবাদ করেছেন। অরুণাভ গীতাঞ্জলি শ্রী-কে জানান যে রেত সমাধি উপন্যাসটিকে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছে এবং ডেইজ়ি রকওয়েল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন, যিনি হিন্দি জানেন এবং নিজেও লেখিকা। ইংরেজি অনুবাদ টুম্ব অব স্যান্ড সাহিত্যিক গীতাঞ্জলি শ্রীকে এনে দেয় আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার, ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে প্রথম বার। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার বিজয়ী অমর মিত্র ২০২২ সালে ও হেনরি পুরস্কার পেয়েছেন, ৪৫ বছর আগে লেখা ‘গাওঁবুড়ো’ ছোটগল্পটির জন্য। এই গল্পটি ‘দি ওল্ড ম্যান অব কুসুমপুর’ নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন সাংবাদিক অনীশ গুপ্ত। যখন এই গল্পটি ও হেনরি পুরস্কারের জন্য বিবেচনার পর্যায়ে, অনুবাদককে অনুরোধ করা হয় কিছু শব্দের পরিবর্তন করার জন্য, যাতে পশ্চিমের পাঠকদের কাছে গল্পটি সহজ ও বোধগম্য হয়। যেমন আমরা সবাই পরিচিত ‘কোয়াক ডাক্তার’ শব্দটির সঙ্গে। অনীশ গুপ্ত এই শব্দটিকে ‘উইজ়ার্ড’ শব্দে পরিবর্তন করেন। অনুবাদককে লেখক ও লেখিকার লেখার ধারা, মনস্তত্ত্ব, গল্পের পটভূমিকা, মূল ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। তবেই অন্য ভাষায় গল্পটির পরিবেশন সম্ভব হয়। অনুবাদ একটি শিল্পকর্ম, যার মাধ্যমে ভারতীয় ভাষার লেখকেরা বিশ্বের দরবারে আরও পরিচিতি পেতে পারেন।
সুপ্রিয় দেবরায়, বরোদা, গুজরাত
ভাষান্তরের ভার
বিতস্তা ঘোষালের “অনুবাদে ‘বিশ্বসাথে যোগ’” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। অনুবাদ যে শুধু একটা নতুন পাঠেরই জন্ম দেয় তা-ই নয়, সংস্কৃতি ও রাজনীতির নতুন নতুন বৃত্তে সেই পাঠকে নিয়ে যেতেও সাহায্য করে। মানুষের মনের দরজা খুলে দেয়। প্রবন্ধকার যথার্থই বলেছেন, বিদেশি ভাষা থেকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের তুলনায় পিছিয়ে থেকেছে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে অনুবাদের কাজ। এবং এই কাজটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রমাণও পাওয়া যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কথায়। তিনি দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে মেধা রয়েছে তা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঞ্চারিত হবে সাহিত্যের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই। সত্যিই তো, একটি ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমেও সমৃদ্ধ হয়।
প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে অনুবাদের বিবিধ সমস্যার কথাও। সেখানে এক দিকে যেমন আছে মূল টেক্সটের সঙ্গে অনূদিত অংশের ভিন্নতা, অন্য দিকে আছে অনুবাদকর্মে মূলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হওয়ার ব্যর্থতাও। এটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথাও নয় যে, একটা ভাষা থেকে অপর ভাষায় অনুবাদটা মোটেই কোনও সহজ কাজ নয়। এই কাজের দুরূহতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক জাক দেরিদাও এক বার বলেছিলেন, অনুবাদককে দোষ দেওয়া অন্যায় কারণ তিনি সব সময়ই ভুল করবেন।
এক-একটা বাক্য এক-এক ভাষায় এক-এক ভাবে অনুরণিত হয়। আবার, শুধু সেই ভাষাটাকে জানলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বা জীবনধারাকেও ভাল ভাবে জানতে হবে এবং অনুবাদটা করতে হবে মূল রচনার ভাষা থেকেই, অর্থাৎ যে ভাষায় টেক্সটি সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল। এটাও মাথায় রাখতে হবে, এই কাজটা করতে হবে সম্পূর্ণ ভালবেসে ও তার মধ্যে একনিষ্ঠ ভাবে মনোনিবেশ করে। অন্যথা, মূলের থেকে অনুবাদে পৌঁছতে গিয়ে বিচ্যুতির সম্ভাবনাও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং তাতে লাভের থেকে ক্ষতিই হবে বেশি। উইলিয়াম রাদিচে যেমন গীতাঞ্জলির ইয়েটস-পরিমার্জিত অনুবাদটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, প্রচলিত পাঠে কমা’র আধিক্য দিয়ে বাইবেলি ছন্দ চাপিয়ে এবং বাইবেল-এর মতো করে অনুচ্ছেদ বিভাজন করে ইয়েটস অন্যায় করেছেন।
অনুবাদের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অবশ্য অনেক সময় নিজের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে অভিযোগ তুলে ই এম ফর্স্টার-বিশেষজ্ঞ মেরি লাগো পর্যন্ত বলেছিলেন, দ্রুত তৈরি করা অনুবাদগুলিতে কল্পনাশক্তির ও আগ্রহের অভাব রয়েছে। অন্যতম রবীন্দ্রানুরাগী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোও রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা-থাকাকালীন এমন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা তাঁকে মুখে মুখে অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া বলেন অনুবাদটা লিখে দিতে। তখন রবীন্দ্রনাথ যে লিখিত রূপটি উপস্থিত করলেন তাতে অনেক কিছুই বাদ থেকে গেল। এবং ওকাম্পোর মতে, সেই অংশগুলোই ছিল কবিতার মূল কেন্দ্র। এতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের মানুষ ওকাম্পো ওই অংশগুলোতে আগ্রহী হবেন না। তাঁর এই কথা শুনে ওকাম্পো অপমানিত বোধ করেছিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য একেবারেই তা ছিল না। এটা ছিল তাঁর নিজের বিশ্বাসের বিষয় এবং এটা তাঁর ভুল ছিল।
অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি মন্তব্যের আশ্রয় নেব। তিনি বলেছিলেন, লেখনী হচ্ছে লেখকের রক্ত। লেখনীকে তৈরির জন্য সারা বিশ্বের সঙ্গে যে ভাবে যুক্ত হতে হবে সেই পদ্ধতিটার নাম অনুবাদ। এই পত্রলেখক এর সঙ্গে শুধু যোগ করতে চায়— শুধু বিশ্ব নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গেও লেখনীকে যুক্ত হতে হবে।
গৌতম নারায়ণ দেব, কলকাতা-৭৪
উদ্যোগ চাই
বিতস্তা ঘোষালের “অনুবাদে ‘বিশ্বসাথে যোগ’” অত্যন্ত বাস্তবধর্মী একটি প্রবন্ধ। অনুবাদ সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবল ভাবে জড়িত। সাহিত্যের মধ্যে যেমন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, তেমনই অনুবাদ সাহিত্যও কিন্তু সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা।
দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত আছে। মরাঠি, গুজরাতি, কন্নড়, তেলুগু, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য আছে। এক রাজ্যের মানুষের পক্ষে অন্য রাজ্যের ভাষা রপ্ত করে, তার পর সেই এলাকার সাহিত্য অনুবাদ করে নিজের রাজ্যের সাহিত্যভান্ডার ও মানুষের মন সমৃদ্ধ করা, এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই ভাবে আপন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামীদামি সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকারের অনুবাদে আমরা যেমন জ্ঞানার্জন করতে পারছি, বিশ্বকে জানতে পারছি, তেমনটি কিন্তু আমার স্বদেশে পারছি না। বর্তমান সাহিত্যিক, কবি, অনুবাদকদের এগিয়ে আসতে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীকে চিনতে ও চেনাতে হবে, তবেই তো আমরা জাতিগত ভাবে এবং ভারতবাসী হিসাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আরও উচ্চাসনে বিরাজ করতে পারব।
মানিক কুমার বসু, কলকাতা-১০৮
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)