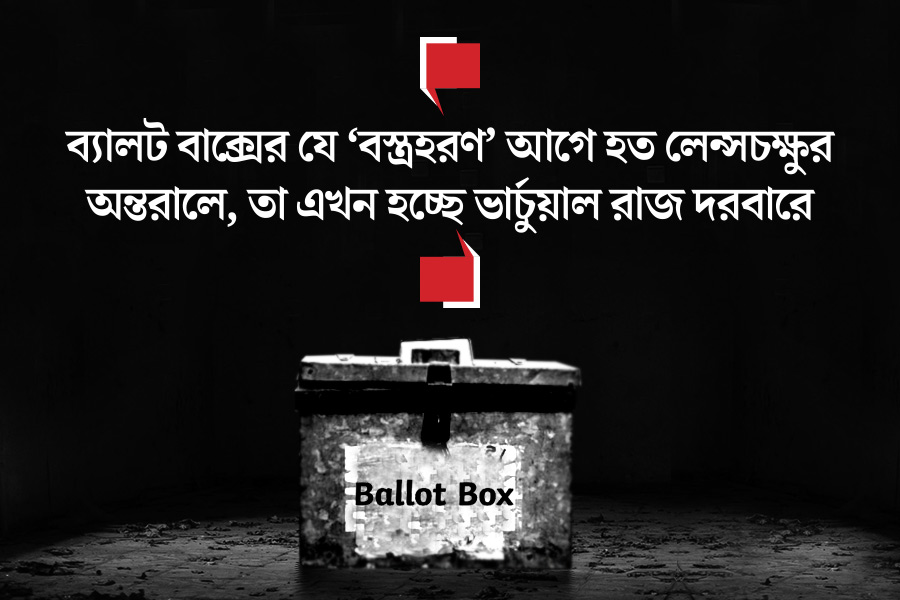চিনের উপর নির্ভরতা কম করতে কি ভারত সফল? অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রে কী প্রভাব এই নীতির?
চিনের প্রতি নির্ভরশীলতা কমাতে পশ্চিমী দুনিয়া যে সব নীতি অনুসরণ করেছে, ভারতও তা-ই করতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে কি সত্যিই চিন-নির্ভরতা কমেছে এ দেশের?
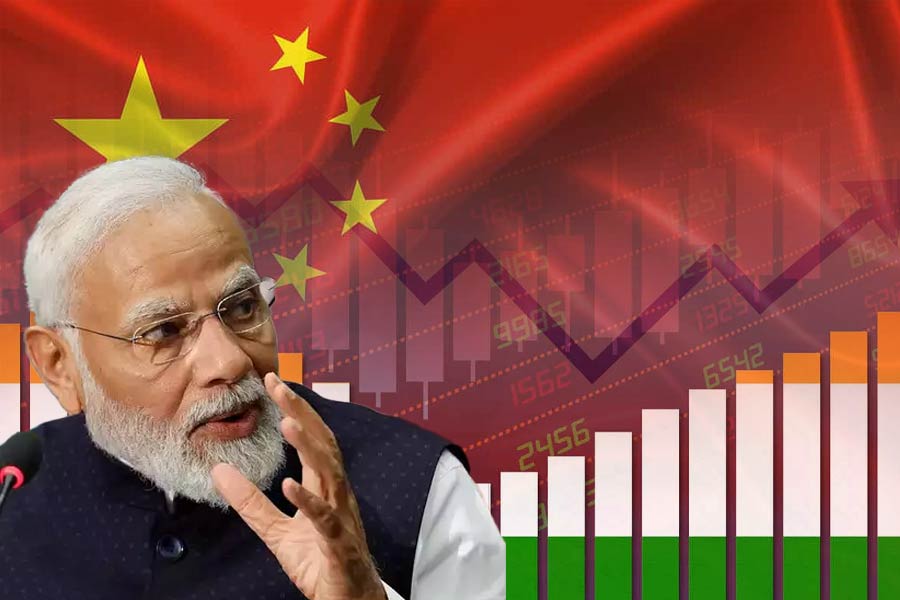
চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে গিয়ে কতখানি আত্মনির্ভর হল ভারতীয় অর্থনীতি? — ফাইল চিত্র।

টি এন নাইনান
১৯৯১ এবং তার পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি কার্যত দেশীয় এবং বিশ্ববাজারে বিনিয়োগের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল। এই সব সংস্কার রেগন-থ্যাচার জমানার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সেটি হল অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে ফেলা। বিষয়টিকে ‘লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন’ (উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন) বা সংক্ষেপে ‘এলপিজি’ বলে উল্লেখ করা হতে থাকে। বৃহত্তর অর্থে বাজার অর্থনীতি যে ভারতের উপকারেই আসবে, এমন এক বিশ্বাসকে ধাপে ধাপে (অথচ আংশিক ভাবে) প্রকাশ্যে আনার কাজ শুরু হয়। এর ফলে অবশ্য অর্থনীতির দ্রুততর বৃদ্ধি, মুদ্রস্ফীতি হ্রাস, বাণিজ্য-সমতায় উন্নতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে দেখলে দেশের অর্থনীতিকে আগের থেকে বেশি দৃঢ় বলে মনে হতে থাকে।
কিন্তু খুব শীঘ্রই এর গোলমেলে দিকগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পোৎপাদন হ্রাস, উপযুক্ত চাকরির অভাব এবং সামাজিক অসাম্য প্রকট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেখা যায়, বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পণ্য এবং উপকরণের জন্য চিনের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ বেড়েছে। পাশাপাশি সৌরশক্তি উৎপাদন, বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা দূষণের মাত্রা কমানোর প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করে। এ সবের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায়, বাণিজ্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বেড়েছে, শুল্কের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, শুল্ক ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধা নতুন করে দেখা দিয়েছে, চিনা পণ্যের উপর কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। এই সময়েই শিল্পে সরকার-নির্ধারিত বিনিয়োগের পরিমাণ নতুন করে বাড়ে। এর ফলে বিনিয়োগে ভর্তুকি, উৎপাদনে ইনসেন্টিভ প্রদান, শুল্কছাড় এবং কিছু বাছাই বণিক গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক নীতি থেকে এই পরিস্থিতিকে হয়তো সম্পূর্ণ অর্থে উল্টো দিকে ঘুরে যাওয়া বলা যাবে না (বিশেষত যেহেতু সেই সময়কার আর্থিক সংস্কারগুলি কখনওই করে ওঠা সম্ভব হয়নি)। কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণে যে একটি বড়সড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা না-কমে উল্টে বেড়ে গিয়েছএ, তা অস্বীকার করা যায়নি।
এর ফলে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পশ্চিমী দুনিয়ায় সে সময় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে যাচ্ছিল, তার প্রভাব এ দেশেও এসে পড়ে। আমেরিকা-সহ অন্যত্র শিল্পোৎপাদন কমানোর ফলে চাকরির বাজার সঙ্কুচিত হয়, অসাম্য প্রকট হয়ে ওঠে এবং চিনের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। সেই সঙ্গে রাজনীতি আরও বেশি মাত্রায় গণমুখী হয়ে ওঠে, অর্থনীতিতে জাতীয়তাবাদী চরিত্র বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অবাধ বাণিজ্য নিয়ে এক সময়ে যাঁরা গলা ফাটাতেন, তাঁরা তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘সর্বাগ্রে আমেরিকা’ নীতি বা পরবর্তী কালে বাইডেনের ‘নিউ-ওল্ড’ নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাণিজ্য চুক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটান, বিনিয়োগে ইনসেন্টিভের মাত্রা বাড়াতে চান, কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে আঞ্চলিক স্তরে আবদ্ধ রাখতে উদ্যোগী হন। একই সঙ্গে চিনা পণ্যের আমদানির উপর বাধা আরোপিত হয়, চিনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির আদান-প্রদানও নিষিদ্ধ হয়।
এ সবের ফলে ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সংস্থা অতি দ্রুত আমেরিকার দিকে ঝোঁকে। আমেরিকার শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ দু’বছরে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। উল্লিখিত অঞ্চলের যে সব দেশ এক সময়ে এর বিরোধিতা করেছিল, এখন তারাই আমেরিকার বিনিয়োগ-ভর্তুকির নীতিকে অনুসরণ করে এবং চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে নিয়ন্ত্রণ আনে। প্রত্যুত্তরে বেজিংও তার নীতি বদলায়। তারা গ্যালিয়াম এবং জার্মেনিয়ামের রফতানি নিষিদ্ধ করে। এই দুই উপকরণ ইলেক্ট্রনিক্স, বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নির্মাণ এবং টেলিকম শিল্পে ব্যবহৃত হয় (উল্লেখ্য, ভারত বিশ্বে এই দুই উপকরণের রফতানিতে তৃতীয় স্থানে আছে)। সেই সঙ্গে চিন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সরব হয়, মুক্ত বাজারের দাবি জানাতে থাকে। কারণ, বিদ্যুৎচালিত গাড়ি-সহ অন্যন্য পণ্যের রফতানি উদ্বৃত্ত তার কাছে দায় হয়ে দাঁড়ায়।
অন্য দিকে, বিভিন্ন দেশ চিনা পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রমেই কঠোর হতে শুরু করে। আমেরিকা এবং ইউরোপে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি পিছু ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫০০ আমেরিকান ডলার। জার্মানি থেকে ইনটেল একটি ‘চিপ’ নির্মাণকেন্দ্র তৈরির জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি পায়। জেনারেল ইলেক্ট্রিকের মতো সংস্থা, যারা এক সময়ে উৎপাদনে গুরুত্ব কমাতে চেয়েছিল, তারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। গুরুত্বপুর্ণ শিল্পক্ষেত্রগুলিতে নতুন করে উৎপাদন বাড়নোর হিড়িক পড়ে। এবং এই ক্ষেত্রগুলি থেকে বিপুল আয় আশা করা হতে থাকে।
এই সব নীতির পরিণাম কি শেষমেশ ভাল দাঁড়ায়? অতিরিক্ত উৎপাদন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন, ভর্তুকিপ্রাপ্ত এবং সরকারের তরফে সুরক্ষাপ্রাপ্ত বাজারগুলির ক্ষেত্রে অবশ্যই এর ফল ভাল দাঁড়ায়নি। শুল্কবৃদ্ধি অনিবার্য ভাবে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যদিও চিন থেকে দূরে থাকার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হয়, এর সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, চিনের তরফে এক রকমের প্রতিশোধস্পৃহা এখনও রয়ে গিয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির উপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, অনিবার্য ভাবে সরকারি ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। মাও জে দং যে ‘প্রাচ্য বাতাস’-এর উপমা দিয়েছিলেন, তাকে ‘পশ্চিমী বাতাস’ টপকে যেতে পারেনি। বরং চিনের প্রতি নির্ভরতার পরিমাণ ঝড়ের বেগে বেড়ে গিয়েছে।
ভারতও অন্যদের মতো একই নীতিতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। কিন্তু তার এই বিশ্বাস খুব বেশি দৃঢ় হতে পারেনি। উৎপাদনে বৈচিত্র আনা এবং যোগানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে অন্যান্য দেশ তেমন সুবিধে করে উঠতে না পারলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রশংসা আদায় করার মতো জায়গায় যেতে পেরেছে। ভারতকে রফতানির বিকল্প হিসেবে উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কর্মনিযুক্তি নিয়ে বেশি করে ভাবতে হয়েছে। যার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য দেখা দিয়েছে। মোবাইল ফোনের ‘অ্যাসেম্বলিং’ শিল্পের ক্ষেত্র তার প্রমাণ। কিন্তু একই সঙ্গে বৃহৎ দেশ হওয়ার অসুবিধাগুলির মোকাবিলাও তাকে করতে হচ্ছে এবং আমদানির বিকল্প নির্মাণের ব্যাপারে জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হচ্ছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy