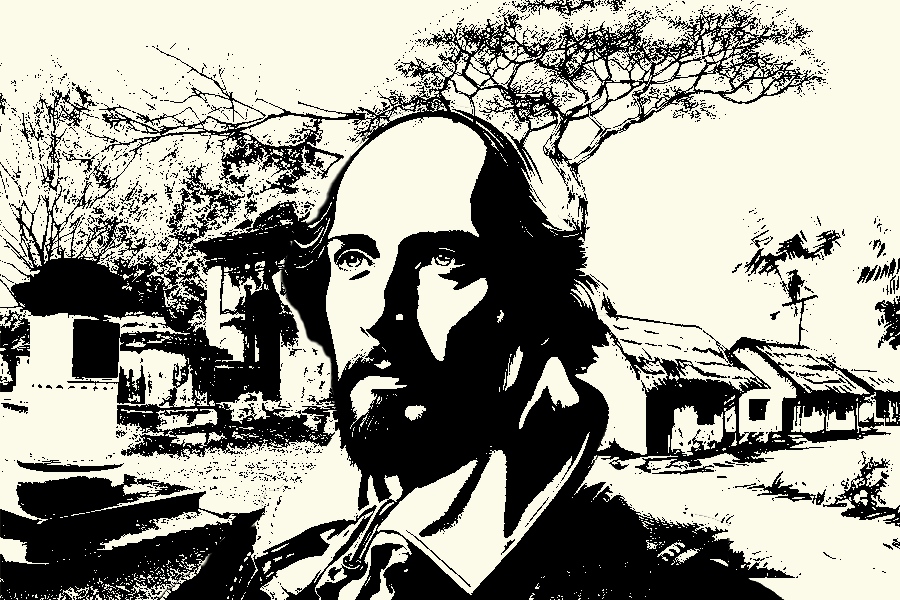মন্বন্তর-মারিতেও স্বাস্থ্যবিধি না মানাই কি বাঙালির বৈশিষ্ট্য?
গ্রামবাংলার ম্যালেরিয়া যা-ই হোক, করোনা নয়। অক্সিজেন লাগত না। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া-র কথা বলা যায়।

গৌতম চক্রবর্তী
আদৌ উচিত কি ভ্যাকসিন নেওয়া? যদি জিনিসটা আদৌ মেলে, তা হলে কোভ্যাক্সিন না কোভিশিল্ড? নিলেও তো মুখচ্ছদ এঁটে, স্যানিটাইজ়েশন চালাতে চালাতে জীবন জেরবার হবে। আর দ্বিতীয় তরঙ্গে তো টিকা নিয়েও কত লোক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন! ভাবতে ভাবতেই চোখ আটকাল প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক-এ।
পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল, এই সংশয় চিরন্তন। প্লেগের টিকা এসে গিয়েছে। মহাস্থবির বাঙালির মনোভাব জানাচ্ছেন, “কেউ বললে, টিকে নেবার দশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ কাবার হয়ে যায়। কেউ বললে, পেট থেকে এত পয়সা মাপের মাংসের বড়া তুলে নিয়ে তার ভেতর প্লেগের বীজ পুরে দেওয়া হয়।” সংশয় বাঙালির স্বভাবধর্ম।
স্কুলবেলা থেকে জানি, “মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি।” কিন্তু মাস্টারমশাইরা বলেননি, মন্বন্তর-মারিতে স্বাস্থ্যবিধি না মানাই বাঙালির বৈশিষ্ট্য। উপরমহলে সংযোগ থাকলে তা সহজতর। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের কথাই ভাবুন! চাকরি খুঁজতে সে বর্মা গিয়েছে। জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে ভিড়বার আগেই ডেকের যাত্রীদের মধ্যে ‘কেরেন্টিন’ বলে ভয়ার্ত চিৎকার। “তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া গিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়।”
অভয়ার অনুরোধে শ্রীকান্ত কোয়রান্টিনে যাওয়ার জন্য ছোট স্টিমারে ওঠে। জাহাজের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে তার বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। ডাক্তার হাত নেড়ে তাকে ডাকেন, “আপনাকে যেতে হবে না।” মহামারির সময়েও বাঙালি স্বেচ্ছাচারী। সে দ্বিতীয় বা তৃতীয়, যে তরঙ্গই আসুক না কেন!
দ্বিতীয় তরঙ্গ কি আজই প্রথম? ১৮৮৬ সালে বাংলায় ম্যালেরিয়ার জন্য সরকারি ওষুধপত্র নিতে আসেন ৪৬,১২৭ জন। চার বছরের মধ্যে ১৮৯০ সালে রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ছাপিয়ে যায়।
এই ওষুধ-ভরসার পুরোটাই রোগীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার প্রসার নয়। রোগের গতিপ্রকৃতি, সরকারি নীতিরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অতিমারির কোনও পর্যায়েই ঔপনিবেশিক সরকার কেবল খোলা বাজারে ওষুধের উপর নির্ভর করেনি। গ্রামগঞ্জের হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মায় পোস্ট অফিসেও ম্যালেরিয়ার ওষুধ মিলত। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন তাঁর ঠাকুরদার কথা জানাতে গিয়ে লেখেন, বর্ধমানের গ্রামেও “বারো মাস তিনি এক ডেলা করে কুইনিন খেতেন। পোস্ট অফিস থেকে কেনা বড়ো কুইনিনের শিশি থেকে গুঁড়ো নিয়ে ছোট মার্বেলের স্লেটে— যেমন ডাক্তারখানায় তখন থাকত— ঢেলে জল দিয়ে ছুরি করে মাখতেন, হাত দিতেন না। তাই খেয়ে তবে প্রাতরাশ করতেন।”
খোলা বাজার ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় মহামারি রুখতে সেখানে তখন বাংলায় হরেক সংস্থার হরেক কিসিমের বিজ্ঞাপন। বোঝা যায়, নাগরিক মধ্যবিত্ত খদ্দেরকে আকর্ষণের জন্য। শ’ ওয়ালেস বার করেছে ‘ডাস্ট গান’। বিজ্ঞাপনে লেখা, ‘ফর ড্রাই স্প্রেয়িং ইন ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল’। মার্টিন হ্যারিস এনেছে ‘কুইনাইন সল্ট’। তারই মধ্যে বসন্তপুরের করালীচরণ রায় ছড়ায় আফসোস করছেন, “ম্যালেরিয়া বাড়ে যত পেটেন্ট ওষুধ তত/ চারিদিকে হতেছে উদয়/ দু চারটি বাদে তার কোনটিতে নাহি সার/ শুধু তাহা প্রবঞ্চনা ময়।” উপনিবেশ ‘সোনার বাংলা’র স্বপ্ন দেখায়নি, মানুষকে অতিমারিতে পুরোপুরি খোলা বাজারে ঠেলে দেয়নি।
গ্রামবাংলার ম্যালেরিয়া যা-ই হোক, করোনা নয়। অক্সিজেন লাগত না। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া-র কথা বলা যায়। সেখানে অতুল গ্রামে এসে জানতে পারে, জ্ঞানদা ও তার মা দুর্গামণি হরিপালে চলে যাচ্ছে। অতুল বলে, “মেজমাসিমা গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর শেষ দেখাটা দেখতে আসব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ডিপো!” বাংলার মানচিত্রে কোনটা সংক্রমণের ‘রেড জ়োন’, জানিয়ে দিলেন লেখক।
পরের অধ্যায়ে, দুর্গামণি বাপের বাড়ি হরিপালে পৌঁছোনোর পরই শরৎচন্দ্রের সেই চমৎকার লাইন, “শম্ভু চাটুয্যের সে দিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন। অতএব, সূর্যাস্তের পরই তিনি প্রস্তুত হইয়া বিছানা গ্রহণ করিয়াছিলেন।”
যে জ্বর নিয়ম করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে, আবার ছেড়েও যায়, গ্রামের গেরস্ত শম্ভুরা এই ভাবেই তার সঙ্গে মানিয়ে নিতেন। এটাই জনজীবন। ব্রিটিশরা একটা গোড়ার কথা জানত। দায়িত্ব না এড়িয়ে সরকার ওষুধ, হাসপাতালের বন্দোবস্ত করবে, বাকিটা লোকে নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝে নেবে।
বাঙালির ট্র্যাজেডি অন্যত্র। অতিমারিতে তার ব্রাহ্মণত্ব ও জাতপাতের অহঙ্কার বাড়ে। শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই উপন্যাসে গ্রামে কলেরা দেখা গিয়েছে। তারিণী মুখুজ্যের ছোট ছেলে ভেদবমিতে মারা গিয়েছে। পরের দিন উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন দেখে, তারিণীর বাড়ির মহিলারা পুকুরঘাটে সেই মৃত ছেলের কাপড় কাচছে। বৃন্দাবন বারণ করে। তারিণী উল্টে অভিশাপ দেয়, “উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।”
আরও আছে। বিভূতিভূষণের বিপিনের সংসার উপন্যাসে ম্যালেরিয়ার সিজ়ন। হাতুড়ে ডাক্তার বিপিনের হাটচালায় রোগীর ভিড়। সেখানে “সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, যদু ডাক্তারের পসার একেবারে মাটি হইয়া গেল।... দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন... যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক, আপনি হলেন ব্রাহ্মণ! কিসে আর কিসে?”
বাঙালি ব্রাহ্মণ যে কী বস্তু, প্রমাণ সুকুমার সেনের আত্মজীবনীতে। বর্ধমান, হুগলির গ্রামের অনেকে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ঘরছাড়া। ইংরেজ সরকার দায়িত্ব এড়াল না, লঙ্গরখানা খুলল। সেখানে সরকারি টিকিট দেখালে দুঃস্থরা খাবার পাবেন। কিন্তু বিপৎকালেও রান্না করা খাবার খেতে বাঙালি হিন্দুদের আপত্তি। মুসলমান দূর অস্ত্, উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে লঙ্গরখানায় রান্না খাবার নিতে নারাজ।
এত জাতপাত, এত শ্রেণিবিভাজন, ওষুধ নিয়ে এত সংশয়েও বাঙালি সে দিন হারায়নি তার স্বকীয়তা। ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দ, নিবেদিতারা কলকাতার রাস্তায় প্লেগ রোগীর সেবায় নেমেছিলেন, জানা কথা। পরের বছরই স্বাস্থ্য পত্রিকার খবর: “গত বৎসর প্লেগের প্রকোপের সময় সংকীর্ত্তনের মহা ধুম পড়িয়াছিল। এ বৎসর প্লেগ ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধরিয়াছে, প্রতি দিন প্রতি পল্লীতে মহা ধুমধামে দলে দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইতেছে।” সেই সেকেন্ড ওয়েভেও বাঙালি হারায়নি নিজস্বতা। সংবাদদাতা জানিয়েছেন, “হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরাও দলে দলে এই নামকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছে।”
প্লেগের আরও গল্প আছে। ১৮৯৭ সালে এল ‘মহামারি আইন’। এই আইনবলে রোগ সন্দেহে পৃথকীকরণ, রেল ও সড়ক যাত্রীদের পরীক্ষা ও প্রয়োজনে আটক করা অবধি যে কোনও ব্যবস্থা করতে পারত ব্রিটিশ সরকার। গোলটা ছিল এই দমননীতিতেই। প্লেগ কর্মচারীরা গেরস্তের বাড়িতে ঢুকে মেয়েদেরও পরীক্ষা করবে, আব্রুহানি ঘটবে, জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, সেখানে জাত-ধর্ম ব্যতিরেকে শুয়ে থাকতে হবে। মানে, নিজের শরীরের অধিকারও ভারতীয়দের নেই, সবই ঔপনিবেশিক সরকারের বলপ্রয়োগের বিষয়।
অতএব, বিদ্রোহ। কলকাতার ঝাড়ুদার, মেথর, কুলি-মজুরেরা কাজ বন্ধ করল, টিকাদারদের ধরে পেটানো শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশ জানায়, “যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল, তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজতক্মা পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল।”
অচিরে সরকার দমননীতির ভুল বুঝল। পৃথক পারিবারিক, জাতীয় হাসপাতাল, ওয়ার্ড হাসপাতাল চালু করা হল। পুরুষদের পরীক্ষার জন্য পুরুষ ডাক্তার, মেয়েদের জন্য স্ত্রী-ডাক্তারের বন্দোবস্ত হল। সরকার ভুল করেছে, শুধরেও নিয়েছে। হাত তুলে ‘সবই মানুষের দায়িত্ব’ বলে সান্ধ্য বার্তা দেয়নি।
প্লেগে সুরেশের মৃত্যুর কথাও না বললে নয়। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসে বড়লোকের খেয়ালি ছেলে, বন্ধু মহিমের স্ত্রী অচলাকে নিয়ে পশ্চিমে পালায় সে। শেষে প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে সংক্রমণ। অচলাকে অনুরোধ করে, “ব’লো যে, সংসারে আর পাঁচ জনের যেমন মৃত্যু হয়, তাঁর মৃত্যুও তেমনি হয়েছে— মরণকে কেবল এড়াতে পারেন নি বলেই মরেছেন, নইলে মরবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না।” যে সব বাঙালি আজ মাস্ক ছাড়া হাটে-মাঠে-রাস্তায়-বাজারে ঘুরছেন, তাঁরা সকলে সুরেশের উত্তরসূরি কি না, অক্সিজেনের অভাবে খাবি খাওয়ার সময়েও তাঁদের সে রকম মনের জোর থাকবে কি না, সে সব প্রশ্ন ভাবী শরৎচন্দ্রদের জন্য তোলা থাক!
গল্প যে কত! বিভূতিভূষণের অশনি-সংকেত উপন্যাসে গঙ্গাচরণ ‘গাঁ বন্ধ’ করতে যাবে। মানে, গ্রামে যাতে ওলাউঠো বা কলেরা না ঢোকে, সে জন্য মন্ত্র পড়ে গ্রামের চার দিকে গণ্ডি টানতে হবে। গাঁ বন্ধ করতে কী কী লাগবে, ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ যজমানদের ফর্দ দেয়। দশ সের আলোচাল, আড়াই সের গাওয়া ঘি, আড়াই সের সন্দেশ, তিনটে শাড়ি ইত্যাদি।
১৯৪৩ সাল, ক’দিন পরেই এ সব গ্রামে শোনা যাবে মন্বন্তরের পদধ্বনি। চালের দাম হুহু বাড়বে, কেউ খিদের জ্বালায় বুনো শাক আর কচু খেয়ে মরে পড়ে থাকবে। তখনও দুর্যোগের মেঘ দেখা দেয়নি। গঙ্গাচরণের স্ত্রী স্বামীকে বলে, “গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো? এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা...।” গঙ্গাচরণ হাসে, “আমি পাঠশালার ছেলেদের ‘স্বাস্থ্য প্রবেশিকা’ বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। তাতেই গাঁ বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।”
সে যুগে গ্রাম্য বাঙালি লোকাচার মেনে ‘গাঁ বন্ধ’ করতে গেলেও ভিতরে বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যবিধিতেই ভরসা রাখত। একুশ শতকে বাঙালির দিয়া জ্বালানো, থালা বাজানোয় অবশ্য এই রকম সাবটেক্সট ছিল না। শুধু প্রধানমন্ত্রীর হুকুমনামা ছিল।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy