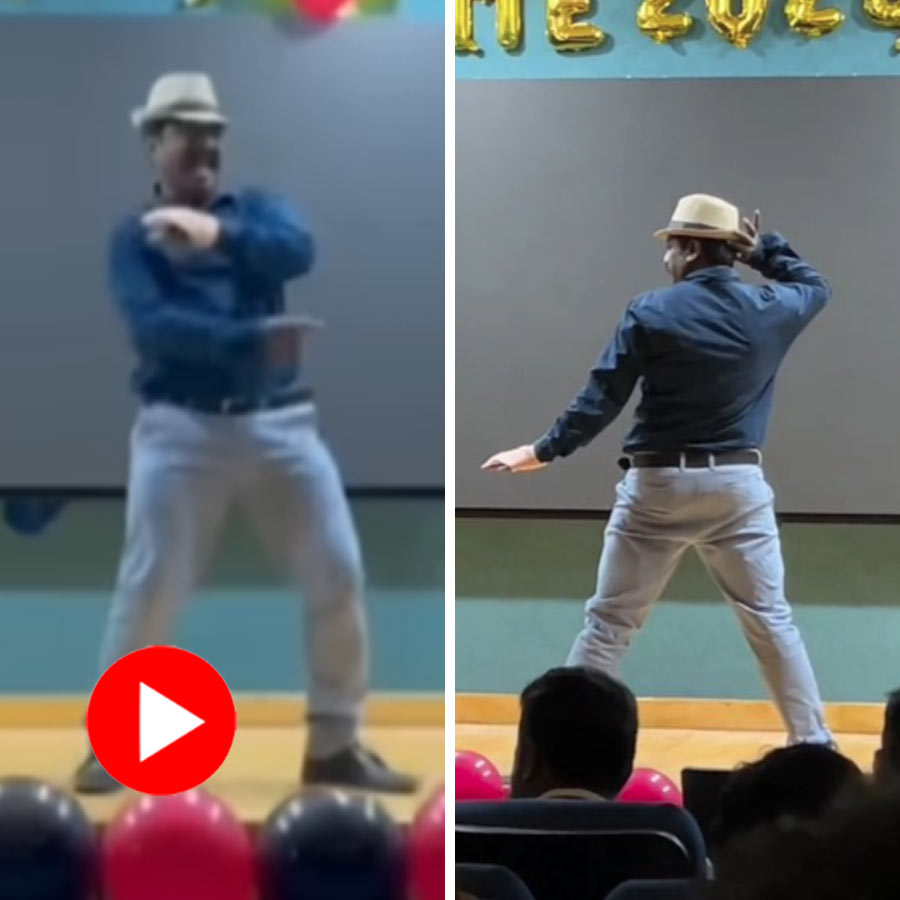নিজে গাড়ি চালাতে পারি না, তা নিয়ে ভারী সঙ্কুচিত থাকি। তাই আমেরিকায় আজকাল গাড়িরা নিজেরাই নিজেদের চালাচ্ছে দেখে মনটা নেচে উঠল। সাদা গাড়ির মাথায় কালো টুপি, সেটা ঘুরে ঘুরে চার দিকের ‘ডেটা’ সংগ্রহ করছে। আর সে সব তথ্য চটজলদি ‘প্রসেস’ করে গতিপথ ঠিক করার কাজটা করছে কৃত্রিম মেধা (এআই)। বছর চার-পাঁচ হল এমন গাড়ি সায়েন্স ফিকশনের পাতা থেকে নেমেছে রাস্তায়। ২০২৫ সালে বড় করে নামছে বাজারে।জানুয়ারির গোড়াতেই খবর, আমেরিকার কিছু শহরে ‘উবর’ অ্যাপ দিয়ে চালকহীন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ক’দিন পর। চালকহীন মিনিবাস চলা শুরু হচ্ছে নরওয়ের অসলো, জার্মানির ক্রোনা, সুইটজ়ারল্যান্ডের জেনিভায়। তবে সব চাইতে বেশি চালকহীন গাড়ি চলছে যে দেশে, তার নাম চিন। বেজিং-সহ উনিশটি শহরে চলছে রোবোট্যাক্সি, রোবোবাস। ২০৩০ সালের মধ্যে সাবেক গাড়ির পাশাপাশি চালকহীন গাড়ি চলবে বিশ্বের নানা শহরে। ভারতেও গোটাকতক ‘স্টার্টআপ’ লেগে রয়েছে, যাতে ভিড়, বিশৃঙ্খল রাস্তাতে চালকহীন গাড়ি চলে, তার কৌশল খুঁজতে।
চালকহীন গাড়ি চড়ব, ভাবতে উত্তেজনা আছে, ভাড়া কমার আশা আছে, রয়েছে ক্লাচ-অ্যাকসিলারেটর গুলিয়ে ফেলার গ্লানি থেকে মুক্তি। সেই খুশির আলো ফোটার আগেই ঘনিয়ে আসে লজ্জার মেঘ। ড্রাইভারদের ভাত মেরে ট্যাক্সি চড়ার শখ? ছি! কলকাতায় রোবোট্যাক্সি ডেকে বইমেলা যেতে এখনও হয়তো বছর ছয়-সাত, কিন্তু তার পর? এ বছর ‘কলকাতার প্রতীক’ সাত হাজার হলুদ ট্যাক্সির সাড়ে চার হাজারই বুড়ো হওয়ায় বাতিল হবে। ২০১৫-য় অ্যাপ ক্যাব এল স্মার্ট ফোনের হাত ধরে, ‘ট্যাক্সিওয়ালা’ পিছু হটলেন। এআই এলে অ্যাপ ক্যাব চালকদের কী হবে?
আর যাঁরা অ্যাপ ক্যাব ডাকেন, তাঁদেরই বা কী হবে? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ব্যাঙ্ক-কর্মী, গ্রাহক-সম্পর্ক কর্মী, সাংবাদিকদের চাকরি গেল বলে। নির্মাণ, উৎপাদন, পরিবহণ, অজস্র কর্মক্ষেত্রে যে সব কাজ মানুষ করছে, তার অর্ধেক কাজ এখন, এই মুহূর্তে, এআই-সহ নানা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দিয়ে করানো যায়, বলছে ম্যাকিনসে সংস্থার সমীক্ষা। এআই-এর জন্যে বিশ্বে চার কোটি থেকে আট কোটি কাজ চলে যাবে ২০৩০ সালের মধ্যে। হাতে মাত্র পাঁচ-সাত বছর।
কর্পোরেট কর্তারা ভরসা দিচ্ছেন, পুরনো কাজ যাক না, নতুন কাজ আসবে। স্বয়ংক্রিয় গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি, গাড়িকে শেখানো-পড়ানোর জন্য সফটওয়্যার কর্মী, সেন্সর আরও সূক্ষ্ম করতে হার্ডওয়্যার কর্মী, ট্যাক্সি-বাহিনীর ব্যবস্থাপক, কত রকম কর্মী লাগবে। কিন্তু এ সব নতুন কাজ কী করে শিখবে লোকে? প্রশ্ন তুললেই টুপি থেকে পায়রা বার করার মতো, বাজেটের বাক্স থেকে সরকার ফস করে বার করে ফেলে নানা প্রকল্প— প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা, ন্যাশনাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রমোশন স্কিম। কাজের বেলা দেখা যায়, দিল্লি দূর অস্ত্— ২০১৫ সালে কেন্দ্র লক্ষ্য নিয়েছিল, ২০২২ সালের মধ্যে চল্লিশ কোটি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২৪ অবধি ‘স্কিল ইন্ডিয়া মিশন’ ট্রেনিং দিয়েছে দেড় কোটিরও কম লোককে। চাকরি পাওয়ার হার কহতব্য নয়। অথচ, ভারতের আশি শতাংশ সংস্থা দক্ষ কর্মীর অভাবে ভুগছে। কাজের কর্মী নেই, কর্মীর কাজ নেই।
আরও ভাল কাজ কে না চায়? ড্রাইভার রাতদিন গাড়ি চালান, যাতে ছেলেকে ড্রাইভারি না করতে হয়, পরিচারিকা চার বাড়ি কাজ করেন যাতে মেয়েকে না বাবু-বাড়ি যেতে হয়। কিন্তু সরকার বা কর্পোরেট কর্তারা যে কথাগুলো চেপে যান, সেগুলো তাঁরা আন্দাজে বোঝেন। এক, যত কাজ চলে যাচ্ছে, অত কাজ তৈরি হচ্ছে না। দুই, যত তাড়াতাড়ি কাজ যাচ্ছে, অত তাড়াতাড়ি কাজ তৈরি হচ্ছে না। আর তিন, যাদের কাজ যাচ্ছে, তাদের জন্য কাজ তৈরি হচ্ছে না। তা হলে পুরনো কাজ আঁকড়ে ধরা ছাড়া উপায় কী? আমেরিকার ট্যাক্সি চালকদের তেত্রিশটি ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছে, চালকহীন গাড়িকে যেন ছাড়পত্র না দেওয়া হয়। ওহায়োর চালকরা স্লোগান দিয়েছেন, ‘পিপল বিফোর রোবটস।’
চিনে ট্যাক্সি চালকের সংখ্যা সত্তর লক্ষ। তাঁদের কী হবে, সে প্রশ্ন করলে বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অর্থনীতির অধ্যাপক বলেছেন, নতুন কাজ তৈরি, আর পুরনো কাজ ধ্বংস, এই দুটোর গতির মধ্যে একটা ভারসাম্য চাই। সে তো চাই, কিন্তু দেয় কে? চালকহীন গাড়ির মতো নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষায় শিল্পপতিদের বিপুল ব্যয় হয়, তাঁরা সেই টাকা তুলতে মুখিয়ে থাকেন। আইন-বিধি দিয়ে, কর বসিয়ে, পুরনো কাজ মিলিয়ে যাওয়ার আগে নতুন কাজ তৈরি, কর্মী তৈরি, কর্মহীনের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রেরই।সেটা তার কর্তব্যও বটে— সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। নতুন প্রযুক্তি একঘেয়ে, বিপজ্জনক কাজ থেকে মুক্তি দেয়। গাড়ি-চালক, গৃহপরিচারক, সাফাইকর্মীরাও যেন সেই মুক্তির স্বাদ পান, দাসশ্রমের অপর কোনও খাঁচায় বন্দি না হতে হয় তাঁদের, তা দেখবে কে, রাষ্ট্র ছাড়া? তেমন রাষ্ট্রের উপযুক্ত রাজনীতি আজ চাই।
সেই রাজনীতি কর্মহীনদের ভাতা, ঋণ-অনুদান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে না। কাজ হারানোর ভয়কে জাতি-ভাষা-ধর্ম হারানোর ভয়ে পরিণত করে হাড় জ্বালাতন করবে না। আবার, শিল্প কখন উৎপাদনকুশল, উন্নয়ন-বান্ধব আর কখন অপচয়বহুল, দারিদ্র-প্রসবকারী, তার বিচার করতেও পিছপা হবে না। নতুন প্রযুক্তি নতুন কাজ তৈরি করছে ঠিকই, কিন্তু সে সব কাজ যে সব সময় আরও ‘উন্নত’ কাজ হচ্ছে না, তা গিগ ডেলিভারি কর্মীদের দিকে দেখলেই বোঝা যায়। সমস্যা কেবল কিছু খারাপ মালিক, ‘বস’-কে নিয়ে নয়; যে কোনও কর্মীকে দিনে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা কাজ করিয়ে, ছিবড়ে করে অবশেষে ছেঁটে ফেলাই ভারতের শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রে আজ ‘ওয়ার্ক এথিক’। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য, ভারতে একান্ন শতাংশ কর্মী সপ্তাহে ঊনপঞ্চাশ ঘণ্টা বা তারও বেশি কাজ করেন। অতিরিক্ত শ্রম (ওভারওয়ার্ক), ক্লান্তির জন্য কাজ ছেড়ে দেওয়া (বার্নআউট), নানা নিরিখে ভারত শীর্ষের দিকে।
অথচ, প্রয়োজন ঠিক উল্টো। এআই-যুগে চাহিদা বাড়বে চিন্তাপ্রধান, সৃষ্টিশীল কাজের। চাই এমন কর্মী, যাঁরা নতুন নতুন প্রশ্ন তুলবেন, বিকল্প খুঁজবেন। যাঁরা ভাষা, গণিত, দৃশ্যকল্প নিয়ে খেলা করতে পারবেন। এমন কর্মী তৈরি করতে চাইলে কী করা চাই, তার আলোচনা সে ভাবে শুরুই হল না। শিক্ষা, স্কলারশিপ, গবেষণার বাজেট ছেঁটে, স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালানো এআই যুগের কর্মী তৈরির ‘নীতি’ হতে পারে না। যেমন, কাটমানির লোভে ঠিকাদারতন্ত্রের হাতে শ্রমিকের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া ‘রাজনীতি’ হতে পারে না। চটজলদি বাজিমাতের রাজনীতি-করা নেতারা এ যুগে ডাইনোসর। নিজের দাপট রাখতে গিয়ে তাঁরা দেশটাকেও জুরাসিক পার্ক তৈরি করছেন। এমন ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ তৈরি করেছেন তাঁরা, যে স্মার্টফোন-মালিকদের সংখ্যায় ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় (চিনের পরে) হলেও, স্মার্টফোন-হীন লোকের সংখ্যায় বিশ্বে প্রথম।
অতি-সস্তার শ্রম না হলে শিল্প লাটে উঠবে, এই ভয়ের মোকাবিলাও করতে হবে রাজনীতিকে। ৩১ জানুয়ারি, ১৮৬৫ আমেরিকার কংগ্রেস কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি দিয়েছিল কাপাস খেতমালিকদের দাসত্ব থেকে। সংশোধন পাশ করার মতো ভোট পেতে কত কৌশল করতে হয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কনকে, তা স্টিভেন স্পিলবার্গের লিঙ্কন (২০১২) ছবিটি দেখলে মালুম হয়। দাসপ্রথা উঠে গিয়ে ক্ষতি হয়নি, বরং নয়া প্রযুক্তি এসে কাপাস উৎপাদন বাড়িয়েছিল।
একশো ষাট বছর পরে শ্রম-দাসত্ব ঘোচানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির এআই। নস্টালজিয়া-আঠায় আটকে রোবট-বিরোধিতার সময় এ নয়। প্রশ্ন করা চাই, বিপুল কর্মনাশের যে সঙ্কট ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে, রাষ্ট্র কী করে তার মোকাবিলা করবে? রাজনীতি কি নতুন কাজ তৈরির সওয়াল করবে, না কি জোর দেবে জনকল্যাণে, যত দিন না শিল্প তার নিজের নিয়মে এআই যথেষ্ট কাজ তৈরি করে? দলীয় রাজনীতির অন্তহীন খ্যাস্তাখ্যাচাং থেকে বেরিয়ে এ সব জরুরি কথাগুলো এ বার তোলা চাই। চালকের আসন থেকে মানুষকে সরাতে পারে রোবট, কিন্তু রোবটকে কাজে লাগানোর নীতি তৈরির আসনে বসে মানুষই।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)