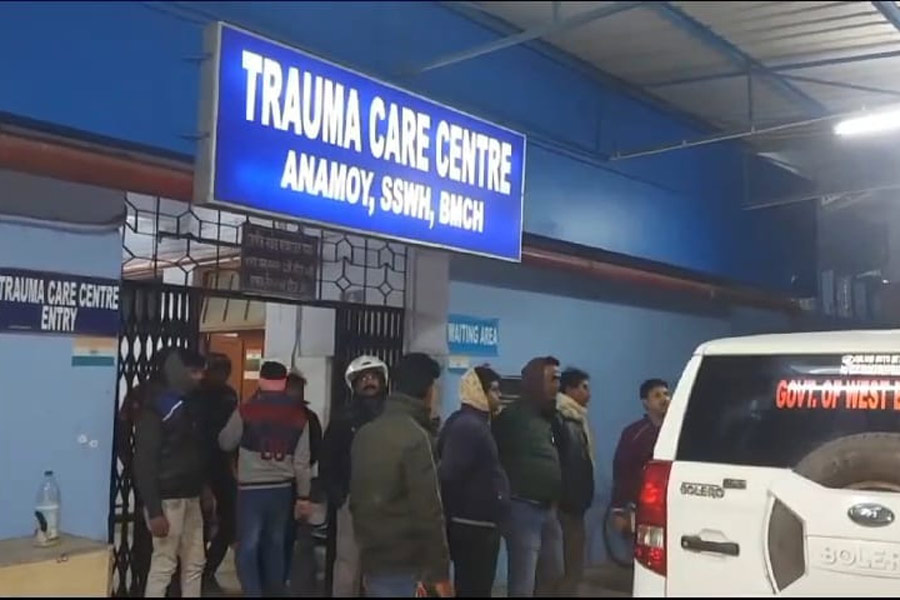সুযোগ পেলেই মাছ ধরতে ভালবাসতেন
পচুই মদের গাদ দিয়ে তৈরি হত সেই ছিপের চার। আমাদের খোশবাসপুর গ্রামে। কলকাতার বাড়িতে আবার দুপুর অবধি টানা লেখা, তার পর অফিস। এ রকমই অলীক মানুষ ছিলেন আমার পিতৃতুল্য বড়দা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। আগামী বুধবার তাঁর নব্বই বছর। সৈয়দ কওসর জামালপচুই মদের গাদ দিয়ে তৈরি হত সেই ছিপের চার। আমাদের খোশবাসপুর গ্রামে। কলকাতার বাড়িতে আবার দুপুর অবধি টানা লেখা, তার পর অফিস। এ রকমই অলীক মানুষ ছিলেন আমার পিতৃতুল্য বড়দা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। আগামী বুধবার তাঁর নব্বই বছর। সৈয়দ কওসর জামাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।
মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি-বহরমপুর হাইওয়ের ধারে আমাদের গ্রাম। খোশবাসপুর। রাঢ় বাংলার ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী রুক্ষতার স্পর্শ, গাছপালা কম, গ্রামের দুপাশে ধু ধু ধানখেত, দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে দ্বারকা নদী। এই নদীর অববাহিকায় এক সময় ছিল বিস্তৃত তৃণভূমি— মানুষসমান ঘাস, কাশ ও নলখাগড়ার জঙ্গল। আর কিছু দূরে হিজল অঞ্চল— অনেক খালবিল ভরা নিচু এলাকা, প্রতি বর্ষায় বন্যায় ভাসত, প্রকৃতিও অকৃপণ ছিল না। ফলে এখানকার মানুষের জীবন ছিল বন্য প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি। ছেলেবেলায় দেখা আমার গ্রাম, নদী ও হিজল অঞ্চলের প্রকৃতি এখন নিশ্চয় বদলে গেছে। কিন্তু এই জীবনের পুরনো ছবিটা বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অনেক গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। এই সব রচনায় ফেলে আসা জীবনকে ফিরে দেখার সুযোগ আমিও পাই। আসলে সে সবের সবটাই তো কল্পনার নির্মাণ নয়, বাস্তব থেকে উঠে আসা জীবনের উপকরণ।
বড়দা যখন খোশবাসপুর ছেড়েছেন আমার বয়স তখন চোদ্দো বছর। ছেলেবেলার এই সময়টা জুড়ে সব সময় তাঁকে দেখেছি বলা যাবে না। প্রথম ছ’বছরের কিছু টুকরো স্মৃতি ছাড়া কিছু নেই। এ সময় দাদা লোকগান আলকাপের দল নিয়ে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদা, সাঁওতাল পরগনায় ঘুরছেন। তখন তিনি ‘ওস্তাদ সিরাজ’ কিংবা ‘সিরাজ মাস্টার’। আসলে তিনি তাঁর দলের নির্দেশক ও পরিচালক দুই-ই। এই সময়ের দু’-একটি স্মৃতি মনে করতে পারি। কখনও কখনও দাদা তাঁর দলবল নিয়ে বাড়িতে আসতেন। আমাদের বাড়ির একটি নতুন অংশ, যা তখনও তৈরি হচ্ছিল, সেখানে এসে থাকতেন। যত দূর মনে পড়ে রিহার্সাল হত, গানবাজনা হত। আমরা ছোটরা ওঁদের দূর থেকে দেখতাম। তাঁর দলের ‘ছোকরা’কে দেখে মজা পেতাম, কারণ মেয়েদের মতো লম্বা চুল ছিল তার। আর একটি ঝাপসা ছবি মনে আছে। আমাদের গ্রামের কাছেই রণগ্রামে এক বার দাদার দলের আলকাপ হচ্ছে মধ্যরাত থেকে। খুব সকালে আমি গেছি ছোড়দার সঙ্গে। ‘ওস্তাদ সিরাজ’-এর দলের সঙ্গে কার দলের পালা কিচ্ছু জানি না। শুধু মনে আছে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত দাদা নিচু মঞ্চে পালা গাইছেন, আর বিপুল দর্শক তাঁর চার পাশে বসে ও দাঁড়িয়ে শুনছে।
আমি স্কুলে যাচ্ছি যখন, দাদা আলকাপ ত্যাগ করে গ্রামে ফিরেছেন, বিয়েও হয়েছে। তাঁকে বাড়িতে নিয়মিত দেখার সুযোগ পাই। এই সময়ের স্মৃতি বেশ উজ্জ্বল। স্কুল থেকে ফেরার পর আমার কাজ ছিল বিকেলে বড় রাস্তার মোড় থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসা। বাসে করে বহরমপুর থেকে কাগজ সংগ্রহ করে কান্দি ফেরার পথে এক ভদ্রলোক, হয়তো তিনিই কাগজের এজেন্ট, আমাকে দেখে সেই দিনের কাগজটি বাস থেকে ছুড়ে দেবেন, আর আমি বাড়ি ফিরে দাদাকে সেটি দেব। দাদার পড়া হলে অন্যরা পড়বে। দাদা সে সময় একটি সমবায় সমিতি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। আমাদের এখানে সমবায় সমিতি প্রায়শই স্থায়ী হয় না। দাদা যে সে সময় অন্য চাকরির চেষ্টা করছিলেন তা এখন অনুমান করতে পারি।
ছিপে মাছ ধরার খুব শখ ছিল বড়দার। সুযোগ পেলেই মাছ ধরতে যেতেন। মনে আছে, যার দিঘিতে মাছ ধরতে যাবেন, তাকে চিঠি লিখে দিতেন। নিয়ে যেতাম আমি। সবাইকে দেখেছি সানন্দে রাজি হতে। মাছ ধরতে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি দরকার হত। ছুড়ে দেওয়া বড়শির কাছে ছড়ানো হত ‘চার’। কত বিচিত্র উপাদান দিয়ে এই চার বানানো হত। পচুই মদের ‘খাড়া’ বা গাদ ভাল ‘চার’ হত। কখনও ছোট ভাই জমিল, কখনও আমি এ সব সংগ্রহ করে আনতাম। দাদার ছিপে কত বার যে উঠতে দেখেছি নানা ধরনের মাছ! আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই মাছ ব্যাগে করে বাড়ি নিয়ে এসেছি। দাদার আর একটি শখ ছিল ফুলগাছ লাগানো। বাড়ির বাগানের দিকে ফাঁকা জায়গায় বেড়া দিয়ে লাগাতেন কত ধরনের গাছ। ডালিয়া, জিনিয়া, সূর্যমুখী ইত্যাদি ফুলের সঙ্গে আমার পরিচয় তখনই ঘটেছিল। ১৯৫৬ থেকেই দাদা আবার সাহিত্যচর্চায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছিলেন।
১৯৬৪ থেকে বড়দা কলকাতায়। বৌদি, দুই পুত্র ও কন্যাকে তখনই কলকাতা আনেননি। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ইউনিয়নের মুখপত্র ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় চাকরি এবং ক্যান্টোফার লেনে বাড়ি ভাড়া করার পরই তাদের নিয়ে এসেছেন। সেই বাড়িতে আমরা এসেছিলাম ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে। আমরা মানে মা, আমি ও আমার ছোট দুই ভাই। ছোড়দা তখন কলকাতায়, হস্টেলে থেকে কলেজে পড়েন। এই সময়ের পর থেকে দাদাকে আমরা গ্রামের বাড়িতে পেতাম বছরে মাত্র এ কবার, পুজোর সময়, দাদা, বৌদি, ছেলেমেয়ে-সহ। যে ক’দিন ওঁরা বাড়িতে থাকতেন, সে ক’দিন আমাদের বাড়িতে উৎসবের আবহ। দাদার সঙ্গে কত লোক যে সে সময় দেখা করতে আসত! দাদার জন্যই আমাদের বাড়ির সামনের লনে লোকদলের গান ও অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। দলগুলো কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই অনুষ্ঠান করে যেত। আর আমাদের বাড়ির ভেতরের লম্বা বারান্দায় কিংবা উঠোনে চেয়ার পেতে বড়দার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলছে বাবা ও অন্য দাদাদের। লক্ষ করেছি, এক সময়ের রাজনীতি-করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনছেন এবং নিজের মত দিচ্ছেন। রাজনীতি থেকে সাহিত্য, গ্রাম থেকে শহর, মার্ক্সবাদ থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ— কিছুই সে আলোচনায় বাদ যেত না। আমরা ছোটরা একটু দূর থেকে শুনতাম। কলেজে পড়ার সময় আমিও দু’একটি ক্ষেত্রে যে আলোচনায় যোগ দিইনি, তা নয়।
বড়দা চেয়েছিলেন আমি কলকাতার কলেজে পড়ি, কিন্তু নানা কারণে তখন হয়ে ওঠেনি। আমি কলকাতা এসেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে, একাত্তরের গোড়ায়। ওঁর আগ্রহেই আমি ওঁদের বাড়িতে থেকেছি। কলকাতায় এসে দেখি এ এক অন্য বড়দা। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই লিখতে বসেন। মাঝে বাজার ঘুরে আসেন। নিজে বাজার করতে ভালবাসতেন, খুব ব্যস্ত থাকলে আমি যেতাম। বাজার থেকে ফিরে বেলা একটা পর্যন্ত লেখেন। এর মধ্যেই মাঝে-মাঝে পত্রিকা-সম্পাদক, প্রকাশক ও তরুণ গল্পকারেরা দেখা করতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। বেলা একটা নাগাদ স্নান-খাওয়া। দুটোর মধ্যে অফিস বেরিয়ে যান। তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায়। ফেরেন রাত ন’টায়। এক দিন অফিস থেকে রাতে বাড়ি ফিরছেন, সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দাদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, “আমার ভাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ করছে।” সুনীলদা সৌজন্যবশে আগ্রহ দেখালেন, “কী নিয়ে পড়ছ?” আমি বলার আগেই দাদা বলে দিলেন, “ইংরেজি।” এ বার আমি কিছু না বললে ভাল দেখায় না। ওঁর অনেক কবিতাই আমার মুখস্থ। সদ্য সদ্য আমিও কবিতা লিখতে শুরু করেছি, দু’-একটি লিটল ম্যাগাজ়িনে বেরিয়েছে। তবু বললাম, “আমি আপনার সব উপন্যাস পড়েছি।” ১৯৭২ সাল বলেই এ কথা বলতে পেরেছিলাম। উপন্যাসের সংখ্যা তো তখন বেশি ছিল না। সুনীলদা বললেন, “ও সব কিছুই হয়নি, তুমি আমার কবিতা পড়ো।” আমার কবিতা লেখার কথা দাদাও জানতেন বলে মনে হয় না। তবে কফি হাউসে আমাকে আড্ডা দিতে দেখেছেন।
১৯৭৩-এর এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে দাদা আমাকে বললেন, “আগামী কাল ‘দেশ’ এ তোর কবিতা বেরোচ্ছে।” আমি অবাক। মাত্র ক’দিন আগে একটি কবিতা ডাকে পাঠিয়েছি, মনোনয়নের চিঠিও আসেনি। আমি বললাম, “জমিলের নয় তো? ও এখন কবিতা লিখছে।” দাদা বললেন, “না, না, আমি নিজে দেখলাম।” সত্যিই আমার কবিতা ‘দেশ’-এ বেরিয়েছিল। সেই প্রথম আমার কবিতা সম্পর্কে দাদার সঙ্গে কথা। আর এক দিন বলেছিলেন, “রেডিয়োর কবিতা সিংহ তোকে দেখা করতে বলেছেন।” হয়েছিল কী, আমি আকাশবাণী-র ‘যুববাণী’-তে অংশ নিতে চাই জানিয়ে একটি চিঠি দিয়ে এসেছিলাম, সেখানে দাদার কোনও সংযোগ ছিল না। কবিতাদি কী ভাবে দাদার সঙ্গে আমাকে যুক্ত করেছিলেন, তা অনেক দিন ওঁর সঙ্গে চাকরি করেও জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়েনি। ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকায় দাদার ধারাবাহিক উপন্যাস ‘বন্যা’ শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই বাগবাজার স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে
কবি মণীন্দ্র রায়ের কাছে পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিতে হয়েছে আমাকে।
১৯৭১-এর মার্চ থেকে ১৯৭৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত দাদার বাড়িতে থাকার সময় অনেক কবি-লেখককে কাছ থেকে দেখেছি। রবিবার খুব সকালে আসতে দেখেছি প্রফুল্ল রায়কে, অনেক ক্ষণ গল্প করে চলে যেতেন। দেখেছি মুর্শিদাবাদ থেকেই যাঁর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতীনদাকে ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতেও দেখেছি। এক বার সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দাদা ডিনারে ডেকেছেন। দাদা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন। আসার সময় পেরিয়ে গেলেও ওঁরা আসছেন না। এক সময় নীচে গাড়ির শব্দ পেয়ে আমি নীচে পৌঁছে দেখি ওঁরা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ। শক্তিদা এগিয়ে যেতেই সন্তোষকুমার বললেন, “আমি আগে যাব। তোমরা আমার জুনিয়র, আমার পেছনে এসো।” উনি সবার আগে সিঁড়িতে উঠছেন, অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন লেফট-রাইট বলতে বলতে উঠে আসার জন্য। ওঁদের দেরি করে আসার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হতে সময় লাগেনি।
এই তিন বছরের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে দেখিনি, শুনেছি উনি ক্যান্টোফার লেনের বাড়িতে এসেছিলেন। বড়দার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্বের কথা কম শুনিনি। দাদার স্মরণসভায় ওঁকে বলতে শুনেছি সে কথা। উনি তখন থাকতেন কালীঘাটের একটা মেসে। দাদা সেখানে যেতেন। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে রাতে হেঁটে ফিরতে হয়েছে দাদাকে। কখনও শীর্ষেন্দুদা দাদাকে হাজরা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছেন, দাদা আবার কথা বলতে বলতে মেস অবধি চলে গেছেন। নানা বিষয়ে ওঁদের মধ্যে তর্কও হত খুব। শীর্ষেন্দুদার কাছে শুনেছি, আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করার সময়ও ওঁদের মধুর তর্ক অফিস থেকে বেরিয়ে বাসস্টপ পৌঁছনোর সময় পর্যন্ত চলত।
চাকরিসূত্রে আমাকে কলকাতা ছেড়ে অন্য শহরে থাকতে হয়েছে। আবার কলকাতা এলেও সব সময় দাদার কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবু যখন গিয়েছি পারিবারিক কথাই বেশি হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি উপন্যাস আমাকে উৎসর্গ করেছেন। পরে একটি ছোটদের বই দিয়েছেন আমার পুত্রের নামে। ওঁর চলে যাওয়ার দশ দিন আগে আমার স্ত্রী স্বপ্নাকে নিয়ে দেখা করতে গেছি। দেখামাত্র বললেন, “তোদের কথা মনে হচ্ছিল ক’দিন ধরে।... তোর জন্য একটা বই রেখেছি। দিল্লি থেকে আমার গল্পের ইংরেজি অনুবাদের বই। বইয়ের ভূমিকাটি আমার ভাল লেগেছে।” ভেতরের ঘর থেকে ‘ডাই, সেড দ্য ট্রি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ়’ বইটি এনে আমার হাতে দিয়েছেন। অনেক ক্ষণ ছিলাম সে দিন আমরা। কথা বললেন শঙ্খ ঘোষের নতুন গ্রন্থ ইকবালের কবিতার অনুবাদ নিয়ে। গ্রন্থটি র্যাক থেকে নামিয়ে আমাকে দেখতেও দিলেন। আর যা অভাবিত ছিল, সেই প্রসঙ্গ— “তোর কবিতা অনেক কাগজে পড়ছি।” আমি চুপ করে থেকেছি। জানতে চাইলেন আমার পুত্র ঋজুর কথা। চলে আসার সময় আবার মনে করিয়ে দেন, “ঋজুকে পাঠাবি তো এক দিন। অনেক দিন ওকে দেখিনি।”
আকাশবাণীর জন্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী দাদার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। দাদা চলে যাওয়ার পর সেটি সম্প্রচার করার কথা। তার আগে এক বার শুনে নিচ্ছিলাম স্টুডিয়োয় বসে। দেড় ঘণ্টার সাক্ষাৎকার। এডিটিং-এর দরকার ছিল। অত ক্ষণ ধরে নিজের ছেলেবেলা, স্কুলজীবন, আলকাপজীবন, লেখক হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। দাদার সঙ্গে বয়সের ব্যবধানের জন্য এত সব কিছুই জানতাম না। ফরাজি আন্দোলনের অন্যতম মুখ আমার দাদু কী ভাবে আস্তে আস্তে নিজেই এক জন ‘পির’ হয়ে উঠেছিলেন, বাবার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান, অসহযোগ আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়ে জেলে কাটানো, আরও কত অজস্র তথ্য—শুনতে শুনতে কখন যে আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে বুঝতে পারিনি।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy