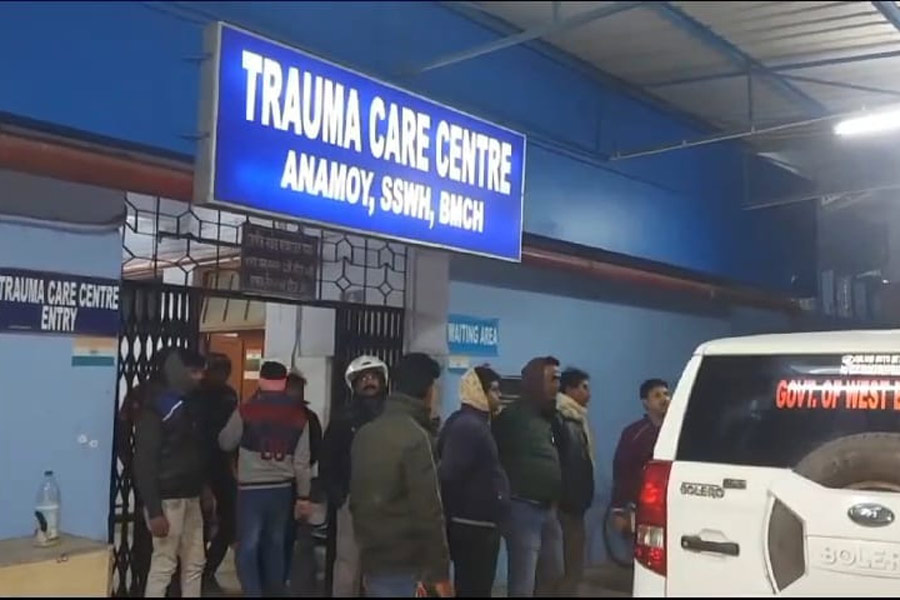মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ
‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’-এর বহু শতক আগেই যেন তিনি দেখিয়েছিলেন ব্ল্যাক গড ম্যাটারস। আজ তাঁর জন্মতিথি। নারায়ণের দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা দোলযাত্রা। আজ ভালবাসায় রঙিন হয়ে সবার রঙে রং মেলানোর দিন।

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবচতুর্দশীর পরদিন মৌনী অমাবস্যা।… রাত্রি প্রভাতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্ণতিথি পূর্ণিমায় মাধবের রঙ খেলা, হোলি-উৎসব, আবীরে রঙে কুমকুমে পৃথিবী রাঙা হয়ে যাবে… বসন্ত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ফুটতে শুরু করেছিল যে রাঙা পলাশস্তবক… তার ঝরার পালা শুরু আজ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিয়ে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে বাতাস খেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই অমাবস্যার রাত্রিতে স্নান করে ঝরা পলাশ কুড়িয়ে আনবে,
রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরি করবে মাধবরঞ্জনের জন্য রাঙা রঙ। দোল-পূর্ণিমা হোলি-উৎসব। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা দোলযাত্রা। দ্বাপরে কানহাইয়ালালের ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠলীলা দোললীলা, ভারতের বসন্তোৎসব হোলি; বাংলার প্রাণচৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর জন্মতিথি।”
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাস মলুটির রাজবাড়িতে বসে লেখা, যেটা ঘটনাচক্রে আমার দাদুর বাড়ি। এই উপন্যাসটাও সেখানেই লেখা কি না আমার জানা নেই, কিন্তু তখনও ট্যুরিস্ট স্পট না হয়ে ওঠা বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ওই গ্রামের অসংখ্য শিবমন্দিরের একটির সিঁড়িতে বসে আমার সদ্যপ্রয়াত ছোটমামা শিল্পরসিক সতীনাথ রায় আমাকে বলেছিলেন যে, তারাশঙ্করের ‘রাধা’ উপন্যাসে মলুটির কথাও আসতে পারত, কারণ নীলাচলে যাবার পথে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মলুটিতে পা রেখেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।
হয়তো রেখেছিলেন, নবদ্বীপ থেকে পুরী যাবার পথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ক্ষণকাল, হয়তো বা রাখেননি। আমার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি কৌতূহলকর ঘটনা হল, মলুটি গ্রামে ষড়ভুজ কৃষ্ণমূর্তির উপস্থিতি। সম্প্রতি গবেষক তুহিন মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে পড়লাম, ষড়ভুজ কৃষ্ণমূর্তি মলুটি ছাড়া আর কোথাও নেই। অবশ্য তুহিনবাবু মনে করেছেন যে, মূর্তিটি শ্রীচৈতন্যেরও হতে পারে, যেহেতু ষড়ভুজ চৈতন্যের মূর্তি (যেখানে চৈতন্যের দু’টি হাত রামের, দু’টি কৃষ্ণের এবং দু’টি চৈতন্যের নিজের) কাটোয়া-বাঁশবেড়িয়াতেও দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন মলুটিতে বাস করা প্রবাদপুরুষ ডেভিড ম্যাককাচ্চনও এই রকম ভেবেছিলেন বলে শুনেছি। তবে, তুহিনবাবু দামি একটি কথা বলেছেন, মলুটির কৃষ্ণমূর্তি চৈতন্যের হলেও তা দুর্লভ, কারণ গৌরাঙ্গের শিঙাধারী ষড়ভুজ মূর্তি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি।
গেলেই বা কী হত? ‘যা আর কারও কাছে নেই তা আমার কাছে আছে’ এই উপলব্ধি একটি ‘বাতাসা’কে নিয়েও যদি হয়, তবুও তা ‘আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা’রই ভিন্ন রূপ। তার চেয়ে, ‘নাস্তিগহ্বরের মধ্যে থেকে উঠে আসা সর্বহারা’ অধিক চৈতন্যস্বরূপ নয়?
আমার বাবার ছোটমামার ঢাকা শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে অল্পস্বল্প নামডাক ছিল। এক বার কোনও একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকায় আসা রবীন্দ্রনাথের পায়ে নিজের হারমোনিয়াম ছুঁইয়ে এনেছিলেন, এই ছিল ওঁর সর্বোচ্চ গর্ব। কিন্তু কেবল মাত্র সেই হারমোনিয়ামটা কাঁখে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসার সময় সীমান্ত-ভক্ষকদের নজরে পড়ে যান উনি। ভিতরে করে সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছে, এই সন্দেহে হারমোনিয়ামটাকে ফালাফালা করে দেয় তারা। সেই ঘটনার পরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মানুষটার, মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করতেন, “রবীন্দ্রনাথের পায়ে ছোয়াইয়া আনলাম তাও…”
ওই হারমোনিয়ামের শোকে উনি এক রকম জেদ ধরেই দণ্ডকারণ্যে চলে যান, পরে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গান গেয়ে ভিক্ষে করতেন বলে শুনেছি। জীবনের শেষ সময়টা আমাদের কাছে এসে ছিলেন আর তখনই ওই পাগলের ভিতরকার প্রদীপটাকে জ্বলতে দেখেছিলাম। কী অসহ্য লাগত, যখন উনি আমাদের বুড়ির ঘর পোড়ানোর ভিতর এসে শামিল হতেন; ‘আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল’ থামিয়ে দিয়ে বলে উঠতেন, “সর্বশূন্যতার ধারে/ জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে/ দাও নাড়া;/ ভিতরে কে দিবে সাড়া/ মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিঃশ্বাস।/ ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।/ তার কাছে নত হয় শির/ চরম বেদনাশৈলে ঊর্ধ্বচূড় যাহার মন্দির…”
কার কবিতা, কেন বলছে, কিছুই জানতাম না সেই ছ’-সাত বছর বয়সে, কিন্তু নদীর স্রোতের প্রায় চলে যেতে যেতে ‘যখন সময় থমকে দাঁড়ায়’, সে রকমই কোনও এক পলে, আবু সয়ীদ আয়ুবের ‘পান্থজনের সখা’-য় পঙ্ক্তিগুলো খুঁজে পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তিরিশ বছর পরের এক মধ্যরাত্রে। চলে গিয়েছিলাম ‘বীথিকা’র ‘দুর্ভাগিনী’ কবিতার কাছে, বার বার পড়েছিলাম তার শেষ দুটি পঙ্ক্তি, “অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন/ কেন ওগো কেন?”
না, কোনও উত্তর পাই না, কিন্তু একটা উপলব্ধি হয় যেখানে ওই দুর্ভাগা কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায় ‘দুর্ভাগিনী’র গলায় খুঁজে পেতে পারেন নিজ কণ্ঠস্বর, ঠিক যে রকম ‘রাধা’কে নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে কৃষ্ণের লাগি বেদনা-বিহ্বল হতেন গোরাচাঁদ। আমার ভিতরে তোমার বেদনা ধারণ করতে পারলে তবেই তো তোমাকে ঈশ্বর মনে হবে আমার, তবেই তো ‘অ্যাই শোন’ না বলে, ‘বোল’ বলতে পারব আমি! ‘হল্লাবোল’-এর জনপ্রিয়তার কারণ সে ‘হরিবোল’ এর উত্তরসূরি, ‘হরিবোল’-এর গর্ভেই তার জন্ম। মানুষকে ‘হরি’ ভাবো না, হরিকে বলতে দাও না বলেই তো ‘হল্লা’ বলে। ভারতবর্ষকে এই ‘বোল’ শব্দে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন মহাপ্রভু আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে জেনেছিল যে তাদের বোবা-কালার মতো শুনতে বলছে না কেউ, অন্তরের আকুতিকে আত্মার উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে বলছে। সেই প্রথম, ‘মেটামরফোসিস’, উপমহাদেশে।
“ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্/ যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে”।
শব্দের জ্যোতি যদি সংসার জুড়ে না জ্বলত, তা হলে পৃথিবী ডুবে যেত অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে আমাদের পরিত্রাণ করার জন্যই রঙের মধ্যে রস মিশিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ। আর সেই রস রং হয়ে ফুটে উঠেছিল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ‘কিষানগড়ের রাধা’ নামটার সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। শিল্পী নীরদ মজুমদারের একটি প্রবন্ধও আছে এই বিষয়ে। কিন্তু কী ভাবে কিষানগড়ের রাধার মুখ বাঙালি তনয়ার মতো হল? নবদ্বীপের পণ্ডিতের প্রভাব কত দূর ছড়িয়েছিল যে, রাজপুতানার শিল্পীর তুলিতে গঙ্গামৃত্তিকার স্পর্শ লাগল? মীরাবাইয়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হয়নি, কিন্তু চৈতন্যের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত না হলে মীরা কি তাঁকে নিয়ে লিখতে পারতেন?
অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরে মীরার লিরিকগুলি বাংলায় অনুবাদ করছেন। তাঁর কাছেই পেলাম এই কবিতাটির সন্ধান, যেখানে মীরা বলছেন, “অব তো হরি নাম লৌ লাগী/ সব জগকে উও মাখনচোরা নাম ধরোয়ে বৈরাগী”। এই গানেরই শেষে মীরা বলছেন, “পীতাম্বর কী ভাব দিখাওই কটি কৌপীন কসৈ/ গৌর কৃষ্ণদাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ”। অচিন্ত্যবাবুর অনুবাদে শেষ পঙ্ক্তিটি হয়েছে, “গৌর-কৃষ্ণের দাসী মীরার রসনা গায় গোরাগুণ তন্ময়”। এই সূত্রেই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ‘সাধক ও সাধনা’ বইটির ‘দোল-দুলাল শ্রীচৈতন্য’ লেখাটির কথা এসে পড়ে। ১৩৪৪ সালের ‘আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা’য় প্রকাশিত লেখাটির শুরুতেই পাচ্ছি, “বাংলার বাইরেও বহুস্থানে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব আছেন।… গুজরাতে ‘নওসারি’ বিভাগে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব আছেন। একবার দোলপূর্ণিমায় তাঁহাদের কীর্তনে শুনিতেছিলাম ‘জয় জয় শ্রীচৈতন্য দোল-দুলাল’। দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁহারা দোল বলেন না, বলেন হোলি। তবু বাংলার অনুকরণে এই ‘দোল-দুলাল’ কথাটা বড়ো সুন্দর লাগিয়াছিল।”
ক্ষিতিমোহন সেনের এই লেখাটি শেষ হচ্ছে, মীরার একটি ভজন দিয়ে, “ফাগুনকে দিন যায় রে/ হোলি খেল অপার রে...”। শব্দগুলোয় ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, মীরা যেন ভার্চুয়াল হোলিই খেলছেন। কত লেখায় পড়েছি যে সে কালে, হয়তো এ কালেও, বড়লোকরা আবির আর আতর এক সঙ্গে না করে হোলি খেলতে পারতেন না। কিন্তু সাধারণের বেলা, আকুলতাই একমাত্র সুগন্ধ। মীরা এখানে যেন সেই ‘আতর’-এর কথাই বলছেন, “অন্তরকে পট খোল দিয়ো হৈ/ কঁহা পার কঁহা বার রে/ মীরাকে প্রভু পরম মনোহর/ চরণ কমল বলিহার রে”।
জীবন যখন শুকায়ে যায়, তখন এই আকুলতার সন্ধানেই উর মাটি চুর করি আমরা। করুণাধারা তো কোনও বড়বাবুর দিঘি নয়, করুণাধারা সেই স্রোত যা আমাকে কাঁদায় বলেই তোমাকে ভেজায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সেই ট্রেন যেমন বাঁশি দিয়ে ভারতবর্ষের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল, নিমাই যেন বাঁশির টানে হারিয়ে গিয়েছিলেন এই ভারতে। আসলে হারাননি, ভারতকেই টেনে এনেছিলেন নিজের বাঙালিয়ানায়। ওড়িশার প্রতাপরুদ্র থেকে দাক্ষিণাত্যের রামানন্দ রায়, কিংবা উত্তর ভারতের পাঠানরা, যাঁরা গাত্রবর্ণ এবং উচ্চতা দেখে তাঁকে নিজেদের এক জন ভেবেছিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁর বাঙালি পরিচয় বাদ দিয়ে কারও সঙ্গে মেশেননি। শ্রীচৈতন্য রসাস্বাদনের প্রামাণ্য গ্রন্থ, কৃষ্ণদাস বিরচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ বাংলায় লিখিত। ওই বইয়ের কথায় একটু পরে আসছি, আগে অন্য একটি অনালোচিত দিকে আলো ফেলার প্রয়োজন।
শ্রীচৈতন্যর মুখের কথা, “নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন”। এই শিরোনামেই ইতিহাসবিদ তারাপদ মুখোপাধ্যায় যে বইটি লিখেছেন তাতে স্পষ্টই লেখা, “ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বৃন্দাবন নির্জন বনস্থলী, দ্বিতীয়ার্ধে মন্দির পরিকীর্ণ তীর্থস্থলী।… বৃন্দাবনের এই রূপান্তর চৈতন্যের প্রবর্তনায় এবং প্রধানত রূপ-সনাতন’সহ অন্য গৌরগণের উদ্যোগে। তাঁদের রচিত শাস্ত্রে, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে, আবিষ্কৃত তীর্থে… পৌরাণিক বৃন্দারণ্য মধ্যযুগে নতুন গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।”
এখান থেকে বলাই যায় যে, বৃন্দাবনে ‘কানু সঙ্গ খেলে হোরী’ অনেক অর্থেই বৃহত্তর ভারতে বাঙালির বিজয়পতাকা। চৈতন্য এবং তাঁর লীলাপার্ষদরা ‘বর্জিত’ ভাবতেন না উত্তর-পশ্চিম ভারতকে, উল্টো দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও ‘বহিরাগত’ তকমা পেতে হয়নি মথুরা-বৃন্দাবনে। বরং মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে উঠেছিল, বাঙালি নবজাগরণের আউটপোস্ট।
এই ‘হয়ে ওঠা’ হয়ে উঠত না রাজশক্তির আনুকূল্য না পেলে। রাজা বিহারীমল, রাজা টোডরমল এবং অবশ্যই বীরবল বৈষ্ণবধর্ম এবং গৌরগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেই শ্রদ্ধাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে সম্রাট আকবরের কাছে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর ভাবধারা পৌঁছে দিতে। ফলস্বরূপ বাংলার মানুষের তৈরি ‘মদনমোহন মন্দির’-এ অম্বররাজ বিহারীমলের সুপারিশে সম্রাট আকবরের ফরমানে দু’শো বিঘে জমি দান। বৃন্দাবনের মন্দিরের ভূসম্পত্তি সেই প্রথম।
ইতিহাস এখানে থেমে যায়। ইতিহাস একে ‘হিন্দু’ দেবতার ভরণপোষণের জন্য ‘মুসলমান’ সম্রাটের দান হিসেবেই চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু কবিতা ইতিহাস থেকে উঠে এলেও ইতিহাসের বেড়াকে মানে না। তাই আমরা সম্রাট আকবরের আমলে জনপ্রিয়, এমন কবিতা পেয়ে যাই …
“কানহা’তে অব ঘর ঝগড়ো পাসারো/ কৈসে হুয়ে নিরাওয়ারো।
ওয়হ সব ঘেরো করত হ্যায় তেরো রস/ অনরস কৌন মন্ত্র পড় ডারো॥
মুরলী বজায় কীনী সব বোরী/ লাজ দৈ তজ অপনে অপনে মে বিসারো।
তানসেন কে প্রভু কহত তুমহি সো তুম জীতো হম হারোঁ॥”
এই কবিতা অনুবাদের স্পর্ধা আমার নেই, শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলি, ট্রেনে আলাপ হওয়া যে মুসাফিরের থেকে এই কবিতার কথা প্রথম শুনেছিলাম আমি, তিনি বিশেষ ভাবে খেয়াল করতে বলেছিলেন কবিতাটির শেষ পঙ্ক্তি, যেখানে কৃষ্ণকে তানসেনের প্রভু বলে উল্লেখ করে কবি তাঁর কাছে নিজের পরাজয় যাচ্ঞা করছেন। এখানে শিল্পীর ধর্ম যা খুশি হতে পারে, কিন্তু তার প্রভু কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, কারণ ওই এক জনের হাতেই যে বাঁশি আছে!
আমার কৈশোরে, কুড়ি-পঁচিশ জনের একটি সঙ্কীর্তনের দলের সঙ্গে, দোলপূর্ণিমার সকালে আমিও পথে বেরোতাম। কখনও খোল গলায় নিয়ে, কখনও বা করতাল হাতে। “প্রভাত সমীরে শচীর আঙিনা মাঝে গোরাচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে” গানে মুখরিত হয়ে উঠত চার পাশ, বিশ্বপ্রকৃতির তাপ কমে যেত গোরাজননীর উল্লেখে। এই কবিতার অনুরণন আমায় কানে কানে বলে যে, সেই আঙিনা বন্যায় ভেসে গেছে, প্রলয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পার্টিশনে ভাগ হয়ে গেছে, কিংবা প্রোমোটারের গ্রাসে চলে গেছে এ কেবল অর্ধসত্য; চিরসত্য এই যে সেই আঙিনা নিয়ত জন্ম নিচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে সম্রাটের দরবারে, জন্ম নিচ্ছে কেরানির ছেঁড়া ছাতায়, জন্ম নিচ্ছে ধলেশ্বরী নদীতীরে।
মোগল দরবারে হোলি খেলার রমরমা সম্ভবপর হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ভাবামৃতের উচ্ছ্বাসে। সনাতন-রূপ-জীব প্রমুখ গোস্বামীর অলৌকিক সাধনা শুধু বৃন্দাবন, মথুরা তথা উত্তর ভারতের জনমানসকেই নয়, রাজশক্তিকেও প্রভাবিত করেছিল। এই ধারা আকবরেই শেষ হয়ে যায়নি। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে পাচ্ছি, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে কেশবদেব মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মিত হয়। মথুরার এই মন্দির দেখে ট্যাভারনিয়ের, বার্নিয়ার প্রমুখ পর্যটক মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তুমুল হোলিখেলা হত বলে জনশ্রুতি। কিন্তু ধ্বংসের অভিঘাত কি রং আর রসের উৎসব মুছে দিতে পেরেছিল?
কখনওই নয়। বরং ঔরঙ্গজেবের উত্তরপুরুষদের দ্বারাই ওই কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই মহম্মদ শাহর কলমে আমরা পাই, “হোরী কি ঋতু আই সখী রী চলো পিয়া পে খেলিয়ে হোরী/ আবির গুলাল উড়াবত আওত শিরপর গাগর রস কি ভরী রী/ মহম্মদ শা সব মিল মিল খেলে মুখ
পর আবির মলো রী”-র মতো জীবন্ত অনুরাগের গান।
‘সব মিল মিল কে’— দোলযাত্রাকে সামনে রেখে এই বার্তাই মহাপ্রভু চারিয়ে দিয়েছিলেন আসমুদ্রহিমাচল। তাঁর মুখনিঃসৃত, “ নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা”— আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোনওটাই নই, নই ব্রহ্মচারী বা গৃহী বা বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী। আসলে বলতে চেয়েছিলেন, ‘আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে’। কিন্তু তিনি যে গৌরাঙ্গ! কী ভাবে মেশাবেন তিনি সবার রঙে রঙ?
আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের এক শহরে খোল-করতাল সমেত হরেকৃষ্ণ-হরেরাম করতে থাকা এক দঙ্গল সাহেব দেখে হেঁচকি উঠেছিল আমার। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলব বলে। উত্তর কলকাতার বাঙালি অভয়চরণ দে সত্তরের কাছাকাছি বয়সে আমেরিকায় পৌঁছে কী ভাবে এমন লাখো-লাখো শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণপ্রাণ তৈরি করলেন, কিনারা পাইনি ভেবে। ‘ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস’ বা ইসকন নিয়ে ভাল-মন্দ যা খুশি ধারণা থাকতে পারে কিন্তু তার বিপুল সর্বদেশীয় ভক্তমণ্ডলী বিস্ময়ের উদ্রেক করবেই। আমার আগে ধারণা ছিল যে, মূলত শ্বেতাঙ্গরাই এই সবের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু আমেরিকায় কিছু দিন কাছ থেকে এদের একটি শাখার কাজ দেখে অন্য একটি সত্যের আবিষ্কারে চমৎকৃত হয়েছিলাম। শয়ে-শয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ইদানীং কৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরছেন কারণ একটি বিকল্প চেতনা। সেই চেতনার দারুণ প্রকাশ দেখেছিলাম শিকাগোর কয়েকটি ছেলেমেয়ের টি-শার্টে। ‘এভরিওয়ান ক্যান সি/ মাই গড ইজ ব্ল্যাক লাইক মি’-র মতো লাইন লেখা ছিল টি-শার্টগুলোর বেশ কয়েকটায়। আর একটায় মার্টিন লুথার কিং, ম্যালকম এক্স এবং নন্দ ঘোষের বেটার ছবি এক সঙ্গে দিয়ে লেখা, ‘মাই রিভোল্ট, মাই ড্রিমস, মাই গড’!
কৃষ্ণাঙ্গ জননেতা জেসি জ্যাকসন সেই যে বলেছিলেন, “...ফ্রম স্লেভশিপ টু কম্প্যানিয়নশিপ, ফ্রম আউটহাউস টু হোয়াইট হাউস আওয়ার জার্নি হ্যাজ় জাস্ট বিগ্যান,” অসম্মান থেকে সম্মানের দিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ চণ্ডালদের যাত্রা কিন্তু মহাপ্রভুই শুরু করে গিয়েছিলেন। টোনি কে স্টুয়ার্ট, তাঁর ‘দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড’ বইয়ে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় কোনও নেতৃত্ব কিংবা সাংগঠনিক কর্তৃত্ব ছাড়া বৈষ্ণবসমাজ টিকে রয়েছে এবং ছড়াচ্ছে কারণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ই ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর মতের সূত্র ধরে ওই মহাগ্রন্থের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পাই, “তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল/ গাঢ় তৃষ্ণে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল”। গৌরাঙ্গ নিজেকে সমর্পণ করছেন জগন্নাথের চরণে, ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ এর পথিকৃৎ নয় কি
এই ‘ব্ল্যাক গডস ম্যাটার’? মহাপ্রভু যে ব্রজের নিবাসী না হয়ে নীলাচলেই
রয়ে গেলেন, তার একটি কারণ হয়তো নীলাচলে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই প্রান্ত থেকেই ভক্ত সমাগম হবার ফলে, গৌরাঙ্গ ভারতের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতের মহাসঙ্গম সংঘটিত হত প্রতিনিয়ত।
শিব যেমন তাঁর জটায় গঙ্গার আগমনে ত্রস্ত সতীকে অঙ্গে ধারণ করে হয়ে উঠেছিলেন অর্ধনারীশ্বর, আলো আর কালোকে আপন সত্তায় ধারণ করে মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ স্বয়ং। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, সনাতন গোস্বামীর ‘কৃষ্ণ একাই উপাস্য’ তত্ত্ব স্বীকার না করে রূপ গোস্বামী যুগল রাধাকৃষ্ণকেই উপাস্য মনে করেছিলেন। আর কৃষ্ণদাসের কলমে রাধা-কৃষ্ণ যেন যুগনদ্ধ একমূর্তি দেবতা।
এই যুগল সত্তার উদ্যাপনই কি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, ‘অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম, হয় যায় রয়’? মা সারদা তাই কি বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেতেন ‘দক্ষিণেশ্বরে রেতে…’?
বৃন্দাবনে ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আশ্রমে লেখা আছে, ‘আমি যাঁহার পূজা করি সে যদি কথাই না বলবেন তবে আমি তাঁহার পূজা করিব কেন?’ পড়ে মনে হয় রাধা-কৃষ্ণের যুগল-উৎসব আসলে ক্ষমতার সঙ্গে সমতার কথোপকথন, পরমাত্মা আর পরমাণুর যুগলবন্দি। আমার বাবার ছোটমামা ‘রোদন-ভরা এ বসন্ত’ গানটা গাইতেন কি দোলের সন্ধ্যায়? মনে পড়ে না। কিন্তু আমি জানি, দোলের দিন প্রতিটি প্রাণ অন্য প্রাণের দিকে ছুটে যেতে চায়, মিশে যেতে চায় না, এক হয়েও স্বতন্ত্র থাকতে চায়; ‘আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে’ কেবল নয়, আবরণ ছিঁড়ে গেলে চায় কেউ বরণ করে নিক সাদরে।
কাটোয়ার গঙ্গায় ডুব দিয়ে মস্তকমুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন নিমাই। ওই কাটোয়াতেই এক মানুষীকে ঘরে তৈরি ছানার সন্দেশ বিক্রি করতে দেখেছি। অদ্ভুত সব নাম ছিল সন্দেশগুলোর। ‘অদ্বৈত’, ‘নিতাই’, ‘হরিদাস’ ‘নদেরচাঁদ’... এই রকম সব নাম দিয়ে সন্দেশগুলি তিনি বিক্রি করতেন। হয়তো মেলায় আগত বৈষ্ণবদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যেই অমন নামকরণ। আমি এক বার ‘পঞ্চাশ টাকায় দশটা সন্দেশ’ শুনে বলেছিলাম, “পঞ্চাশ টাকায় বারোটা সন্দেশ হবে, ঠাকুমা?”
উত্তরে আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, “সব ক’টা সন্দেশ নিয়ে যা। ঠাকুমা বলিস না।”
সেই হ্লাদিনী শক্তি এখনও পৃথিবীতে,
না পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন, জানি না। যদি পৃথিবীতেই থাকেন, তা হলে আমি এ বারের দোলে ওঁর পায়ে নয়, গালে আবির দিতে চাই।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy