
ইতিহাসের পালাবদলই তাঁর লেখার উপাদান
তাঁর ‘শতাব্দী’ উপন্যাসে ধরা আছে সামন্ততন্ত্রের অবসান। ‘গৌরীগ্রাম’ আর ‘মালঙ্গীর কথা’ জানিয়েছে তেভাগা আন্দোলনের কথা। ‘পুব থেকে পশ্চিম’ উপন্যাসের বিষয়, পূর্ব বাংলা থেকে ভেসে আসা ছিন্নমূল মানুষদের লড়াই। তরুণ সাহিত্যিকদের জায়গা করে দেওয়াতেই আগ্রহ ছিল বেশি। নিজের সাহিত্যকর্ম নিয়ে বরাবরই প্রচারবিমুখ ছিলেন রমেশচন্দ্র সেন।
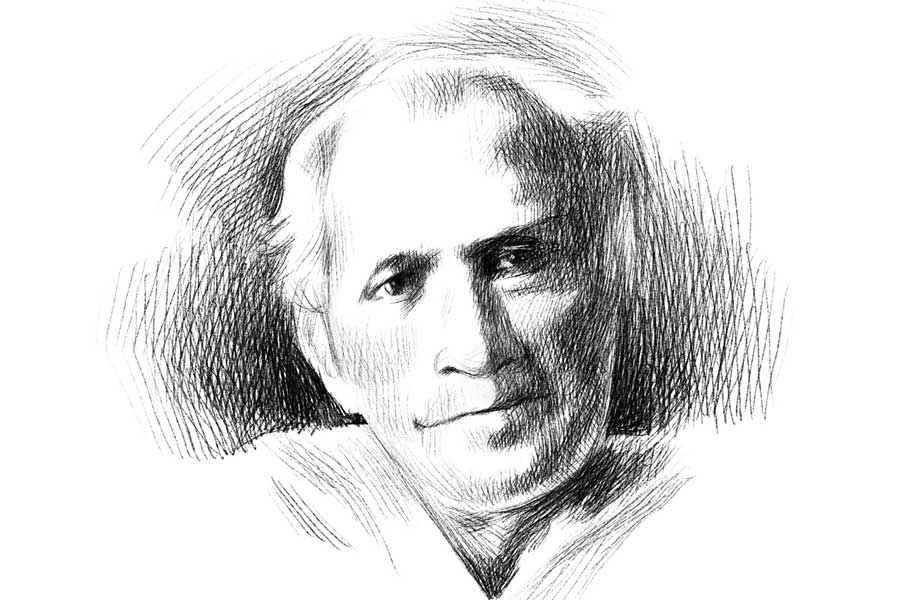
কথাসাহিত্যিক: রমেশচন্দ্র সেন। গভীর সমাজচেতনাও তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ছবি: রৌদ্র মিত্র
রাহুল দাশগুপ্ত
এই আত্মপ্রচারের যুগেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রচার-বিমুখ। সাহিত্যক্ষেত্রের নবাগত অনেক লেখককে তাঁর সমিতির সহায়তায় প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করলেও তিনি নিজে কখনও সামনে এগিয়ে এসে নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না। খ্যাতির মোহ কোনোদিন তাঁর দেখিনি। সাহিত্যিক-সুলভ কোনও অহংকারও তাঁর ছিল না।” এ ভাবেই রমেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন শিবরাম চক্রবর্তী, তাঁর ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা’ গ্রন্থে। রমেশচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২ অগস্ট। সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অনুবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, রমেশচন্দ্র তাঁর ‘এপিক দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করে’। গভীর আগ্রহে তিনি রুশ সাহিত্যও পাঠ করেছিলেন।
পিতার মৃত্যুর পর লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। পৈতৃক কবিরাজি পেশা অবলম্বন করে তিনি পরিবারের হাল ধরেন। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দেন। কবিরাজ হিসাবে রমেশচন্দ্র বহু জায়গায় ঘুরেছেন। ডাক্তারির প্রয়োজনে বিচিত্রধর্মী মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর মেলামেশা। এক যৌনকর্মীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন ‘কাজল’ উপন্যাসটি।
১৯১১ সালে তিনি ‘সাহিত্যপ্রচার সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ সালে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, ‘সাহিত্য সেবক সমিতি’। এই সংগঠন টানা ৫০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তখনকার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক এই সমিতিতে এসেছেন এবং যুক্ত থেকেছেন। প্রথম দিকে এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যেত। শিশুর মতো সরল এই বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে মিশতেন, উপদেশ দিতেন। সমাজে অত প্রতিষ্ঠা তাঁর, অত পাণ্ডিত্য, কিন্তু আমাদের সমিতিতে যখন তিনি আসতেন, মনে হত শাস্ত্রীমশাইআমাদেরই একজন।”
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের ভাষায়, “তখন ‘বিচিত্রা’য় ‘পথের পাঁচালী’ বেরুচ্ছিল। ‘বিচিত্রা’ সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন বিভূতিভূষণকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য এতদিন যেন ছিল ধনী ও মধ্যবিত্তের জীবনালেখ্য। ধনীর ড্রইংরুমে বসত তার আসর। এই সময় বিভূতিবাবু আনলেন রিলিফ, পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন বাংলা পল্লীর শ্যামস্নিগ্ধ রূপ। অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতিবাবু আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। রোজই আসতেন, গল্প করতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁর আলোচনার বিষয় থাকত প্রকৃতি। প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, সামান্য চেষ্টা করলেই আমরা পরলোকগত আত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।”
রমেশচন্দ্র আরও লিখেছেন, “এর কিছুদিন পরে আমাদের আড্ডায় এলেন প্রতিভাধর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর সৌম্য-মূর্তি, দৃঢ় বলিষ্ঠ-গড়ন। তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখ সবাইকে আকৃষ্ট করত। অল্প কয়েকটি গল্প লিখে এর মধ্যেই তিনি প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। সমালোচকরা এই তরুণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। প্রথম থেকেই তাঁর সাহিত্যে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর ছিল, ছিল একটা অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য, নর ও নারীর গভীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কারবার। ক্রমে ক্রমে তিনি সমিতির অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে ওঠেন। বহু বন্ধু থাকলেও মানুষটি ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। তাঁর মত সাহিত্যস্রষ্টাদের চরিত্রের ধরণই বোধহয় এইরূপ।”
শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “দু-বছর সমিতির কর্ণধার ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র। তিনি সভায় দীর্ঘ প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন আসর জমানোর মানুষ। বৈঠকী গল্প বলতেন। নিজের কথা তিনি কখনও বলতেন না। নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কেও একটি কথাও বলেননি। এ বিষয়ে তাঁর মতো শালীনতা-সম্পন্ন লোক সাহিত্য-জগতে খুব অল্পই দেখেছি।” তিনি আরও জানিয়েছেন, “এই সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। বয়সে তরুণ, সাহিত্যে একেবারেই নবাগত। সমিতিতে তারাশঙ্করের প্রথম পঠিত গল্প শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর সেই দিনের সভার কথা একাধিক রচনায়উল্লেখ করেছেন।”
সমিতির কাজেই ছিল রমেশচন্দ্রের যাবতীয় উদ্যোগ। নতুন সাহিত্যিকদের কাছে এই সমিতি ছিল দাঁড়াবার জায়গা। জীবনের বেশির ভাগ সময় রমেশচন্দ্র ব্যয় করেছেন অনুজ লেখকদের লেখা সংস্কারে, রচনা প্রকাশের উদ্যোগে। চিত্তরঞ্জন দেবের ভাষায়, “কীভাবে তরুণ সাহিত্যিকরা দাঁড়াতে পারবে এই যেন ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাদের লেখা নিজে পকেটে করে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছেন কোনও না কোনও কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে।”
শুধু তরুণ লেখকেরাই নয়, সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্কটেও তিনি ছুটে যেতেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের চর্মরোগ হয়েছে, ওষুধ নিয়ে রমেশচন্দ্র ছুটেছেন তাঁর পাইকপাড়ার বাড়িতে। অর্থকষ্টে কাতর তরুণ কবিকে আর্থিক সহায়তা দিতে লাঠি হাতে অশক্ত শরীরে পথে বেরিয়েছেন, যাতে তার জন্য একটা টিউশনি যোগাড় করতে পারেন! মাথায় সাদা চুল, সৌম্য, শান্ত, দীর্ঘাকৃতি, ঋজু দেহের মানুষটি স্নেহ, উদারতা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগী মানুষটি বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন বলে তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েক বার পুলিশ হানা দেয়।
১৯৪২ সালে রমেশচন্দ্র হৃদরোগজনিত কারণে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দোতলা থেকে নেমে এক তলায় কবিরাজখানায় এসে বসাও তাঁর বারণ হয়ে যায়। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে লিখে রমেশচন্দ্র এই সময় তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘শতাব্দী’। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র রাজেশ্বর মণ্ডল জমিকেন্দ্রিক আধিপত্যে সন্তুষ্ট না থেকে ব্যবসায় নামে, এবং শেষ পর্যন্ত কারখানা পত্তন করে স্বাধীন শিল্পপতি হয়ে ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এই কাহিনিটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বিশাল ক্যানভাসে অজস্র চরিত্রের আসা-যাওয়ায়, প্রকৃতি ও মানুষের বর্ণাঢ্য উপস্থাপনায়।
রাজেশ্বরের চার ছেলের মধ্যে বড় ছেলে লিবারাল মধ্যবিত্ত, মেজো ছেলে মুনাফাসর্বস্ব পুঁজিপতি, সেজো ছেলে বলশেভিক মতবাদে বিশ্বাসী পুঁজিহারা এবং ছোট ছেলে নৈরাশ্যপীড়িত বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষের প্রতীক হয়ে ওঠে। এ ভাবেই ভারতীয় বাস্তবতার নানা স্তরকে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতের এক বিশদ, অন্তর্ভেদী ও সত্যনিষ্ঠ ছবি পাওয়া যায় এই এপিক উপন্যাসে। ‘প্রবাসী’-তে এই বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে রাজেশ্বর প্রসঙ্গে নলিনীকুমার ভদ্র লিখেছিলেন, “মাটির প্রতি তাঁহার গভীর টান আর তাহার অপরাজেয় পৌরুষ ন্যুট হামসুনের নোবেলজয়ী ‘গ্রোথ অফ দ্য সয়েল’ উপন্যাসের নায়ক চাষী আইজাকের কথা মনে করাইয়া দেয়।”
পরের বছর, ১৯৪৬ সালে রমেশচন্দ্র লেখেন তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস, ‘কুরপালা’। ব্যক্তির বদলে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে আস্ত একটি গ্রাম, ‘কুরপালা’। চাষি-জোলার গ্রাম কুরপালাকে বদলে দিতে থাকে পুঁজি ও মুনাফার থাবা। ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে সামন্তবাদ ও জমিদারতন্ত্র, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জিতে যেতে থাকে উদীয়মান ধনতন্ত্র। চাষির সহজ সরল যৌথজীবন, সুন্দর সামাজিক বন্ধন ভেঙে পড়ে। তারা হয়ে যায় সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষ, কারখানার দিনমজুর হওয়ার জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী। নিম্নবর্গের মধ্যে জাতীয় রাজনীতি কত অপ্রাসঙ্গিক, কারখানার মালিক ও শিল্প-পুঁজিপতিরাই যে ভবিষ্যৎ নেতা, তাও দেখিয়েছেন লেখক।
১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় পতিতাপল্লির জীবন নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস, ‘কাজল’। গণিকা-জীবনের এই ‘প্রথম মৌলিক মানচিত্র’র সঙ্গে বার বার তুলনা টানা হয়েছে এমিল জ়োলার ‘নানা’ বা আলেকসান্দার কুপরিনের ‘ইয়ামা’র। গ্রাম্য পুরোহিতের বিধবা কন্যা কাজল চতুর প্রেমিক পাঁচুর হাত ধরে ওঠে সোনাবাগান পল্লিতে। কাজলের নরকযাত্রা শুরু হয়। প্রেমিক তাকে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়, রাষ্ট্র ও আইন কেড়ে নেয় সন্তানকে, সে চিনতে থাকে তথাকথিত সভ্য, শিক্ষিত, ভদ্র, পরিশীলিত সমাজের আসল মুখ। শেষ পর্যন্ত পথের কুকুরের মতো নিরাশ্রয় হয়ে যায় তার জীবন। কুপরিনের ওদেসা বন্দরের গণিকাপল্লির মতো এই বইটিও গণিকাজীবনের যাবতীয় বঞ্চনা, নিগ্রহ, অসহায়তাকে তুলে ধরেছে।
‘গৌরীগ্রাম’ (১৯৫৩) এবং ‘মালঙ্গীর কথা’ (১৯৫৪) রমেশচন্দ্রের আরও দু’টি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এই দু’টি উপন্যাসেই বিষয় হিসেবে এসেছে ‘তেভাগার লড়াই’। ‘গৌরীগ্রাম’ উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লড়াইয়ের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ব বাংলায় যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম নৌকোগুলিকে বাজেয়াপ্ত করলে নৌজীবী প্রচুর মানুষ কর্মচ্যুত হয়। জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকোটি সরকার বাজেয়াপ্ত করলে গোকুল জীবিকার খোঁজে শহরে আসতে বাধ্য হয়। ১৯৪৩ সালের কলকাতার পথে পথে অজস্র কঙ্কালের ভিড়ে চোর প্রতিপন্ন হয়ে জনতার প্রহারে সে অসুস্থ উন্মাদ ভিক্ষুকে পরিণত হয়। এই সার্বিক বিপর্যয়ের মধ্যেও গোকুলের ছেলে মানিক মজুতদার-কালোবাজারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে, গৌরী মাঠে বসে থাকে তেভাগার প্রত্যাশায়। ব্রিটিশ শাসকের হাতে সুপরিকল্পিত ভাবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতীয় গ্রামজীবনের সর্বাত্মক ধ্বংস নিয়ে লেখা উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে বাংলার এক ক্রান্তিলগ্ন সময়ের মানবিক দলিল।
‘পুব থেকে পশ্চিম’ (১৯৫৬) উপন্যাসের বিষয়, ১৯৫০-এর আগে ও ঠিক তার পরে পূর্ব বাংলা থেকে ছিন্নমূল মানুষদের ভেসে আসা এবং টিকে থাকার লড়াই। পূর্ব বাংলার শ্রীপুর গ্রামের মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দেয়, নানা দুঃখকষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে কলোনি তৈরি করে বসবাস শুরু করে। এই যাত্রাপথের বর্ণনাই মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। জাহাজঘাটায় এসে ছিন্নমূল মানুষেরা দেখে খাদ্যসামগ্রী অগ্নিমূল্য, চোর-ডাকাতের ভিড়। তারা মুরগি-ভর্তি ঝাঁকার মতো ট্রেনে চেপে বেনাপোল সীমান্তে আসে, সেখানে তল্লাশির নামে চলে ছিনতাই ও ধর্ষণ, শিয়ালদহ স্টেশনে অমানুষিক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবারও স্বপ্নভঙ্গ হয়।
রমেশচন্দ্র সেনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস, ‘সাগ্নিক’। ১৯১১-১৯ সময়কালে বাংলার যুবক-যুবতীরা কী দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের মুক্তির জন্য মরণপণ লড়াই করেছিল, তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে জেলের মধ্যে নায়ক শুভর চেতনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। গীতা ও অশ্বিনীকুমার দত্তের ‘ভক্তিযোগ’ ছিল তার প্রিয় বই। জেলের দুঃসহ জীবন, একঘেয়েমি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মায়ের জন্য চিন্তা তাকে পীড়িত করে।
রমেশচন্দ্রের গল্পেও উঠে এসেছে দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত বাংলার প্রান্তিক মানুষ। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, ‘প্রেত’, ‘একফালি জমি’, ‘মৃত ও অমৃত’ ইত্যাদি। নদীর মোহনায় দিক্ভ্রান্ত মাঝিদের নিয়ে তিনি লিখেছেন ‘তারা তিনজন’। জলাভূমির শ্মশান আগলানো ডোমদের নিয়ে লেখা তাঁর গল্প, ‘ডোমের চিতা’, যেখানে হারুর চিতায় বদন চাল আর মাছ সিদ্ধ করে। জ্বলন্ত মৃতদেহের ভিতর থেকে শোনা যায় ফুটন্ত ভাতের টগবগ শব্দ। পশুদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে ‘সাদা ঘোড়া’ গল্পে। বন্যায় বাড়িঘর ভেসে যাওয়া মাধবের পরিবার কলকাতার ফুটপাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের জীবনে ক্ষুধার অন্নের অভিঘাত নিয়ে লেখা হয়েছে ‘ভাত’। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বেশ কিছু স্মরণীয় গল্প লিখেছেন তিনি।
১৯৬২ সালের ১ জুন দুর্যোগপূর্ণ এক দিনে রমেশচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে। ঝড়-জলের মধ্যে শ্মশানে সে দিন উপস্থিত ছিলেন ধূলিমলিন এক তরুণ ঔপন্যাসিক, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যের প্রতি উন্মাদ ভালবাসা, আমৃত্যু ব্যাধি ও নিরন্তর দারিদ্র, এই তিন সঙ্গীকে নিয়েই রমেশচন্দ্র কাটিয়ে গেছেন জীবনের আটষট্টি বছর। সত্যনিষ্ঠ ভাবে তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক ভারতকে দেখেছিলেন। তাঁর স্বদেশে ক্রমশ সামন্ততন্ত্রের জায়গা নিয়েছে ধনতন্ত্র, কৃষক হয়েছে মজুর, একে একে এসেছে যুদ্ধ, কৃষক আন্দোলন, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের স্রোত। দেশ ও জাতির ইতিহাসের এই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেই রমেশচন্দ্র পরম যত্নে অক্ষয় করে রেখে গিয়েছেন।
নিজের দেশ ও মানুষকে অন্তর থেকে ভালবেসেছিলেন রমেশচন্দ্র। প্রান্তিক, ছিন্নমূল মানুষের প্রতি ছিল গভীর সমবেদনা। সমস্ত প্রতিকূলতা ও সঙ্কটের বিরুদ্ধে তাদের আপসহীন লড়াইকে তিনি আজীবন সম্মান করে গিয়েছেন। এই অনন্য লেখকের মৃত্যুর পর দীপেন্দ্রনাথ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লিখেছিলেন, “বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি দেখেছেন কত মামুলি লেখক ও মানুষ কি সোনার কাঠির স্পর্শে দিগ্বিজয়ী হয়। রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত, দরিদ্র ও বিড়ম্বিতই থেকেছেন। কোনোদিন তাঁকে একটু ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও প্রলুব্ধ হতে দেখা যায়নি।” আজকের এই ছিন্নমূল সময়ে রমেশচন্দ্রকে পাঠ করার অর্থ নিজের দেশ ও জাতির শিকড়ের কাছেই নতুন করে ফিরে যাওয়া।
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy








