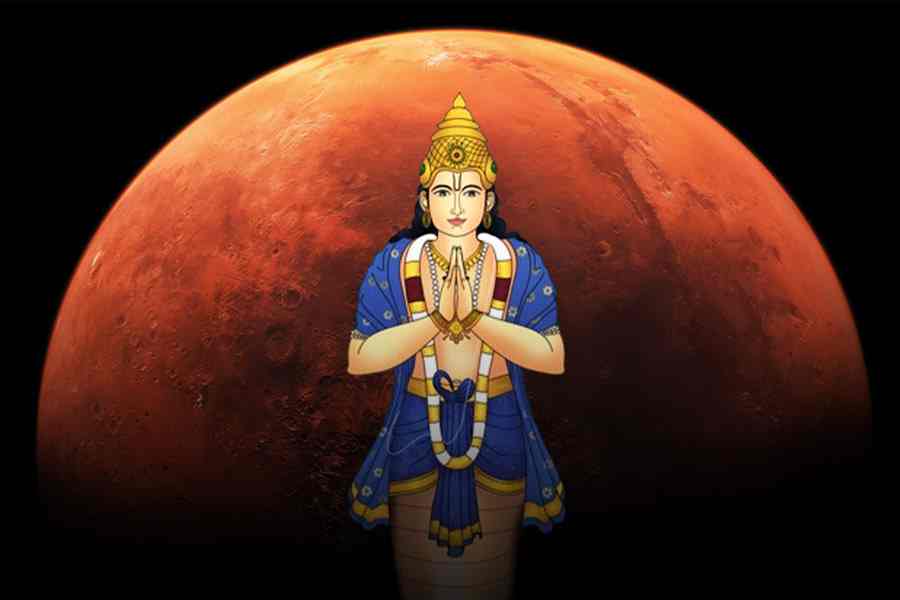শ্রাবণের শেষ দিনে কাশীপুরে
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা নিয়ে আজও মানুষের কৌতূহল। কী ঘটেছিল সে দিন তার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে। লিখছেন শংকরভক্ত পরিবৃত হয়েও খরচ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। কেরানি, ছাপোষা লোকেরা এত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
রোদনভরা শুধু বসন্তই নয়, বর্ষামুখর আষাঢ়-শ্রাবণেই ভাগ্যহীন বাংলার যত বিচ্ছেদবেদনা। আষাঢ়-শ্রাবণের বিচ্ছেদ যন্ত্রণার একটা তালিকা এক সময়ে তৈরি করেছিলাম।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : ১৫ অগস্ট ১৮৮৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ২৯ জুলাই ১৮৯১
স্বামী বিবেকানন্দ : ৪ জুলাই ১৯০২
শ্রীমা সারদামণি : ২১ জুলাই ১৯২০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : ১৬ জুন ১৯২৫
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ: ৭ অগস্ট ১৯৪১
ডা. বিধানচন্দ্র রায়: ১ জুলাই ১৯৬২
সপ্তরথীর এই তালিকা দেখে পুলিশের এক কর্তা আমাকে বলেছিলেন, ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে সাহেবরাও বোধহয় পাঁজি দেখতেন, নইলে ক্ষুদিরামের বিদায়দিন (১১. ০৮. ১৯০৮) কেন এই অগস্টেই ?
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিদায়দিনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়েও শ্রাবণের শেষ দিনের কথা মনে পড়ে যায়। তার পর কত সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আজও মানুষ বারবার জানতে চায় কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে সে রাত্রে কী হয়েছিল এবং কেমন ভাবে তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যবৃন্দ, যাঁরা পরবর্তী কালে ভারতবিজয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে বিশ্ববিজয়ে বার হয়েছিলেন বিশ্বজনের হৃদয় জয় করতে।
শিষ্য বিবেকানন্দের মহাপ্রস্থানের বিস্তারিত বিবরণ আজও আমাদের আয়ত্তে নেই, কিন্তু ১৮৮৬ সালের অগস্ট মাসে পরমহংস রামকৃষ্ণের বিদায়কাহিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন স্বামী প্রভানন্দ—‘বরুণ মহারাজ’ নামে যিনি পাঠকমহলে সুপরিচিত। তিন দশক আগে (১৩৯২- ১৩৯৪) দু’খণ্ডে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন সমস্ত টুকিটাকি সংগ্রহ করে। এবং সেই সঙ্গে আছেন বিভিন্ন গবেষক যাঁরা ঠাকুরের সংখ্যাহীন চিকিৎসকদের কীর্তিকথা ও শ্মশানঘাটে দাহকালে কী ঘটেছিল কিংবা কী হওয়া উচিত ছিল, তার বিবরণ বিভিন্ন বই এবং স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এক সময়ে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম এই সন্ধানে ‘রামকৃষ্ণ রহস্যামৃত’ লিখতে গিয়ে, যেখানে বলতে চেয়েছিলাম—মহাশ্মশানে সে দিন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল এবং লুট হয়েছিল পরমহংসের চিতাভস্ম, যার কিছুটা আজও বোধহয় গোপনাবস্থায় রয়েছে অজানা ভক্তগৃহে, যার অর্থ মঠের ‘আত্মারামের কৌটা’র বাইরেও কোথাও কোথাও আজও থাকতে পারে উনিশ শতকের পরমপুরুষের চিতাভস্ম।
ইতিহাস-সচেতন বরুণ মহারাজ পরমহংসের শেষ অসুখ সম্বন্ধে যথেষ্ট হিসেব করেছেন, রোগাক্রান্ত হয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে সুচিকিৎসার জন্য ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শে বেরিয়ে পড়ে, কাশীপুর বাগানবাড়িতে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫-তে উঠে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে ২৪৭ দিন অতিবাহিত করেছিলেন। ওই বছর জুলাই মাসে ধরা পড়ে তাঁর গলরোগের উপসর্গ এবং ডাক্তারের পরামর্শে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে সাত দিন এবং শ্যামপুকুরে ৭০ দিন কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে আসার দু’টি কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, ‘ওখানকার ঘর স্যাৎসেঁতে। বাহ্যে যাবার সুবিধা নেই।’
দক্ষিণেশ্বর ছাড়ার তিন দিন আগে তিনি তালতলায় ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেম্বারে গিয়েছিলেন। অনেকেই ভুল করেন, ইনিই বুঝি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদেব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেহাবসান শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের ১৫ বছর আগে। তাঁর ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুরেরই স্মরণীয় মন্তব্য, ‘দুর্গাচরণ ডাক্তার, এ তো মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকতো, কিন্তু কাজের বেলায়, চিকিৎসা করবার সময় কোনো ভুল হবে না।’
বলরাম বসুর ভবন থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীর বিবরণ দিতে গিয়ে বরুণ মহারাজের দু’টি খণ্ড লেগে গিয়েছে। আমরা কাশীপুর পর্বেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। শ্যামপুকুরে স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি দেখে নরেন্দ্রনাথ নাকি চেয়েছিলেন, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে চলুন, সেখানে কালী আছেন। ঠাকুরের ইচ্ছাও তা-ই, কিন্তু রানি রাসমণির পৌত্র ত্রৈলোক্যের অসহযোগিতায় তা সম্ভব হয়নি। অতএব কাশীপুর। এই উদ্যানবাটী ভক্ত ডা. রামচন্দ্র দত্ত খুঁজে পেয়েছিলেন মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সাহায্যে, মাসিক ভাড়া ৮০ টাকা। এত টাকা ভাড়ায় চিন্তিত ঠাকুর প্রিয় শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলেছিলেন, ‘বাড়িভাড়াটা তুমি দিও।’ সুরেন্দ্রনাথ ন’মাস এই ভাড়ার দায়িত্ব নেন।
কাশীপুরের অন্ত্যলীলা পর্বে সেবকের অভাব হয়নি। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথও রয়েছেন পুরোভাগে। তাঁদের অনেক কাজ—চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, রোগীর পথ্য সংগ্রহ করা, হাটবাজার করা। পরবর্তী কালের স্বামী অভেদানন্দ তথা তখনকার কালীপ্রসাদ কিছু বর্ণনা রেখে গিয়েছেন—‘প্রথম প্রথম আমরা দুই তিনজন সেবা-শুশ্রূষা করিতাম, শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্য রন্ধন করিতেন।’ পরে সেবকগণের সংখ্যা বাড়ায় একজন পাচক ব্রাহ্মণ নিয়োগ করতে হয়। সেবক লাটু মহারাজের বর্ণনা—‘লোরেন ভাই, রাখাল ভাই, শরোট ভাই, শশী ভাই, বুড়ো গোপাল দাদা, ছোট গোপাল ভাই, নিরঞ্জন ভাই, কালী ভাই, বাবুরাম ভাই—এরা সব বাড়ি ছেড়ে রয়ে গেলো।’ তার পর যোগ দেন যোগীন্দ্র ও তারক। সকলের নেতৃত্ব যে নরেন্দ্রনাথের, তা বিশ্বস্তসূত্রেই জানা যাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
ভক্ত পরিবৃত হয়েও খরচ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। কেরানি, ছাপোষা লোকেরা এত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন? ঠাকুরের কথায় বলরাম বসু পথ্যের খরচ দিতে রাজি হলেন। ‘যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাইরে থাকব, ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।’ লাটু মহারাজ জানাচ্ছেন, ‘রামবাবু হামাদের সব খরচখরচা দিতেন।’ মাস্টারমশাই ‘শ্রীম’ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, টাকাপয়সা নেই। যত সব নড়েভোলা ভক্ত আসতেন বলে ঠাকুর হাসাহাসি করে জিজ্ঞেস করতেন, ‘ক’খানা গাড়ি এসেছে ?’ লাটু একদিন উত্তর দিলেন, উনিশখানা। তখন ঠাকুরের রসিকতা, ‘মোটে এই!’ খরচের বাড়াবাড়ি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে যে মন-কষাকষি হয়েছিল, তা শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকারের দৃষ্টি এড়ায়নি।
‘করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়া খাতায়।’
এই হিসেব রাখার কথায় নরেন বেজায় চটে উঠেছিলেন, ‘এত হিসেব রাখারাখি কেন ? এখানে কেউ তো চুরি করতে আসেনি।’ দেখা যাচ্ছে, হিসেবপত্তর সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মতামত পরে বেশ পাল্টে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, দাতারা হিসেব চায় এবং মাছের টাকা শাকে এবং শাকের টাকা মাছে খরচ করতে হলে, দাতাদের আগাম জানাতে হবে। সেই সব কঠিন হিসেবি আইন আজও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে উন্নতশির রাখতে বিশেষ সাহায্য করছে। ঠাকুর নিজেও বলতেন, গেরস্তর রক্ত জল করা অর্থের অপচয় চলবে না। কাশীপুরে খরচের হিসেব রাখার দায়িত্ব গোপাল দাদা না হুটকো গোপালের উপরে পড়েছিল, তা নিয়ে আজও একটু সন্দেহ আছে। তাপস সেবকেরা যে ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবে খুশি হননি, তা বরুণ মহারাজ বিস্তৃত ভাবেই লিখেছেন। কেউ কেউ চেয়েছিলেন, দু’-তিন জনই যথেষ্ট এবং সেবকেরা যে যার বাড়ি ফিরে যাক। বিরক্ত নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছেয় সায় দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, ‘আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়।’
নরেন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন, ভিক্ষা করেই খরচপত্র চালাবেন। সেই মতো নরেন্দ্রনাথ-সহ কয়েক জন ত্যাগী সন্তান শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ভিক্ষায় বার হয়েছিলেন এবং সেই পবিত্র ভিক্ষান্ন থেকে শ্রীমা তরল মণ্ড তৈরি করে ঠাকুরকে পথ্য দেন। শোনা যায়, এই সময়ে ভক্ত মাড়োয়ারিদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার কথা উঠেছিল। তাঁরা টাকাকড়ি নিয়ে তৈরিও ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হয়নি। এ ছাড়াও অর্থসাহায্যের জন্য নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর আরও দু’জনের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন পাইকপাড়ার জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিতে রাজি হয়ে বলেছিলেন, ‘আমিই সব খরচ দেবো। যখন পারবো না তখন বলব, তখন তোমরা অন্যত্র চেষ্টা করবে।’
এরই মধ্যে নমো নমো করে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন হয়েছিল কাশীপুরে এবং উল্লেখযোগ্য খবর, উপহার পাওয়া একজোড়া চটিজুতো চুরি যায়। তার বদলে যে চটিজুতো আনা হয়, তা যে এখনও বেলুড় মঠে পুজো হয়, তাও বরুণ মহারাজ লিখতে ভোলেননি। তিনি আরও একটি মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। তখনও ‘ঠাকুর’ নামটা তেমন প্রচলিত হয়নি, সবাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ‘পরমহংসমশায়’ বা ‘পরমহংসদেব’ বলতেন।
সেবকদের দিবারাত্র সেবাকার্য সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, রান্না করার পাচক অসুস্থ হলে সেবকরাই পালা করে রাঁধত—ভাত ডাল রুটি চচ্চড়ি ঝোল। একদিন চচ্চড়িতে ফোড়ন দেওয়ার সময়ে গন্ধ পাওয়ায় ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী রান্না হচ্ছে রে তোদের ? যা আমার জন্য একটু নিয়ে আয়।’ সেই চচ্চড়ির স্বাদ সে দিন তিনি নিয়েছিলেন। সেবকদের শরীর সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্বেগ কম নয়। ‘সেবার ত্রুটি হবে বলে তোমরা নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছো না, তোমরা বাপু অসময়ে খাওয়াদাওয়া কোরো না।’
ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় কথামৃতকার শ্রীম খবর পান, ঠাকুরের অসুখ খুব বেড়েছে এবং তিনি রক্তবমি করছেন। ‘ডাবর ভরে যায় রক্তে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান।’ এই সময়ে দুঃসাহসী নরেন্দ্রনাথের মুখে দেখা যায় গুরুর কণ্ঠনিঃসৃত টাটকা রক্ত! স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, ‘নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের পথ্য গ্রহণের পর তাঁহার নিষ্ঠীবন মিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে পান করিলেন।’ তাঁকে অনুসরণ করে নিরঞ্জন, শশী (পরে রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরৎ (ভবিষ্যতে স্বামী সারদানন্দ) ওই রক্ত পান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি
ঠাকুরের পেটের রোগের কথাও উঠতে পারে, এই রোগ কোনও দিন তাঁকে ছাড়েনি। বিখ্যাত হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত (ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের গুরু) শুধু ঠাকুরের চিকিৎসাই করেননি, রোগীর দুর্বল শরীরের কথা ভেবে কোমল চটি এনে নিজের হাতে রামকৃষ্ণদেবকে পরিয়ে দেন। তাঁর ওযুধ খেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাসাধিক কাল বেশ ভাল ছিলেন। এক সময়ে ঠান্ডা লেগে কাশি বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তাররা পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খেতে নির্দেশ দিলেন। ঠাকুর বললেন, ‘যে দোকানে কালীমূর্তি আছে সেখান থেকে মাংস আনবি।’ মা ঠাকরুন বলেছেন, ‘কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখনো তেজপাতা ও আলু মশলা দিতাম, তুলোর মতো সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।’ এই সময়ে শ্রীরামপুর থেকে দৈব ওষুধও আনা হয়, যা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’র অমৃত কথাকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নানা ওষুধের সঙ্গে জনৈক কবিরাজ যে হরিতাল ভস্ম ওষুধ দিয়েছিলেন, তাও যন্ত্রণাতাড়িত ঠাকুর বিনা প্রতিবাদে খেতেন।
বরুণ মহারাজ অনেক খবর নিয়ে লিখেছেন, জানুয়ারির গোড়ার দিকে নরেন্দ্রনাথ একবার বাড়ি যান এবং তাঁর মা সেই সময়ে আদর করে ছেলেকে হরিণের মাংস খাওয়ান। একই সময় ডাক্তাররা পরমহংসদেবকে গুগলির ঝোল খেতে বলায় শ্রীমা একটু ইতস্তত করায় ঠাকুর তাঁর সহধর্মিণীকে বলেন, ‘ছেলেরা পুকুর থেকে গুগলি এনে তৈরি করে দেবে, তুমি রান্না করে দেবে।’ এই সময়ে খাওয়ার বড়ই কষ্ট, শ্রীমা বলেছেন, ‘এক একদিন নাক দিয়ে গলা দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়তো, অসহ্য কষ্ট হতো।’ রোগ নিরাময়ের জন্য রামকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্তের কথাও উঠেছিল। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, ‘ও রামলাল, তুই ১০ টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা কালীকে নিবেদন করে বামুনটামুনদের বিলিয়ে দে।’
মার্চ মাসের মাঝামাঝি আট মাস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তেমন ফল না হওয়ায় ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার জে এম কোটসকে নিয়ে আসেন। এঁকে ঠাকুরের ভাল লাগেনি, চলে যাওয়ার পর ঠাকুরের নির্দেশে বিছানাপত্রে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এক ভক্ত (ভাই ভূপতি) ডাক্তারের বত্রিশ টাকা ভিজিট দেন। কেউ কেউ বলেন, ডা. কোটস টাকা নেননি।
এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। ডা. রাজেন্দ্র দত্ত এক সময়ে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং ডাক্তার সরকার তার দিনলিপিতে লেখেন, ‘আগামী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে তাঁকে দেখতে যাবো।’ ২২ এপ্রিল এঁরা দু’জনে একসঙ্গে ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন—যখন তিনি বলেন, বড্ড খরচা হচ্ছে। রসিক মহেন্দ্রনাথ সে বার নরেনের সামনেই বলেন, ‘কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্তের পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।’ আর শ্রীমকে ঠাকুর বলেন, ‘ওরা কামিনী-কাঞ্চন না হলে চলে না বলছে, আমার যে কি অবস্থা জানে না।’ ২৩ মে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কাশীপুরে এসেছিলেন ঠাকুরকে দেখতে। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার অনেক দিন আসেন না, ডা. রাজেন্দ্র দত্তও রোজ আসছেন না। ঠাকুরের কী হবে ভেবে সবাই বেশ চিন্তিত।
১৫ অগস্ট আর দূরে নয়। স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন, মহাপ্রস্থানের দু’দিন আগে তিনি বলেন, ‘দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালোবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।’
শনিবার, ৩০ শ্রাবণ, রাখিপূর্ণিমা। আগের দিন থেকে পরিস্থিতি ভাল না। ঠাকুরের ক্ষত পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রবল কষ্ট দেখে সেবক বুড়োগোপাল তাঁর কাজ বন্ধ করায় ঠাকুর বললেন, ‘না না, তুমি ধুইয়ে দাও।’ আসলে সকলের আশাদীপ স্তিমিত।
এ বার শ্রাবণের সেই শেষ দিন, রবিবার ১৫ অগস্ট। পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ ১৫ না ১৬ অগস্ট, তা নিয়ে একটু ধন্দ আছে। স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন, ১৬ অগস্ট। কিন্তু সরকারি ডেথ রেজিস্টারে উল্লিখিত ১৫ অগস্ট। এর কারণ রবিবার মধ্যরাত্রে ব্যাপারটা ঘটলেও, রাত একটার আগে ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। ভক্তরা তখনও ভাবছেন, সমাধি এবং তাঁরা সকাল পর্যন্ত তাঁর সমাধিভঙ্গের জন্য বুকে পিঠে ঘি মালিশ করে যাচ্ছেন।
মহাসমাধিকে কেন্দ্র করে যে সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রয়েছে, তার মধ্যে আমরা স্বামী অভেদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বিবরণের উপর একটু নজর দেব। অভেদানন্দ ‘আমার জীবনকথা ১ম খণ্ড’য় বলেছেন, ‘রবিবার, পূর্ণিমা ৩১ শ্রাবণ তিনি মহাসমাধি লাভ করেন।... সেদিন রাত্রে ৬টার সময় আমরা সকলে তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম, সাধারণতঃ যেমন সমাধি হয় তেমনই হইল, তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। আমরাও সমবেত স্বরে ওঁকার ধ্বনি করিতে লাগিলাম, সকলের মনে আশা ছিল যে, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইবে এবং শীঘ্রই তিনি চৈতন্যলাভ করিবেন।’
স্বামী প্রভানন্দ ১৫ অগস্টের সকাল ৮টা থেকে বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করেছেন, যখন ঠাকুর চাইলেন পাঁজি থেকে পড়ে শোনাতে।
‘আজও বাগবাজারের রাখাল মুখার্জি এসেছেন।’ এই ভক্ত সাহেবি ধরনের মানুষ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীর্ণ শরীর দেখে তিনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছেন এবং জেনেছেন, মুরগির জুস খেলে ঠাকুরের শরীরে বল হবে। তিনি ঠাকুরকে মুরগির জুস খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলে ঠাকুর বললেন, ‘খেতে আপত্তি নেই, তবে লোকাচার। আচ্ছা, কাল দেখা যাবে।’
পরবর্তী দৃশ্যে তিনি সারদামণিকে বললেন, ‘এসেছো ? দ্যাখো আমি যেন কোথায় যাচ্ছি। জলের ভিতর দিয়ে অ-নে-ক দূরে।’ সারদামণিকে কাঁদতে দেখে বললেন, ‘তোমার ভাবনা কি ? যেমন ছিলে তেমন থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করছে, তোমায় তেমন করবে।’
সে দিন আরও অলক্ষুনে ভাব। শ্রীমা যে খিচুড়ি রাঁধছিলেন তা ধরে গেল, একটা জলের কুঁজো চুরমার হয়ে গেল। বরুণ মহারাজ তথ্যসমুদ্র মন্থন করে বলছেন, সে দিন পথ্যের প্রায় সবটাই মুখের বাইরে পড়ে যায় এবং ঠাকুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি বলেন, ‘পেটে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ির ক্ষুধা, কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।’
লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা অনুযায়ী তিনি পাখার বাতাস করছিলেন, রাত প্রায় ১১টা, শ্রীরামকৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার পরেই মনে হল, যেন তাঁর সমাধি হয়েছে। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, মহাপ্রস্থানের পূর্বে তিনি এক গ্লাস পায়সম পান করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পথ্য সেবনের পর নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, তখন তিনি বারংবার নরেনকে বলেন, ‘এসব ছেলেদের তুই দেখিস।’
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জীবনসায়াহ্নে রচিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত’ বইতে শেষ সময়ের অনেক খবরাখবর দিয়েছেন। দুঃসহ বেদনায় যখন কোনও কিছু গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন—‘ভেতরে এত ক্ষিধে যে, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই, কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।’ বৈকুণ্ঠনাথের মন্তব্য, এই দৃশ্য থেকেই নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে প্রভুর জন্মোৎসবে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা করেন, ‘যাহা ভারতে কেন, জগতের কোনো প্রদেশেই দেখা যায় না।’
আবার ফেরা যাক স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথায়, ‘সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তখন সকলেই আমরা হতাশ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালে মাতাঠাকুরানিকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া ‘মা কোথায় গেলি গো’ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন... প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর সহধর্মিণী শ্রীমাকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালী বলিয়া সম্বোধন করিতেন।’
আরও খবর সংগৃহীত রয়েছে বরুণ মহারাজের বিখ্যাত বইয়ের শেষ অধ্যায়ে। ঠাকুরের জ্ঞান হারানোর পরে কারও জন্য অপেক্ষা না করে শশী ছুটে যান ডাক্তারের খোঁজে এবং কয়েক মাইল দৌড়ে ডাক্তারের বাড়ি পৌঁছে জানেন, ডাক্তার নবীন পাল অন্যত্র রোগী দেখতে গিয়েছেন। ঠিকানা জেনে শশী আবার ছুটতে থাকেন, পথে ডাক্তারের দেখা পান এবং তাঁকে নিয়ে ফিরলেন উদ্যানবাটীতে। ঠাকুর তখনও নাকি বলেছিলেন, ‘আজ আমার বড্ড ক্লেশ হইতেছে। দুইটি পার্শ্ব যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে।’
বিশিষ্ট ভেষজ বিজ্ঞানী নবীন পাল ঠাকুরের শেষ সময়ের চিকিৎসক। তিনি ঠিক কোন সময়ে ১৫ অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে এসেছিলেন, তা কিছুটা ধোঁয়াশায় ভরা। বরুণ মহারাজের মতে, সেটি ছিল চন্দ্রালোকিত রাত। পাইকপাড়ার রাজাদের কাঙালি বিদায় থাকায় সারারাত ধরে রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত ছিল।
এর পরেই আসা যেতে পারে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিখ্যাত দিনলিপিতে। সোমবার সকালবেলাতেই তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছিল, তিনি এলেন প্রায় একটার সময়ে, ডাফ স্ট্রিটের এক রোগিণীকে দেখে। তাঁর দিনলিপি—আমি তাকে মৃত দেখলাম—রাত একটায় তাঁর দেহাবসান ঘটেছে। তিনি বাম পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন। পদদ্বয় গুটানো, চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত, মুখ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত। যাঁরা তখনও সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করে ডা. সরকার বললেন, একটা ছবি নেওয়ার ব্যবস্থা করা যাক এবং সেই জন্যে নিজের ব্যাগ থেকে দশ টাকা বার করে দিলেন। সে দিন তোলা বেঙ্গল ফোটোগ্রাফারের দু’খানি ছবির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। কে সেখানে উপস্থিত এবং উপস্থিত নন, সে বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয়েছে। অন্তিম শয়ানে রামকৃষ্ণের দু’টি ছবি নিয়ে এখনও বিস্তারিত অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে। বিদেশি সন্ন্যাসী গবেষক স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের টীকা— ‘শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব শরীর একটি সুসজ্জিত খাটের উপর শয়ান। কিঞ্চিৎ বাম দিকে কাত হয়ে। মুখমণ্ডল অতীব শীর্ণ। চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত এবং বাহুদ্বয় দেহের উপর স্থাপিত। দক্ষিণপদ বামপদের উপর ন্যস্ত। ললাটের উপর চন্দনের প্রলেপ এবং কণ্ঠে মাল্যরাজি। খাটটি ফুল ও মালা দিয়ে ঢাকা, খাটের চারকোণে মশারি টাঙানোর চারটি ছতরি। পশ্চাতে কাশীপুর উদ্যানটির কিয়দংশ দৃশ্যমান। বাঁ দিকে বিছানার একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ঠাকুরের ব্যবহৃত, রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশের বেশি ভক্ত ও সুহৃদ খাটের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।’
বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার্সের দু’টি ছবিই অনুরূপ। প্রভেদ এই যে, কয়েক জন ভক্ত তাঁদের স্থান পরিবর্তন করেছেন। একটিতে নরেন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বশরীরে একটি চাদর রয়েছে, অন্যটিতে তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।
স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের টীকা— ‘প্রায় পাঁচটার সময় তাঁর পূতদেহ নীচের তলায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেই সময়ে ফোটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছিল। এক ঘণ্টা পরে শ্মশানযাত্রা। চিতার উপর দেহ স্থাপিত হল। ত্রৈলোক্য সান্যাল সুন্দর কয়েকটি ভজন গাইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।’ এই ত্রৈলোক্যনাথ (১৮৪০-১৯১৬) খ্যাতনামা গীতিকার ও গায়ক। ঠাকুরের প্রিয় গান ‘আমায় দে মা পাগল করে’, ‘গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার’ এঁরই রচনা। ছদ্মনামে রচিত এঁর ‘নববৃন্দাবন’ নাটকে নরেন্দ্রনাথ কয়েক বার অভিনয় করেন।
‘শ্মশানযাত্রার সময়ে একখণ্ড মেঘ থেকে বড় বড় দানার বৃষ্টি ঝরে পড়লো।’ দাহকার্য কতক্ষণে সম্পন্ন হয়েছিল তা নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন দু’ঘণ্টা, কেউ এক ঘণ্টা। কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের ডেথ রেজিস্টারে খবর লেখাতে গিয়েছিলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯ অগস্ট ১৮৮৬। সেখানে মৃতের নাম—রামকৃষ্ট পরমহংস। বয়স ৫২। পেশা ‘প্রিচার’। মৃত্যুর কারণ—গলায় আলসার। খবর এনেছেন— গোপালচন্দ্র ঘোষ, ফ্রেন্ড। ইনিই পরবর্তী কালে স্বামী অদ্বৈতানন্দ।
শ্মশানে সাধকের দেহদাহ যে ত্যাগী ভক্তদের ইচ্ছায় হয়নি, তার ইঙ্গিত পরবর্তী কালে স্বামীজির চিঠিতেই পাওয়া যাচ্ছে। চার বছর পরে (২৬ মে ১৮৯০) তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন, ‘ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব।’
এই দুঃখ থেকেই যে গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠের সৃষ্টি ও রামকৃষ্ণমন্দিরে ‘আত্মারামের কৌটা’র সযত্ন সংরক্ষণ, তা বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়।
তথ্যসূত্র :
স্বামী বিবেকানন্দ : পত্রাবলী, স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, স্বামী প্রভানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্ত্যলীলা, কালীজীবন দেবশর্মা : শ্রীরামকৃষ্ণ পরিক্রমা
-

২০২৫ সালে রাহু কোন রাশিকে কোন বিষয়ে ভাল ফল দান করবে? কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন?
-

ভারত বিরোধিতা? ট্রাম্পের ‘গভর্নর’ মন্তব্য? মাস্কের কথা সত্যি প্রমাণ করে কেন পদত্যাগ করলেন ট্রুডো?
-

এআই কি ত্বকের ক্যানসার আগে থেকে চিহ্নিত করতে পারবে? আশার আলো দেখালেন ভারতীয় গবেষক
-

নতুন চুক্তি নিয়ে কথা বলেনি আল নাসের, ইউরোপে ফিরতে চান রোনাল্ডো, কোন ক্লাবে খেলবেন?
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy
Log In / Create Account
We will send you a One Time Password on this mobile number or email id
Or Continue with
By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy