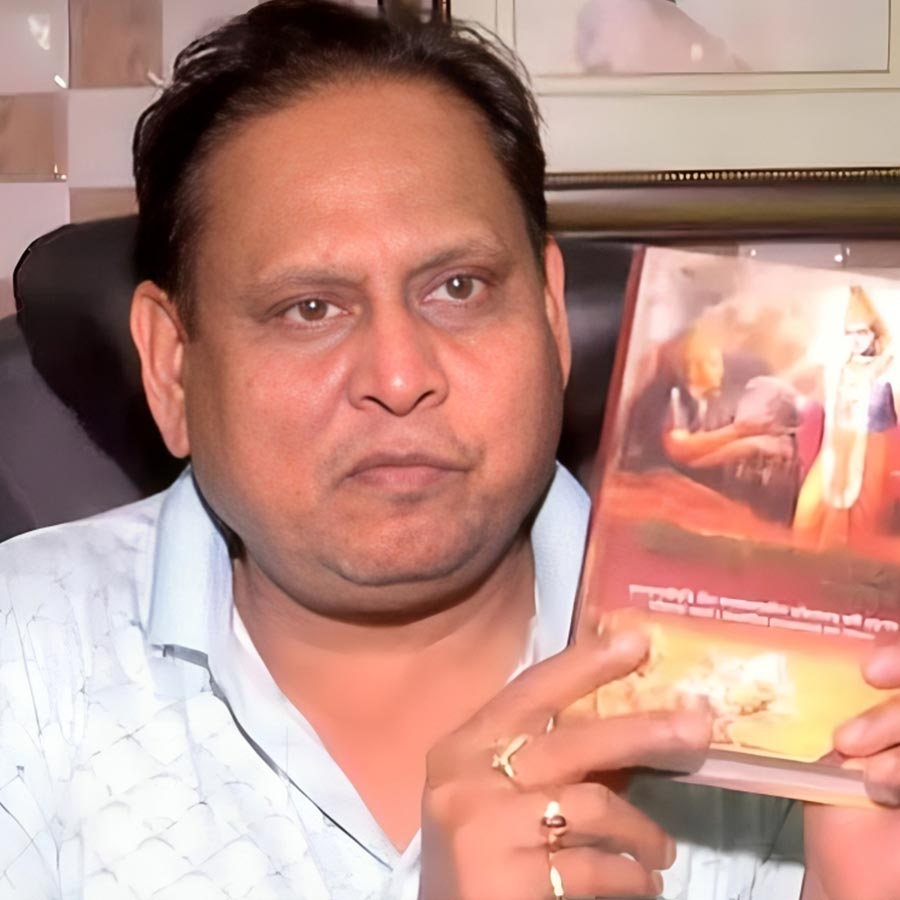পাখি আর মানুষ নাকি দ্বিজ। পাখির ডিমজন্মের পরে প্রস্ফুটিত জীবজীবন। মানুষের দেহজন্মের পরে উত্তরণ-জন্ম। কিন্তু মৃত্যুও যে এক বারের বেশি হয়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ তা জানিয়ে দিয়ে গেল। চার পাশে শোনা গেল, তাঁর বিষয়ে সামাজিক মানুষজন বলছেন সে কথা।
আত্ম-অবমাননার সহজতম পথ অন্যকে অপমান করা। অবশ্য মান-সম্মান, রুচি-অরুচি পরিবর্তনশীল। গোরা উপন্যাসের শুরুতে মেলে, বিনয় দেখতে পায়, ‘ঠিকাগাড়ির উপরে একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া’ পড়ায় ‘বৃদ্ধগোছের’ এক ব্যক্তি ঈষৎ-জখম। লোকটির সঙ্গে রয়েছে সতেরো-আঠারো বছরের একটি ‘কোমলতামণ্ডিত’ মেয়ে। বিনয় সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও পরে তার মনে হতে লাগল, উচিত-কর্তব্যের কিছুমাত্র করে উঠতে পারেনি। নবীনার চকিত আকর্ষণে বিনয়ের ঔচিত্যবোধ খানিক অনুচিত ভাবেই তুঙ্গতুমুল হয়ে উঠেছিল ঠিকই, তবে আচরণের মাপ তো সমসাময়িক সামাজিকতার নিরিখেই বিবেচ্য। তাই বিনয়ের উপচিকীর্ষা তার আপন সামাজিকতার বোধেরই প্রতিফলন। সেই ভাবটিকে আজ আর আমরা ধরতে পারব না। ভদ্রতার সঙ্গে আত্মশান্তির বন্ধন আজকের এই আমিত্ব-প্রধান সময়ে বোঝা কঠিন। তা ছাড়া, শূন্য কলসি বাজেও বেশি।
একাধিক বার ‘মরণ’ যখন, তা হলে তো প্রশ্ন জাগেই, কে এই প্রতুল মুখোপাধ্যায়? গায়ক ছাড়া তো নন বিশেষ কেউ। বাণিজ্যসফল গায়কও নন। তবু দু’ভাবে প্রয়াত প্রতুলের নির্যাতন সম্পন্ন হল। শোনা গেল, তাঁর গান এক সময়ে ভাসালেও পরে নিজেই ভেসে গিয়েছেন। শোনা গেল, শিল্পীই নন তিনি, প্রচারকাঠি মাত্র। জীবনের মধ্য-শেষ পর্বে বেছে নেওয়া রাজনৈতিক শিবিরের কারণে শিল্প-বিবেচনার বদলে মুখ্য হয়ে উঠল শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা।
শিল্প কী? কে নির্ধারণ করেন? আগে রাজা ঠিক করতেন শিল্প কারে কয়, এখনও করেন। আজ বাড়তি পাওনা, প্রচার-নিরিখে শিল্পী-বিচার। এই বিচার-কাঁটাটি ‘আমিত্ব’-নির্ভর। আপনার ‘আমি’ কী ভাবছে, সেটিই ধ্রুব। প্রত্যেকের ‘আমি’ই জ্ঞানবণ্টনের নির্বাধ অধিকারী। ‘আই থিঙ্ক’, ‘আই ডোন্ট থিঙ্ক’ বলার এই স্বাদু রসনায় আমরা মুহ্যমান। কাজেই, প্রতুল বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার অন্যতম পথিকৃৎ, এমন কথা কেউ বললে উল্টো প্রশ্ন আসবে— কে তা স্থির করল? আসবে প্রশ্ন— প্রতুল কি আদৌ কবি?
আর পাঁচটা সৃজনশাখার মতো কাব্য-পরিসরেও কে কবি কে নন, তা নির্ধারণের অধিকারী সবজানতা সমাজ, সর্বজ্ঞ সমালোচক। তবে এখানে পরম-দুষ্টু জীবনানন্দ একটু অন্য ভাবে খুঁচিয়ে দেন, “‘বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—’/ বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর/ বুঝিলাম সে তো কবি নয়— সে যে আরূঢ় ভণিতা”!
প্রতুল বিষয়ে আপত্তির প্রথম কারণটিও দাদাগিরি-সঞ্জাত। এ প্রবণতা অপ্রতুল নয়, সব রঙের মন্দুরার ছায়াপিণ্ডেরই তা অধীত বিক্রম। আগে চাঁদ সওদাগর ডান হাতেই সব কাজ করতেন যখন, তখন বাঁ-হাতে মনসাপুজোর ভাবনাটি নিয্যস অমঙ্গলকাব্যিক স্খলন, বলাই যায়। কিন্তু উল্টোটা বললে? কিংবা যদি চাঁদ বলে ওঠেন— যা করেছি, বেশ করেছি— তখন? তখন ধুন্ধুমার! চাঁদের সত্যিই উচিত ছিল, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বামপন্থী-ডানপন্থীদের সঙ্গে, সমাজমাধ্যমের সঙ্গে, পণ্ডিতম্মন্য জনে-জনে জিগ্যেস করে তার পরে ‘ডিঙ্গা ভাসাও’ গর্জন তোলা, প্রচারপূজ্যকে অস্বীকার করা, নয়া উপচার-পদ্ধতি প্রণয়ন।
চিরসখা ডাইনোসর, বামপন্থী সিপিএম, সোনার পাথরবাটি, সমাজতান্ত্রিক অতিবাম, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ বিজেপি, দয়ালু মশা, সাম্যবাদী কংগ্রেস, ভোটব্যাঙ্ক-নিরাসক্ত বাজেট, বহুসুবিধামুখী তৃণমূল, সর্বোপরি মানবদরদি রাজনীতি নিয়ে গবেষণা আপনি-আমি করতেই পারি। তবে সমাজে কার্বন মনোক্সাইড ছড়িয়ে সামাজিক হওয়ার প্রবণতাটি নতুনও নয়। চিরন্তন এই প্রবণতার চরিত্র বদলেছে। সহজ হয়েছে খাটো করার কৃৎকৌশল। ছিদ্রসন্ধানী বৃদ্ধশোভিত পাড়ার রকের জায়গা নিয়েছে সমাজমাধ্যম। সেখানে সদাসর্বদা বসে ‘চোখে আঙুল দাদা’। সব দেখছেন। চণ্ডীসেলাই থেকে জুতোপাঠ, সবেতে খুঁত ধরছেন। সে কালের মধ্যবিত্ত-একান্নবর্তী পরিবারের চিরবেকার ফুলকাকা কিংবা জঙ্গলের বিগতপরাক্রম সুবৃদ্ধ সিংহের হতাশা-স্মৃতিই যেন ভেসে ওঠে। অভিজাত ভিক্টোরীয় উন্নাসিকতাও বলা যেতে পারে। যে-চামচে কেবল সমালোচনার গলিত পরমান্নই ওঠে।
কিন্তু শিল্পের পরিসরেও এতই দুঃসাহস? পুকুরঘাট বা পাড়ার রকের মতো সমাজমাধ্যম কি এমনই মিষ্টি নিখিল-ভুবন, যেখানে ঈর্ষাবিষ-আত্মগ্লানিও উজাড় করে দেওয়া যায়? যায়, কেননা এই নিখিল-ভুবনের আদতই হল, নিজেকে ভাসিয়ে তোলা। সাঁতার না-জানা ডুবন্ত মানুষ অন্যকে ডুবিয়ে-চুবিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন।
প্রতুল কোন ভাবাদর্শের ছিলেন, তা তাঁর গান শুনলে বোঝা কঠিন নয় সম্ভবত। তবে স্বঘোষিত, সুখী কমরেডগণের দলে প্রতুল কোনও দিনই ছিলেন না। যদি ধরেও নেওয়া যায়, তিনি তথাকথিত ‘সাম্যবাদী’ শিবিরেই একদা ‘ভার্চুয়াল’ সই করেছিলেন, তা হলে প্রশ্ন— রবীন্দ্রনাথের কুন্তী প্রয়াসী হয়েছিলেন কর্ণকে পাণ্ডবদলে ফেরাতে। প্রতুল নামের গানজগতের জাতকুলমানহীন কর্ণ সে-অপচেষ্টার সৌভাগ্যটুকুও পেয়েছিলেন, নিয়েছিলেন? জনবিচ্ছিন্নতা কি এতটাই ক্রোধের জন্ম দেয়, তাঁর মতো শিল্পীকেও অপাঙ্ক্তেয় করার মতো?
‘নান্দীকার’ প্রযোজিত শেষ সাক্ষাৎকার নাটকের একটি সংলাপ মনে পড়ে, যেখানে মন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী এক সাধারণ লোক ঘরে টাঙানো লেনিনের ছবি দেখিয়ে মন্ত্রীকেই বলে— ‘আপনার জাতের লোকেদের লেনিন দু’মাইল দূর থেকে চিনে নিতে পারতেন!’ কে শ্রেণিশত্রু? যিনি বন্ধ কল-কারখানায়, সমাবেশে আন্দোলনের গান গেয়ে বেড়ালেন? না কি জীবনে পথে না-নামা সমালোচকেরা? পছন্দের দল না করলেই শ্রেণিশত্রু— বঙ্গীয় শ্রেণিভাবনার এখন না আছে মাটিযোগ, না আছে আদর্শ। সাধারণ হয়ে ওঠার ক্ষমতা না থাকলে অসাধারণ হওয়া সম্ভব?
এই অলীক কুনাট্যরঙ্গ নতুন নয়। ছোটবেলায় পাড়ায় এক শ্রেণিসচেতন দাদা বুঝিয়েছিলেন— ‘শোন, সলিলের ‘হয়তো তাকে দেখোনি কেউ’টা শোন! বুঝবি, রবীন্দ্রনাথের ময়নাপাড়ার কৃষ্ণকলি ধারেকাছে আসে না!’ সে দিন পারিনি, আজ বলি— হে দাদা, আপনার যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথের একটি চুলদাড়িও ছিন্ন হবে না, কিন্তু কী নিদারুণ অপমানই না করেছিলেন অতুলনীয় সঙ্গীতকার সলিলকে আর তাঁর একটি অসামান্য গানকে! না, কোনও লক্ষ্মণরেখায় বন্দি থাকেনি গণনাট্যের ভাল গান। শিল্প কোনও দিনই বন্দি নয়। শিল্পের আনন্দেই আকাশ-বাতাস কাঁপাতে পারে ‘পথে এবার নামো সাথী’। শ্রেণিপরীক্ষকের ‘অনুমতি’ ছাড়াই হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ঠিক যেমন হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার আগে পরীক্ষকের অনুমতি নেয়নি প্রতুলের ‘আমি বাংলায় গান গাই’।
তথাকথিত প্রেমের গান না-গেয়েও হৃদয়ে আবির মাখিয়েছেন প্রতুল। ব্যক্তিজীবনে তিনি কোন দলের সমর্থক, মঙ্গলময়ের উপাসক না কি মঙ্গল পাণ্ডের— যায় আসে না কিছুই! সমাজমাধ্যমের পিচে বাঁ-হাতি স্পিনার আর ডান-হাতি পেসারদের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্ক্তির উল্লেখ রইল— ‘কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে’। শিল্পের রাজনীতি অবশ্যই থাকে, তবে তা শিল্পলীন। শিল্পীরও থাকতে পারে নির্দিষ্ট বা বিবর্তিত রাজনীতি। তার চর্চা দোষেরও নয়। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ব্যক্তিজীবন ঘিরে এই আক্রমণ— আক্রান্ত নয়, আক্রমণকারীদের বিষয়েই কিছু বলে যায়। ডাইনোসর কেন মুছে গেছে, তার গবেষণা কঠিন। তবে তুলনায় সহজ, তথাকথিত রাজনীতির অলীক আদর্শ কেন উবে গিয়েছে, তার অনুধাবন।
রাজনীতি মানেই দল? সমাজ মানেই শিবির? এই দর্শনেই আক্রমণ করা হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে, মহাশ্বেতা দেবীকে? ‘কী কাজ কী কথা সেটা তত বড়ো কথা নয় আগে বলো তুমি কোন দল’— লিখে গিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ— ‘আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন দল’!
তর্কের আলিম্পনে মায়ার অধিকার বড় কম! কিন্তু সেই নিমেষগুলোর কী হবে, কী হবে সেই সব স্মৃতিমেদুর দিনরাত্রির, যাতে মায়ামুহূর্ত লেগে আছে মুখর পথে-ঘাটে-মাঠে চকিত আবেশ ঘনিয়ে ওঠার! তাঁর গানে কেন সরণি জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ত একটি-দু’টি-অগণন নিমেষ? সেই সব সন্ধ্যাসঙ্গীতের কী হবে, ব্যস্ত শহরের এঁদো গলিতে যখন অরুণ মিত্রের ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি/ তোমারা ভাঙা ডালে সূর্য বসাও’ কবিতার সুরসাম্পান ভাসিয়ে দিয়ে প্রতুলের কণ্ঠ ‘হাঃ হাঃ’ আত্মশ্লেষে ডুব দিত,ভেসে উঠত এক দমবন্ধ-উদার অসহায়তায়! এমনই অজস্র গান! কেন বিমূর্ত সঙ্গীত অমন ভাবে তাঁর শরীর জুড়ে মূর্ত হয়ে উঠত? কেন তাঁর গান শেষ হওয়ার পরেও শ্রোতার মাথায় নতুন করে শুরু হত নির্জন পথচলা?
চিকন কণ্ঠে হঠাৎ-গর্জন, হাসিকেও স্বরস্থান করে তোলা, অর্কেস্ট্রার মতো ঝনঝন বাজতে থাকা হাত-পা সঞ্চালন, গানে কীর্তনের মতো নাট্যবীজের নিরন্তর রসরোপণ, বাদ্যসঙ্গতের ইঙ্গিত-মূর্ছনা কণ্ঠে, হাততালিতে ধারণ করে অনায়াস একাই অগুনতি হয়ে ওঠার জাদু— এই সব কিছুই ‘ভণিতা’ময় বাঙালির চিরসঞ্চয় হয়ে রয়ে গেল! মধুরের অভীষ্ট পাগলামি প্রতুল!
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)