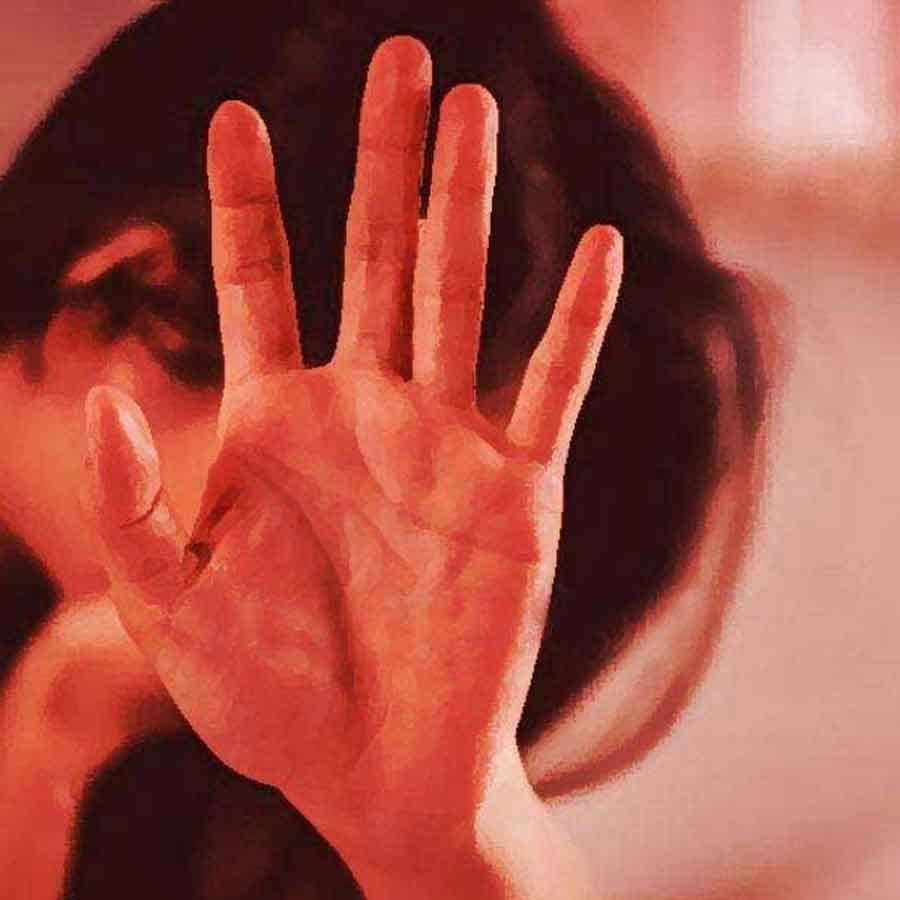ছোটবেলায় একটা খেলা খেলতাম বন্ধুরা মিলে, অনুমান করার খেলা। আমি একটা শব্দ ভাবলাম, সেটাই আসলে উত্তরটা। কিন্তু সেটা মুখে বলা যাবে না, বলা হবে তার অনুষঙ্গ আছে এমন কোনও শব্দ। ধরা যাক আমি বললাম, কুলো। এ বার তা শুনে এক জন বলল, মা— তার মনে হয়তো মায়েদের কুলো নিয়ে কাজ করার ছবিটা গেঁথে। উত্তরের কাছাকাছি গেলে আমি মাথা নাড়ব: হ্যাঁ, বা না। আর এক জন বলল, চাল। কেউ বলল, লক্ষ্মী। এ ভাবেই অনুমান চলল এগিয়ে, হতে হতে যেই না কেউ বলেছে হালখাতা, তক্ষুনি সমবেত হইহইয়ে এসে পড়েছে আসল উত্তর: নববর্ষ!
এ কালের ছোটরা এ সব বোকা-বোকা খেলা খেলে না। সময়টাও এত হাবাগোবা নয় আর, আগাগোড়া চতুরালির, উপরন্তু অনুমান বা কল্পনার কাজটাজও এখন এআই দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তবে কিনা, এই সব নিরিমিষ নির্বিষ খেলার ছলেই আগে একটা কাজ হয়ে যেত: সমাজজীবনের যা কিছু উৎসব-উদ্যাপন, তার অনুষঙ্গ আর অভিজ্ঞানগুলো বসে যেত মগজে আর মনে। নববর্ষ বলতেই যে বৈশাখ, পয়লা, কুলো, মেলা, পুতুল, হালখাতা, এই সব শব্দ আর তা ঘিরে সুখস্মৃতির ভিড়, সে তো আমৃত্যু মোছার নয়। শব্দ তো প্রতীক: তালের বড়া বললে জন্মাষ্টমী, নাড়ু বললেই লক্ষ্মীপুজো, সিমুই বললে ইদ, বো ব্যারাক বলতে ক্রিসমাস ইভ, নববর্ষ বলতে মঙ্গল শোভাযাত্রার রূপ রস স্বাদ গন্ধ আবেগ ভেসে ওঠে যদি, ভেবে দেখলে সে এক চমৎকার ব্যায়াম: মানুষের স্মৃতি ও সত্তার।
সাধারণ মানুষ এ ভাবেই ভাবে। প্রতীক দিয়ে, রূপকল্প দিয়ে ভাবতে তার সুবিধে হয়, সেই প্রতীকগুলোকে ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনে চোখের সামনে দেখতে পেলে তার একটা নিশ্চিন্তির বোধ হয়। এ কারণেই বাইরে থেকে কোনও একটা প্রতীক মোছার চেষ্টা হলে তার আঁতে ঘা পড়ে— দিল্লির সি আর পার্কের মাছবাজার নিয়ে হম্বিতম্বি আর ঢাকায় মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে টানাপড়েন, এই দুই-ই বাঙালির কাছে— অন্তত বৃহত্তর অর্থে, বাংলাদেশ কি পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু বাঙালি কি মুসলমান বাঙালি এই সব কিছু অতিক্রমী যে বাঙালি আর বাঙালিয়ানা বুঝি— তার কাছে সমান আঘাতের হওয়া ‘উচিত’।
এ বুঝতে খুব তলিয়ে ভাবতে হবে না, দুই বঙ্গভূমেই বাঙালি-পরিচিতির চিরচেনা প্রতীকগুলিতে আঘাত হানছে আসলে রাজনীতি, ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি— এবং শেষ বিচারে ক্ষমতাতন্ত্র। ‘দিল্লির বাঙালি’র জাত ও আক্ষরিক অর্থেই ‘পাত’-এর অবমাননায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির আঁতে খুব কিছু লেগেছে বলে বোধ হচ্ছে না, এ রাজ্যের বাঙালি এখন এতই বহুধাবিভক্ত এবং বাঙালিয়ানা-বিবিক্ত যে, জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা সবই তার কাছে ‘যা গেছে তা যাক’ কিংবা ‘যা হবে তা হোক’ এই দুইয়ে পর্যবসিত। অভ্যস্ত দাম্পত্যের মতো তবু রবীন্দ্রনাথ এখনও খানিকটা সেঁটে আছেন, তা বাদে মূলগত ভাবে বাঙালি পরিচিতির দিকচিহ্নগুলি তার জীবনে কোথায়! এমনকি বাঙালির নিজস্ব জাতিগত উৎসব নববর্ষও স্রেফ একটা ছুটির দিন বই আজ আর বেশি কী!
এই পরিস্থিতিতে, মুখে স্বীকার না করলেও এ দেশের বা রাজ্যের বাঙালি আসলে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে ছিল— পদ্মাপারের দিকে। যে দেশের নামটাই তার মুখের ভাষার নামে; পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের মাতৃভাষা যে উদ্যাপনীয়, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীকে সেই স্বীকৃতিটি আদায় করে ছেড়েছে যে বঙ্গভূমি— তার দিকে। সে অবাক বিস্ময়ে দেখেছে বাংলাদেশ নেচে গেয়ে সেজে বসন্ত ঋতু উদ্যাপন করে পয়লা ফাল্গুনে, ক্যালেন্ডারে যে বাংলা তারিখের খবরও সে রাখে না। নিজের দেশে রিয়ালিটি শো থেকে পাড়ার জলসায় যখন মুখ্যত হিন্দি জগঝম্প, তখন সে অবাক হয়ে শুনেছে, পড়শি দেশে কোন তন্ময়তায় গীত হয়ে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল লালন। কলকাতার দুর্গাপূজারও আগে ইউনেস্কো-র আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা পেয়েছে ঢাকার রাজপথে নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা— তা জেনে কি পুলক হয়নি তার: কেউ তো পেরেছে, কেউ তো ধর্ম-সম্প্রদায়েরও ঊর্ধ্বে নিয্যস বাঙালিয়ানার প্রতীকটুকু বছর-শুরুর দিনে এ ভাবে ধরে রেখেছে নিয়ম করে?
পদ্মা দিয়ে যে অন্য জল বইছে গত কয়েক মাসে, ১৪৩২-এর নববর্ষে এ খবরটিও বিলক্ষণ জানা। জানা হয়ে গেছে, ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’র নাম পাল্টে গেছে, কাদের নাকি ‘মঙ্গল’ শব্দে আপত্তি। ঢাকার চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের হাতে গড়া সুদৃশ্য বিচিত্র বাঘ হাতি ঘোড়া পেঁচা পাখির ট্যাবলো পুতুল মুখোশ, কৃষক-জেলে’সহ গ্রামবাংলার চিরন্তন প্রতীকেরা বছর বছর ছিল শোভাযাত্রার ‘শোভা’ (ছবি), এ বছর তা ছাপিয়ে দেখা গিয়েছে রাজনীতির পালাবদলের নায়ক-খলনায়ক-পার্শ্বচরিত্রদের রূপকল্প, আরও অনেক কিছু। সমসময়ের ছাপ উৎসবের গায়ে এসে পড়বেই, স্বাভাবিক। কিন্তু তার কতটুকু স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়া, আর কতটা ধর্ম বা ক্ষমতার রাজনীতির হাঁ-মুখে উৎসবের আত্মসাৎ— সেটুকু না বুঝতে পারলে সমূহ বিপদ বাঙালির, বাঙালিত্বেরই। বাঙালিত্ব=অসাম্প্রদায়িকতা, এই সত্য পাল্টে দিতে দু’পারেই প্রবল রুই-কাতলারা ভেসে উঠেছে, ‘কে দেখেছে কে দেখেছে’ করতে গিয়ে না শেষটায় তাদের মুখেই পড়তে হয়!
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)