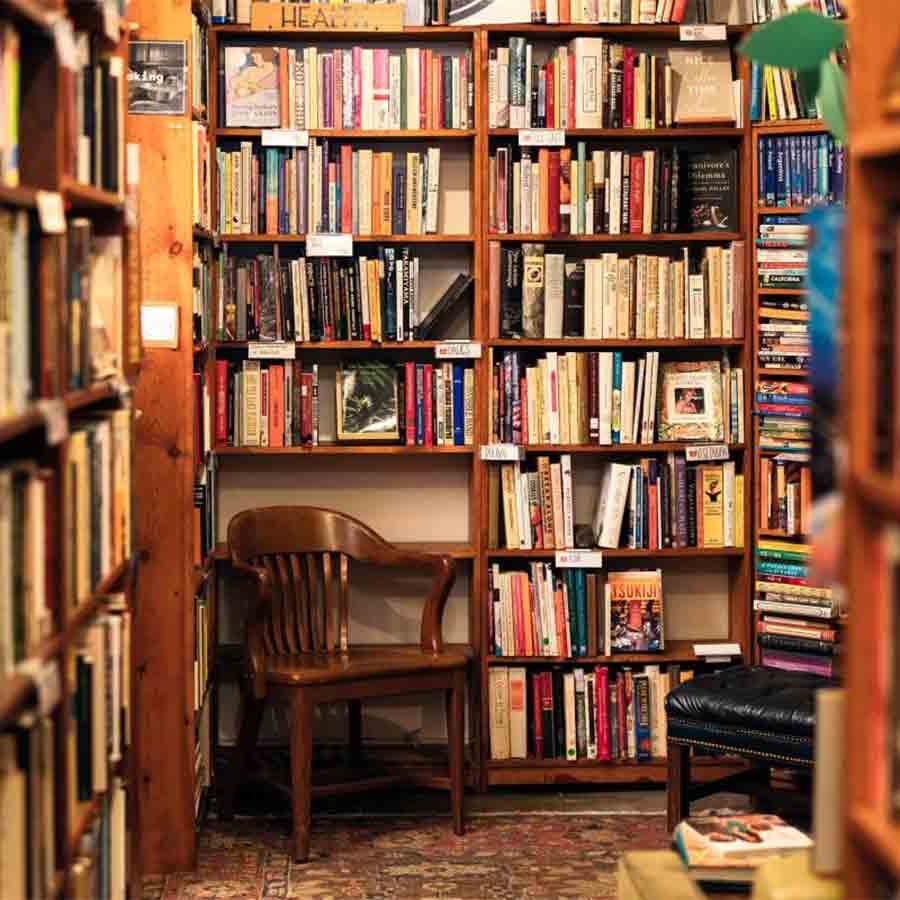মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি, পঞ্চ হাজার গ্রন্থ/ সোনার জলে দাগ পড়ে না,/ খোলে না কেউ পাতা”— বিশ্বকবির এই উপলব্ধি বাংলার গ্রন্থাগারগুলির দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়। এক কালে বাংলার গ্রন্থাগার ছিল দেশের অন্যান্য রাজ্যের কাছে দৃষ্টান্ত। সেই ঐতিহ্য নষ্ট হতে শুরু করে একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই। আজ তার কঙ্কালসার চেহারা। কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক গ্রন্থাগার, নজরদারির অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হাজার-হাজার বই।
বাংলার গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ বাম আমলের শেষ দিক থেকেই বন্ধ। ২০২১ সালে গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি সে ভাবে। ফলে এক জন কর্মীকে দু’টি-তিনটি করে গ্রন্থাগার দেখতে হচ্ছে। কমছে পাঠক। আবার অনেক পাঠক খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁর প্রিয় গ্রন্থাগার। এই চক্রাবর্তেই বাংলার পাঠাগার বিলুপ্তির পথে।
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। জমিদাররাও এই আন্দোলনে শামিল হন। ১৮০৪ সালে উত্তরপাড়া ও বালির সীমানা বালিখাল মানুষ পেরোত নৌকোয়। ১৮৪৬ সালে বালিখালের উপর তৈরি হল পাকা সেতু। ফলে কলকাতার সঙ্গে উত্তরপাড়ার যোগাযোগ সহজ হল। এর কয়েক বছর পরে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি গ্রন্থাগার তৈরির পরিকল্পনা করেন। জমিদারের কয়েক জন পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে একটি অতিথিশালা নির্মাণের অনুরোধ জানান। প্রত্যুত্তরে জমিদার বলেন, ‘আমি এক নতুন ধরনের অতিথিভবন তৈরি করব। যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের জীবনযাত্রার মূল রসদ খুঁজে পাবে।’
১৮৫৪ সালে সেই পরিকল্পনার কথা তৎকালীন কমিশনারের কাছে জানালে তিনি তা খারিজ করে দেন। হতাশ হলেও জয়কৃষ্ণ কাজ চালিয়ে গেলেন। ১৮৫৯ সালের ১৪ এপ্রিল উত্তরপাড়ায় সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল এশিয়ার সম্ভবত প্রথম নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার। প্রথম দিকে জয়কৃষ্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়েই এর সূচনা করলেন। উইলিয়াম কেরির রামায়ণ, হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ, বহু বাংলা সাময়িকপত্র সহ এই প্রতিষ্ঠানে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজার ।
১৯৬৪ সালে সরকারি অধিগ্রহণের পর জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রথম শ্রেণির গ্রন্থাগারের মর্যাদা লাভ করে। ২০০৮ সালে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন একে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেয়। এখানে সংরক্ষিত আছে তালপাতা, ভূর্জপত্র, প্যাপিরাসে লেখা প্রায় এক হাজার পুঁথি।
বিংশ শতকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা গ্রন্থাগারগুলিকে ঘিরে নতুন ধরনের আন্দোলন দানা বাঁধল। এই আন্দোলন সংগঠিত করতে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এগিয়ে এলেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দও মনে করছিলেন, গ্রন্থাগারকে স্বনির্ভর নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে সাধারণের আরও কাছে নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় এই উদ্যোগ শুরু হল ১৯১৪ সালে অন্ধ্র গ্রন্থাগার পরিষদ ও ১৯২১ সালে মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের পর।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে গড়ে উঠছে একটার পর একটা গ্রন্থাগার। রাজনীতির উত্তপ্ত আবহে গ্রন্থাগারকে ঘিরে আন্দোলন তুঙ্গে উঠল, যখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরানোর প্রস্তাব হয়। শুধু গ্রন্থাগারকে ঘিরে এমন আন্দোলন কলকাতা এর আগে দেখেনি।
১৯২৪ সালে কর্নাটকে হয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ওই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের। ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে এই নতুন সংগঠন। প্রধান কর্মসচিব হয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীলকুমার ঘোষ। শুরু হল গ্রন্থাগার পরিষদের পথ চলা। এরই মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই পড়ে ফেলেছেন ১২৯২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় ‘বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘লাইব্রেরী’ নামক প্রবন্ধটি। আদর্শ গ্রন্থাগার কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্র-দর্শনের পরিচয় মেলে এখানে। পরিষদের উৎসাহী সদস্যরা যোগাযোগ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। সর্বসম্মতিতেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন, গ্রন্থসজ্জা, পুস্তক নির্বাচন থেকে শুরু করে পরিষেবা প্রদানেও পরিষদের সদস্যরা রবীন্দ্রনাথকেই আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বকবি ‘লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য’ নামে একটি অভিভাষণ রচনা করলেন। শারীরিক কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারায় অভিভাষণটি পাঠ করলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
এই পরিষদ শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্র-স্নেহধন্য কবিগুরুর সচিব অপূর্বকুমার চন্দ, রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কেও সভাপতি হিসেবে পেয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজীবন ছিলেন পরিষদের পুরোধা।
ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে প্রায় শ’খানেক পাবলিক লাইব্রেরি বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠে। বিংশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় দশকের মধ্যে এই লাইব্রেরিগুলি মিলে তৈরি হয় ‘অল বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন’। বেলগাঁও সম্মেলনের পর সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রতিটি রাজ্যে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হবে। ইংরেজি ‘বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন’-এর নতুন নাম হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। স্বাধীনতার প্রায় আড়াই দশক আগে থেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।
সত্তর দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নানা ভাবে ব্যাহত করল। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় সব ওলটপালট হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দের অনেকে আত্মগোপন করলেন। জরুরি অবস্থা শেষ হতেই সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ল। সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে বামপন্থীরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে গ্রন্থাগার আইন পাসের উদ্যোগ নেবেন। নির্বাচনের পর অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধানরা ১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন পাস করাতে সক্ষম হলেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্য গঠন করল স্টেট লাইব্রেরি প্ল্যানিং কমিটি। আশির দশকে প্রশাসনের উচ্চস্তর থেকে জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু বিভাগ এবং সাক্ষরতা কেন্দ্র, তরুণদের জন্য কেরিয়ার গাইডেন্স স্কিম চালু হলেও সেগুলি সে ভাবে কার্যকর হয়নি।
প্রাচীনতার দিক থেকে বাংলার গ্রন্থাগারের ইতিহাস ইংল্যান্ড বা আমেরিকার থেকেও প্রাচীন। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত মহাবিহারে একটি উন্নত মানের গ্রন্থাগার ছিল। রাজ্যের ত্রিস্তরীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে মোট ২৪৮০টি গ্রন্থাগার রয়েছে, এর মধ্যে ১৩টি সরকারি। ২৪৬০টি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার। ৮৫টি গ্রন্থাগার মডেল গ্রন্থাগার হিসেবে চিহ্নিত। ২০০টি গ্রন্থাগারকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধানে তৈরি হয়েছিল গ্লোবাল মেম্বারশিপ প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু ইন্টারনেটের সরবরাহ না থাকায় মিলছে না পরিষেবা। গ্রন্থাগারে আড়াই লক্ষের উপর বই থাকলেও নজরদারির অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক বই। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে এটি চলে আসে বিধাননগরের কাছে কাঁকুড়গাছিতে। এখানে পাঠকের সংখ্যা কয়েক হাজার, কিন্তু পরিষেবা নিয়ে খুশি নন তাঁরা।
একই চিত্র জেলাগুলিতেও। ২৪টি জেলায় রয়েছে ২৪৮০টি গ্রন্থাগার। এর মধ্যে গ্রামে রয়েছে দেড় হাজার। ২৬টি গ্রন্থাগারের কোনও অস্তিত্ব নেই। ২৪৫৪টি গ্রন্থাগারের মধ্যে বর্তমানে কর্মীর অভাবে বন্ধ রয়েছে ৪৯০টি। ১৯০০ গ্রন্থাগার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ৬০০টি গ্রন্থাগারে নিয়মিত গ্রন্থাগারিক নেই। গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নিজের জেলা পূর্ব বর্ধমানেও ১২টি গ্রন্থাগার বন্ধ। কর্মী সঙ্কটের অভিযোগ করছে কর্মচারী সংগঠনগুলো। সাড়ে পাঁচ হাজার অনুমোদিত পদের মধ্যে চার হাজারের বেশি শূন্য। ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য ৭৩৮টি গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কলকাতা জেলার চল্লিশটি এবং উত্তর দিনাজপুরের বারোটি শূন্য পদে এখনও কোনও পরীক্ষা হয়নি।
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু গ্রন্থাগার চালাচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরাই। মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরে একটি গ্রন্থাগার এর উদাহরণ। এই মুর্শিদাবাদেই আঠারোটি গ্রন্থাগারে তালা ঝুলছে। কর্মীর অভাবে কাজ হচ্ছে না কোচবিহারের রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙা সাধারণ পাঠাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিলনতীর্থ পাঠাগারে।
জেলাওয়াড়ি হিসাব বলছে, রাজ্যে বেশ কিছু শতকপ্রাচীন গ্রন্থাগার রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে শ্রীগুরু গ্রন্থাশ্রম, প্যারীমোহন মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরি, নৈহাটির বঙ্কিম পাঠাগার এবং বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী, হাসনাবাদে আড়বেলিয়া সেবক সমিতি পাঠাগার, ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির, শ্যামনগরের মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার, আগরপাড়া পাঠাগার, টাকির সৈয়দপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রন্থাগার, কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিটের নজরুল পাঠাগার, কালীঘাটের সত্যচরণ ইনস্টিটিউট এবং এই রকমই আরও অনেকগুলি। কর্মীর অভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও ধুঁকছে।
প্রশ্ন উঠছে গ্রন্থাগারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই ভাবেই কি চলতে থাকবে বাংলার গ্রন্থাগারগুলি? কেরল, অরুণাচল, তামিলনাডু যা পারে, আমরা তা পারি না কেন? মানুষের বই পড়ার অভ্যাস ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলেই কি এই বিপত্তি! তাই কি উৎসাহ হারাচ্ছে প্রশাসন। সময়ই হয়তো এর উত্তর দেবে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)