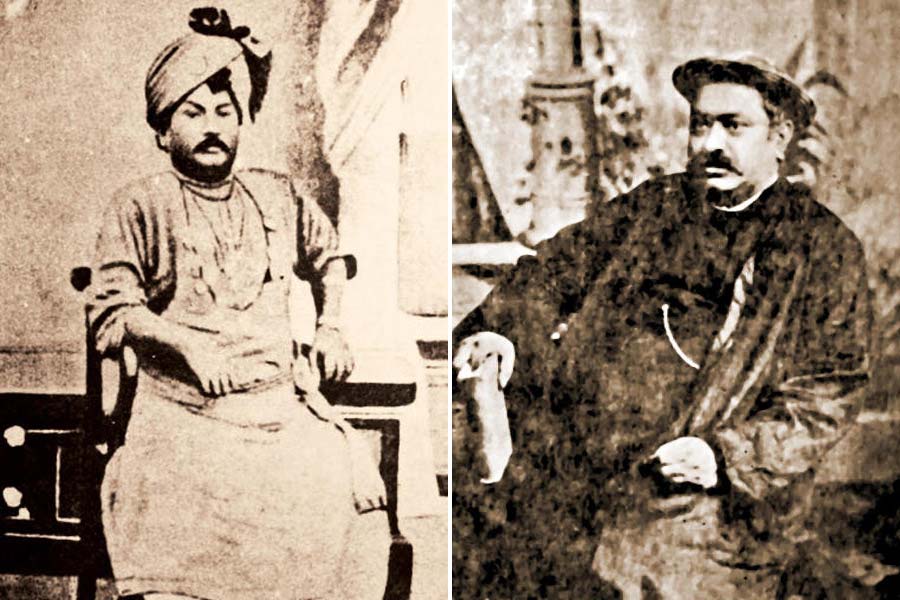আমাদের ছেলেবেলায় যে সব বাংলা স্বদেশপ্রেমের গান গেয়েছি নানা মিছিল-মিটিং-সভায়, সেই সব গান একটু ভাবলেই মনপ্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে সময়ে নেতাজির আহ্বানে মানুষ এগিয়ে এসেছিল, সেই ‘হিন্দু মেলা’-র (১৮৬৭) সময় থেকে বাংলা স্বদেশি গানের ইতিবৃত্ত শুরু।
ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দু মেলা (১৮৬৭) যেন এক নতুন যুগের আরম্ভবিন্দু। এই সময় আমাদের দেশের বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলি স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলেছিল। বিভিন্ন সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান, জনসমাবেশ, মিছিলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল এই স্বদেশি গান। লোকের মুখে মুখেই এই সকল স্বদেশি গান প্রচারিত হয়েছিল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ তখনও ‘বঙ্গদর্শন’-এর মাধ্যমে বাংলার ঘরে ঘরে এসে পৌঁছয়নি। ওই গ্রন্থের ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতটি ১৮৭৫ সালে রচিত। পরে ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে ‘আনন্দমঠ’-এ সংযোজিত হয়। তার বহু পূর্বেই নবগোপাল মিত্র কর্তৃক ১৮৬৭ সালে ‘হিন্দু মেলা’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ‘বন্দে মাতরম্’ শব্দ দু’টি জনসাধারণের মনে নতুন আবেগ সঞ্চার করেছিল। ওই সময়, হিন্দু মেলার অন্যতম সংগঠক, নাট্যকার মনোমোহন বসুর ‘দিনের দিন সবে/ দীন হয়ে পরাধীন’ গানটি এই মেলার প্রথম বছর আনুষ্ঠানিক ভাবে গীত হয়। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গাওয়া হয় রবীন্দ্র-অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অসামান্য স্বদেশি গান— ‘মিলে সব ভারতসন্তান,/ একতান মন-প্রাণ,/ গাও ভারতের যশোগান।’ সত্যেন্দ্রনাথের এই গান সমগ্র ভারতের উপযোগী প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছিল। এই গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন, “এই মহাসঙ্গীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরীর তটে, বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। এই বিংশ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্রও ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।”
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অশ্রুমতী’ নাটকের বিশেষ একটি গান ‘চল রে চল সবে ভারত-সন্তান/ মাতৃভূমি করে আহ্বান’ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী রচিত, ‘অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী!/ গাহ আজি হিন্দুস্তান’ প্রভৃতি গানগুলি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কৃতী-যশস্বী সন্তানেরা প্রধানত হিন্দু মেলাকে উপলক্ষ করে রচনা করেছিলেন নতুন নতুন স্বদেশপ্রেমের গান। ১৮৭৭ সালে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দু মেলা’ উপলক্ষে রচনা করলেন, ‘অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান’।
এক দিকে হিন্দু মেলার আহ্বান, অন্য দিকে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র, তাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের সঙ্গে ভারতবাসীর দ্রুত পরিচয় ঘটার ফলে সমসাময়িক দেশের সাহিত্য ও কাব্যে ইউরোপীয় প্রভাব পড়ে। আমাদের জাতীয় জীবনে সে যুগের কবি-সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের রচিত কাব্য, নাটক এবং সঙ্গীতগুলি ধীর ধীরে বিস্মৃতির পথে হারিয়ে গেলেও বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সেই সব গান অক্ষয় হয়ে আছে।
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘ভারত সঙ্গীত’-এর বাণী কবির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হল, ‘বাজো রে শিঙা বাজো এই রবে, শুনিয়া ভারত জাগুক সবে।’ এলাহাবাদ প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় রচিত ‘কত কাল পরে/ বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতারি/ পার হবে?’ বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-পঙ্ক্তি হয়ে আছে। উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত বিখ্যাত ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ নাটকের ‘হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল/ সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল’ গানটি সে-কালের তরুণদের মুখে মুখে ফিরত। সমকালীন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’-এর অংশবিশেষ ‘স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়’ বিপ্লবীরা মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতেন।
স্বদেশি গানের গৌরবময় অধ্যায় শুরু হয় ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বহু স্বদেশি গান রচনা করেছেন। সরকারি নিষেধের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষকে মৈত্রীর বন্ধনে বেঁধেছিলেন। রাখিবন্ধনের পুণ্য দিনে সকলের সঙ্গে পথে নেমে কবি গাইলেন— ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল/ বাংলার বায়ু, বাংলার ফল...’।
অতুলপ্রসাদ সেন-এর মন্তব্য: ‘সেই সময়কার গানগুলি বঙ্গ ভাষার ও বাঙালি প্রাণ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার বোধহয়, সে সময় বঙ্গদেশে যে দেশপ্রীতির স্রোত বহিয়াছিল, তাহার উৎস রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যাইত— ‘আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালবাসি’; পথে পথে শোনা যাইত— ‘বাংলার মাটি বাংলার জল/ বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হোক পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান’।
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বার বার বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে সরকারি ঘোষণায় বলা হল, ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা হবে। বাঙালি মরিয়া হয়ে, সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেন। শুরু হল বিদেশি দ্রব্য বর্জন। এই সময় কবি রজনীকান্ত সেন গান বাঁধলেন, ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই/ দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।’
এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি ইংরেজ বাহাদুরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা অত্যাচার-উৎপীড়নে মাত্রা বাড়িয়েছে, তবু ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রে জাগ্রত বাংলার মানুষকে এতটুকুও দুর্বল করতে পারেনি। সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ লিখলেন, “দি মন্ত্র (বন্দে মাতরম্) হ্যাড বিন গিভন অ্যান্ড ইন আ সিঙ্গল ডে আ হোল পিপল হ্যাড বিন কনভার্টেড টু দ্য রিলিজিয়ন অব পেট্রিয়টিজ়ম। দি মাদার হ্যাড রিভিল্ড হারসেল্ফ।”
মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সংগ্রামে। পুলিশের হাতে প্রহার, কারাদণ্ড, ফাঁসি, নির্বাসন— সবই তরুণ-সংগ্রামীদের কপালে জোটে। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা কাণ্ডে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেফতার হলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর প্রখর বুদ্ধি, আইনি অভিজ্ঞতা ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে অরবিন্দকে মুক্ত করলেন। সেই বছরই ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ ইউরোপীয় ক্লাব-প্রত্যাগত একটি ফিটন গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে তার উপরে বোমা নিক্ষেপ করেন ক্ষুদিরাম। গাড়িতে দু’জন ইউরোপীয় মহিলা ও তাঁর কন্যা ছিলেন, দু’জনেরই মৃত্যু হয়। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হলেন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় (১২ অগস্ট, ১৯০৮)। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরে বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস লিখলেন— ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’, গানটির কথা ও সুর মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।
বরিশালের যাত্রা দলের অধিকারী অশ্বিনীকুমার দত্তের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত চারণকবি মুকুন্দ দাস পথে পথে গান গেয়ে মানুষের চেতনায় বিদেশি শোষণের, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে গানে গানে চারণকবি বরিশালবাসীকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তুললেন। যাত্রা দলের অধিকারী মুকুন্দ দাসের গান ‘আয় রে বাঙালী আয় সেজে আয়,/ আয় লেগে যাই দেশের কাজে’, ‘ছিল ধান গোলা ভরা/ শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।’ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সব গান সভা-সমিতিতে গেয়ে চারণকবিকে বহু বার কারাবরণ করতে হয়েছে।
মুকুন্দ দাসের যাত্রাপালার সব গানগুলি যে তাঁরই রচনা এমন নয়; তাঁর গলায় গীত অনেক স্বদেশি গানই হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন নামে এক কবির রচনা। এমনই একটি সুপ্রসিদ্ধ গান— ‘সাবধান সাবধান/ আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড/ রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান’। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে এই চারণকবি স্বদেশি যাত্রাগান দিয়ে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।
প্রখ্যাত কাব্যকার স্বদেশপ্রেমী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) রচিত বহু স্বদেশি গান সে সময় বিপ্লবীদের মুখে মুখে ফিরত। এঁর রচিত স্মরণীয় একটি গান— ‘মা গো, যায় যেন জীবন চলে/ শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে/ বন্দে মাতরম্ ব’লে।’ কাব্যবিশারদের এই গান গেয়ে এক কালে দলে দলে স্বদেশপ্রেমী যুবক আত্মদান করেছিল।
রবীন্দ্রনাথের ‘অয়ি ভুবনমনমোহিনী’ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতবাবু লিখছেন, “১৮৯৬, ডিসেম্বরে কংগ্রেসের ১২শ অধিবেশন কলকাতার বিডন স্কোয়্যার। রবীন্দ্রনাথ নিজ সুরে ‘বন্দে মাতরম্’ গাহেন। জোড়াসাঁকোর বাটিতে কংগ্রেসের অভ্যাগতদের আমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত গান— ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’ গাহিয়াছিলেন।”
‘গীত-প্রবেশিকা’-য় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘স্বরলিপি’ বইটিতে নানা ধরনের গান ও সেই সব গানের স্বরলিপি আছে। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ গানটিও আছে। গানটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত হরফে ছাপা; কিন্তু স্বরলিপি বাংলায়। গানটির তলায় লেখা, রচনা: বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর এবং সুর: রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। নিজের দেওয়া সুরে ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯-তে রেকর্ড করেন। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে বিশিষ্ট সরোদবাদক তিমিরবরণের সুর সংযোজনায় ও পরিচালনায় ‘বন্দে মাতরম্’ রেকর্ড প্রকাশ করে আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। এর আগে পর্যন্ত ‘বন্দে মাতরম্’ দেশ রাগে গাওয়া হয়ে এসেছিল, তিমিরবরণই প্রথম দুর্গা রাগে গানটির সুর দেন। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইভা গুহ, আরতি বল, শিবানী সরকার, পরেশ দেব, ধীরেন দাস, সুধীর চক্রবর্তী, সাগরময় ঘোষ প্রমুখ।
১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সূচনাস্বরূপ ভারতের সর্বত্র ‘হরতাল’ পালিত হয়। শুরু হয় অহিংসা সত্যাগ্রহ। এই সময় ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গজনকে ‘চরকার গান’ শোনালেন— ‘ভোমরায় গান গায়, চরকায় শোনো ভাই...।’
কবি-গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশপ্রেমের গানগুলি যেমন কথায় সমৃদ্ধ, তেমনই সুরে ও গীত-রীতিতে অভিনব ও উদাত্ত। কবির রচিত— ‘উঠো গো ভারতলক্ষ্মী’, ‘হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর’, ‘বলো বলো বলো সবে...’ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানগুলি হয়ে উঠেছিল জাতীয় আন্দোলনের মহাযজ্ঞে বিপ্লবী সৈনিকদের হাতিয়ার।
নিধুবাবু, অর্থাৎ রামনিধি গুপ্ত ছিলেন টপ্পা গানের প্রবর্তক। এই নিধুবাবুই সর্বপ্রথম ভাষাজননীর বন্দনাগীতি গেয়েছিলেন এবং তাঁর এই গান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গানটির শুরু—‘নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনে স্বদেশীয় ভাষা/ পূরে কি আশা?’ অতুলপ্রসাদ সেন বাউল সুরে এই গানেরই প্রতিধ্বনি করলেন তাঁর এই গানে— ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা’।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বদেশি গান রচনায় যে আবেগ দ্বারা দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, তা বিস্ময়কর। কবির দেশবন্দনা— ‘ভারত আমার, ভারত আমার/ যেখানে মানব মেলিল নেত্র’ বা ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা/ আমাদের এই বসুন্ধরা’, আবার ভারতবর্ষের রূপ বর্ণনায়— ‘শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা...’ প্রভৃতি গানগুলি বাঙালির শোণিতে মিশে আছে। কখনও কাতর কণ্ঠে মিনতির সুরে কবি গাইলেন, ‘একবার গালভরা মা ডাকে/ মা বলে ডাক, মা বলে ডাক, মা বলে ডাক মাকে।’
স্বদেশি আন্দোলনে দেশের সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করতে দিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির ভূমিকা সমরাঙ্গনে তূর্যধ্বনির মতো আবেগময়, প্রাণময়। সঞ্জীবনী মন্ত্রোচ্চারণের মতো, যা মনকে উদ্দীপ্ত করে, উল্লসিত করে। ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ’— ভারতবর্ষে এমন গৌরবগীতি আর হওয়ার নয়। যে সব কৃতী ভারতীয় দেশ-বিদেশে ভারতের জাতীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, দিজেন্দ্রলাল ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁদের কথাও স্মরণ করেছেন, সুর ও বাণীতে; ‘একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়/ একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।’
কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গানের জন্য কারাবরণ করেছিলেন; কিন্তু কারা প্রাচীরের লৌহবেষ্টনী বিদ্রোহী কবি-গীতিকারের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। কবি গান বাঁধলেন, ‘কারার এই লৌহ কপাট...’, ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রের মতোই এই গান কণ্ঠে কণ্ঠে দেশের সর্ব স্তরে আলোড়ন তুলল। কবির ‘সর্বহারা’ কাব্যের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার’ বিখ্যাত গানটি ১৯২৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লিখিত এবং কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রথম গীত হয়। নজরুলের স্বদেশি গানে আছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, যৌবন চাঞ্চল্য আর তীব্র অসহিষ্ণুতা। নজরুলের গান, গানের অভিনব সুর বাংলার স্বদেশি গানে নতুন উন্মাদনা জাগিয়েছিল। তাঁর রচিত, ইংরেজি ‘মার্চিং সং’-এর অনুকরণে সুরারোপিত, ‘চল্ চল্ চল্/ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’, ‘টলমল টলমল পদভারে’ বাংলার স্বদেশি গানে এক অভিনব সংযোজন।
নজরুলের সমসাময়িক কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাসের রচিত ‘বন্ধন ভয়, তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা/ আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা’ অথবা ‘শ্মশানে কি নতুন করে লাগল সবুজ রং/ সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কি বন্দে মাতরম্’, কবির বিখ্যাত গীতিনাট্য ‘অভ্যুদয়’-এর গানগুলি গত চারের দশকে জনমানসে বিশেষ উন্মাদনা জাগিয়েছিল। ১৯৪২ সালে অগস্ট আন্দোলনের অব্যবহিত পরে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য গান রচনা করেছিলেন— ‘নয়ই অগস্ট তোমায় নমস্কার...’ এই গানটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর ‘চক্রশোভিত উড়ে নিশান/ নবভারতের বাজে বিষাণ’ গানটি ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণার পরই সম্প্রচারিত হয়েছিল।
স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেও বাংলা স্বদেশি গান রচিত হয়েছে; বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তাগিদে— চলচ্চিত্র ও নাটকের প্রয়োজনে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল তরুণ নির্ভীক সৈনিক দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে মোহিনী চৌধুরী লিখলেন— ‘মুক্তির মন্দিরসোপান তলে/ কত প্রাণ হল বলিদান/ লেখা আছে অশ্রুজলে,’ কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উদাত্তকণ্ঠে গীত এই গানটি এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙালির মুখে মুখে শহিদদের উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে।
মোহিনী চৌধুরীর সমসাময়িক স্বনামধন্য গীত-রচয়িতা তথা আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম পথিকৃৎ সলিল চৌধুরীর ‘ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে’; ‘এ দেশ, এ দেশ/ আমার এ দেশ/ এই দেশেতেই জন্মেছি মা’, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার গোপাল দাশগুপ্ত-র ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা,’ সঙ্গীত পরিচালক প্রবীর মজুমদারের কথায় ও সুরে অপূর্ব আবেগময় গান ‘মাটিতে জন্ম নিলাম/ মাটি তাই রক্তে মিশেছে’ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানগুলিও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)