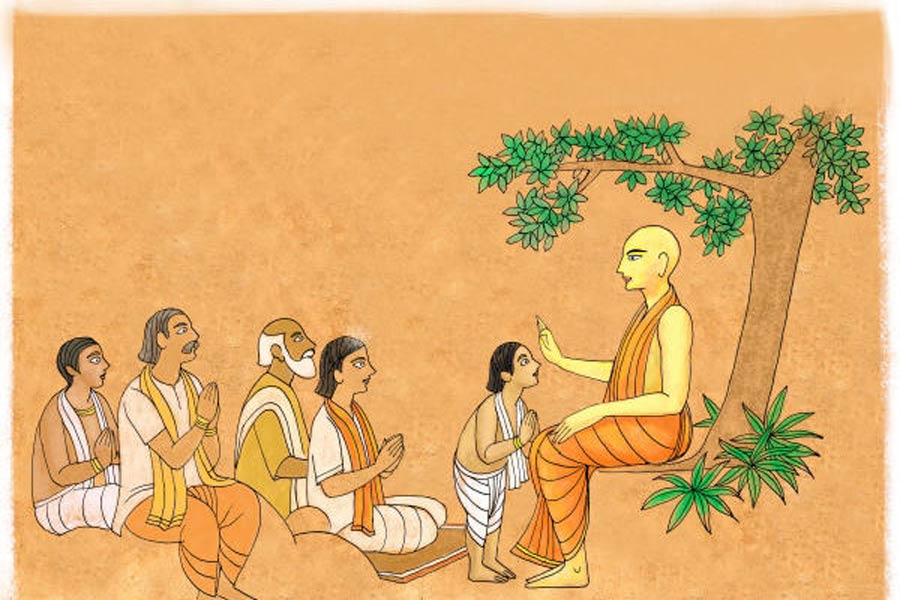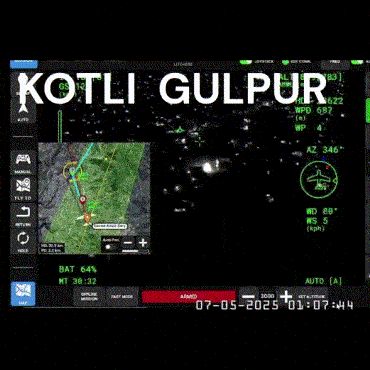চৈতন্যদেব তখন পাকাপাকি ভাবে পুরীর বাসিন্দা। আমাদের হালিশহরের শিবানন্দ সেন এক দল মানুষকে নিয়ে রথের আগে আগে প্রতি বছর পুরী যান— ‘শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান’। আজকের ভাষায় গাইড, সে আমলে বোধহয় ছড়িদার গোছের কিছু একটা বলা হত শিবানন্দ সেনমশাইকে। পার্থক্য শুধু এই যে, তিনি নিজের দায়িত্বে এবং ব্যয়ে পুরীযাত্রী সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। শুধু পথ দেখানো নয়, পথে এত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্থানীয় শাসকের বা রাজকর্মচারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা— সমস্তই তাঁর দায়িত্ব। কে নেই সেই যাত্রীদলে! নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভুর মতো ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে শ্রীধরের মতো মানুষ, খোলাবেচা যাঁর বৃত্তি। এক বিচিত্র মানব-দলের মিছিল। এমনকি সকলে শিবানন্দের পূর্বপরিচিতও নন। সেই সঙ্গে মহিলারা রয়েছেন, যেমন শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরনি মালিনী দেবী বা অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী। বাচ্চাকাচ্চাও রয়েছে, আমাদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, এই দলে হয়তো আছেন শিবানন্দ সেনের পত্নীর কোলে বালকবয়সের পরমানন্দ সেন। যিনি পরবর্তী কালের বিখ্যাত কবি এবং নাট্যকার, ‘কবিকর্ণপূর’ নামে যিনি সবিশেষ প্রসিদ্ধ হবেন। যাত্রীদলের উদ্দেশ্য রথ দেখা এবং কলা বেচা। অর্থাৎ রথারূঢ় জগন্নাথদেবের দর্শন, সেই সঙ্গে চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ। বর্ষার কয়েক মাস পুরীতে কাটিয়ে তাঁরা ফের সদলবলে গৌড়ে ফিরে আসতেন। অবশ্য দু’চার জন লোক ফি-বছরই ছিটকে যেতেন। মহাপ্রভুকে ছেড়ে তাঁদের আর ঘরে ফেরা হত না!
এমন যাত্রার বিবরণ চৈতন্য জীবনীসাহিত্যে প্রায় সকলেই দিয়েছেন। চৈতন্যলীলার আদিব্যাস যাঁকে বলা হয়, সেই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর থেকে শুরু করে তাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ অবধি বিভিন্ন লোকের রচনায় রথযাত্রা উপলক্ষে ‘গৌড়িয়া’দের শ্রীক্ষেত্র পর্যটনের বৃত্তান্ত ফিরে ফিরে আসে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, শুধু গৌড়িয়াদের পুরী যাওয়া নয়— বিচিত্র মানুষের বিচিত্র সব ভ্রমণকাহিনি এই চরিতগুলির অনেকটা জুড়ে আছে। আজ আমরা যাকে ‘মাইগ্রেশন’ বলি, তা তো শুধু আজকের বাস্তবতা নয়, আদ্যিকাল থেকেই মানুষের ইতিহাস যেন নিরন্তর ঘটে চলা যাতায়াতের আখ্যানমালা। শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে এই বাৎসরিক যাতায়াতের বিবরণে এমনই সব আখ্যান ঝিকমিক করে। কিন্তু আজ ঠিক সে প্রসঙ্গ নয়, আমাদের দৃষ্টি আজ শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের লেখা একটি নাটকের দিকে। যাত্রার আখ্যান আসবে খানিক, কারণ সেই আশ্চর্য নাটকও যাতায়াতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। নাটকটির নাম ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’। নাম থেকেই খানিকটা আঁচ করা যায় যে, কৃষ্ণমিশ্রের বিখ্যাত নাটক ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’-এর প্রেরণা কবিকর্ণপূরের রচনায় কাজ করেছে। নাটকের ভিতরের কাঠামো আর বিষয়বস্তু থেকে সেই ভাবনা আরও দৃঢ় হয়, একটু পরে সে প্রসঙ্গ আসবে। আপাতত যা বলার, সমস্ত প্রভাব সত্ত্বেও ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। এবং পরমানন্দ সেন নিজেও এই নাটকের অন্যতম চরিত্র।
শিবানন্দ সেনের ‘ঘাটি সমাধান’ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে গৌরাঙ্গের অনুগত এবং অন্তরঙ্গ জন। ফলে চৈতন্যদেবের আদেশে যখন যাত্রীদলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দায় তাঁর ওপর পড়ল, ফি-বছর সে দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। একটা সুবিধে হয়েছিল, ওড়িশার পথঘাট চেনা ছিল তাঁর। শিবানন্দের বাড়ি ছিল কুমারহট্ট-কাঞ্চনপল্লিতে। অর্থাৎ আজকের হালিশহর-কাঁচরাপাড়ায়। অঞ্চলটি অনেক দিন ধরেই বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র, কাছেই চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর জন্মভিটে। শিবানন্দের দীক্ষাগুরু শ্রীনাথ চক্রবর্তীও গৌরগত প্রাণ ছিলেন, সে কথা স্পষ্ট হয় শ্রীনাথের লেখা ভাগবত পুরাণের টীকাগ্রন্থটির নাম থেকেই— ‘শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা’। শিবানন্দের যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছিল, সে কালের রীতি অনুযায়ী গুরু শ্রীনাথ চক্রবর্তীকেই তা সমর্পণ করেছিলেন। আজকের কল্যাণী পুরসভা এলাকায় যে কৃষ্ণরায় বা কৃষ্ণরাই মন্দির, সেখানেই এই বিগ্রহ বর্তমান। শ্রীনাথের দৌহিত্র বংশ তাঁর সেবায়েত। মন্দির অবশ্য অনেক পরবর্তী কালে তৈরি। যে কথা বলার জন্য এ সব তথ্যের আমদানি, চৈতন্যপন্থার যে গোড়ার দিকের সামাজিক বা সাংগঠনিক ভিত্তিভূমি, তাতে শিবানন্দ সেনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শুধু ধনী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁকে দেখলে ভুল হবে। তা তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু সেই সঙ্গে মতাদর্শগত ভূমিকাও তাঁর ছিল। শিবানন্দ নিজে এক জন পদকর্তা মহাজন। অন্তত ছ’টি পদ তাঁর ভণিতায় প্রচলিত। তার মধ্যে জগাই-মাধাই উদ্ধারের পদটির ডকুমেন্টেশেনের জন্যই কোনও বিকল্প নেই— ‘অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর’। তিনি সত্যিই ‘রসিক মরমিজন’ ছিলেন। গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ বিষয়ে লিখছেন— ‘গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥ রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥’ চরিতামৃত থেকে বৈষ্ণব বন্দনা পর্যন্ত শিবানন্দের প্রশস্তিতে মুখর।
এহেন পিতার পুত্র পরমানন্দ। তাঁর জন্ম নিয়েও অলৌকিক আখ্যান আছে। চরিতামৃতে তার কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই। তবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দু’দফায় বালক পরমানন্দের অন্তত তিনটি সাক্ষাতের যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়েছেন, তা আমাদের জন্য দরকারি। একটি সাক্ষাতে পরমানন্দ নিতান্ত শিশু, সে চৈতন্যদেবের পায়ের আঙুল চোষে। এবং এই ঘটনায় চরিতকার শিশুর মধ্যে মহাপ্রভু কর্তৃক অলৌকিক ভাবে কাব্যশক্তির সঞ্চারের ইঙ্গিত দেখেন। দ্বিতীয় সাক্ষাতে মহাপ্রভু বালক পরমানন্দকে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলতে বললে সে চুপ করে থাকে। কিছুতেই কিছু বলছে না দেখে মহাপ্রভু রসিকতা করেন যে, “আমি সারা দুনিয়ার স্থাবর জঙ্গম সবাইকে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা করে ফেললাম, কেবল এই বালকের কাছে আমায় হার মানতে হল!” তখন স্বরূপ দামোদর বলেন যে, “বালক নিশ্চয় কৃষ্ণনামকে মনে মনে জপ করছে।” ইঙ্গিত স্পষ্ট, প্রকারান্তরে মহাপ্রভু পরমানন্দের দীক্ষাগুরু হয়ে গেলেন! যা অভাবনীয়, কারণ মহাপ্রভু কাউকে দীক্ষা দেননি বলেই সাধারণত মনে করা হয়। তৃতীয় সাক্ষাৎ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। মহাপ্রভু বালককে বলছেন, ‘পড়ো’। আর অবিশ্বাস্য শুনতে লাগলেও সাত বছরের পরমানন্দ মুখে মুখে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলে দেয়। কৃষ্ণদাস অবশ্য শ্লোকটি উদ্ধৃত করছেন পরমানন্দের লেখা ‘আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ’ বই থেকে। কিন্তু সে যা-ই হোক, এমন অপূর্ব শ্লোক শুনে স্বয়ং মহাপ্রভুই নাকি তাঁকে ‘কবিকর্ণপূর’ উপাধিটি দিয়েছিলেন। এ সব জনশ্রুতি থেকেই মালুম হয় যে, কবিকর্ণপূর মোটেই হেলাফেলার লোক নন। আর চৈতন্য-কৃপাধন্য কবির চৈতন্যচরিত বাড়তি মনোযোগ দাবি করে।
এর পূর্ববর্তী সংস্কৃতে লেখা একমাত্র চৈতন্যচরিত হল মুরারি গুপ্তের কড়চা। মুরারি চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে বড় হলেও একই পাঠশালায় পড়তেন। ফলে তাঁর লেখার প্রামাণিকতা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষ করে বাল্যলীলার ক্ষেত্রে তাঁর কড়চার উপরেই সকলে নির্ভর করেছেন। আর একটি কড়চা স্বরূপ দামোদরের, কিন্তু চরিতামৃতের উদ্ধৃতি ছাড়া তার আর কোনও হদিস নেই। সুতরাং পরমানন্দের নাটক থেকে পরবর্তী চরিতকারেরা সকলেই তথ্য, ঘটনা, শ্লোক, উপমা, বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু হয়তো সংস্কৃত ভাষায় লেখা বলেই এই বইটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রসার খুব বেশি হয়নি। এবং এ ঘটনা আজকের নয়। এশিয়াটিক সোসাইটি যখন প্রথম বইটি প্রকাশ করে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে, সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখছেন যে, পাণ্ডুলিপি তৈরি করবার জন্য তিনি মাত্র তিনটে পুঁথি জোগাড় করে উঠতে পেরেছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।
‘চৈতন্যভাগবত’ এবং ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ পুঁথি যে কী বিপুল সংখ্যায় বাংলায় পাওয়া যায়, এ বিষয়ে যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন। সেই তুলনায় ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’-এর পুঁথির স্বল্পতায় একটু অবাকই হতে হয়। যদি ১৪৯৪ শক অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের আশপাশে বইটি লেখা হয়েছে এ কথা মেনে নেওয়া যায়, তা হলে বলতে হয় যে, এই বই চৈতন্যদেবের প্রয়াণকাল থেকে খুব বেশি দূরে দাঁড়িয়ে নেই। পরমানন্দকে পরবর্তী পদকর্তা ‘চৈতন্যের বরপুত্র’ পর্যন্ত বলেছেন। অথচ তাঁর নাটকের প্রচার তেমন করে হচ্ছে না। তাঁর অন্য একটি বই ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ অবশ্য কিঞ্চিৎ বেশি চর্চিত, কারণ সম্প্রদায়গত ভাবে চৈতন্যপন্থীদের স্বীকৃতির জন্য এই বইটির বিকল্প নেই। নাটকটি কিন্তু ঘরে ঘরে পাঠ্য হয়ে ওঠেনি। পুঁথির বেশি প্রতিলিপি না হওয়াটা অন্তত সে রকমই ইঙ্গিত করে। সসম্ভ্রমে নাটকের উল্লেখ যদিও সকলেই করছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যিনি তথ্য আহরণ এবং ঋণস্বীকার করা নিয়ে খুবই নিষ্ঠাবান, তিনি লিখেছেন, “শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর। ইঁহার মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥” লক্ষণীয়, ‘ইঁহা’ মানে এখানে রূপ গোস্বামী, যিনি কৃষ্ণদাসের মতোই বৃন্দাবনে থাকতেন। অথচ তাঁর বিষয়ে তথ্য পরমানন্দের নাটক থেকে গ্রহণ করছেন কৃষ্ণদাস! এবং এ রকম আরও অনেক প্রসঙ্গে ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করছেন। ফলে মান্যতার সমস্যা এই নাটকের নেই। তা সত্ত্বেও, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের লেখালিখির মতো ছড়িয়ে পড়তে এই নাটককে দেখি না।
এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা তত্ত্ব চালু আছে। অনেকে চৈতন্য-অনুসারীদের শাস্ত্রচর্চার ভরকেন্দ্র বৃন্দাবনে সরে যাওয়ার সঙ্গে জুড়ে এই ঘটনাটিকে দেখতে চান। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, বৃন্দাবন ও বাংলার চৈতন্যপন্থীদের মধ্যে একটি ফারাক লক্ষ করা যায়। বৃন্দাবনের তাত্ত্বিকরা যেখানে মহাপ্রভুকে অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেও তাঁকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ‘উপায়’ হিসেবে তুলে ধরেছেন, সেখানে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং শিবানন্দ সেন প্রমুখের কাছে মহাপ্রভুই ‘উপেয়’ হিসেবে গণ্য। সেই জন্যে গৌরনাগরী বা গৌরপারম্যবাদীদের কাছে কৃষ্ণ পূর্ণ হলে গৌর ‘পূর্ণতম’ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে নানা রকম কারণ ও সংযোগসূত্রে বৃন্দাবনের সিদ্ধান্ত গৌড়মণ্ডলে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কবিকর্ণপূরের জনপ্রিয়তায় কিঞ্চিৎ ভাটা পড়ে। বিমানবিহারী এর মধ্যে প্রায় এক ধরনের ষড়যন্ত্রের গন্ধ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ভাষায়, “...শ্রীচৈতন্যের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম স্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রাচীনতম চরিতাখ্যায়ক কবিকর্ণপূর ও মুরারি গুপ্তের গ্রন্থগুলি চাপা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।” তবে বলে রাখা ভাল যে, এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আকর্ষণীয় মনে হলেও তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো অনেক পণ্ডিতই এ কথা মানেন না। এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক পেশ করাই যায়, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাণ বিচারের সেই গভীর অরণ্যে আপাতত আমরা প্রবেশ করব না, কারণ তা বিপদসঙ্কুল এবং সেখান থেকে বেরোনো কিঞ্চিৎ মুশকিল। এই সব জটিল জল্পনায় না গিয়ে বরং ভেবে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদি বঙ্গভাষায় ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ না লিখতেন, আর তার মধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সংস্কৃত লেখালিখির সারাৎসার তর্জমা না করতেন, তা হলে গোস্বামী সিদ্ধান্ত কি এত দ্রুত সাধারণ্যে প্রচার পেত? বলে রাখা যাক যে, কবিকর্ণপূরের নাটকের প্রথম বাংলা তর্জমা করছেন প্রেমদাস। পয়ারে করা সেই অনুবাদের নাম ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী’। মোটামুটি ভাবে ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের আশপাশে সেই অনুবাদ হয়েছে। এবং তত দিনে চৈতন্যপ্রপত্তির মহাগ্রন্থ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচনার পর শতক অতিক্রান্ত। ফল, সহজেই অনুমেয়।
প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারতের অন্য সব সম্প্রদায়ের মতোই, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদেরও কোনও কালেই কোনও রকম কেন্দ্রিকতা ছিল না। এমনকি স্বয়ং চৈতন্যের জীবদ্দশায়ও তাঁর পার্ষদ এবং অনুগামীরা বহু বিচিত্র মত ও পথের চর্চা করতেন। পরবর্তী কালে সেই ভাবান্দোলন আরও বিকেন্দ্রিত হয়েছে। কখনওসখনও কেউ কেউ এই সব বিচিত্র পথকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে কেন্দ্রীয় কোনও প্রতিষ্ঠান সে রকম ভাবে কখনওই গড়ে ওঠেনি। খুবই স্থানিক, স্বতন্ত্র সব বিশ্বাসের ধারাকে কে-ই বা নিয়ন্ত্রণ করবে? আর কী ভাবেই বা করবে? ফলে বৃহত্তর পরিসরে সেন্সরশিপ কাজই করবে না। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আরও দু’টি কারণে ধোপে টিকবে না। কারণ পরমানন্দকে ‘চাপা দেওয়া’ যদি এতই প্রয়োজন হত, তা হলে রূপ গোস্বামী তাঁর ‘পদ্যাবলী’ সঙ্কলনে কবিকর্ণপূরের শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে সম্মান জানাতেন না। আর দ্বিতীয়ত, পরমানন্দের বাংলায় রচিত পদাবলি এত জনপ্রিয় হত না। ‘পরশমণির সাথে, কি দিব তুলনা রে, পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা। আমার গৌরাঙ্গের গুণে, নাচিয়া গাহিয়া রে, রতন হইল কত জনা॥’ এই রকম সরল বাংলায় লেখা পদ বা ব্রজবুলি পদে তিনি আশ্চর্য অনায়াস। এবং মান্য পদসঙ্কলনে যেমন, কীর্তনেও তেমন, তাঁর কয়েকটি পদ অপরিহার্য। বস্তুত ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকেও এই কাব্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।
নাটক বলেই অন্যান্য চরিতগ্রন্থের তুলনায় এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এটি দশ অঙ্কের নাটক। প্রচুর চরিত্র। ঘটনারও কমতি নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে, এই নাটকে রথযাত্রা প্রসঙ্গটি বার বার ফিরে আসে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে রচনা, ফলে আসতেই পারে। কিন্তু রথযাত্রা এখানে শুধু মাত্র একটি ‘ইভেন্ট’ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। প্রথমত, নাটকের প্রস্তাবনাই হচ্ছে রথযাত্রা উপলক্ষে। সংস্কৃত নাটকের প্রথা অনুসারে— নান্দী অন্তে সূত্রধারের প্রবেশ হয়। সূত্রধার সাধারণত পারিপার্শ্বিক বা নটীর সঙ্গে কথোপকথনে নাটকটির প্রস্তাবনা করেন। যে নাটকটি অভিনয় হবে, তার সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এই দুনিয়া থেকে নাটকের দুনিয়ায় দর্শকদের প্রবেশ করতে সাহায্য করেন।
কবিকর্ণপূরের নাটকের প্রস্তাবনা হচ্ছে রথযাত্রায় সমাগত ভক্তদের কথোপকথনে। চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটেছে। সুতরাং বিধিবিধান অনুসারে রথযাত্রা হচ্ছে বটে, কিন্তু কারও প্রাণে আনন্দ নেই। ভক্তেরা বিরহে অধীর। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সোনার ঝাড়ু নিয়ে পথ পরিষ্কার করছেন, কিন্তু মন তাঁর বিমুখ হয়ে আছে। তিনি পরমানন্দকে ডেকে নিভৃতে বলছেন, “দেখুন, সেই নীলগিরির অধীশ্বর জগন্নাথ আছেন, সেই রথযাত্রা আছে, বৈভব আছে, সেই গুণ্ডিচামন্দির, দিগ্বিদিক থেকে আগত দর্শনার্থী ভক্তকুল, সেই বাদ্য, সেই আরতি, সেই নন্দনবনকে হার মানাতে পারে এমন সব উপবন আছে, সবই আগের মতোই রয়েছে, শুধু মহাপ্রভু নেই বলে আমার মনে হচ্ছে যেন কিছুতেই আর কিছু নেই! মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে।” এই অংশে রথযাত্রায় কোনও এক বার মহাপ্রভুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত শীল ভট্টারিকার যঃ কৌমারহরঃ কবিতাটির প্রতিধ্বনি যদি কেউ শুনতে পান, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কবিতার ‘ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি’ শুধু সাহিত্য নয়, আমাদের ইতিহাসকেও সংক্রমিত করে থাকে এমন। যাই হোক, প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের মহিমা অনেক বললেন, চৈতন্যবিরহে নিজের ব্যাকুলতার কথাও বললেন। এবং সেই বিরহজ্বালা মেটানোর উপায় হিসেবে চৈতন্যের লীলাকথা নিয়ে পরমানন্দকে একটি নাটক রচনার দায়িত্ব দিলেন। পরমানন্দ বলছেন যে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করার জন্য চৈতন্য চন্দ্রের উদয়। বিশেষ করে লক্ষ করতে হয় যে, সেই চাঁদ উদয়ের ঘটনাটি ঘটছে রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে। তার উপর প্রতাপরুদ্রদেব নিজে এই নাটকের অন্যতম চরিত্রও বটে।

উৎসব: জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ ঘিরে লোকারণ্য পুরীর রাজপথ।
নাটক শুরু হয়ে গেল। সূত্রধার আর পারিপার্শ্বিকের কথাবার্তায় এর পর আমরা গৌরাঙ্গ আর তাঁর পার্ষদ-ভক্তদের পরিচয়ও পেয়ে গেলাম। আর যা পেলাম তা হল চৈতন্যের অবতারত্বের প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ, স্বয়ং ভগবান। আর সঙ্কীর্তনই এই কলিযুগে তাঁর ভক্তিযোগ প্রকাশের প্রধান পথ। নিজের নিন্দা শুনে আর থাকতে না পেরে মঞ্চে প্রবেশ করে কলি। তার সঙ্গে আসে অধর্ম। এখানেই কবিকর্ণপূরের বৈশিষ্ট্য। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি, একেবারে একই সমতলে বিমূর্ত সব ধারণাকে নিয়ে আসেন মূর্তিমন্ত রূপে। এই ভাবেই অদ্বৈত, গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীবাস, শচীদেবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মঞ্চে আসে ভক্তি, বৈরাগ্য, বিবেক, মৈত্রী, প্রেমভক্তি ইত্যাদি চরিত্র। এর আগে উল্লিখিত ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকে এই ‘ট্রোপ’টির ব্যবহার ছিল, সেখানে বিবেক আর মহামোহ এই দুই রাজার যুদ্ধের প্রতীকে কাশীতে অদ্বৈতবেদান্ত এবং বৈষ্ণবধর্মের টানাপড়েন দৃশ্যায়িত হয়েছে। তার আগে ‘ভাগবত-মাহাত্ম্য’-এও ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য এদের ‘পার্সনিফিকেশন’ দেখা গেছে। নারদের সঙ্গে কথোপকথনে সেখানে ভক্তি বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক সূত্রায়ন করা হয়েছে। কিন্তু পরমানন্দের অভিনবত্ব— মতাদর্শগত ধারণা আর মানবচরিত্রকে এক সঙ্গে ব্যবহার করায়। যে চরিত্রগুলির অনেককে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর সম্ভাব্য দর্শক-পাঠকদের মধ্যে এখনও যে সব চরিত্রের স্মৃতি সজীব, তাঁদের অন্য ভাবে দেখাবার এ এক জবরদস্ত টেকনিক। পরমানন্দ নিজে বা চৈতন্যের পার্ষদেরা চরিত্র হিসেবে চৈতন্যের রূপ-গুণ-দিব্যভাবের কথা বলছেন, অলৌকিক নানা ঘটনা বর্ণনা করছেন সে এক রকম। কিন্তু ভক্তিদেবী বা কলি রীতিমতো চরিত্র হিসাবে এসে চৈতন্যের প্রশস্তি করলে তা বক্তব্যকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। বলা যেতে পারে যে, এই প্রতীকধর্মিতার ফলে ঘটনাবলি এবং সেই সব ঘটনার লৌকিক বা অলৌকিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার কাজটা সমান্তরালে চলতে থাকে। কবিকর্ণপূরের নাটকে আসলে দৃশ্যকাব্যকে ব্যবহার করে তত্ত্বায়নের একটি প্রচেষ্টা দেখা যায়। চৈতন্যপন্থার তত্ত্বায়নে যা যা জরুরি— যেমন রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের কথোপকথন, কিংবা রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান— ইত্যাদি সমস্ত প্রসঙ্গই কিন্তু কবিকর্ণপূর তাঁর নাটকে রেখেছেন। এই উপাদানগুলিই পরে কৃষ্ণদাসের হাতে আরও পরিণত রূপ নেবে।
প্রয়োগনৈপুণ্যের এ রকম আর একটি দৃষ্টান্ত হল, তৃতীয় অঙ্কে নাটকের ভিতর আর একটি নাটক। বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের দানলীলা অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তারই দৃশ্যরূপ এখানে পরিবেশিত হয়। এবং তা হয় নাটকের সমস্ত নিয়ম মেনে। আবার সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক আসে, আবার প্রস্তাবনা হয়। সেই নাটকের দর্শক মঞ্চে হাজির থাকে। রাধা কৃষ্ণ দূতী সকলেই রীতিমতো অভিনয় করে। দানলীলা এগোয়। একটি ‘ক্লাইম্যাকটিক’ মুহূর্তে জরতীকে সরিয়ে দিয়ে নিত্যানন্দ তার জায়গা নেন। ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এত ক্ষণ জরতী নিতাইয়ের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে অভিনয়ের কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট একটি জিনিস, কিন্তু দুর্দান্ত ব্যবহার। নাটকের ভিতরের নাটকে যদি আবেশ হয়, তা হলে ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকেই বা আবেশ হতে বাধা কোথায়? ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকটি জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসবে অভিনীতও হয়েছে। তা হলে প্রস্তাবনায় যেমন বলা হয়েছিল, গৌরাঙ্গের অভিনয় দেখে বিরহজ্বালার উপশম ব্যাপারটিও সম্ভাব্য হয়ে ওঠে।
শেষ যে প্রসঙ্গটি বলা দরকার, এই নাটক সময়ের ও স্থানের অনুক্রম কী ভাবে ভেঙে দেয়। নাটকটি শুরু হয়েছিল রথে। শেষও হয় রথের পর হোরাপঞ্চমী উপলক্ষে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ভক্তদের কথোপকথনে। পুরীতে শুরু এবং শেষ। কিন্তু এর মধ্যে চৈতন্যচরিতের প্রায় সমস্ত প্রধান ঘটনা বর্ণিত বা দৃশ্যায়িত হয়। স্থান নবদ্বীপকেন্দ্রিক গৌড়মণ্ডল, দাক্ষিণাত্য, মথুরা-বৃন্দাবন এবং পুরী। ভক্তদের বিরহ দিয়ে শুরু, ভক্তমিলন ও বরদানে শেষ। প্রতাপরুদ্রও সেখানে উপস্থিত। ক্রমের এই রকম পরিবর্তন তো অন্য চরিতগ্রন্থেও কমবেশি হয়। এখানে বৈশিষ্ট্য কী? ঘটনার এবং বর্ণনার সচেতন ও পরিকল্পিত বিন্যাস। নাটক বলেই দৃশ্যকাব্যের নিজস্ব নিয়মে সেই পুনর্বিন্যাস গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সিনেমায় যেমন ফ্ল্যাশব্যাক। ফলে নায়কের মহানতা এবং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার কাজটি অনেক সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়।
খেয়াল করলে দেখা যায়, কতগুলি বিষয় এবং অনুভূতি কী কুশলতার সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হয়। অপ্রকটের পর সমবেত ভক্তদের যে বিরহব্যাকুলতা থেকে সূত্রধার শুরু করেছিলেন, নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শ্রীবাসঙ্গনে কীর্তন— কৃষ্ণলীলায় মহারাসের প্রতিসাম্যে যা গঠিত— সেখান থেকে সন্ন্যাসের জন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান এবং তার ফলে ভক্তদের শোকোচ্ছ্বাসে সেই বিরহেরই অনুরণন। আবার প্রতাপরুদ্রের যে ব্যক্তিগত বিরহ থেকে নাটকের উৎপত্তি, তা ফিরে আসে অষ্টম অঙ্কে। মহাপ্রভু রাজা বা বিষয়ীর দর্শন পাপ বলে মনে করেন, এ দিকে প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভুর দর্শন লাভের আশায় বার বার কাকুতি-মিনতি করেন। রাজার মনোকষ্টে যেন সেই প্রস্তাবনা দৃশ্যের পুনরাভিনয়। যে-হেতু দাক্ষিণাত্য, গৌড় আর মথুরামণ্ডলে পরিব্রাজন আছে, আর নবদ্বীপ থেকে সন্ন্যাসযাত্রা আছে, ফলে নানা রকম বিরহের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসে। ভক্তেরা কাঁদেন— ‘হা প্রাণনাথ ক্কাসি ক্কাসি’। কোথায় কোথায় তুমি? বিরহ বর্ণনায় পরমানন্দ অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি অদ্ভুত দক্ষতায় প্রতিটি বিরহের পর একটি মিলন, সংক্ষিপ্ত হলেও, ঘটিয়ে তোলেন। ঘটনার সুচিন্তিত বিন্যাস ছাড়া এ সম্ভব হত না। আর চূড়ান্ত যে বিরহ, মহাপ্রভুর তিরোধান, সেই বিন্দু থেকেই নাটক শুরু হওয়ার ফলে শেষটা মিলন দিয়েই হচ্ছে। তা রসশাস্ত্রসম্মত এবং বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অনুসারী। ভুলে গেলে চলবে না, কবিকর্ণপূর কিন্তু ‘অলঙ্কারকৌস্তুভ’ নামে বইটিরও রচয়িতা। ফলে নাটকের ভিতরকার কৃৎকৌশল তিনি যথেষ্ট জানেন। জানেন বলেই এই রকম একখানি নাটক লিখে উঠতে পারছেন, যার পরিক্রমা রথযাত্রা, আর আরও কত রকমের যাত্রার পথে। যে দৃশ্যকাব্যের ভেতর সমন্বিত হয়ে যাচ্ছে সম্প্রদায়গত বিশ্বাস আর দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এক জায়গায় কর্ণপূর উপমা দিয়েছেন যে, গৌরাঙ্গ যেন একটি গাছ, তার ডালে রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন পাখিদু’টি বাসা বেঁধে আছে। ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক সম্পর্কেও উপমাটি একটু পাল্টে ব্যবহার করা যায়— এই নাট্যবৃক্ষে চরিত-ইতিহাস আর তত্ত্ব-রস যুগলে বসেছে।
তথ্যসূত্র: নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন: তারাপদ মুখোপাধ্যায়; চৈতন্যচরিতের উপাদান: বিমানবিহারী মজুমদার; গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান: হরিদাস দাস
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)