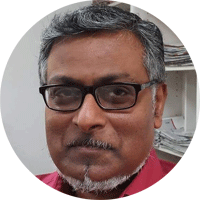সেই সেকালে হুতোম মন্তব্য করেছিলেন, “শুনেছি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ খেতে দোষ কী ? আর বষ্টমদের মদ খেতেও বিধি আছে, দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কেষ্ট বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।” কাজেই হুতোমের আমলে মোসাহেব, গাইয়ে-বাজিয়ে আর বাইজিতে মাতোয়ারা বাবুদের বৈঠকখানায় থাকত মদ ও মাংসের এলাহি আয়োজন।
আর একালের কলকেতায় দোলের আগের দিন অলিতে গলিতে মদের দোকানগুলির সামনে যে বিরাট লাইন পড়ে, অতীতের খাদ্যসঙ্কটের সময় কোনও রেশন দোকানের সামনেও তত বড় লাইন দেখা গেছে কি না সন্দেহ। উৎসবে-ব্যসনে খাবারদাবার নিয়ে বাঙালি ছুতমার্গ দেখায়নি। বরং নবরাত্রিতে সবার উপরে ঢালাও নিরামিষ খাবার চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। নবরাত্রির সময় উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় একটানা ন'দিন ধরে মাছ-মাংস-ডিমের দোকান বন্ধ থাকে।
সেই ধারা এ বার এখানেও! তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সম্ভবত এ বারই প্রথম নবদ্বীপে দোলযাত্রা উপলক্ষে তিন দিন ধরে মাছ-মাংসের দোকান বন্ধ রাখা হচ্ছে। আমিষ খাবার ও মাছ-মাংসের দোকান বন্ধ থাকলেও দোলের দিন আধ বেলা ছাড়া অন্য দিন মদের দোকানও বন্ধ থাকবে কি না তার কোনও খবর অবশ্য নেই। নবদ্বীপ পুরসভার পুর প্রতিনিধিরা প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোল উৎসবের তিন দিন নাগরিকদের নিরামিষ খাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। দোলের দিন রং মেখে ভূত হয়ে ফাগুনের এই আগুন-ঝরা গরমে অবেলায় স্নান করে অনেকেরই যেমন পাতলা মাংসের ঝোল-ভাত না হলে চলে না, অনেক বাড়িতেই তেমনই দোলপূর্ণিমায় নিরামিষ আহার। কিন্তু সে তো যার যার পারিবারিক রীতি। সেখানে পুরসভা বা প্রশাসনের ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবেই অন্যতর রাজনৈতিক বার্তা বয়ে আনে।
শারদোৎসবে ইদানীং তো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা চলছেই। এ বারে দোলের দু'দিন আগে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে উদ্যাপিত হল ‘দোলযাত্রা ও হোলির মিলন উৎসব’। দুঃখ এটাই, যা ছিল আমাদের চিরাচরিত সামাজিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক অঙ্গ, আজ তাকেই সম্প্রীতির সিলমোহর লাগিয়ে বাজারে হাজির করতে হচ্ছে। সকলেরই জানা যে, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ যাত্রাপালায় নিজেই কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। মোগল আমলে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের দরবারে গোলাপের পাপড়ির আবির দিয়ে মহা সমারোহে পালিত হত হোলি যার পরিচিতি ছিল নানা নামে— মেহ্ফিল-এ-হোলি, ইদ-এ-গুলাবি বা আব-এ-পাশি। আমির খুসরো, নিজামুদ্দিন আউলিয়া কিংবা বাবা বুল্লে শাহের মতো সুফি কবিদের লেখায় রয়েছে হোলির প্রশস্তি। আর আজও বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারি মন্দিরে কৃষ্ণের পোশাক পরম যত্নে তৈরি করে দেন মুসলিম ওস্তাগরেরা।
তবে হুতোম যে ছবিটি দিয়েছেন, তা হল সেকালের শহর কলকাতার খণ্ডিত অংশের বাবু কালচারের চেহারা। সমগ্র সমাজের চিত্রটি মোটেও সে রকম ছিল না। দুর্গোৎসবের পাশাপাশি আমাদের এই বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাই আবহমান কাল ধরে জনপ্রিয় উৎসব। কৃষ্ণ ছিলেন শ্যামবর্ণ আর রাধারানি গৌরবর্ণা। রাধারানি ও তাঁর সখীরা এই নিয়ে কৃষ্ণকে খেপাতেন। একদিন কৃষ্ণ সেই কথা গিয়ে জানালেন মা যশোদাকে। তখন তিনি বললেন, রাধারানিকে রং মাখিয়ে দিলে তার চেহারাও সেই রঙের হয়ে যাবে।
কথিত আছে, সেই থেকেই ব্রজধামে শুরু হয়েছিল রঙের উৎসব। রাধারানির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই হোলি খেলা স্বর্গীয় প্রেমের এক চিরনবীন লোককথায় যেমন রূপান্তরিত হল, তেমনই হোলিও হয়ে উঠেছে প্রেম ও সখ্যের চিরন্তন প্রতীক। ফাগে-গুলালে-আবিরে-কুঙ্কুমে রঞ্জিত এই হোলি পুরোপুরি কৃষ্ণলীলারই অঙ্গ। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে, মন্দির স্থাপত্যে, ভক্তিগীতিতে, কীর্তনে কিংবা পল্লিগীতিতে অথবা চিত্রকলায় রাধাকৃষ্ণের হোলিখেলা যেন এক আকর্ষণীয় সম্পদ। আবার বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা শ্রীচৈতন্যের জন্ম দোলপূর্ণিমায়। বৃন্দাবনের হোলি দেখে এসে মহাপ্রভু বঙ্গদেশে দোল উৎসবের প্রবর্তন করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব পালনও মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এইবাংলায়। তাই দোল উৎসবকে ঘিরে এক সময় ছিল মানুষের অন্তরের ভক্তি, আবেগ ও ভালবাসা।
অর্থহীন হুল্লোড়ের মানসিকতায় কলুষিত ছিল না সেই আন্তরিক ভাব। এই বসন্তোৎসব মূলত আর্যদের উৎসব। মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসা আর্যরা শীত চলে যাওয়ার সময় যে আনন্দোৎসবে শামিল হত, তাতে শীতের প্রতিনিধিত্ব করত একটা ভেড়া। তার পিঠে বসে থাকত ভেড়ার লোম থেকে তৈরি কম্বলে জড়ানো বুড়ি। পূর্ণিমার আগের রাতে সে যুগের আর্যরা শীতের প্রতীক ওই বুড়িকে আগুনে পুড়িয়ে দিত। পরের দিন থেকে শুরু হত বসন্তোৎসব। রাজা শালিবাহনের দিনপঞ্জি মতে, আগে ফাল্গুন ছিল বছরের শেষ মাস। এক দিকে পুরনো মালিন্যকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে আবাহনের প্রস্তুতি, আবার খেত থেকে শীতের শস্য ঘরে তোলার আনন্দ। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রকৃত আবহ। অশুভের গ্লানি ও মালিন্য থেকে মুক্তির জন্য শরণ নেওয়া হয় সর্বশুদ্ধিকারী অগ্নির।
রঙের মাতনে মেতে ওঠার আগে পালিত হয় প্রতীকী বসন্ত উৎসব। হোলির এই দাহ উৎসব দক্ষিণ ভারতে ‘কামদহনম’ বা ‘কামাহন’ নামে জনপ্রিয়। স্থানভেদে এর নানা রূপান্তর। আমাদের বাংলায় খড়-বিচালি, তালপাতা দিয়ে তৈরি ‘বুড়ির ঘরে’র মধ্যে পিটুলির ভেড়া বানিয়ে রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর নাম ‘চাঁচর’ বা চলতি কথায় ‘মেড়া পোড়া’।বহু দিন পর্যন্ত সেখানে জ্যান্ত ভেড়াকে আগুনে পোড়ানো হত। ওড়িশায় আবার এর নাম ‘মেন্টা পোড়েই’। শোনা যায় জগন্নাথ মন্দিরের পাশে দোলমঞ্চে নাকি এখনও একটি ভেড়ার গায়ে একটু আগুন ছুঁইয়ে নেওয়া হয়। হোলিকা দহন উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই উত্তর ভারতে বিশেষত উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাবে হোলির রমরমা।
এই উৎসবের সময় চাঁদ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে থাকে বলে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এই উৎসবকে লোকেরা বলে ‘ফাগুয়া’। আমাদের বাংলায় কিন্তু এই উৎসবের ধারাটা কিছুটা অন্য রকম। ফাল্গুনে নয়, বসন্তের আগমন এখানে মাঘেই। এক মাস আগের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথিতে শীতের শেষ আর সরস্বতী পুজোর দিন শ্রীপঞ্চমীতে বসন্ত ঋতুর সূচনা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি লিখেছেন, কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সে দিন সূর্যরূপ কৃষ্ণ বিশাখা অর্থাৎ রাধানক্ষত্রে থাকেন। ইনি ব্রজের কৃষ্ণ। শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ণ। সে দিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন অর্থাৎ দোলন।তেমনই মাঘী পূর্ণিমায় সূর্যের উত্তরায়ণ। সে দিন কৃষ্ণের দোলযাত্রা হওয়ারকথা। কিন্তু ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দোল কী কারণে হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি।
দোল উৎসব উপলক্ষে নাগরিক সংস্কৃতির যে খণ্ডচিত্র হুতোম দেখিয়েছেন, তার বিপ্রতীপে গ্রামবাংলার এক সজল কোমল উৎসবের মনোরম বিবরণ মেলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখায়। যে গ্রামের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। মাঠে রবিশস্যে সোনালি রং ধরেছে, ছোলার খেতে ছোলা পেকে উঠেছে, কোথাও বিস্তীর্ণ অড়হরের খেত। কোথাও খেত থেকে পাকা লঙ্কা তুলে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় লাল ফুলের রাশি। পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের রক্তিম আভা পড়েছে দিঘির স্বচ্ছ জলে। গোবিন্দপুর গ্রামের পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে এই দিঘির পাশ দিয়ে। অদূরে প্রবাহিত নদীতে খেয়ানৌকায় পারাপার করছে গ্রামের নারী-পুরুষ। কারও কোলে শিশু, কেউ আবার জমিদারের নতুন জামাতার জন্য পাঠানো দোলের তত্ত্ব নিয়ে নৌকার মাচানের ওপরে বসে রয়েছে। মাঝি নৌকার মাথায় বসে লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। গ্রামের মহিলারা নদীতে গা ধুয়ে, পিতলের কলসিতে জল ভরে ভেজা কাপড়ে রঙিন গামছা কাঁধে ফেলে বাড়ির পথে চলেছে। তাদের কথাবার্তা, হাসি আর পায়ের মলের রুনুরুনু শব্দে বসন্তের পরিবেশ আরও মধুর। ও দিকে ক্রমে নদীর জলে আঁধার নেমে এল।
দোলের আগের দিন শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যায় গোবিন্দদেবের দোলের অধিবাস। তাই সেখানে বেজে উঠেছে ঢাকঢোল। সে দিন দুপুরেই গোবিন্দপুরের আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গৃহদেবতাদের নিয়ে আসা হয়েছে গোবিন্দদেবের পুজোর দালানে। এক একটি বিগ্রহের সিংহাসন চার জন করে বাহক বহন করে এনেছে। কোনও কোনও ঠাকুর এসেছেন অনেক দূর থেকে। তাঁদের বাহকের সংখ্যা বেশি। সঙ্গে দু’টি ঢাক, একটি কাঁসি। আবার ঢোল, ঢাক, কাঁসি, ডগর ও সানাইবাদন সহযোগে কোনও কোনও ধনী পরিবারের দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয়েছে অনেক বেশি আড়ম্বরের মাধ্যমে। বিকেলের মধ্যেই গোবিন্দদেবের বিরাট আঙিনা হয়ে উঠল উৎসবমুখর। বিভিন্ন গ্রামের ‘চোদ্দো ঠাকুর’ চোদ্দোটি সিংহাসনে বসেছেন। বিগ্রহগুলির নানা নাম— কেউ মদনমোহন, কেউ গোপাল, কেউ গোপীনাথ, কেউ রাধাবল্লভ, কেউ বা নারায়ণ। এক একটি বিগ্রহের এক এক রকম রূপ। কোনও বিগ্রহমূর্তি প্রসারিত ডান হাতে একটি নাড়ু নিয়ে দুই জানু ও বাঁ হাতে ভর দিয়ে সবার অতিপরিচিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। কেউ ত্রিভঙ্গমুরারি— পায়ে আলতা, অধরে মুরলী, মাথায় শিখিপুচ্ছ।
সিংহাসনগুলি নানা আকারের। কোনওটি সোনালি বা রুপোলি রাংতায় সুসজ্জিত,কোনওটি হলুদ বা লাল কাপড়ে মোড়া, কোনও সিংহাসন মল্লিকা, জুঁই, বেল বা চাঁপা ফুলে শোভিত। সভার ঠিক মাঝখানে নাড়ুগোপালের মতো গোবিন্দদেব বসে রয়েছেন অলঙ্কৃত রুপোর সিংহাসনে। তাঁর কপালে চন্দনের তিলক, পরনে হলুদ পোশাক, সর্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার, মাথার উপরে রুপোর ছাতা। সিংহাসনে শয্যার চারদিকে হলুদ মখমলের ছোট ছোট গোল বালিশ। গোবিন্দদেবের আঙিনাখানি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি দরজায় কুশের তৈরি দড়িতে দুলছে আম্রপল্লব ও শোলার কদমফুল। মূল প্রবেশদ্বারে দেবদারু ও কামিনী গাছের পাতায় সাজানো সুদৃশ্য তোরণ, তার দু’পাশে কলাগাছের সারি। আঙিনার উপরে সাদা কাপড়ের চাঁদোয়া। তার চার কোনায় ও মাঝখানে এঁটে দেওয়া হয়েছে লাল কাপড় দিয়ে তৈরি পদ্মফুল। পুরো আঙিনা গোবরজলে লেপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বেলা পড়ে আসতেই সেখানে গ্রামের যাবতীয় ছেলেপুলে, বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষের ভিড় জমতে শুরু করল। মহিলারা ভিতরের পথ দিয়ে চিকের আড়ালে এসে দাঁড়াল। দেউড়ির পাশের ছোট একটি ঘরে বসে বাজনদারেরা অধিবাসের বাজনা বাজাতে লাগল।সন্ধ্যায় গোবিন্দদেবের সেবায়েত পরিবার বাঁড়ুজ্যে বংশধরেরা পট্টবস্ত্র পরে খালি পায়ে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের কারও গায়ে রাধাকৃষ্ণের নামাবলি, কারও দেহে রেশমের চাদর, কারও মাথায় টিকি, গলায় তুলসীমালা, প্রায় সকলের সর্বাঙ্গে তিলকচন্দনের ছাপ। খোল, করতাল, কাঁসর, রামশিঙা নিয়ে তাঁরা নগর-সঙ্কীর্তনে বার হবেন। গ্রামের পথের দু’পাশে কাতারে কাতারে লোক। সঙ্কীর্তন শুরু হওয়ার ঠিক আগে ঢাকের ধ্বনি থেমে গেল। তখন শোনা গেল মৃদঙ্গের আওয়াজ আর সকলে গান ধরলেন— ‘আনন্দবদনে সবে হরি হরি বল। হরি বলে বাহু তুলে রাধার কুঞ্জে চল।শ্রীরাধার কুঞ্জে হেমাখি হরিপদ-রজো হে।’ সঙ্গে সঙ্গে জনতার ভিড়ে সকলে ডান হাত তুলে সমস্বরে গাইতে লাগলেন, ‘মাখি হরিপদ-রজো হে!’ সঙ্কীর্তনকারীরা নামগান গাইতে গাইতে প্রাঙ্গণ ছেড়ে দেউড়ির বাইরে এল। চার জন করে বাহক দেহে গঙ্গাজল ছিটিয়ে এক একটি বিগ্রহের সিংহাসন কাঁধে করে সঙ্কীর্তন-দলের পিছন পিছন চলল। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, সানাই, বাঁশি, ডগর, কাড়ার আওয়াজে পুরো গ্রাম মুখরিত। কিছু দূরেই ফাঁকা ময়দান। সেখানে রথ ও দোলের মেলা বসে। মাঠের এক পাশে ইটের তৈরি দোলমঞ্চ। উৎসব উপলক্ষে চুনকাম করে সেটি সাজানো হয়েছে। দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে সঙ্কীর্তনকারীদের শোভাযাত্রা এগোল বাজারের দিকে। প্রত্যেক প্রতিমার সিংহাসনের দু’পাশে তখন বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হল। রংমশালের লাল, সবুজও সাদা আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠল। বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা ছোট ছোট সিংহাসনে মাটির গোপাল বসিয়ে উৎসবের দলে শামিল হল। গ্রামের তেমাথা, চৌমাথাও পথের দু’পাশে অপেক্ষারত সকলে এক একটি ঠাকুরের সিংহাসন দেখতে পেলেই হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। সঙ্কীর্তনের দল চলে গেলে বৃদ্ধারা পথের উপরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পথের রজ ভক্তিভরে গলায়, ঠোঁটে ও মাথায় ছোঁয়াচ্ছেন। অর্ধেক গ্রাম পরিক্রমার পর আচার্যপাড়ায় ছিল ‘বৈকালি’র আয়োজন।
দশ-বারো জন ব্রাহ্মণ বড় বড় রেকাবে কমলালেবু, আখ, শশা, পেয়ারা, শাঁকালু, আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফলমূল ও নানা ধর্রনে ‘ভিজে’ সাজিয়ে আনল। ছানা, ক্ষীর, সর, দুধ, কাঁচাগোল্লাও থরে থরে সাজিয়ে আনা হল। কয়েক জন পুরোহিত সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোচ্চারণের শেষে কয়েকটি ফুল ফেলে এই সব ফলমূল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করে দিলেন। তার পরে সকলে সারি বেঁধে বসে প্রসাদ পেলেন। বড় বড় পাথরের খোরায় চিনির শরবত ছিল। আর ছিল বাতাসা ও মণ্ডা। আবার দ্বিতীয় দফায় গ্রাম পরিক্রমা শুরু হল। তার পরে সব সিংহাসন নিয়ে আসা হল দোলমঞ্চে। সেখানে তখন বিরাট জমায়েত। গোবিন্দদেবের দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করার সময়ে নেড়াপোড়ার আয়োজন। সব শেষ হলে গোবিন্দদেবকে নিয়ে যাওয়া হল দালানে। তার পরে আতশবাজির প্রদর্শনী। ভুঁইচাঁপা, তুবড়ি, চরকি, সীতাহার আর হাউই বাজির কারসাজি দেখে গোটা গ্রাম রোমাঞ্চিত।
আবার দোলপূর্ণিমার সকালে নতুন উৎসাহে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। গোবিন্দদেবের দোলযাত্রা। রাত শেষ হতেই অন্যান্য গ্রামের বিগ্রহেরা বাহকের কাঁধে চেপে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। আর সকল অলঙ্কারে সজ্জিত গোবিন্দদেবকে নিয়ে আসা হল দোলমঞ্চে। বেলা বারোটার পর থেকেই বহু গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে সমবেত হল দোলতলায়। জমজমাট মেলা। সেখানে মণিহারি জিনিস ও নানা রকম মিষ্টির দোকানই বেশি। চিঁড়া, মুড়কি, মন্ডা, রসকরা, চিনি ও গুড়ের ছাঁচ, তেলেভাজা, জিলিপি, মিঠাই, বাতাসা। অন্য দিকে কাঠের পুতুল, তাস, বোতাম, ছুরি, কাঁচি, তালাচাবি, দেশলাই বাক্স, কাঠের কৌটো, টিনের বাঁশি, ঝুটো মোতির মালা, পিতলের বালা, কালীঘাটের এক পয়সা দামের পট ইত্যাদি সামগ্রী।
এ ছাড়াও রয়েছে আবিরের দোকান, কুমোরের হাঁড়ি, মাটির পুতুল। পান, সিগারেট।চারদিকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, কোলাহল। তার মধ্যেই আবির, গুলাল, পিচকারির খুনখারাপি রঙে ছেলে-বুড়ো সবাই রঙিন। চারদিক লালে লাল। সূর্যাস্তের পরে গোবিন্দদেবের বিশেষ আরতি। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে বাঁশির সুর।গোবিন্দপুরের এই ছবিই কম বেশি দেখা গিয়েছে গ্রাম মফস্সল শহরে দোলযাত্রা ও তার আগের দিনে কয়েক দশক আগে পর্যন্ত। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাঢ়বঙ্গের কোথাও কোথাও ঝুমুর শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে চিরন্তন বিরহগীতি — ‘একদিন নিকুঞ্জবনে রাধারে পড়িল মনে আকুল হলেন শ্যামরায়। কেবল বাঁশরী হাতে দোসর নাহিক সাথে কেবা এনে রাধারে মিলায়...’ গ্রামের সঙ্কীর্তনের আদলেই দোলের সকালে শহরের পথেও চোখে পড়েছে প্রভাতফেরি। ব্যস্ত জনপদ যানবাহনের শব্দে মুখরিত হওয়ার আগে গৃহস্থের অনভ্যস্ত কানে ভেসে এসেছে ‘ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল’। সারা দিনের দোল খেলার চিহ্ন থেকে যায় পথেঘাটে, বাড়ির আঙিনায়। আর তারই মধ্যে অনেক বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা বসত ঘরোয়া গানবাজনার আসর। পরবর্তী কালে ঘরোয়া পরিসর ছেড়ে বসন্তোৎসব উদ্যাপনে অনেকেরই গন্তব্য হয়ে দাঁড়াল শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীর সেই আশ্রমিক পরিবেশকে নানা ভাবে বিস্রস্ত করে দিল বাইরে থেকে আছড়ে পড়া বিশৃঙ্খল জনতার ঢেউ। তারই জেরে বিশ্বভারতীতেও মাঝেমাঝে বন্ধ রাখতে হয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান।
একদা শহুরে সমাজের যে খণ্ডিত চিত্র হুতোম তুলে ধরেছিলেন, কয়েক যুগ পরে যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে সেই মোচ্ছব ও হুল্লোড়ের ছবিই যেন আজ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। আগে উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হত বিশেষ খাওয়াদাওয়া ও গানবাজনার। আর আজ যে কোনও পুজো-পার্বণ বা উৎসবের সেই মাধুর্য পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে। এখন ব্যক্তিগত পরিসরে খানাপিনা, হুল্লোড় আর ফুর্তিই মুখ্য, বাকি সব গৌণ। কারও জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা দোল-দুর্গোৎসব যা-ই হোক না কেন, এই উচ্চকিত উদ্যাপনই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আনন্দের মাপকাঠি। উৎসব তার লোকায়ত চরিত্র হারিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তির বিনোদনের উপকরণ।
- দোলযাত্রা প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মীয় লোকেদের উৎসব হলেও সকলেই এই উৎসবে মেতে ওঠেন। আগামী ১৪ মার্চ শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব।
- দোলে যদি রং খেলতেই হয়, তার আগে থেকেই ত্বকের যত্ন নেওয়া ভাল। এমন কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করবেন না, যাতে কিছু বিশেষ ধরনের রাসায়নিক মেশানো আছে।
-
ভিন্ধর্মী বলেই কি ফহাদের গালে রং নেই? কটাক্ষ শুরু হতেই স্বামীর পাশে দাঁড়ালেন স্বরা
-
রং ছাপিয়ে প্রেমের জোয়ার! আবিররাঙা নীল-তৃণা, সুস্মিতার জন্য সাহেবের মেনু কী?
-
ফোনে রং ঢুকে গিয়েছে? জলে ভিজে ফোন বন্ধ, মুশকিল আসান হবে সহজ কিছু কৌশলে
-
রং খেলার পর হাঁচি-কাশি, অ্যালার্জির সমস্যা হচ্ছে? কোন কোন পানীয় বাড়ির সকলকে খাওয়াবেন
-
‘কিশোরী’ নয়, দেব রঙিন অন্য রঙে! দুই ‘সন্তান’ নিয়ে পুজোপাঠে মিমি, ঊষসী কলকাতার মালাইকা?