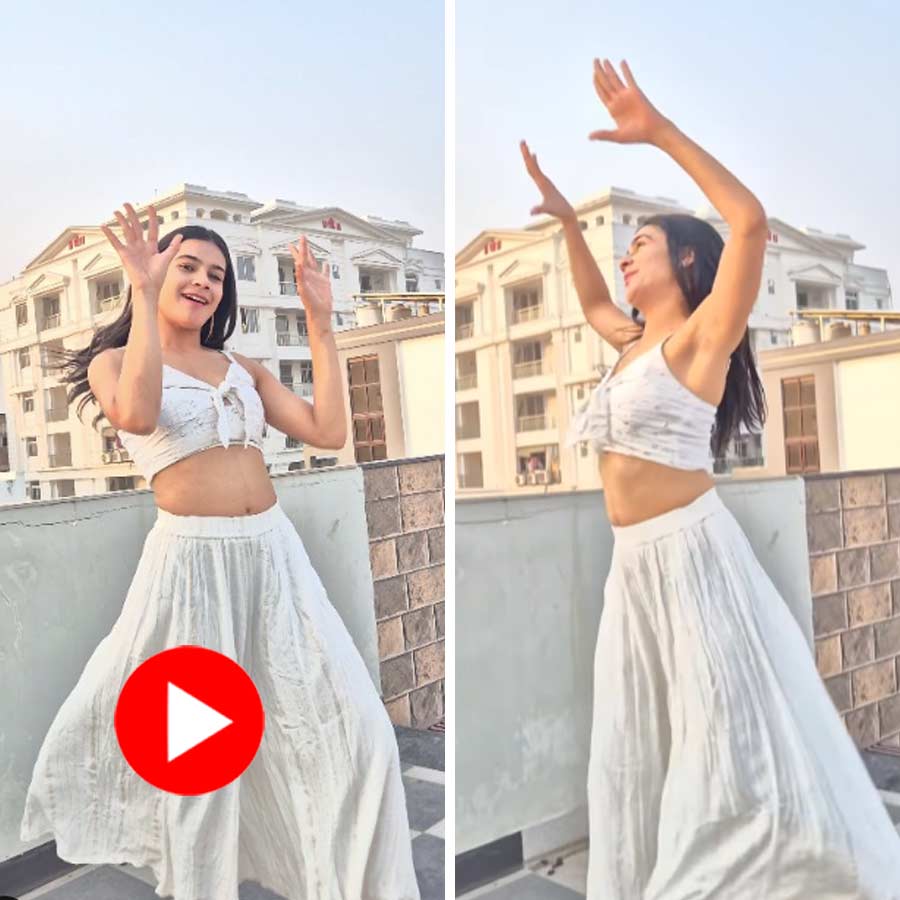নিজের চেনা চৌহদ্দিতেই আচমকা পড়ে যাচ্ছেন। অথচ, মধ্য চল্লিশের ব্যক্তিটির পায়ে কোনও সমস্যা নেই। আবার, আচমকা হয়তো দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হচ্ছে বাড়ির প্রবীণ মানুষটির। এ সব ক্ষেত্রে হতেই পারে, মধ্য চল্লিশের অথবা প্রবীণ ব্যক্তিটির চোখ ‘সাইলেন্ট কিলার’ বা গ্লকোমার শিকার। এই রোগের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলে তিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। তখন পরীক্ষায় ধরা পড়ে, ছানি নয়, গ্লকোমার শিকার তিনি।
তত দিনে রোগী তাঁর দৃষ্টিশক্তির অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন। গ্লকোমায় হারানো দৃষ্টি চিকিৎসা করেও ফেরানো যায় না। কারণ, এই রোগে ক্ষতি হয় অপটিক নার্ভের (স্নায়ু)। ‘‘গ্লকোমা নিয়ে তাই রোগী ও চিকিৎসক উভয়কেই সচেতন করতে এক দশকেরও বেশি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহকে ‘বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ’ পালন করে আসছে ওয়ার্ল্ড গ্লকোমা অ্যাসোসিয়েশন। এ বছর ৯-১৫ মার্চ বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ।’’— বলছিলেন চক্ষু-শল্য চিকিৎসক এবং ওয়ার্ল্ড গ্লকোমা অ্যাসোসিয়েশনের পেশেন্ট কমিটির সদস্য টুটুল চক্রবর্তী।
২০২০ সালের পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে আট কোটি মানুষ গ্লকোমার শিকার। বর্তমানে সেই সংখ্যা ১০ কোটি ছুঁয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে চিকিৎসক মহল। এ দিকে, সচেতনতা আগের তুলনায় বাড়লেও তা জেলা বা গ্রাম স্তরে অনেক পিছিয়ে। ফলে নীরব এই ঘাতকের কবলে দৃষ্টিহীন হয়ে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছেন বহু নিম্নবিত্ত পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যও।
গ্লকোমা এমন একটি অবস্থা, যা চোখের ভিতরে চাপ বা ইন্ট্রাওকুলার প্রেশার জমা হওয়ার কারণে অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি করে। এই স্নায়ুই মস্তিষ্কে ছবি পাঠায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্নায়ু খারাপ হলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারায় এবং তা আর ফেরে না। টুটুল বলেন, ‘‘গ্লকোমার নিয়মিত চিকিৎসা শুরু হলে চোখের চাপ কমিয়ে বাকি দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখা সম্ভব। পরিবারের কেউ গ্লকোমা আক্রান্ত থাকলে, এর আশঙ্কা বাড়ে।’’
চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, গ্লকোমা বেশি হয় চল্লিশোর্ধ্বদের। তবে তরুণ, শিশু এমনকি সদ্যোজাতদেরও এটি হতে পারে। চিকিৎসার পরিভাষায় দু’রকমের গ্লকোমা হয়— মুখ্য (প্রাইমারি) গ্লকোমা এবং গৌণ (সেকেন্ডারি) গ্লকোমা। মুখ্য গ্লকোমা দু’ধরনের। একটি ওপেন-অ্যাঙ্গেল বা ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা। এর কারণ, চোখের ‘ড্রেন স্ট্রাকচার’ আপাতদৃষ্টিতে ঠিক মনে হলেও চোখের জল (অ্যাকুয়াস হিউমার) যে ভাবে বেরোনো উচিত, সে ভাবে বেরোয় না। দ্বিতীয়টি অ্যাঙ্গেল-ক্লোজ়ার গ্লকোমা বা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল-ক্লোজ়ার গ্লকোমা বা ক্রনিক অ্যাঙ্গেল-ক্লোজ়ার গ্লকোমা বা ন্যারো-অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা। এ ক্ষেত্রে চোখের ‘ড্রেন স্ট্রাকচার’ খুব সঙ্কীর্ণ হওয়ায় অ্যাকুয়াস হিউমার যে ভাবে বেরোনো উচিত, সে ভাবে বেরোতে পারে না। ফলে চোখে হঠাৎ চাপ তৈরি হয়। টুটুলের মতে, এশিয়ায়, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে চোখের ‘ড্রেন স্ট্রাকচার’ সঙ্কীর্ণ হয়। এঁদের একটি অংশের আবার চোখের চাপও অতিরিক্ত থাকে। তাঁদের সকলেই যে গ্লকোমায় আক্রান্ত হবেন, তেমন নয়। তবে এঁদের চিকিৎসকের নিয়মিত নজরদারিতে থাকা দরকার। এঁদের যখন পার্শ্ব দৃষ্টিশক্তি (পেরিফেরাল ভিশন) চলে যায়, তখন তাকে বলে ‘প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজ়ার গ্লকোমা’।
চক্ষু-শল্য চিকিৎসক দেবাশিস চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, চোখের অন্য অসুখ, চোখের পুরনো আঘাত, রেটিনার অস্ত্রোপচার, কর্নিয়া প্রতিস্থাপন, মায়োপিয়া বা ডায়াবিটিসের মতো কোনও রোগের কারণেও চোখের চাপ বেড়ে সেকেন্ডারি গ্লকোমা হয়। চোখের ড্রপ বা ত্বকের মলমে থাকা কিছু ধরনের স্টেরয়েডের দীর্ঘ ব্যবহারেও গ্লকোমা হতে পারে। শিশুদের জন্মগত গ্লকোমা প্রকাশ পায় নবজাতক বা শিশুর জন্মের প্রথম কয়েক বছরেই। কোনও শিশুর আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা, চোখ ঘষা বা কুঁচকে ফেলা গ্লকোমার কারণ। দেবাশিস বলেন, ‘‘শিশুদের ক্ষেত্রে গ্লকোমার একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার। বড়দের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে চোখের ড্রপ দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে লেজ়ারথেরাপি বা অস্ত্রোপচারও করা হয়।’’
ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা আক্রান্তদের বেশির ভাগেরই কোনও উপসর্গ থাকে না। যত দিনে তা প্রকাশ পায়, তত দিনে রোগ অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে পার্শ্ব দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। সেন্ট্রাল ভিশন দিয়েই রোগীর দৃষ্টিশক্তি থাকে। কিন্তু সেটিও নষ্ট হলে সম্পূর্ণ অন্ধত্বের শিকার হন রোগী। অ্যাঙ্গেল-ক্লোজ়ার গ্লকোমার লক্ষণগুলি দ্রুত এবং আরও স্পষ্ট দেখা দেয়। ফলে ক্ষতি দ্রুত হতে পারে।
তাই দুই চিকিৎসকেরই পরামর্শ, পরিবারে গ্লকোমার ইতিহাস থাকলে বাড়তি সতর্ক হতে হবে। চল্লিশের আগেই চোখের নিয়মিত পরীক্ষা শুরু করাতে হবে হাসপাতাল বা চক্ষু চিকিৎসকের কাছে গিয়ে। যাতে চিকিৎসকের সন্দেহ হলে তিনি গ্লকোমার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)