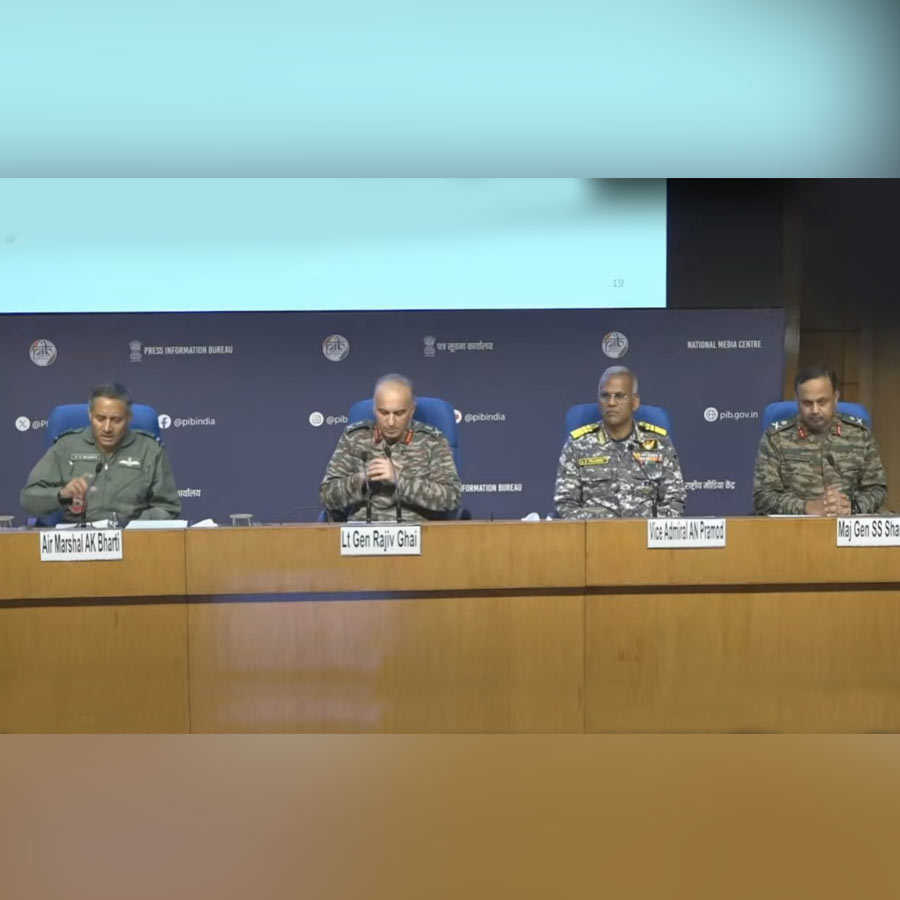“সকালে ঘুম থেকে উঠেই হয় ফেসবুক নয়তো হোয়াটস অ্যাপে চ্যাট”। বাড়ির লোকটির মৃদু মন্তব্য কানে যেতেই টনক নড়ল। আরে আমি তো সকাল থেকে মোবাইল নিয়েই পড়ে আছি। ও দিকে ‘ভাষা দিবস’ নিয়ে লেখার খালি পাতাগুলো পত পত করে উড়ছে জানলার ফাগুন হাওয়ায়।
আবার লেখা নিয়ে বসি। ‘বিপন্ন মাতৃভাষা’ নিয়ে কিছু চর্বিতচর্বণ লেখা। ওই যে, “আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, ...আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই...” শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে গানটা আওড়াই। অথচ বাংলায় প্রভূত সাহিত্যচর্চা করলেও আমি তো জানি, আমি নিজেও বেশ ভাল রকম ‘খিচুড়ি’ ভাষায় কথা বলি সময় বিশেষে। ওই চ্যাট ট্যাট করতে বসলেই আর এস এম এস বার্তায় হাবিজাবি শর্ট ফর্মে কথোপকথন চালাই। এটা দস্তুর। ভেবে লাভ নেই। আমরা যতই লোক দেখানো বাংলা ও বাঙালিত্ব নিয়ে শ্লাঘা দেখাই—আমরা কিন্তু এক অর্থে বেজায় হিপোক্রিট। অথচ দেখুন, এই ‘আমি’ ‘আপনি’ আমরা মনে প্রাণে বাঙালিই। হ্যঁা, মুম্বই পরবাস যাপনে অভ্যস্ত আমরা কিন্তু আদতে বাঙালিই। আমাদের মাতৃভাষা নিখাদ বাংলা। যদিও তাতে মিশে থাকে হিন্দি ইংরাজি, কিছু মরাঠি শব্দ বা বাকধারা।

ভাষা হল পরস্পরের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। যদিও এটা বলা কঠিন যে মানুষ কবে থেকে প্রথম কথা বলতে শিখেছে। প্রস্তর যুগে যখন প্রাচীন মানুষ কেবলমাত্র গাছের ফলমূল আর শিকার করে আনা বনের পশুপাখির মাংস খেয়ে দিব্যি বেচে থাকত, তখন থেকেই নিজেদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ বা ভাব বিনিময়ের জন্য বাধ্য হয়েই তারা ভাষা তৈরি করেছিল। ক্রমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল ভাষা ও তার বিস্তার। দিনকালের গতিময়তার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে এক ভাষা থেকে সৃষ্টি হল আরও বহুবিধ ভাষার। কালের নিয়মে ভাষায় এসেছে রদবদলও।
ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখা যায় প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। এরও বহু পরে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দের প্রায় কাছাকাছি সময়ে সম্রাট অশোকের লিপি সৃষ্টি হয়েছিল। তারও পর কুণাল লিপি, গুপ্ত আমলে গুপ্ত লিপি, মৌর্য লিপি, আর্যলিপি, কুটিল লিপি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছিল। এক হাজার খ্রিস্টাব্দের সময় নাগাদ প্রাচীন বাংলা লিপির সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক পরিবর্তনের পথ বেয়ে বাংলা লিপিরও সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। যেখানে বহু ভাষারই নিজস্ব কোনও বর্ণমালা নেই, তারা অন্য ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখেসেখানে বাংলা ভাষার নিজের বর্ণমালা থাকা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে অবশ্যই বিরাট শ্লাঘার বিষয়।
সমগ্র বিশ্বে এখন প্রায় পাঁচ হাজার ভাষায় মানুষ কথা বলেন। যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই হল আফ্রিকার ব্যবহৃত ভাষা। উচ্চারণ, শব্দের ব্যবহার ও বাক্য নির্মাণের দিক থেকে যা একটা অন্যটার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভাষাবিদরা এই ভাষাগুলিকে মোটামুটি কুড়িটির মতো পরিবারে ভাগ করেছেন। তবে একটা লক্ষণীয় মজার ব্যাপার হল আফ্রিকারই সিয়েরলিওন দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা। অন্য দিকে ক্রমবিকাশের ফলে পরিবর্তিত হতে হতে প্রাচীন ইংরাজি ভাষারও নতুন অনেক ব্যবহারিক পরিবর্তন হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ইংরাজি ভাষা ছিল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দেশজ ভাষার সংমিশ্রণ। স্ক্যন্ডিনেভিয়ান আঞ্চলের দেশসমূহের মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানে ভাষায় ব্যবহৃত ব্যাকরণ ও শব্দাবলি অনেক সহজতর রূপ লাভ করে। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে রোমান জার্মান গ্রিক ল্যাটিন শব্দের মিশ্রণ জড়িয়ে আছে। পনেরোশো শতক আধুনিক ইংরাজির সূচনা হয়।

শেক্সপীয়ারের রচনার মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকে আধুনিক ইংরাজির গ্রহণযোগ্যতা আসে। এবং ১৬০৪ সালে প্রথম ইংরাজি শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে এখানকার আধুনিক ইংরাজি শব্দের প্রচুর ফারাক আছে। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে পৃথিবীতে একশো কোটিরও বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, সেটি হল চিনা ভাষা। একটা সময় পর্যন্ত তো পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি বই ছাপানো হত চিনা ভাষায়। চিনা শব্দে প্রায় সত্তর হাজার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রধানত তাইওয়ান ও চিনে এই ভাষার প্রচলন বেশি। ও দিকে ফরাসি ভাষায় বিশ্বে প্রায় দশ কোটি মানুষ কথা বলেন। ফ্রান্স তো বটেই, সুইজারল্যান্ড, জার্মান, বেলজিয়াম, কানাডা, আফ্রিকা, ইতালি দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রায় ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হয়। আবার ব্রাজিল, এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু অংশে এবং পর্তুগালে, পতুর্গিজ ভাষায় কথা বলেন সাড়ে তেরো কোটিরও কিছু বেশি মানুষ। রোমান ভাষায় কথা বলেন বলকান ও রোমানিয়ার আড়াই কোটি মানুষ। মায়া সভ্যতার যুগে গ্রিক ভাষার প্রচলন হলেও মায়া সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। পরে খ্রিস্টপূর্ব আট শতকের শেষ দিকে গ্রিক ভাষার অক্ষরমালা লিখিত হয়। আধুনিক গ্রিক ভাষা ১৮৩০ সালে গ্রিসের স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নতুন করে। হালের স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন পৃথিবীর প্রায় তেত্রিশ কোটিরও বেশি মানুষ। চিলি, মেক্সিকো, পানামা, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, গুয়েতামালা, গিনি, কিউবা, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, এল সালভাদর ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রভাষাই হল স্প্যানিশ। এমনকী কানাডা মরক্কো ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্রেও স্প্যানিশ ভাষার চর্চা হয়। স্পেন নানা দেশে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে শুরু করার সঙ্গে তাদের ভাষাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে আমেরিকার প্রায় সব জায়গায়ই। আরও কিছু পরে আঠারোশো শতকে স্পেন আমেরিকার উপনিবেশ শাসনে পরাভূত হলেও লাটিন আমেরিকায় স্প্যানিশ ভাষা প্রায় সব জাতির রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রয়োগ হয়। আরবি ভাষা সেমেটিক ভাষা পরিবারের অন্যতম সদস্য। যেমন হিব্রু গিজ সিরিকা আরামিক পুনিক মোয়াবাইট নাবাটিয়ান ইত্যাদি বহু সহস্র বছর ধরে এই ভাষা চলছে।
আমরা বিশ্বাস করি নিখাদ বাঙালিয়ানায়। মুম্বইয়ে থেকেও। আমরা নববর্ষ-এর দিনে আটপৌরে স্টাইলে দামি ঢাকাই জামদানি পড়ি। কপালে বড় টিপ, একটু শাখা সিঁদুর। বাড়িতে বাংলা বর্ষপূর্তির দিনে জলখাবারে ফুলকো লুচি আর কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সাদা আলুর চচ্চরি আর বেগুন ভাজা।
দুপুরে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নামী রেস্তোরাঁয় বাঙালিয়ানা ভোজ। মাটি ও কলাপাতার বাসনে মোচার ঘণ্ট, পোস্ত বড়া, তেল কই, ধোকার ডালনা, ভেটকি পাতুরি, পার্শে ঝাল, মিষ্টি দই, রাবড়ি। যদিও কলকাতায় থাকলে এই আদিখ্যেতাগুলো একটু বেশিই হয়। পঁচিশে বৈশাখ বাইশে শ্রাবণে শুধুই রবীন্দ্রনাথ।

আমরা ‘শুভ জন্মদিন’ পালন না করে ধুমধাম করে পালন করি ‘হ্যাপি বার্থডে’। সঙ্গে অতিথিদের ‘রিটার্ন গিফ্ট’। মুঠোফোন আর ফেসবুক টাইমলাইনে শুধুই বার্থডে উইশ সবই ইংরাজিতে। স্মার্ট ফোন ফেসবুকেও দিব্যি বাংলা অপশন রয়েছে। সকালের প্রথম অফস্ক্রিন অথবা অনস্ক্রিন সাক্ষাতে বা চ্যাটে ভুলেও ‘সুপ্রভাত’ বলি না। এখন আর কেউ ‘ভেতো বাঙালি’ বলে ঠাট্টা করতে পারবে না। তাই তো সাত সকালেই চেনা পরিচিত দেখলেই প্রথমেই বলে দিই প্রথম আলাপে ‘হাই, গুড মর্নিং, হ্যাভ এ নাইস ডে’। বিদায়কালে বেশ গলা তুলেই বলি ‘বাই...সি ইউ সুন’। আমরা এমন সব কেতা দেখাই যে অবাঙালি পেলেই নিজের মাতৃভাষা বেমালুম ভুলে বাংলা উচ্চারণে প্রায় নির্ভুল হিন্দিতে কথা বলি। বাংলা বিজ্ঞাপনে অ-বাংলা শব্দগুচ্ছের বিরুদ্ধে আমাদের তেমন ক্ষোভ নেই।
অথচ ‘উনিশ মে’ ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ ভাষাদিবস নিয়ে লিখতে বসি। ভারী যত্নে, পরম আবেগে কবি একদা লিখেছিলেন, “মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা...”। আমাদের এই বাংলা ভাষা এমনই এক ঐতিহ্য আছে যা কিনা বৃহত্ এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আগলে রেখেছে নিজস্ব বনেদিয়ানায়। বস্তুত ভাষাকে মাধ্যম করেই এক একটি অঞ্চল বিশেষে এক একটি জনজাতির সৃষ্টি হয়। নিজেদের কথিত মাতৃভাষার গর্বেই একটা অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করেন। এ ভাবেই ক্রমান্বয়ে একই অঞ্চলবাসী, যারা একই ভাষা ব্যবহার করেন, তারা নিজেদের এক জাতি এক প্রাণ বলে বিবেচনা করেন। মাতৃভাষাই সমস্ত গোষ্ঠীকে এক জাতিতে একত্রীভূত করে।
বাংলা ভাষার ব্যবহার এখন পৃথিবীর এক বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা। পৃথিবীর জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় ২৩ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বিশ্বে বহুল প্রচারিত ভাষাগুলির মধ্যে সংখ্যানুসারে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ থেকে সপ্তমের মধ্যে। ইংরাজি, চৈনিক, স্প্যানিশ ইত্যাদির পরই বাংলা ভাষার স্থান। দক্ষিণ-এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে বাংলা ভাষাটি মূলত ইন্দো-আর্য ভাষা। সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।
উত্কর্ষগত দিক দিয়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গান, গদ্যে বাংলা ভাষার বনেদিয়ানা অন্য ভাষাকে ম্লান করে দেয়। খ্রিস্টায় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অপভ্রংশ থেকে যে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব হয়, তার মধ্যে বাংলা একটি। বাংলা ভাষার ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) চর্যাপদ (৯০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ), ২) মধ্য বাংলা (১৪০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যে চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ধরা হয়। ৩) আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)। চর্যাপদ আবিষ্কার বা রচনার কাল হিসেব করলে এর প্রমাণ মেলে। বাংলা ভাষার গদ্য অবশ্য অনেকটা পরে, লিখিত ভাষার হিসেব অনুযায়ী।
তবে ভাষারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা ভাষার কথ্য রূপের জেলাভিত্তিক কিছু কিছু প্রভেদ থাকলেও বাংলা ভাষার লিখিত রূপ বিশেষ করে সাহিত্যে, ইতিহাস, সংবাদপত্রে, গান ইত্যাদিতে এই ভাষা ব্যবহারকারীকে বাঙালি বলে পরিচয় দেয়। মাতৃভাষার জন্য একটা অন্য ধরনের আস্বাদ, শ্লাঘা, অনুভবের ভূমি তৈরি হয় বাঙালি মননে। আমাদের নিজস্ব এই ভাষার একটা বুদ্ধিপ্রদ আভিজাত্য আছে। আমরা শুধু বাংলা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এই গর্ববোধ আমাদের দুই বাংলারই।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন হিসাবে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি গৌরবজ্জ্বল দিন। দিনটিকে বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে ‘শহিদ দিবস’ বা ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবেও পালিত হতে দেখা যায়। স্বাধীনোত্তর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশি সংঘর্ষে আব্দুস সামাদ, রফিক উদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত আব্দুল জব্বর এবং অহিউল্লাহ নামে এক বালক নিহত হন। সে দিনের বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হওয়া মানুষদের স্মরণে প্রতি বছর এই দিনটিকে বাংলাদেশ তুমুল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। জাতিসংঘও এই দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস’ হিসাবে মান্যতা প্রদান করেছে।
বাংলাদেশে একুশের সেই অমর বলিদান নিয়ে সেখানকার গীতিকার আব্দুল গফফর চৌধুরী প্রথম গান লেখেন, “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?’ গানটিতে প্রথম সুরারোপ করেন আব্দুল লতিফ। পরে ১৯৫৪ সালে ওই একই গানে নতুন করে সুরারোপ করেন আলতাফ মাহমুদ। সেই থেকে আজও ভাষা আন্দোলন স্মরণে বাংলাদেশে প্রভাতফেরিতে এই গানটি গাওয়া হয়।
সমসাময়িক বিশ্লেষণে এটা দেখা যায়, বাংলা ভাষার ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালির যে অতীত গৌরব ছিল, তা এখন অনেকখানি ইতিহাসে পরিণত। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলতেই পারেন, ভাবের ঘরে চুরি করার মতোই এই ‘মহান একুশে’ বা ‘উনিশে মে’ পালন করে সত্যিই কী বাংলা ভাষার ব্যবহার বা প্রয়োগের ব্যবহারিক দিক মসৃণ হচ্ছে। বিভিন্ন সাহিত্যসভা বা সেমিনারে প্রথিতযশা সাহিত্যিককে সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায় বাংলা ভাষাটাই আদৌ ‘মোদের গরব মোদের আশা’ আছে কিনা।
সেই গেল শতকের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলার রফিক, বরকত, আব্দুল, জব্বার-এর মাতৃভাষার জন্য আহুতি দানকে এতগুলো বছর পরও স্মরণ করে, আবেগ আতিশয্যে প্রতিবছর ‘ভাষা শহিদ দিবস’ পালন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা শুধু। আ হা। কতই না উদার কণ্ঠে, সোচ্চারে বা ব্যানার লিখনে, পত্রিকার ক্রোড়পত্র জুড়ে ওই কিছু সময় চলে ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র চর্বিতচর্বণ। হয়তো এই আকুল হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশি শহিদ ভাইদের মাতৃভাষার জন্য বলিদান সত্যিই মার্মান্তিক। আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষির ভারত রাষ্ট্রে থেকে প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রভাষা উপস্থিতি অনুভূত করি। গো-বলয়ে রাষ্ট্রভাষা প্রচলন আছেই। তবে দক্ষিণ ভারতের চারটি ভিন্ন ভাষাধর্মী রাজ্যে রাষ্ট্রভাষার প্রতি অদ্ভুত অনীহা প্রকট। চার রাজ্যই তাদের নিজস্ব তামিল, তেলেগু, কন্নঢ়, মালয়ালম ভাষার প্রতি গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হলেও ইংরেজি ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কথা বলতে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ করেন না।
পশ্চিমবঙ্গ তথা অন্য কিছু রাজ্যে নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা থাকলেও সেই সব মাতৃভাষার ব্যবহার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষার ব্যবহারও কমে আসছে। টিভি সিরিয়ালগুলোর বিরতির ফাঁকফোকরে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তিতে বা বাংলা ম্যাগাজিনগুলোর বাংলার লিখিত বিজ্ঞাপনেও কোথাও কোথাও উদ্ভট বাংলা। হয়তো সেগুলি বিজ্ঞাপন কপিরাইটার মূল হিন্দি বা ইংরেজি বিজ্ঞাপনী বিবৃতির অক্ষম বাংলা অনুবাদ। বাংলা ভাষাটাই যেন কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। এখন তো প্রকৃত বাংলার সঙ্গে হিন্দি-ইংরাজি ভাষার মিশেল দেখে দেখে, শুনে আমরা এতটাই ধাতস্থ হয়ে গেছি যে এই জগাখিচুরির ব্যাপারে আর কোনও তাপ-উত্তাপ বোধ করি না।

এটা ঠিক পেশাগত বা বৈবাহিক কারণে কেরিয়ার গঠনে দূর প্রদেশে বসত গড়তে হচ্ছে অনেককে। সুতরাং বাংলার শুদ্ধতাও সেখানে স্থানীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা আর ইংরাজির সঙ্গে ডায়েলেকট-এ মিশে যাচ্ছে। জেন ওয়াইয়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মও ইন্টারনেটে ট্যুইটার ফেসবুক চ্যাটে মোবাইল বার্তাতেও মিশ্র ভাষায় দিব্যি সড়গড় হয়ে গেছি। অযথা তত্ত্বকথায় ভারী ‘একুশে’ দিনের আবেগ আতিশয্যের বাহুল্যতা অনেকটাই আপেক্ষিক মাত্র। এই বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন চাহিদা সত্ত্বেও ভাষার মিশেল যেন ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বাড়বাড়ন্ত একটা রব প্রায়ই ওঠে যে বাংলা বই পড়ার অভ্যেস বা পাঠকের সংখ্যাও দিনকে দিন কমে আসছে। এই সর্বনেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া মানুষকে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নততর করলেও মানুষের বাংলা পাঠের অভ্যাসকে গ্রাস করছে।
এমন একটা কথাও প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসে বাঙালিই নাকি বাংলা ভাষাটাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে। ইংরাজি শিক্ষার মূল্য, কথন ও পঠনপাঠনেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইদানীং কালে বিশেষ করে বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যা কিন্তু বাড়েনি। যদিও কলকাতা বইমেলার কিছু মানুষ ধুয়ো তোলে তারা এখানে প্রতিবছর কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। তবে সেখানে বাংলা বই কত আদৌ বিক্রি হল, তা জেনেও না জানার মতো ভান করে তাঁরা এ কথা বলেন। তবে কলকাতা বইমেলা, সব সময় বাংলাদেশে ‘একুশের বইমেলার’ মতো শুধুমাত্র বাংলা বাংলার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি এটা আমাদের কাছে ভাল হয়েছে।
হয়তো এই অতিরিক্ত আবেগ আতিশয্যকে উসকে দিয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহস্রাব্দের সূচনায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে খাতায় কলমে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ রূপে উদযাপন করার ডাক দিয়েছে। এক যোগে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে, ভাষাপ্রেমী জনগণের কাছে যা প্রভূত তাত্পর্যপূর্ণ। আমরাও এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদা-সহ পালন করছি নানা উত্সব-অনুষ্ঠান-সেমিনার-বক্তৃতা-কবিতা পাঠের আসর ইত্যাদির স্মরণে-বরণে। যদিও বাংলাভাষা নিয়ে পশ্চিমবাংলা, কলকাতায় এই হুজুগ প্রীতি দিনটিকে ঘিরে। ‘মহান একুশে’ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে একটা বিশাল সামাজিক অনুষ্ঠান। তবে ঢের দূর এই মুম্বই মুলুকে বসে তার রেশ পাওয়া কতটাই বা যায়। মুম্বইয়ে বসে বাংলা ভাষার প্রতি স্মৃতিকাতরতা উথলে ওঠে খানিক। ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’, ‘মাতৃভাষা দিবস’ কাছে ঘনিয়ে এলে। এবং খুব হীন ভাবেই এটাই লক্ষণীয় যে, বছরে হুজুগে ক্লান্ত একটা দুটো দিনকে ঘিরে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা, সম্ভ্রম, মাতামাতি।