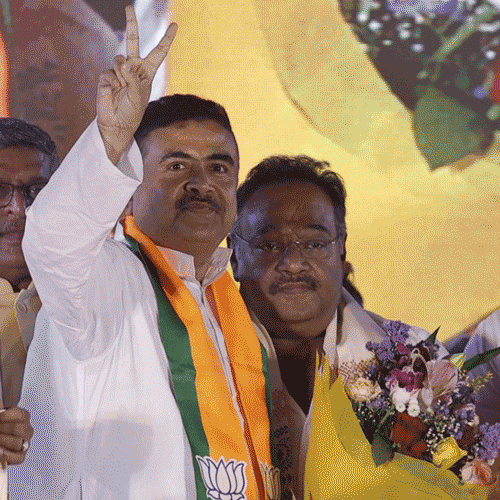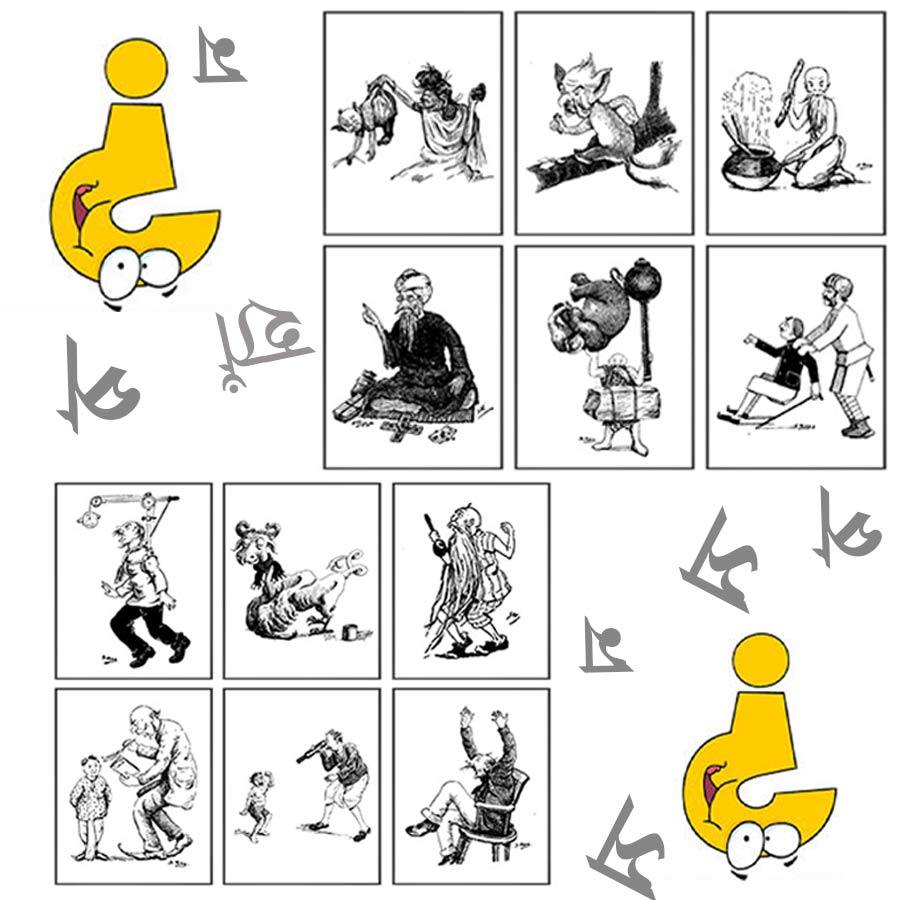অন্তত পাঁচ প্রজন্ম ধরে, ১৮৯০ থেকে, পৃথিবী জুড়ে মে-দিন পালিত হয়ে আসছে। এ কেবল কারখানা শ্রমিকের উদ্যাপন নয়, এর ব্যাপ্তি মানবসমাজ জুড়ে। কার্ল মার্ক্সের কাছে আট ঘন্টার লড়াই ছিল এক দিকে শ্রমিকের অধিকারের দাবি, অন্য দিকে বর্ণবিদ্বেষ বিলোপের পথে একটি পদক্ষেপ। ক্যাপিটাল-এ তিনি আমেরিকায় শ্রমিক নেতাদের আট ঘণ্টার কাজের দাবিকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি সচেতন করে দিচ্ছেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত না দাসপ্রথা উৎখাত হচ্ছে ততক্ষণ আমেরিকার যে কোনও স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনই অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে। যতক্ষণ তাকে কালো চামড়ায় ছাপ মেরে রাখা থাকবে ততক্ষণ সাদা চামড়ার শ্রম নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।” এই প্রশস্তদৃষ্টি চরিতার্থ হয় আট ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিটি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের বাইরে কৃষি ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।
পাঁচ প্রজন্মে পৃথিবী দেখেছে শ্রমিক শ্রেণির পরিচালনায় সরকার, আবার সাক্ষী থেকেছে পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের। পুঁজির দাপটে সংগঠিত শ্রমক্ষেত্র সঙ্কুচিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরদের জোর প্রায় শেষ। এই শক্তিহীনতার সঙ্গে যোগ হয়ে চলেছে সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যেকার বেড়ে চলা, এবং বাড়িয়ে তোলা, দূরত্ব। সামাজিক পরিসরে, বিশেষত বিদ্যাচর্চায়, সংগঠিত শ্রমিকদের বিষয়ে যে-কোনও আলোচনাকেই দেখা হয় ‘সুবিধাভোগী’র স্বার্থরক্ষা হিসেবে। চালু ধারণা হল, সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা শুধু সংখ্যায় নগণ্য নন, তাঁরা যেহেতু নির্দিষ্ট আর্থিক ও অন্যান্য আইনি সুবিধা পেয়ে থাকেন, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। এ-ধারণাও বলশালী যে মালিকপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষিতে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা ছিল জোরালো তাদের জঙ্গি আন্দোলনের কারণে শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, যার ফলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন মার খায়।
যে কোনও জটিল জিনিস সহজ ছকে ফেলে দিয়ে সবচেয়ে লাভ হয় ক্ষমতাবানের। একটা উদাহরণ নিই। ‘ইউনিয়নের আন্দোলনের কারণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প উঠে গেল’, এই প্রচার এত জোরালো যে, মনে হয় শ্রমিকশ্রেণির লোকেরাও এটা বিশ্বাস করে বসেছেন। যেমন, প্রামাণ্য গবেষণার ভিত্তিতে লেখা অচিন চক্রবর্তী ও সহযোগীদের লেখা একটি সাম্প্রতিক বইতে দেখানো হয়েছে কী ভাবে শ্রমিকরা আশঙ্কা করছেন, ‘দাবি তুললে কারখানা উঠে যাবে।’ অথচ, গবেষকরা দেখাচ্ছেন, এ-রাজ্যে কারখানা উঠে যাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ধর্মঘট বা অন্যান্য শ্রমিক অসন্তোষের ভূমিকা মাত্র ১ শতাংশ, ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ হচ্ছে লকআউট। আবার অভিযোগ করা হয়, নতুন কারখানা না হওয়ার কারণ হল জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ভয়। কিন্তু, গবেষকরা দেখাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প কমে যাওয়ার পিছনে ভারত সরকারের নানা নীতির প্রভাবই বড় কারণ: প্রাক্-উদারীকরণ যুগে শিল্প-লাইসেন্স না দেওয়া থেকে পণ্য পরিবহণ মাশুলে সমতার মতো নানা সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিল্পসম্ভাবনার প্রভূত ক্ষতি করেছে। দাবি করা হয়, শ্রমিকদরদি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকায় মালিকপক্ষের ক্ষতি হয়েছে। অথচ, গবেষকরা প্রমাণ দেখাচ্ছেন, এ-রাজ্যে শ্রমিকদের স্বার্থে নানা আইন হলেও তাদের রূপায়ণ থেকেছে খুবই দুর্বল। যেমন কারখানা পরিদর্শন, বিবাদ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি নানা দিক দিয়েই শ্রমিকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে হতে এখন এমন এক অবস্থা যেখানে, “কোনও সংগঠিত ইউনিয়ন নেই... আমরা মিটিংয়ের পর মিটিংয়ে যাই, কিন্তু মালিকপক্ষ সবাই মিলে সই করা চুক্তিটা ভাঙতেই থাকে... স্থায়ী মজুরদের প্রাপ্য আদায় করতে আমরা ব্যর্থ হই, চাইলেই তারা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়।” অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০০৪-০৫ ও ২০১১-১২’র মধ্যে রাজ্যে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার বেড়েছে, কিন্তু শিল্প চলছে প্রধানত ক্যাজুয়ালদের নিয়ে, যাঁদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ আসেনি।
অর্থাৎ কাহিনিটা যত সরল ভাবে পরিবেশন করা হয় তা সে রকম নয়, এর পরতে পরতে জটিলতা। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কে যে পুনর্নির্মাণ ঘটে চলেছে সেখানে পুঁজির প্রতি রাষ্ট্রের নির্ভেজাল পক্ষপাত। যে ভারতে একদা দেশের বিকাশে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে সরকারি ভাবে আলোচনাসভা ডাকা হত, সেখানে আট ঘন্টার মজুরি দিয়ে বারো ঘন্টা খাটানোর বিধি চালু হয়ে গেল কয়েকটি রাজ্যে, অন্যত্রও হল বলে। এই কঠিন সময়ে সমরেশ বসুর শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে-র মতো সৃষ্টির প্রলোভন এড়ানো কঠিন, কিন্তু আমাদের বোধহয় চটজলদি উত্তরের চেয়ে একটু বেশি কিছু চাই। এখন রাজনীতিকে যেমন প্রশ্নবাচী হতে হবে তেমনই বুদ্ধিচর্চাকেও রাজনৈতিক হতে হবে। দুনিয়া জুড়ে মানুষের ওপর অমানুষিকতার বেড়ে ওঠা আক্রমণ শ্রমিক আন্দোলনকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। পথটা কঠিন। শ্রমিক আন্দোলন প্রচণ্ড বাস্তব প্রতিকূলতা ও তত্ত্বগত সঙ্কট, দুই সমস্যার মুখোমুখি। অচিন চক্রবর্তী ও সহযোগীদের কাজটা সে-দিক দিয়ে একটা শিক্ষণীয় শুরুয়াত। একশো তিরিশ বছর আগেকার মে-দিনের সঙ্গে আজকের মে-দিনের যত তফাত থাকুক, তাদের মৌলিক চরিত্র এক: বিশ্বমানবতার স্বার্থরক্ষা। সে-কাজে বাস্তব আন্দোলন ও বুদ্ধির অনুশীলন যত কাছাকাছি আসে ততই মানুষের লাভ।
ঋণ: অচিন চক্রবর্তী, শুভনীল চৌধুরী, সুপূর্ণা ব্যানার্জি, জ়াদ মাহমুদ, লিমিটস অব বারগেনিং: ক্যাপিটাল, লেবার অ্যান্ড দ্য স্টেট ইন কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯
ইমেল-এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।