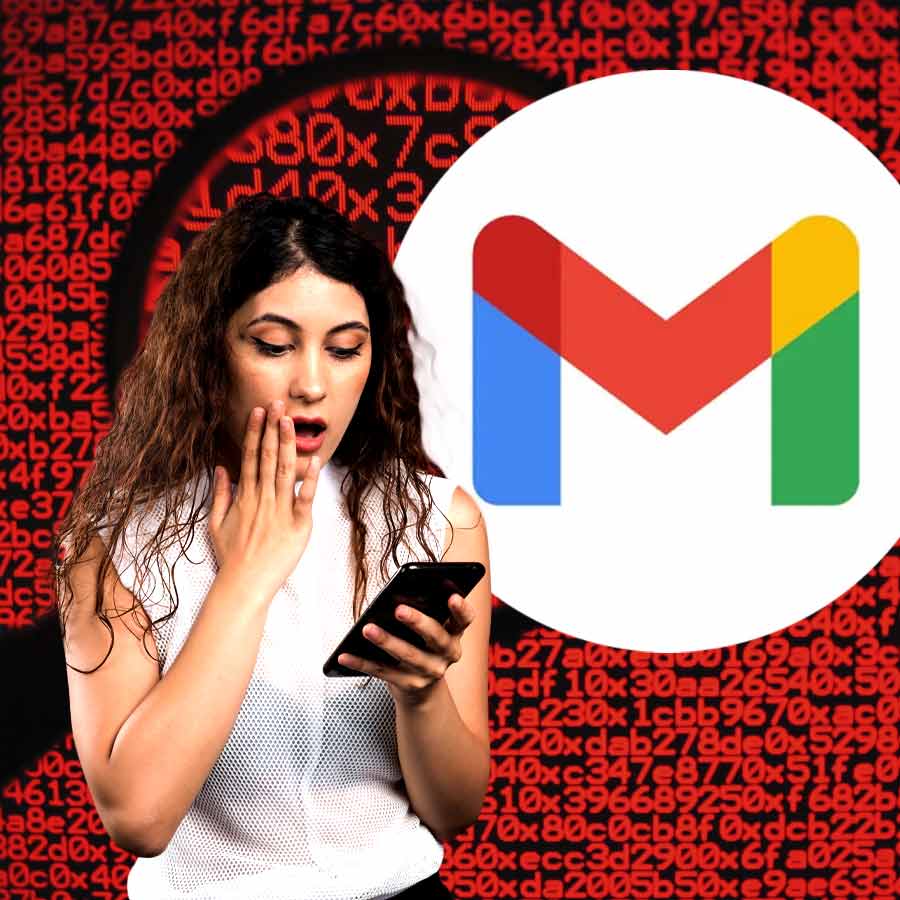গতকাল আলোচনা করেছি জাতীয় শিক্ষনীতির খসড়া ও রূপায়ণের সমস্যা নিয়ে (‘আশ্বস্ত হওয়া গেল না’, ২৭-৬)। বিষয়টি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট: সর্ববিদ্যা সমন্বয়ের কথা বলা হলেও ঝোঁকটা প্রবল ভাবে ভাষা, কলাবিদ্যা ও এক বিশেষ ধরনের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর। কমিটির মাথায় এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তবু, স্কুলশিক্ষার মতোই এখানেও বিজ্ঞান নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ওটার তো দিব্যি রমরমা, আর বাক্যব্যয়ের দরকার কী? বরং তাতে কিছু মানবিক ও সাংস্কৃতিক রসদ ঢোকানো যাক। এর একটা যৌক্তিকতা আছে—আমাদের প্রযুক্তিশিক্ষা যে ভাবে সঙ্কীর্ণ পেশাসর্বস্ব হয়ে পড়েছে তা সমাজের পক্ষে শুভ নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার বিশাল ক্ষেত্রে কি কোথাও কোনও উন্নতি বা উদ্ভাবনের প্রয়োজন বোধ হয়নি?
অন্য রকম উদ্ভাবনের কথা আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন বা ডাক্তারি বিচ্ছিন্ন ভাবে আলাদা প্রতিষ্ঠানের বদলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর আওতায় আনার জোরালো সওয়াল রয়েছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি। যুক্তি আছে বলার, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ‘উচ্চতর’ শিক্ষাদানের সঙ্গে চালু হোক আনুষঙ্গিক কারিগরি ও পরিষেবার প্রশিক্ষণ— একই ক্যাম্পাসে ডাক্তারের পাশাপাশি তৈরি হোক নার্স ও চিকিৎসার যন্ত্রবিদ, কৃষিবিজ্ঞানীর পাশাপাশি কৃষিসহায়ক। সবই সাধু প্রস্তাব, কিন্তু চিকিৎসা কৃষিবিজ্ঞান আইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠ্যবস্তু ও শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে কোনও কথাই থাকবে না?
আমি সাহিত্যের শিক্ষক। ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির এই বিরল গুরুত্বে আমার উৎফুল্ল হওয়া উচিত, কিন্তু হতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এতে বিদ্যার সার্বিক প্রেক্ষাপটে একটা বড় রকম বিকৃতি ঘটছে; ফলে মানবিক বিদ্যাও সরলীকৃত হয়ে পড়ছে, বিনষ্ট হচ্ছে তার নিহিত গুণগুলি। প্রশ্ন ওঠে, এই সুপারিশের উদ্দেশ্য কী? সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য নিখাদ জ্ঞানচর্চা হতে পারে না; লক্ষ্য হবে নাগরিকের মানসিক ও সামাজিক বিকাশ, ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদা মেটানো। কিন্তু ধাপে-ধাপে যত উপরে উঠি, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে গবেষণায়, শুদ্ধ বিদ্যার দিকটা তত গুরুত্ব পায়, পাঠের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে প্রধান লক্ষ্য। আশা রাখতে হয়, একাগ্র বিদ্যাচর্চাই এক ধরনের মূল্যবোধের সঞ্চার করবে।
এইখানেই রিপোর্ট নিয়ে অস্বস্তি। আবার বলছি, এতে অনেক মূল্যবান নীতি ও নির্দেশ আছে; কিন্তু প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য যেন ‘মেন্টাল কন্ডিশনিং’, ছাত্র-শিক্ষকের ভাবনাচিন্তা মায় চরিত্র ও সামাজিক অবস্থান একটা ছাঁচে ফেলা। কিছু ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা সমর্থনীয়, যেমন উচ্চশিক্ষার্থীদের আরও সমাজসচেতন করা। কিন্তু চরিত্রগঠনের এই তরল ফর্মুলা শাসক সম্প্রদায় কী ভাবে প্রয়োগ করবে ভাবলে চিন্তা হয়; একাধারে বিদ্যার জগৎ ও বৃহত্তর সমাজের ক্ষতির আশঙ্কা হয়।
আরও চিন্তার কথা, দেশ জুড়ে সব গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করবে ও তার অর্থ মঞ্জুর করবে এক জাতীয় গবেষণা আয়োগ। অনুমোদনের মানদণ্ড হবে বিষয়টির জাতীয় গুরুত্ব, যা বিচার করবে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে অনেকটা এগিয়েছে— প্রযুক্তিতে ‘ইম্প্রিন্ট’, সমাজবিদ্যায় ‘ইম্প্রেস’ প্রকল্প আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে গবেষণা মঞ্জুরের মূল রাস্তা, আর সেই গবেষণার বিষয় মিলতে হবে পূর্ব-অনুমোদিত তালিকার সঙ্গে। গুজরাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আগেই এমন ফরমান জারি করেছিল; কেরলের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় করেছে সম্প্রতি।
এ ক্ষেত্রে রিপোর্টটি সরকারকে পথনির্দেশ করছে না; সরকারকে অনুসরণ করছে। সারস্বত স্বাধীনতার পূর্বোক্ত সমর্থনে তাই ভরসা কমে যায়। আরও কমে যখন পড়ি উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণযন্ত্র (রেগুলেটরি মেকানিজ়ম)-এর কথা। এর স্পর্শ হবে ‘লাইট বাট টাইট’, সোনার পাথরবাটি; যন্ত্র অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কিন্তু চার-চারটে, চার প্রেক্ষিত থেকে নজর রাখবে। এত যন্ত্র-বেষ্টিত হলে পিষে মরার ভয় থাকে বইকি; অন্তত আওয়াজ আর ধোঁয়ায় ভোগান্তি হবেই।
শেষ প্রসঙ্গে আসি। মানবিক বিদ্যা সচরাচর এতই অবহেলিত যে তার প্রসারের প্রস্তাব শুনলে মাথায় আসে একটা ‘সিনিকাল’ চিন্তা— মনে হয়, কারণটা নিশ্চয় ‘নহিলে খরচ বাড়ে’। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার জন্য কড়ি গুনতে হয়— ছাত্রদেরও, সরকারকেও; কলা শাখার খোঁয়াড়ে অল্প খরচে প্রচুর ছাত্রকে পুরে দেওয়া যায়। আমার বিচারে, বর্তমান রিপোর্টে এই ঝোঁকটার মূল কারণ আর্থিক নয়, তাত্ত্বিক। তবু স্কুল থেকে গবেষণাকেন্দ্র, সব স্তর জুড়ে এত সুপারিশের আর্থিক চাহিদা তো আকাশচুম্বী। তার জোগান নিয়ে কমিটি কী ভেবেছে?
তাঁদের স্পষ্ট মত, এ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্যগুলিরও কম নয়। সে জন্য দীর্ঘকালের দাবি মোতাবেক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ চাই মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৬ শতাংশ; অন্য ভাবে দেখলে, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মোট খরচের ২০ শতাংশ। উপরন্তু শুরুতে এককালীন অনুদান চাওয়া হচ্ছে, সরকারের মোট বাৎসরিক ব্যয়ের ৩ শতাংশ। এত করেও এই চাহিদা মিটবে না, খুঁজতে হবে বেসরকারি লগ্নি; তার অভীষ্ট রূপ হবে জনকল্যাণকর দান বা ফিলানথ্রপি।
বাস্তবটা দেখা যাক। শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল ২০১২-১৩ সালে বাজেটের ৪.৭ শতাংশ, কমতে কমতে ২০১৮-১৯ সালে হয় ৩.৫ শতাংশ। বেসরকারি শিক্ষায়তন, যাতে স্কুলের ৪০ শতাংশ, উচ্চশিক্ষার ৬৭ শতাংশ ছাত্র পড়ে, আইনত চলতে বাধ্য বিনা মুনাফায় সমাজের হিতার্থে। শুনলে লোকে হাসবে। ধর্মীয় ও সমাজসেবী কিছু প্রতিষ্ঠান বাদে অধিকাংশই চলে অঘোষিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে, প্রায়ই কালো টাকার চুম্বক হিসাবে। এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ রিপোর্ট শতহস্ত দূরে রেখেছে, ‘ক্যাপিটেশন ফি’র উল্লেখও নেই। বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আছে, তবে যথেষ্ট নয়। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলির মোট মুনাফা প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। সব সংস্থা সিএসআর-এর আওতায় আসে না; তবু যেগুলি আসে, তাদের মুনাফার ২ শতাংশ ফলপ্রসূ ভাবে শিক্ষা প্রভৃতি হিতকর কাজে খরচ হলে দেশের চেহারা পাল্টে যেত না কি?
আশঙ্কা নিয়েই আলোচনা শেষ করি। রিপোর্টের ফলপ্রসূ ব্যয়বহুল সুপারিশগুলি অর্থাভাবে থমকে না যায়। রূপায়িত না-হয় কেবল কম খরচ বা নিখরচার প্রস্তাব, যাতে শিক্ষার মান বাড়বে না, কিন্তু সমাজের মূল ধারাগুলো অবাঞ্ছিত ভাবে পাল্টে যাবে। (শেষ)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে এমেরিটাস অধ্যাপক
এবার শুধু খবর পড়া নয়, খবর দেখাও। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের YouTube Channel - এ।