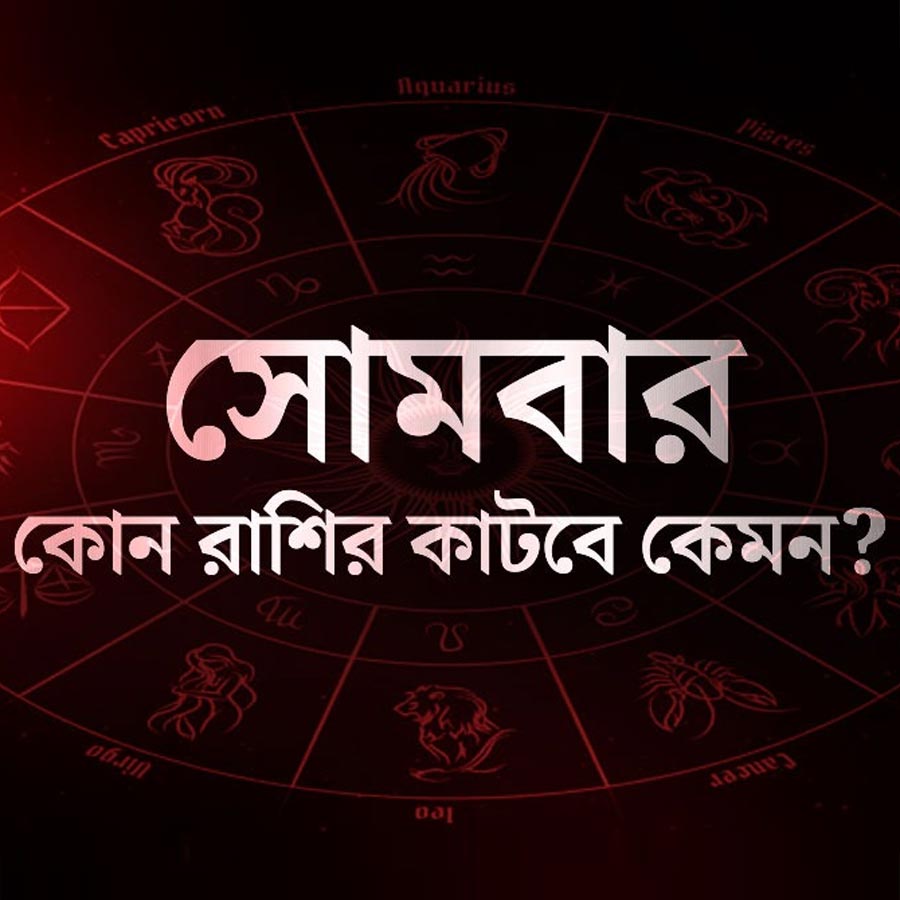ভবিষ্যতের জন্য কি ভারত তৈরি? সে প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না। অন্তত, সম্প্রতি চালু হওয়া ভবিষ্যৎ-মুখী দক্ষতা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সূচক ‘কিউ এস ওয়ার্ল্ড ফিউচার স্কিলস ইন্ডেক্স’-এর মাপকাঠিতে। সূচকের একটি বিভাগে ভারত গোটা দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে আছে— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সবুজ শিল্পের মতো ভবিষ্যতের ক্ষেত্রগুলিতে প্রস্তুতির নিরিখে আমেরিকার পরেই রয়েছে ভারত। সূচকটিতে চারটি মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিল্পের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য; দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের যে দক্ষতার প্রয়োজন হবে তা প্রদানের ক্ষমতা শিক্ষাব্যবস্থার আছে কি না; তৃতীয়ত, যে দক্ষতার চাহিদা রয়েছে বা তৈরি হচ্ছে, সেই মতো নিয়োগের ক্ষমতা কাজের বাজারে আছে কি না; সর্বোপরি, দক্ষতা-চালিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট দেশটি। ১৯০টিরও বেশি দেশ, ২৮ কোটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি, ৫০০০ বিশ্ববিদ্যালয়, ৫০ লক্ষ নিয়োগকারীর দক্ষতার চাহিদা ও ১.৭৫ কোটি গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়েছে এই র্যাঙ্কিং।
একটিতে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও বাকি তিনটিতে পিছিয়ে ভারত। বিশেষত, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে প্রথম ত্রিশটি দেশের সর্বনিম্নে রয়েছে সে। ইঙ্গিত স্পষ্ট— ক্রমপরিবর্তনশীল চাকরির বাজারের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে দেশের কর্মশক্তির একটি বড়সড় ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২২ সালে প্রায় ১০.৩ কোটি দক্ষ কর্মীর চাহিদা ছিল বাজারে। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে প্রায় তিন কোটি কর্মীর ঘাটতি দেখা যায়, যার প্রভাব পড়ে উৎপাদন শিল্প, সেমিকন্ডাকটর, স্বাস্থ্যপরিষেবা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এই ঘাটতি দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করছে, যা বাজারের বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে পারছে না। গত বছর দেশের অধিকাংশ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে দুই-তৃতীয়াংশ আসন খালি থাকার অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন-এর তথ্যই যার অন্যতম উদাহরণ। যদিও, এই সমস্যার অন্যতম কারণ গবেষণা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগের অভাব। বিশ্ব জুড়ে মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের সাপেক্ষে যেখানে এই ক্ষেত্রে ব্যয়ের গড় ১.৯৩%, সেখানে ভারতে তা ০.৬%।
এই সব ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন জরুরি কিছু পদক্ষেপ। যেমন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের চাহিদার সমতা থাকতে হবে। যা অর্জন করা সম্ভব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে। শুধু তা-ই নয়, বদল প্রয়োজন বিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনাতেও। তাত্ত্বিক শিক্ষার তুলনায় জোর দিতে হবে প্রয়োগমূলক শিক্ষার উপরে। পাশাপাশি, দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে উদীয়মান প্রযুক্তি এবং কর্মশক্তির বিবর্তনের উপরেও নজর দেওয়া জরুরি। গবেষণা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে আরও উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে। অন্যান্য দেশের ন্যায়, ভারতের বড় সুবিধা তার নবীন জনসংখ্যা, যারা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে বিশ্ববাজারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্য গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই এ ক্ষেত্রে বাস্তববোধের পরিচায়ক হবে।