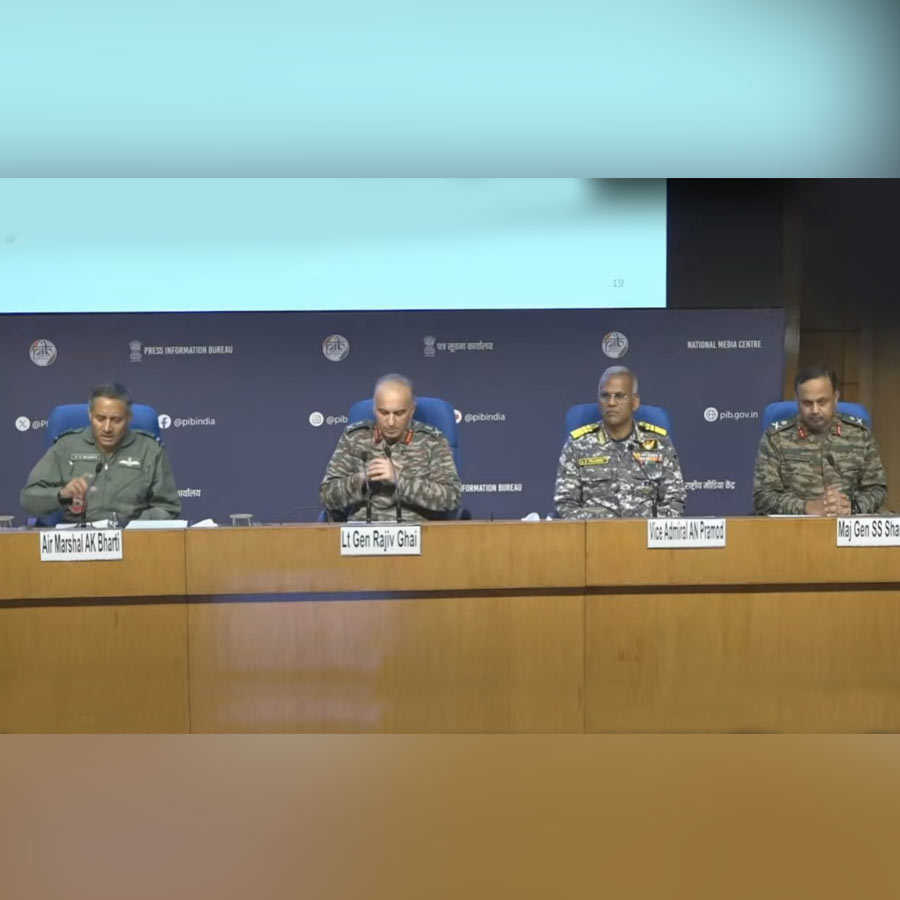বিশ্বযুদ্ধ নয়, অতিমারিও নয়। কেবলমাত্র দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গোটা বিশ্বকে দাঁড় করিয়েছে আরও একটি আর্থিক সঙ্কটের দোরগোড়ায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধের ফলে দুনিয়া জুড়ে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে— বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতির আগাম আশঙ্কায়। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকম। অতিবৃহৎ আর্থিক শক্তিগুলির মধ্যে চিন ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে প্রত্যাঘাতের নীতি; ইউরোপিয়ান কমিশনও আধা যুদ্ধে নেমেছে— তারা আলোচনার দরজা খোলা রেখেই শুল্ক বাড়িয়েছে। আমেরিকার উপরে অতি-নির্ভরশীল ছোট দেশগুলি ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করছে। ভারত এখনও দ্বিধান্বিত, তবে অন্তত স্বল্পমেয়াদে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক নষ্ট করার সাধ্য ভারতের নেই। যে দেশ যেমন প্রতিক্রিয়াই জানাক না কেন, আজকের বিশ্বায়িত জোগান-শৃঙ্খলের যুগে আমেরিকার বর্ধিত শুল্কের প্রভাব সব দেশের উপরেই পড়বে। উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জোগান-শৃঙ্খলের প্রশ্ন বাদ দিলেও, আমেরিকাকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে বাকি বিশ্ব নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য চালিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা অলীক— কারণ, আমেরিকার বাজারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা খোয়ালে সব দেশের পণ্যেরই চাহিদা কমবে। তা অন্য কোনও বাজারে পূরণ হওয়ার নয়। তা ছাড়াও, বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে ভূ-রাজনীতির প্রশ্নও— আমেরিকাকে ছেঁটে ফেললে বিশ্ব-অর্থনীতি আরও বেশি মাত্রায় চিন-নির্ভর হয়ে উঠবে, যা বহু দেশের কাছেই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের মতো দেশ যদি নিজেদের মুদ্রার মূল্য ডলারের সাপেক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করে, তা হলে আমেরিকার বাজারে সে পণ্যের দামের উপরে বর্ধিত শুল্কের প্রভাব পড়বে না; কিন্তু উল্টো দিকে দেশের আমদানির খরচ বাড়বে। অতএব, সে পথটিও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়।
বিশ্ব অর্থনীতির যাত্রাভঙ্গ হয়েছে বটে, কিন্তু ট্রাম্পের নীতিতে আমেরিকার নাকটিও কাটা পড়ল। সে দেশের অর্থব্যবস্থা বহুলাংশে আমদানি-নির্ভর। শুল্ক বাড়ায় আমদানির খরচ বাড়ল, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে পণ্যের দামে। মূল্যস্ফীতি ঘটবে। ফলে, স্বল্পমেয়াদে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ট্রাম্প-প্রশাসনের যুক্তি হল, বাইরের পণ্য আমদানি কমায় আমেরিকার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান এবং বেতনও বাড়বে— ফলে, সাধারণ মানুষ লাভবান হবে। এই যুক্তির গলদ হল, অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানোর মতো পণ্য উৎপাদন করার জন্য আমেরিকান সংস্থাগুলি এখনই প্রস্তুত নয়— উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে তো বটেই, তারও আগে প্রয়োজন অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা। মানুষের আয় ধাক্কা খাওয়ার পরও তাদের ক্রয়ক্ষমতার ভরসায় সংস্থাগুলি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করবে কি না, সে প্রশ্ন অনস্বীকার্য। ফলে আশঙ্কা যে, অন্তত মাঝারি মেয়াদে সে দেশে একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি এবং আর্থিক স্থবিরতা ঘটবে— অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে স্ট্যাগফ্লেশন। আর্থিক বৃদ্ধির হার ধাক্কা খাবে। এই ঘটনার রাজনৈতিক অভিঘাত তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁদের কাজ বিদেশে চালান হয়ে যাওয়া ঠেকানোর অজুহাতে ট্রাম্প এই শুল্কযুদ্ধে নামলেন, এ বার মূল্যস্ফীতি ও বৃদ্ধিহীনতার সাঁড়াশির সামনে তাঁদের ক্ষোভ সামলাবেন কোন অস্ত্রে? এটিই একমাত্র আশার আলো— এই চাপেই ট্রাম্প সংযত হতে পারেন, বা তাঁকে সংযত হতে বাধ্য করা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)