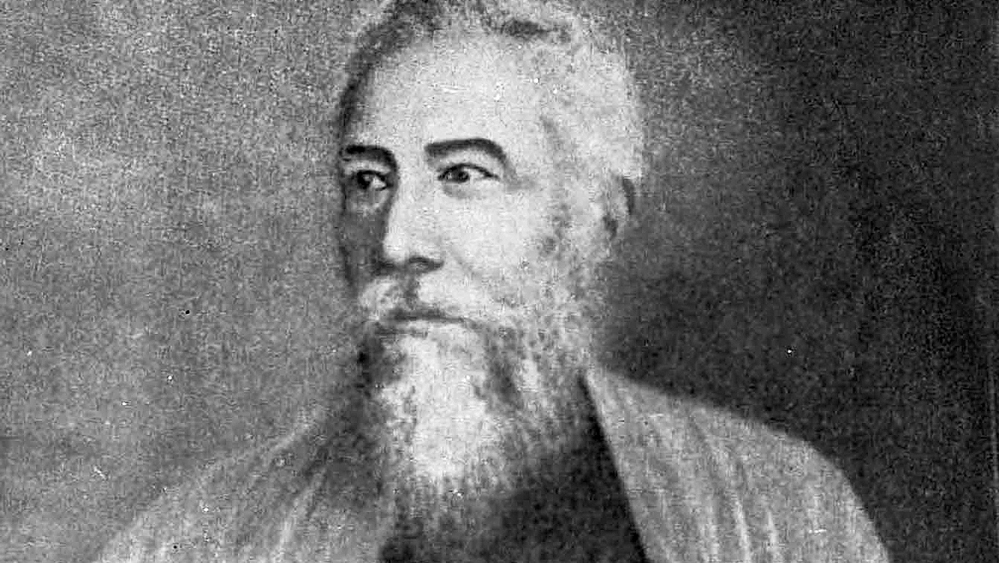চিরশ্রী মজুমদারের ‘ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে’ (পত্রিকা, ২৮-১১) নিবন্ধ সূত্রে কিছু কথা। বিনা বেতনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’। অবশ্য ধর্মশাস্ত্র নিয়েও এখানে আলোচনা হত। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশচেতনার উদ্বোধকও। তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয় ‘ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন’, যা ছিল পরাধীন দেশে মাথা উঁচু করে চলার জন্য রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচারের মঞ্চ। আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত দরখাস্ত প্রেরণ করে মহর্ষি তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও পরিচয় দেন।
পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের যৌবনের সাময়িক উচ্ছলতা, মোহগ্রস্ততা আর বিলাসবৈভবের প্রমোদ-পানসি ডুবে যায়। তার পর থেকে ব্যাকুল হন ব্রহ্মোপাসনায়। উপনিষদ হয় জীবনের আবহসঙ্গীত। পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকর্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। বিষয়কর্মেও ছিলেন যথাযথ।
আদরের রবিকে তিনি নিজে পড়াতেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, ঋজুপাঠ, প্রক্টর লিখিত জ্যোতিষগ্রন্থ। আর তাঁর নিজের পড়ার জন্য ছিল গীতা উপনিষদ-সহ বিভিন্ন গ্রন্থ। এ ছাড়াও ছিল দশ-বারো খণ্ডের বৃহদাকার গিবনের রোমের ইতিহাস। আসলে এক অনাবিল বিশ্বাস ও সম্ভ্রমের উপর দাঁড়িয়ে ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্ক। তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের জীবনের দিগ্দর্শক। এ প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।”
দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিমান, নিত্য উপাসক, ভাবুক। তিনি মহর্ষি। গৃহী হয়েও তিনি ঈশ্বরের নাম করেন। তাই তো ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি পরশমানিক। ঠাকুর তাঁর জীবনকে অভিনন্দিত করেছেন মুক্তকণ্ঠে। বলেছেন— “তুমি জনক রাজার মতো দু’খানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের।” (পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)। এই জন্যই ধর্ম ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথও ছুটে যেতেন জোড়াসাঁকোয়।
এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাতনির কন্যা হেমলতা ঠাকুর (নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) লিখেছেন, বিবেকানন্দ “আসতেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে, আলাপ-আলোচনা করে চলে যেতেন।... আমার মনে আছে, শিকাগো পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকোতে এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন।” (‘পুরোনো কথা’, সাপ্তাহিক দেশ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)।
সুদেব মাল, খরসরাই, হুগলি
দর্শন
‘ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে’ প্রসঙ্গে কিছু কথা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি না। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেন যে, নরেন্দ্রনাথের চোখ দু’টি যোগীর মতো। এ উত্তরে নরেন্দ্রনাথ শান্তি পাননি। ছুটে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। একই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে। উত্তর পেয়েছিলেন, “সেকি গো, দেখেছি বৈকি? এই যেমন তোমাদের দেখছি।”
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যিনি ‘মহর্ষি’ আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র সেন সখেদে এক বার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, “মশাই, বলে দিন কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।” উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, “লোকমান্য, বিদ্যা এ সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হচ্ছে না।” তার পর দিয়েছিলেন অননুকরণীয় উপমা, “ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চিৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।”
সুগত ত্রিপাঠী, মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
বিধবা বিবাহ
সর্বানী গুপ্তের ‘প্রদীপের তলায়’ (১২-১১) পত্র সম্পর্কে কিছু সংযোজন করতে চাই। এটা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীর বিবাহ রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ঘটনার কথা বলে পত্রলেখক কবিকে কটাক্ষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করে লিখেছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পুত্রের সঙ্গে এক বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ বাল্যবিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দিয়েছিলেন। প্রতিমা দেবী ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনীর কন্যা। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় এর ৫ বছর আগে, ১৯০৫ সালে। মহর্ষি জীবিত থাকলে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারত কি না, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে।
সুদীপ বসু, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
রহস্য
দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ (‘শরীরের কষ্ট কখনও ক্লান্ত করেনি তাঁকে’, রবিবাসরীয়, ১-১১) এবং সে বিষয়ে সর্বানী গুপ্তের চিঠির (‘প্রদীপের তলায়’, ১২-১১) প্রসঙ্গে দু’একটি কথা। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী, সাহানা দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবীদের ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ি বহু তথ্য গোপন করেছে, মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে, অন্যায় করেছে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথের নীরবতা। যিনি অন্যায়কারী ও অন্যায়-সহ্যকারী উভয়কেই অপরাধী মনে করেন, যিনি মানুষের অধিকার রক্ষায় সর্বদাই সরব, সেই রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিবারের অন্যায় সম্পর্কে নীরব থেকে গেলেন কেন?
প্রথমেই দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ আসে। শুচিবায়ুগ্রস্ত দিগম্বরী দেবীর প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস থেকে প্রায় মুছে দিতে চেয়েছিলেন। যাঁকে এ কালের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় অন্ত্রপ্রনিয়রদের অগ্রপথিক বলে থাকেন, তাঁরই অর্থে গড়ে তোলা ঠাকুর পরিবারে তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগকে বিদ্যাসাগর পরশ্রীকাতরদের রটনা বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ পিতা বা পরিবারের অন্যদের মুখে পিতামহের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই কি তাঁর সুবিশাল রচনাবলিতে পিতামহকে অল্প একটু স্থানও দিতে পারলেন না? তাঁর এমনই বিরূপ মনোভাব যে, বহু বার ইংল্যান্ডে গিয়েও তিনি উত্তর লন্ডনের কেনসাল গ্রিনে পিতামহের সমাধি দর্শন করতে এক বারও অভিলাষী হলেন না? ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কার-টেগোর কোম্পানির সমস্ত নথিপত্র অগ্নিদগ্ধ করা হয়। পিতামহকে মুছে ফেলার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ একটা যুগের ইতিহাসকেও মুছে ফেলেছিলেন।
কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সেই মৃত্যু রহস্যের উপর কোনও আলোকপাত করেননি তিনি। ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল কাদম্বরীর মৃত্যু হয়। অথচ তার দিন কুড়ির মধ্যে ‘সরোজিনী’ জাহাজে বেড়াতে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতাপশালী পিতার ভয়ে হয়তো তিনি প্রতিবাদ করতে পারেননি। কিন্তু ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথ মুখ খোলেননি।
দিলীপ মজুমদার, কলকাতা-৬০
এই ছবি কেন
‘বিষাইছে বায়ু মেগাসিরিয়াল’ (৩-১২) প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থন করি। কিন্তু যে ছবিটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই সিরিয়ালে ঠিক কোন সঙ্গীত, কোন ককপিট, বিষ আর অপহরণ আছে? যে সিরিয়ালের ইমেজ এ ভাবে নষ্ট করা হল, সেটা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যে সিরিয়ালগুলোর কথা বলা হল, তার মধ্যে কোনও একটার ছবি ব্যবহার করা উচিত ছিল।
ঋত্বিকা দে, ইমেল মারফত
চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।