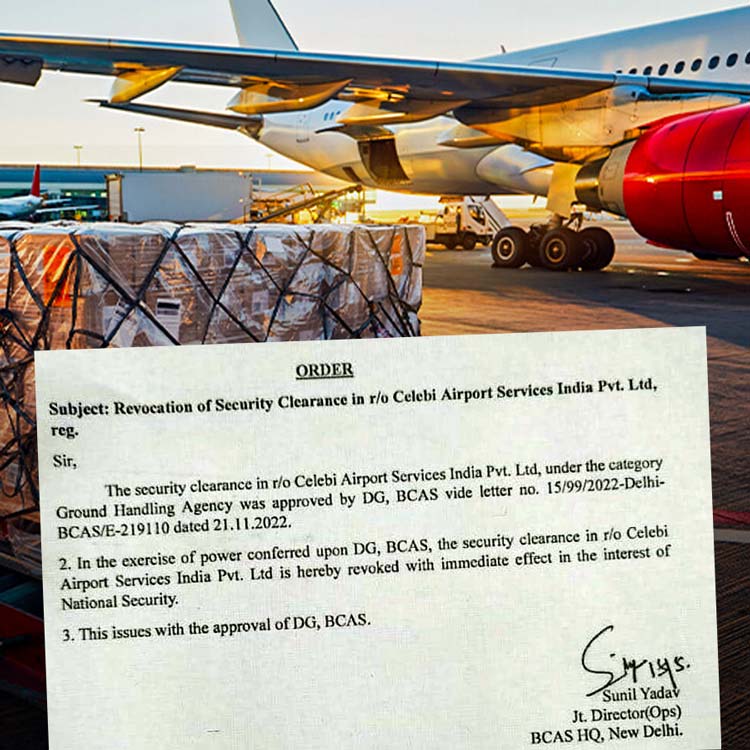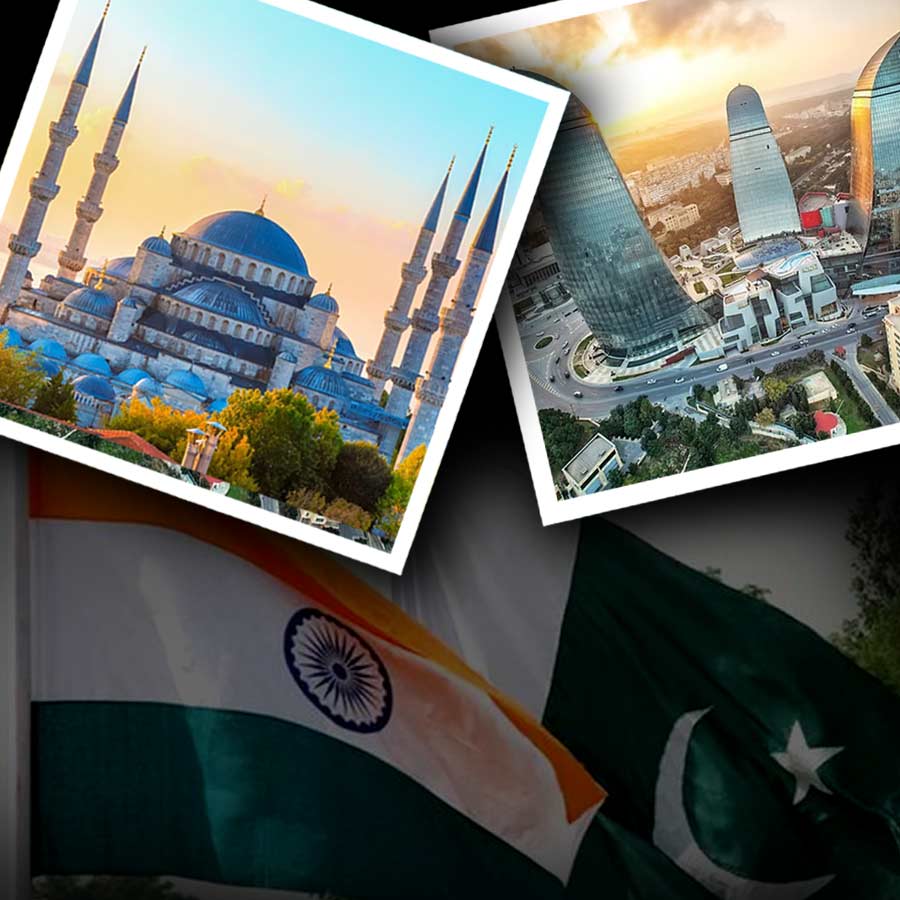এক বন্ধুর কাছে ভারতের এক প্রতিবেশী দেশের কথা শুনছিলাম। তিনি ব্যবসাসূত্রে সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন। কথায় কথায় বললেন, এ বারে একটি পোশাকের কারখানায় গিয়েছিলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর, সেখানে অন্তত কয়েকশো মহিলা সেলাই-মেশিনে কাজ করছেন। খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, সে দেশে চার হাজারের বেশি এমন কারখানা আছে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ কর্মী সেখানে কাজ করেন। মাইনেপত্র বা সুযোগসুবিধা খুব বেশি নয়, কিন্তু সংসার চালাতে এই কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।
শ্রমজীবীদের, অর্থাৎ যাঁরা কৃষি, শিল্প বা পরিষেবাক্ষেত্রে চাকরি বা শ্রমদান করেন, তাঁদের জন্য স্থিতিশীল এবং ভাল আয় নিশ্চিত করা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। মোট জাতীয় আয় বা জিডিপি-তে তাঁদের অবদানকে বলা হয় ‘লেবার শেয়ার অব জিডিপি’। অন্যরা আয় করেন মূলধন বিনিয়োগ করে। বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে দেখা যাচ্ছে, এই লেবার শেয়ার ভারত-সহ অনেক দেশেই কমছে।
লেবার শেয়ার অব জিডিপি গুরুত্বপূর্ণ কেন? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জাতীয় আয়ে উৎপাদন শিল্পের অবদান কমলে লেবার শেয়ার কমে। কারণ সহজবোধ্য। অটোমেশন সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় উৎপাদন শিল্পে সর্বাধিক কর্মসংস্থান হয়। তবে এই সম্পর্ক পুরোপুরি সরল নয়।
২০১০-২৩’এর মধ্যে এশিয়ার অধিকাংশ দেশে জাতীয় আয়ে উৎপাদনের অবদান কমেছে। ২০১০-২৩’এর মধ্যে জাতীয় আয়ে উৎপাদন শিল্পের অবদান ভারতে চার শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় তিন শতাংশ, কোরিয়ায় চার শতাংশ ও তাইল্যান্ডে ছয় শতাংশ কমেছে, অন্য দিকে ভিয়েতনামে ছয় শতাংশ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু দেশ লেবার শেয়ার অব জিডিপি ধরে রাখতে পেরেছে। কোনও কোনও দেশে উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধির হার যত কমেছে, শ্রমিকদের আয় তার থেকে বেশি বেড়েছে। কোরিয়ায় ‘মিনিমাম ওয়েজ’-এর ব্যবস্থা এখানে স্মরণযোগ্য। আসলে লেবার শেয়ার দেশের উৎপাদন কাঠামো, শ্রম বাজার, বিশ্বায়ন, শেয়ার মার্কেট, প্রযুক্তি ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। এগুলিরও আবার পারস্পরিক নির্ভরতা আছে। কিন্তু এগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, বা উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধির হার কী ভাবে বাড়ানো যায় তা তো বিশদ আলোচনার ব্যাপার, আপাতত জাতীয় আয়ে লেবার শেয়ারের হার কমে যাওয়ার তাৎপর্য নিয়ে কিছু কথা।
দেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ শ্রমজীবী। তাই মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, জাতীয় আয়ে লেবার শেয়ার কমলে দেশে আয়-বৈষম্যও বাড়বে। ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ডেটাবেস-এর ভিত্তিতে লেখা সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে (‘ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথ ইনইকোয়ালিটি ইন ইন্ডিয়া, ১৯২২-২০২৩: দ্য রাইজ় অব দ্য বিলিয়নেয়ার রাজ’; ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব, ওয়ার্কিং পেপার ০৯/২০২৪) দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮০ সাল অবধি দেশে অসাম্য একটানা কমেছে, কিন্তু ২০০০ থেকে আবার হুহু করে বেড়েছে। ২০২২-২৩’এর পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশের কাছে জাতীয় আয়ের ২২.৩% এবং মোট সম্পদের ৪০.১% কেন্দ্রীভূত ছিল। দেশের অর্থনীতিতে এর ফল সুদূরপ্রসারী।
আয় বৈষম্যের সঙ্গে বৃদ্ধির সম্পর্ক এখনও নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। মোট চারটি সম্ভাবনা: এক, দু’টি বিষয়ের সম্পর্ক নেগেটিভ, অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটি কমে; দুই, সম্পর্ক পজ়িটিভ, অর্থাৎ দু’টিই এক সঙ্গে বাড়ে বা কমে; তিন, ‘কোনও সম্পর্ক নেই’; এবং চার, সম্পর্ক আছে, কিন্তু তার চরিত্র বিষয়ে ‘নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না’। এ দেশে কী হতে পারে? প্রাথমিক ভাবে তিনটি কার্য-কারণ সংযোগসূত্র চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত, দেশে উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদের পার্থক্য খুব বেশি হলে নানা সামাজিক সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে, ঘন ঘন ধর্মঘট ও কর্মবিরতি হয়। এতে শ্রম দিবস নষ্ট হয়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে এবং বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও, ২০২৩ সালে (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত), সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মঘট ও লকআউটের কারণে মোট ‘মানব-দিন’ হারিয়েছে ৩.৪ লক্ষ। দ্বিতীয়ত, আয়-বৈষম্য বাড়লে সামগ্রিক সঞ্চয় বাড়ে, কারণ ধনীদের প্রান্তিক আয় থেকে সঞ্চয়ের প্রবণতা তুলনায় বেশি। একই সঙ্গে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের আয় বাড়লে সামগ্রিক ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ তাঁদের প্রান্তিক আয় থেকে ভোগের প্রবণতা ধনীদের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ চাহিদা বাড়ে।
আমাদের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ চাহিদার অভাব ধরা হয়। দেশের উপভোক্তাদের একটা বিরাট অংশ গ্রামে থাকেন। তাঁদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা সে ভাবে না বাড়ার ফলে গ্রামে চাহিদা বাড়ছে না, অন্য দিকে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ভোগব্যয় কমছে। অটোমোবাইল শিল্প এবং কিছু সর্বজনীন ভোগ্যপণ্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২০২২-২৩’এর হাউসহোল্ড কনজ়াম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে-তে তে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক খাতে গ্রামের মানুষেরা ৬৩.৫% ব্যয় করেন। শহরে এর অনুপাত ৫৬.৫%। আয়-বৈষম্য বাড়লে বিভিন্ন শ্রেণির ভোগ্যপণ্য খাতে ব্যয়ের উপর ঠিক কী প্রভাব পড়বে তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অত্যাবশ্যক খাতে প্রয়োজন মেটানোর পর যে টাকাটা বাঁচে তা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য খুব বেশি নয়। অবশ্যই রফতানি কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারে।
তৃতীয়ত, আয়-বৈষম্য বাড়লে ক্ষুদ্র ও মাঝারি/অতিক্ষুদ্র উদ্যোগকারীদের পক্ষে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের সংস্থান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে তথ্যের স্বচ্ছতা না থাকলে উভয় পক্ষের জন্যই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়। এ ছাড়া আইনি জটিলতার জন্য ঋণদাতার পক্ষে অনেক সময়ই বকেয়া ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় না, এবং সম্ভাব্য ক্ষতির কথা মাথায় রেখে তারা ঋণ পাওয়ার জন্য কঠিন শর্ত আরোপে বাধ্য হয়। এর ফলে বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়, বিনিয়োগ ও বৃদ্ধির হার কমে।
সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আর্থিক বৈষম্য আর উৎপাদনের বৃদ্ধির হার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আর এই দুই-মুখী সম্পর্ক নির্ভর করছে বহুলাংশে জাতীয় আয়ে শ্রমের অবদানের উপর। আয়-বৈষম্য হ্রাস না হলে, উৎপাদনের স্থিতিশীল বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। সেই কারণেই জাতীয় আয়ে শ্রমের অবদান বৃদ্ধি জরুরি। এটি একটি জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা, তার সমাধানসূত্রও খুব সহজলভ্য নয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধীশক্তি কাজ করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।
তবে একটি সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া যেতে পারে। অতি উচ্চবিত্তদের (হাই নেট ওয়র্থ ইন্ডিভিজুয়ালস) বেশি করে প্রত্যক্ষ করের আওতায় এনে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার।
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ফিলিপিনস
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)