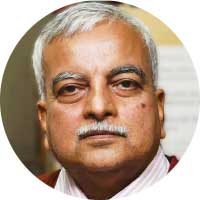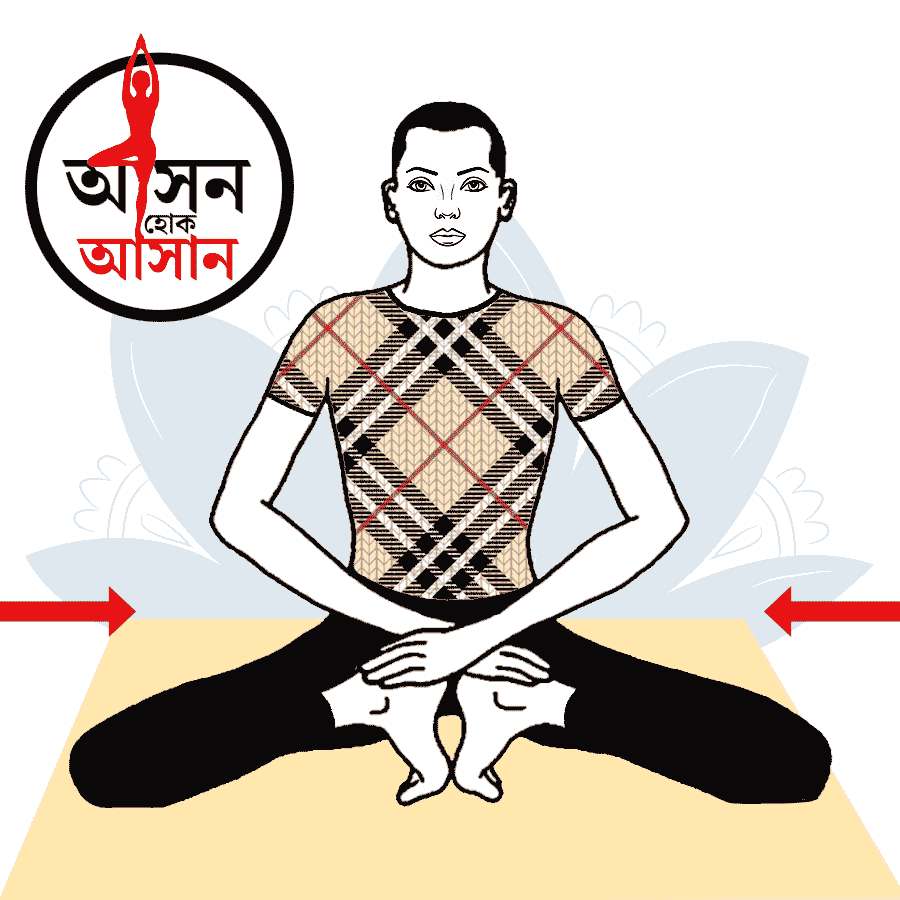১
কিশোরটি পরিবারের সঙ্গে রাজস্থান গিয়েছিল বেড়াতে। অনেক কিছুই দেখেছিল সে। কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছিল এক মন্দিরের কারুকার্য। অনেক কিছু ভুলে গেলেও মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের কথা ভুলতেই পারেনি। রাজস্থান থেকে ফিরে খাতায় আঁকিবুকি করত। ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত সেই মন্দিরের কারুকার্য।
কে জানত বড় হয়ে ওই ছেলেটিকেই দিলওয়ারা মন্দিরের চাতালে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে দিনের পর দিন ওই মন্দিরের পিলারের নকশা তুলতে হবে!
কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টের ছাত্র পড়াতেন। পাশাপাশি, পাড়ার পুজোয় মণ্ডপ সাজাতেন। কখন যে পড়ানোর নেশা ঘুচে মণ্ডপ সাজানোই নেশা হয়ে গেল, বোঝাই গেল না। কস্ট অ্যাকাউন্টের মাস্টারমশাই হয়ে গেলেন থিমশিল্পী। ১০ বছর পাড়ার পুজোয় হাত পাকিয়ে ২০০১ সালে পাড়া থেকে বেরোলেন তিনি। লেক গার্ডেন্সের পাড়ার শিল্পীটিকে মণ্ডপসজ্জার ভার দিল অভিজাত যোধপুর পার্ক সর্বজনীন পুজো কমিটি। পেশাগত থিমশিল্পী হিসাবে সেটাই প্রথম কাজ দীপক ঘোষের। প্রথম বছরের কাজ প্রশংসিত হলেও, দ্বিতীয় বার (২০০২) ওই পুজো কমিটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দীপকের মণ্ডপ জিতে নিল সব পুরস্কার। নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশের বাইরেও।
২০০২ সালে কী এমন করেছিলেন দীপক?
মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরটা যেন যোধপুর পার্কে তুলে এনেছিলেন থার্মোকলের বিশ্বকর্মা। আর তার জন্যই তাঁকে দিলওয়ারা মন্দিরের চাতালে বসে টাকা ছ’দিন ধরে আঁকতে হয়েছিল মন্দিরের বিভিন্ন নকশা। প্রতিটি খিলান, প্রতিটি স্তম্ভ, ছাদের নকশার ছবি তুলে আনবেন বলে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। ছেলেবেলার কিছু কিছু মনে ছিল। মনে ছিল, মাসি সকলের ছবি তুলেছিলেন কম দামি ক্যামেরায়। তবে সেখানে মন্দিরের কারুকার্য নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছবি তোলা হয়েছিল। ওই সব ছবি থেকে মানুষের মুখ খুঁজে পেয়েছেন, মন্দিরের একটি নকশাও পাননি দীপক। তাই নকশার খোঁজে ফের হানা মাউন্ট আবুতে। সঙ্গী সহ-শিল্পী শম্ভু।
মন্দিরে পৌঁছে দীপক বাইরে বড় ঘোষণা দেখে হতবাক, ‘‘মন্দিরের ভিতরের কোনও ছবি তোলা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।’’ মাথায় বাজ পড়ল। কুছ পরোয়া নেই, শম্ভু আর কাগজ-পেন্সিল নিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঘুরতে লাগলেন। নকশা পছন্দ হতেই বসে পড়লেন চাতালে। পেন্সিল দিয়ে সেই নকশা আঁকা শুরু হল। এসেছিলেন দু’দিনের জন্য। থেকে যেতে হল সাত দিন। তবে দুটো সুবিধা হল, প্রথমত, পছন্দের নকশাগুলিকে এঁকে নেওয়ায় তা মাথায় গেঁথে গেল। আর দ্বিতীয়ত, ছবি দেখে ফের আঁকার পরিশ্রমটা লাঘব হল।
কোনও একটা মণ্ডপ গড়ে ওঠার পিছনে কিন্তু এমন এক একটা গল্প থাকে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি যখন আমরা যখন পুজো কভারেজ নিয়ে সর্বাত্মক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তখন দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুরে ভবানীপুর দুর্গোৎসব সমিতির কর্তা উৎপল রায় জোরকদমে থিমের পুজো শুরু করে দিয়েছেন। পাটের মণ্ডপ, এয়ার কন্ডিশন্ড মণ্ডপ, টেরাকোটার মণ্ডপ তখন ভীষণ ভাবে দর্শক টানছে। পুজোর চালচিত্রটাই বদলে দিতে চাইছেন উৎপল। আমরা একটা পুজো শেষ হওয়ার পরে আমরা অপেক্ষা করতাম, পরের পুজোয় কি উপস্থাপনা করেন তিনি। সেই সময় ভবতোষ, সুশান্ত, অমরদারা সে ভাবে পুজোয় আসেননি। তাই চমকের জন্য উৎপলের উপরেই অনেকটা নির্ভর করতে হত।
এক বার গরমকালে উৎপল সপরিবারে দক্ষিণ ভারত ঘুরতে গেলেন। আমার মন বলছিল, এ বার দক্ষিণ ভারত থেকেই নিশ্চয়ই কোনও থিম তুলে আনবেন তিনি। ফেরার পথে আমি দেখা করতে গেলাম ওঁর সঙ্গে। দেখালেন, সিগারেটের প্যাকেটে পেন দিয়ে এঁকে এনেছেন কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ মন্দিরের কিছু অংশ। এঁকে এনেছেন আশপাশের দৃশ্যপট। সেগুলি পর পর সাজিয়েই সে বারের পুজোয় মণ্ডপ গড়েছিলেন শিল্পী।
একটা সময় ছিল যখন এক পুজোর হ্যাপা সামলে কর্মকর্তারা সম্ভাব্য শিল্পী ও তাঁর পরিবারের লোকেদের নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। ‘বিজনেস ট্রিপ’। সেখানে রথ দেখাও হত, কলা বেচাও। শিল্পী হয়তো এমন কোনও লোকেশন খুঁজে পেলেন, যার দৃশ্যপট তুলে আনা যাবে মণ্ডপে। ফিরে আসার পথেই পুজোর প্রাথমিক নকশা তৈরি হয়ে যেত। সম্ভাব্য বাজেটও। শিল্পী নিজের স্টুডিয়োতে কাজ শুরু করে দিতেন। কর্মকর্তারা বাজেট অনুযায়ী অর্থ সংস্থানের উপায় খুঁজতেন। পুজোয় দেখা যেত, শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে কোথাও শৈলশহর, কোথাও একখানি আদিবাসী গ্রাম, কোথাও আবার দেবস্থান। দেশভ্রমণের ফসল।
থিমের পুজোর শুরুতে বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্প ঠাঁই পেতে শুরু করল মণ্ডপে। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বর্ধমানের কাঠের শিল্প, ফুলিয়ার তাঁত, দিনাজপুরের মুখোশ, মেদিনীপুরের মাদুর আর পটচিত্র হয়ে দাঁড়াল মণ্ডপসজ্জার অন্যতম প্রধান শিল্প। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হল বাউল নাচ, ভাদু, টুসু, ছৌ, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালিকে যুক্ত করে মণ্ডপ তৈরির ভাবনা। বাংলা ছেড়ে শিল্পীরা পা রাখতে শুরু করলেন ভিন্রাজ্যে। ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম, গুজরাত, রাজস্থান, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর কেরল— একে একে ওই রাজ্যের রেপ্লিকা হয়ে উঠল মণ্ডপ। সারা দেশের লোকশিল্পীরা পুজোর তিন মাস আগেই ভিড় জমাতে শুরু করতেন কলকাতায়। শিল্পীরা পকেট ভর্তি টাকা, নির্ভেজাল আতিথেয়তা আর বেশ কয়েকটি বাংলা শব্দ ও বাক্য শিখে পাড়ি দিতেন নিজের বাড়িতে। তাঁদের অনেককেই কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলিতে দেখা বছরের পর বছর। বংশ পরম্পরায় কলকাতার পুজো মণ্ডপে ফুল ফোটাচ্ছেন এমন শিল্পীও খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে।
আরও পড়ুন:
২
এক বড় শিল্পী। বেশ কয়েক বছর কাজ করছেন এমন একটা ক্লাবে, যার সদস্যদের অর্থবল যাই থাক না কেন, আন্তরিকতা আর মানবিক গুণে তাঁরা অনেক অনেক বড়।
এক বার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বেহালা ভেসে গিয়েছে। সেই সময়টা (১৯৯৫-২০০৫) শুধু কলকাতার পুজোর নয়, মহানগরীর সমাজ জীবনেও একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ শহরতলি আর দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার। পুকুর-ডোবা সেখানে যা ছিল সব বুজিয়ে ধাঁই ধাঁই করে বাড়ি উঠতে শুরু করেছে। একতলা-দোতলা নয়, চারতলা-পাঁচতলা। একটা যুৎসই নামও হয়েছে বহুতল। জন্ম নিয়েছে একটা নতুন পেশা-প্রমোটারি। পাড়ার দাদা আর রাজনৈতিক নেতাদের বিনা শ্রমে পকেট ভরার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা হয়েছে।
এই সামাজিক পরিবর্তনের একটা বড় কারণ অবশ্য আছে। সেই সময় যৌথ পরিবারের কনসেপ্ট ভেঙে মাইক্রো পরিবারের কনসেপ্টে ঢুকে পড়েছে বাঙালি। বিশাল বারান্দাযুক্ত বড় প্রকোষ্ঠের বাড়ির বদলে বাঙালি পছন্দ করতে শুরু করেছে দেশলাই বাক্সকে। বাতাস চলাচল করে না। পেট রোগা বাঙালির ফুসফুসে শুদ্ধ বাতাস ঢোকার রাস্তাও ওই দেশলাই বাক্সের মতো ফ্ল্যাটে গিয়ে অনেকটাই কমে গেল। তবু একা একা স্বাধীন ভাবে থাকার নেশায় বাঙালি বুঁদ। এর পাশাপাশি বৃদ্ধাবাসের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকল। মাইক্রো ফ্যামিলিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ঠাঁই হবেই বা কী করে?
আর এই পরিস্থিতিতে পুজোর কনসেপ্টের পরিবর্তনটাও লক্ষনীয়। বড় মণ্ডপ, বড় ঠাকুরের পরিবর্তে কমপ্যাক্ট পুজো।
যে পুজোটাকে নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেখানে ফিরে যাই। পুকুর-ডোবা বুজে গিয়ে বেহালায় তখন একটু বৃষ্টি পড়লেই থৈ থৈ জলে অকূল পাথারে পড়ত মানুষ। আমি নিজে দেখেছি, তাদের শিল্পী সপরিবারে জলবন্দি হয়ে পড়েছেন শুনে হরিদেবপুরের ক্লাবটি কী ভাবে সর্বাত্মক ভাবে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে। স্ত্রী আর শিশু কন্যাকে নিয়ে তখন ‘পাগল পাগল’ অবস্থা ওই শিল্পীর। যাঁর হাত ধরে বেহালার কয়েকটি ক্লাবের মতো হরিদেবপুরের ক্লাবটিও ‘থিম’ পুজোয় গা ভাসিয়েছিল। নিজেদের কৃতজ্ঞতা এ ভাবে প্রকাশের নজির এখন আর খুঁজে পাবে কি পুজোর কলকাতা?
অজেয় সংহতি নামের ওই ক্লাবটি দুঃস্থ পরিবারের কোনও প্রতিভাবান ফুটবলার দেখলে তাদের তুলে আনত। নিজেদের ক্লাবে রেখে, অন্য কারও বাড়িতে রেখে তাদের প্রশিক্ষণ দিত। এই ভাবে এই ক্লাবেই অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে কলকাতা ময়দানের বেশ কিছু ফুটবলার, ফুটবল কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতা। অনেকে অতীতের পরিচয় ভুলে গিয়েছেন। কেউ ভীষণ ভাবে অতীতকে আঁকড়ে আছেন। নতুন নতুন ফুটবলার তৈরির পাশাপাশি থিম পুজোয় কিছু করে দেখানোর তাগিদে ময়দানে নেমে শতকরা ১০০ ভাগ সফল হরিদেবপুরের ক্লাবটি। যার প্রধান কান্ডারী ওই শিল্পী আর ক্লাবটির সংগঠন।
প্রথম প্রথম জানতাম ওটা কল্লোল-হিল্লোল নামে দুই খেলাপাগল যুবকের ক্লাব। পরে গিয়ে দেখলাম ওই দুই ভাইয়ের মতো অতি উৎসাহীর সংখ্যা কম নয় সেখানে। অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাস্টারমশাই— কে নেই সেখানে! মাথার উপরে রয়েছেন পাকা মাথার এক সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। পাকা মাথার ওই তুখোড় ইঞ্জিনিয়ার আর বসু পরিবারের দুই ভাই কল্লোল-হিল্লোলই মূল চালিকাশক্তি।
পুজোর বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই বেহালায় পুজোর প্রস্তুতি দেখে অনেক রাতে ওই পুজোটা ঘুরে বাড়িতে ফিরতাম। ওই ত্রিমূর্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। এক বার মাটি আর আলোয় মিশিয়ে থিম করল ওরা। আমি রাতে গেলাম। প্রতিমা চলে এসেছে মণ্ডপে। শুধু খড়ের উপরে মাটি লেপা হয়েছে। মুখ বসানো হয়েছে। আমি প্রতিমার ওই রূপ দেখেই স্তম্ভিত। কাগজেকলমে এবং যে রকম প্রচার হয়েছিল, তাতে অনেকেরই মতো আমারও মনে হয়েছিল থিমশিল্পী নিজেই প্রতিমা গড়েছেন। হোর্ডিং বা ব্যানারেও প্রতিমাশিল্পী বলে আলাদা করে কারও নাম ছিল না। আমি অবাক হয়ে ওই প্রতিমা দেখছিলাম। থিমশিল্পী নিজেই গড়েছেন এমন প্রতিমা! আমার সংশয় বাড়ছিল। ক্লাবেরই এক জন উপযাজক হয়ে এগিয়ে এলেন, ‘‘বর্ধমান থেকে আজই নিয়ে এলাম প্রতিমা। আর যে কুমোর বানাচ্ছে, সে-ও এসেছে।’’
কোথায় সেই কুমোর? প্রতিমার পিছনে খড়ের গাদায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকা এক বেঁটে খাটো, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, একগাল দাড়িওয়ালা যুবককে আমার কাছে হাজির করানো হল। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘আপনি প্রতিমাটা গড়ছেন?’’ বর্ধমানের যুবকটি বললেন, ‘‘আমার বাবা প্রতিমা গড়েন। আমি আর ভাই সাহায্য করি।’’ এখন তো প্রতিমার চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে। চোখ আঁকতে হবে। বাবা আসবেন বর্ধমান থেকে? সলজ্জ জবাব এল, ‘‘ওখানে অনেক কাজ আছে। এই প্রতিমাটি আমাকেই শেষ করতে হবে।’’
এর পর রোজ রাতে আমি হাজির হতাম অজেয় সংহতির নির্মীয়মান মণ্ডপে। ওই প্রতিমাই আমাকে টেনে আনত। আমার সে বারের পুজোর আবিষ্কার, তুরুপের তাস আমি আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। চোখ যে দিন আঁকা হল, আমি স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে। চোখ, হাত, হাতের আঙুল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কি না তা দেখার দারুণ চোখ ছিল আমার স্ত্রীর। আমার স্ত্রীও প্রতিমাটি দেখে অভিভূত। পর দিন কাগজে তাস বার করে দেখালাম। ষষ্ঠীর দিন পুজোর উদ্বোধনেই ভিড় উপচে পড়ল মণ্ডপে। মায়ের মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল, চাঁদের হাসি যেন বাঁধ মানছে না। আর তা হবেই না কেন, প্রতিমা গড়েছেন যে পূর্ণ ইন্দু স্বয়ং। কলকাতার পুজোয় তিনি যে অনেক কিছু দিতে এসেছেন, তা প্রথম বারেই বুঝিয়ে দিলেন বর্ধমানের পূর্ণেন্দু দে। এ যেন খড়চাপা আগুন।
ভাগ্যিস কলকাতার থিম পুজোর অন্যতম স্রষ্টা অমর সরকার নিয়ে এসেছিলেন পূর্ণেন্দুকে। না হলে বর্ধমানের এই ছেলেটিকে কে-ই বা চিনত! আর শুধু পূর্ণেন্দু কেন, অজয় সংহতিতে অমরদার হাতে হাতে কাজ করতে করতে অনেক আধ-শিল্পীই পরবর্তী সময়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। গুরুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কলকাতার থিম পুজোর দ্রোণাচার্য তাঁর ওই কীর্তিতেই কিন্তু ‘অমর’।
৩
ছোট্ট এক চিলতে ঘর। হাওয়া ঢোকা বেরোনোর রাস্তা নেই। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটা গ্যাসের বার্নার। বার্নারের সামনে নির্মীয়মান মাতৃপ্রতিমা। মাটির সাঁচের উপরে দেওয়া হবে গালার প্রলেপ।
ঘরে উপস্থিত পাঁচ পুরুষ ধরে গালার পুতুলের কাজ করা পুরুলিয়ার এক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। কলকাতার দুর্গাপুজোয় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশী এক তরুণ ভাস্কর।
তৃতীয় জন তার ভাই। দাদার ছায়ায় থেকে কাজ শিখে নিতে আগ্রহী সে।
বেহালার যে পুজোর জন্য এই অধ্যাবসায়, তার দু’জন কর্মকর্তা-সহ সেখানে উপস্থিত আমিও। কাজটা কী ভাবে হচ্ছে তা জানার অদম্য ইচ্ছায় বেহালার গলি, তস্য গলিতে শিল্পীর স্টুডিয়োতে আমার পদার্পণ। বেহালার ওই পুজোর দৌলতে পুজোর বাজারে দাম চড়তে শুরু করেছে ওর। কিন্তু কোঁকড়া চুলের ওই শিল্পীর ও সবে কান দেওয়ার সময় নেই। গালার প্রতিমায় চক্ষুদানে মগ্ন হয়ে আছে সে।
গালার খণ্ড আগুনে পুড়িয়ে গলন্ত লাভার টুকরো চিমটে দিয়ে ধরে সেটিকে তুলির মতো ব্যবহার করছিল সে। ফুটন্ত লাভার টপ টপ করে পড়ছে শিল্পীর হাতে ও পায়ে । তাতে কিন্তু চোখ এতটুকুও সরেনি প্রতিমার চোখের তারা থেকে। চক্ষুদান যখন শেষ হল তখন পুবের আকাশ লাল হচ্ছে। তরুণ শিল্পীর চোখেমুখে ঠিকরে বেরোচ্ছে আলো। সফল হওয়ার তৃপ্তি মাখানো সেই চাউনি।
পুরুলিয়ার পোড় খাওয়া গালা শিল্পীও পরিতৃপ্ত। তরুণ শিল্পীকে জড়িয়ে ধরলেন। ওই তরুণ শিল্পী তত ক্ষণে বুঝতে পেরেছে, তার হাতে ও পায়ে জমে আছে গালা। একমাত্র গরম কোনও ধাতু দিয়েই তা গলিয়ে নিতে হবে। তার পরে চটপট কাপড় দিয়ে মুছে তুলে ফেলতে হবে গলে যাওয়া গালা।
নিষ্কৃতি মিলবে একমাত্র তাতেই। সেটা আরও যন্ত্রণাদায়ক।
গালা গলে গলে যখন হাতে পায়ে পড়ছিল তখন সৃষ্টির নেশায় তা বুঝতে পারেনি শিল্পী। তোলার সময়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল।
সে বারের পুজো ওই অসামান্য একটা শিল্প সৃষ্টির স্বীকৃতিও পেয়েছিল তরুণ শিল্পীটি। কিন্তু ওই শিল্পকর্মটির কতটা অধ্যাবসায় কতটা যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল তা মানুষের অজানা।
তার পর থেকে ওই তরুণ শিল্পীর উত্থান হয়েছে উল্কার মতো।
কিন্তু যে ক্লাব তাকে প্রথম কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল, তাদের সে ছাড়তে চায়নি।
এক দিন ওই ক্লাবটি পাশের একটি ক্লাবের সঙ্গে মিশে গেল।
ওই শিল্পী তখন মুক্ত। তাকে নিয়ে শুরু হল বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে দড়ি টানাটানি। সেই সঙ্গে লাফিয়ে বাড়তে লাগল তার পারিশ্রমিকও। তার সান্নিধ্যে থেকে তৈরি হতে লাগল আরও নবীন শিল্পীরা। প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ‘ঘরানা’ তৈরি করতে সক্ষম হল আমাদের গল্পের নায়ক ওই শিল্পী।
প্রতিমার মুখ দেখেই বলে দেওয়া যেত সেটা ওই শিল্পীর সতীর্থ কেউ কিংবা তাকে কাছ থেকে কাজ করতে দেখা অথবা ওর সঙ্গে একই গুরুর কাছে কাজ শেখানোর কারও কাজ।
শিল্পীদের মধ্যে শেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা তখন বেশ বাড়ছে।
এক জন শিল্পী তার সমবয়সি কিংবা বড় কোনও শিল্পীর কাজকে কদর না করার সংস্কৃতি তখন এসে গিয়েছে পুজোর আবহে।
বেহালার যে ক্লাবটিতে কাজ করে ওই শিল্পীর উত্থান, সেখানে এক বার থিম ছিল নৌকা। এক রাতে সেই মণ্ডপে বসেছিলাম আমরা। সময়টা মহালয়ার আশপাশে হবে। ওই শিল্পী তখন মণ্ডপে ছিলেন না। আমরা তার সহ-শিল্পীদের ‘ফিনিশিং টাচ’ দেখছিলাম কৌতূহল নিয়ে।
একটা সময় শিল্পী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। আমাকে দেখেই বলল, ‘‘একটা মণ্ডপ দেখে এলাম বটে! দেবদূতদা তুমি এক বার ঘুরে এসো।’’ সত্যিই সেই কাজটা সে বার নৌকার মণ্ডপের চ্যালেঞ্জার হিসেবে উঠে এসেছিল। অন্য শিল্পীর প্রশংসা করছেন আর এক শিল্পী— এমনটা এখন কল্পনাতীত।
আর সেই মণ্ডপে হয়তো আমার যাওয়াই হত না, যদি না ওই শিল্পী আমাকে বলে দিত। আনন্দবাজারের পাঠকদের তা হলে বঞ্চিত করা হত।
গল্প আরও আছে।
উত্তর কলকাতার এক নামী পুজো যে শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল, সে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিল। পুজোর তখন আর দু’মাস বাকি। ওই পুজো কমিটি শরণাপন্ন হল আমাদের ওই শিল্পীর। সে জানিয়ে দিল, তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে নিজের হাতে গড়া এমন এক নবীন শিল্পীকে দিল সে বছর ওই পুজো সুপার ডুপার হিট। টানা ছ’বছর সে কাজ করল ওই পুজোয়।
গুরু জানত তার ছাত্র তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, কিন্তু একটি পুজোকে বাঁচাতে শিষ্যকে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল সে। বেহালার ওই পুজোয় ষষ্ঠী পুতুল, মেহগনি কাঠের প্রতিমা, গালার পুতুল— তার একের পর এক সৃষ্টি। ষষ্ঠী পুতুলের থিমের সঙ্গে ছিল থিম সং ছিল। সম্ভবত কলকাতার কোনও পুজোর প্রথম থিম সং। পাঁচালির ঢঙে লিখেছিলাম আমি। সুর দিয়েছিলেন পরে বিখ্যাত হয়ে ওঠা এক সঙ্গীতশিল্পীর বাবা। ছেলের সঙ্গে গলাও মিলিয়েছিলেন তিনি।
এর পর আর থেমে থাকেনি ভবতোষ সুতার। বেহালার ওই পুজো থেকে মুক্ত হয়ে সে এমন কয়েকটি থিম করেছিল, যা এখনও চোখে ভাসে। দক্ষিণ কলকাতার একটি মণ্ডপে ওর মাতৃগর্ভের থিম এক অনন্য সৃষ্টি। নিজের হাতে তৈরি যে ধাতব ভাস্কর্য থেকে ওই থিমের সৃষ্টি, সেটি ও আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। আমার বাড়িতে তা সসম্মানে সংরক্ষণ করা আছে।
নিজে দারিদ্রের সঙ্গে লড়ে বড় হয়েছে। ছোটবেলার কষ্টের দিনগুলোই তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটাই।
৪
১৯৯৮ সালে বেহালার সহযাত্রীতে দেবেন লাহা, সতী লাহার হাত ধরে থিম পুজোয় হাতে খড়ি। ১৯৯৯ থেকে একা একা কাজ শুরু বেহালার ওই পুজোতেই। আগে শুধু মণ্ডপ গড়তেন। এখন নিজেই মূর্তি গড়েন। এতে নিজের মতো করে মণ্ডপের কিংবা প্রতিমার রূপটানে পরিবর্তন আনা যায়। সিনেমার সেট তৈরির অভিজ্ঞতাj পুরোটা ঢেলে দিয়েছেন পুজোমণ্ডপের কাজে। তাই বোধহয় কাজে এতটা বৈচিত্র।
প্রতিটি প্রতিমা গড়ার সময়ে মনে করেন, এ যেন তাঁর নিজেরই সত্ত্বা। বলেন, ‘‘ও তো আমারই সৃষ্টি! আমার প্রতিনিধি। আমার সত্ত্বা, আবেগ। যা শুরুতে একতাল কাটামাটি ছিল। আমি যদি আমার আবেগকে ঠিকমতো প্রতিফলিত করতে পারি, তা হলে বাকিরা তার মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন করবেন।’’
কয়েক বছর আগে উত্তর কলকাতায় একটি মণ্ডপে চোখ আঁকছিল সুশান্ত। সাধারণত কাজের সময়ে বাইরের কোনও মানুষের উপস্থিতি পছন্দ করে না ও। প্রতিমার উচ্চতা ৪০ ফুট। চোখ আঁকা হবে বলে পাশে অস্থায়ী ভারা বাঁধা হয়েছিল। তার উপরে বসে স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে চোখ আঁকছিল সুশান্ত। মনে হচ্ছিল যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত। যেন কিছুই ছোঁয়নি ওকে। সুশান্ত বলছিল, ‘‘আমার কাছে এটাই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন, অলৌকিকত্ব। নিজের সৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া। তাই মন না বসলে এই কাজ শুরু করি না।’’ এক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সুশান্ত এক বার বলেছিল, ‘‘এমনও হয়েছে, চোখ আঁকতে উঠেছি। তুলি হাতে নিয়ে বুঝতে পারছি, মনোযোগে ঘাটতি। ওখানেই পাটাতনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। মহালয়ার ভোরে রেডিয়ো শুনে ঘুম ভেঙেছে। শুনতে শুনতে তুলি হাতে প্রতিমার চোখ আঁকতে শুরু করেছি। ব্যস, আর কিছু খেয়াল নেই। শেষ হতে হতে সকাল ১০টা, সাড়ে ১০টা। টানা পাঁচ, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা এক টানা কাজ করে গিয়েছি, বুঝিইনি।’’
একেবারে ১০০ শতাংশ পেশাদার সুশান্ত। বিভিন্ন পেশা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পুজোয় এসেছে। এখন পুজোই ওর একমাত্র পেশা। নেশাও বটে। পেশা আর নেশা মিলে যাওয়ায় একশোতে একশো নম্বর পেতে অভ্যস্ত সে। প্রথমে টেক্সটাইল ডিজাইনে স্নাতোকত্তর । তার পর ঋতুপর্ণ ঘোষের ১৩টি ছবির পোশাক এবং অন্দরসজ্জার বিশেষজ্ঞ। পাশাপাশি, দুর্গাপুজোও চলছিল। এখন শুধুই দুর্গাপুজো ।
২০০৫-এ প্রথম প্রতিমা তৈরি করেছিলেন সুশান্ত। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর থেকে যাবে আজীবন। কেন? এক বার সুশান্ত বলছিল, ‘‘সে বছর দশমীতে যখন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হল আমিও হাউহাউ করে কেঁদেছিলাম। আস্তে আস্তে বুঝতে শিখেছি, একটি শিল্প শেষ না হলে নতুন সৃষ্টি হবে না। একটি প্রতিমার বিসর্জন না হলে সেই নতুন আসবে না। তাই এখন আমি দশমী উপভোগ করি। আমার শিল্পকে আমার পাশাপাশি গোটা বাংলা উপভোগ করল। তার পালা শেষ। আসছে বছর আবার হবে। ফের, নতুনের খোঁজে ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়ব।’’
আর একটা কথা । সুশান্ত আমার পাড়ার ছেলে। সেটা আমি বুক বাজিয়ে বলেই থাকি।