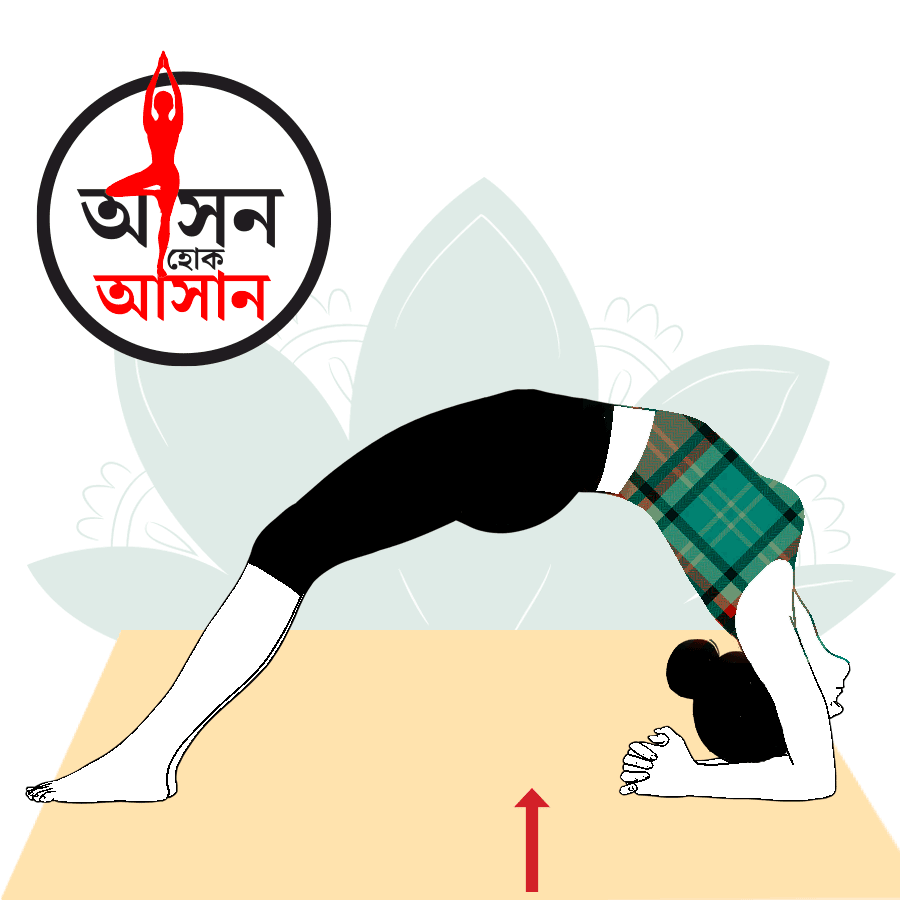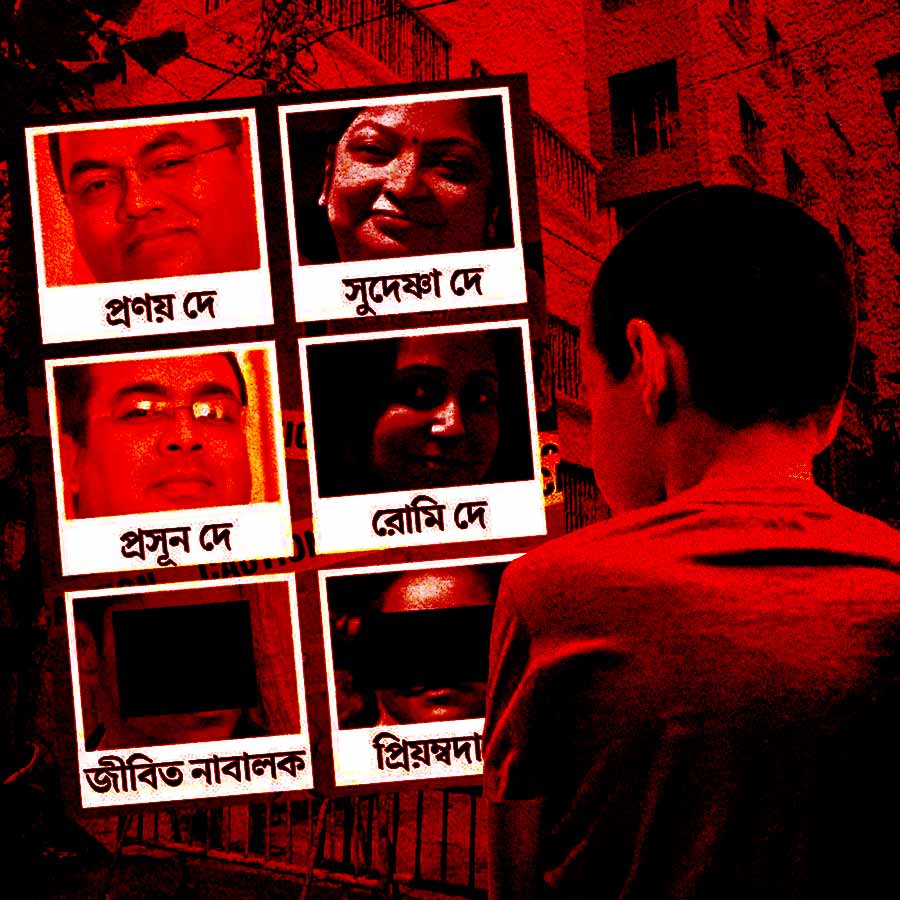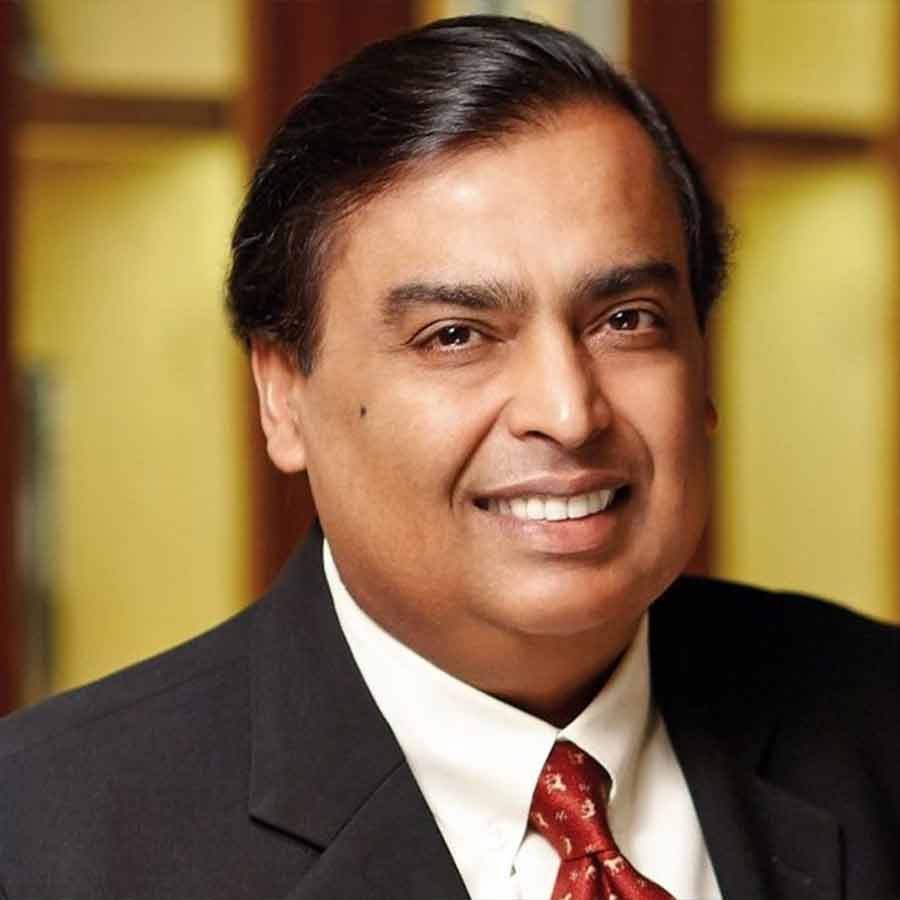ইতিহাসে ২০২৩ সালটি মনে রাখা হবে, কারণ এ বছরেই পর পর দু’দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই সীমা, যা নিয়ে ছিল দীর্ঘ দিনের সতর্কবার্তা—
শিল্পায়ন-পূর্ব জগতের তাপমাত্রার থেকে দু’ডিগ্রি বেশি। যদিও এই ছাড়িয়ে যাওয়া ছিল সাময়িক, কেবল নভেম্বর ১৭ আর ১৮ তারিখে, কিন্তু এ বছর নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত মোট ছিয়াশি দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল শিল্পায়ন-পূর্ব জগতের তাপমাত্রার থেকে দেড় ডিগ্রি বেশি। এর মানে, ২০১৫ সালে প্যারিসে সব দেশের উপস্থিতিতে (কনফারেন্স অব পার্টিজ় বা সিওপি) বিশ্ব উষ্ণায়নের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল (শিল্পায়ন-পূর্ব পৃথিবীর তাপমাত্রার থেকে দেড় থেকে দু’ডিগ্রিতে উত্তাপ বৃদ্ধি সীমিত রাখা), তা ছাড়িয়ে যাওয়ার কিনারায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি।
অনেকে প্রশ্ন করেন, একটা দিনের মধ্যে যেখানে তাপমাত্রার এত বেশি ওঠানামা হয়, সেখানে দেড়-দু’ডিগ্রি বাড়াকে কেন এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? কিন্তু দিনের মধ্যে ওঠানামা আর বিশ্বের তাপমাত্রার বৃদ্ধি, দুটোর তুলনা চলে না। দ্বিতীয়টি হল বিশ্বের গড় তাপমাত্রায় বৃদ্ধি। একে বরং তুলনা করা চলে সব সময়ে জ্বরে আক্রান্ত দেহের সঙ্গে। বিজ্ঞান এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন— মানুষের কার্যকলাপের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড-সহ গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বাড়ার জন্যই বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। যে ভাবে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, এক জায়গা থেকে অন্যত্র
যাত্রা করি, চাষ বা প্রাণিপালন করি, তা-ই বাড়াচ্ছে বিশ্বের তাপমাত্রা।
পৃথিবী আরও উষ্ণ হওয়ার প্রভাব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হচ্ছে। তীব্র গরম (এ বছর মার্চ-এপ্রিলে তাপপ্রবাহ গ্রাস করেছিল গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে), কিংবা বিপুল বৃষ্টিপাত বা খরা (এ বছরও এই উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ু ছিল বিলম্বিত, অনিশ্চিত), সাইক্লোনের হানা (চেন্নাইয়ে আমরা দেখেছি তার বিধ্বংসী রূপ) অথবা হিমবাহ গলে পড়া (সিকিমে ১২০০ মেগাওয়াট তিস্তা ৩ ড্যাম ভেঙে গিয়েছিল হিমবাহ গলা জলপূর্ণ লেক প্লাবিত হয়ে)। এর প্রভাব পড়েছে কৃষিতে— ২০২২ এবং ২০২৩, পর পর দু’বছর মোট গম উৎপাদন কমেছে ভারতে, তীব্র তাপপ্রবাহের জন্য। এক মাসের উপরে তাপপ্রবাহ ইতিহাসে দীর্ঘতম মেয়াদগুলির একটি। এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে সব ক্ষেত্রে, বিশেষত জ্বালানি, পরিবহণ এবং স্বাস্থ্যে। জীববৈচিত্র ও বন্যপ্রাণীর উপরে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা কম হলেও উদ্বেগ বিরাট। দাবানল বাড়ছে, বাড়ছে রোগবাহী কীটপতঙ্গ। ক্ষতি সবচেয়ে বেশি গরিব দেশগুলিতে। রেকর্ড-ভাঙা উত্তাপ, উপর্যুপরি দুর্যোগ বহু মানুষকে ঠেলে দেয় দারিদ্রসীমার তলায়।
এ বছর যদি হয় রেকর্ড ভাঙার, তবে এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গেরও বছর। একের পর এক দেশ প্যারিস চুক্তির অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, উত্তাপবৃদ্ধি দেড় ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য যা যা করবে বলে ঘোষণা করেছিল, তা করতে পারেনি। ফলে আমরা এগিয়ে চলেছি ২১০০ সালে এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে তাপমাত্রা হবে শিল্পায়ন-পূর্ব
বিশ্বের চাইতে আড়াই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আমরা যারা গ্রীষ্মমণ্ডলে থাকি, তাদের কাছে ভয়ানক দুঃসংবাদ।
সম্প্রতি দুবাইতে যে বৈঠক (সিওপি২৮) হল, তা-ও বিশেষ উচ্চাশা দেখায়নি, যদিও এই প্রথম বার উষ্ণায়নে জীবাশ্ম জ্বালানির ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার মূলে রয়েছে টাকার অভাব— আজ যারা ধনী, সেই দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে প্রচুর লাভ করেছিল এক সময়ে। এখন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সেই টাকার ভাগ দিতে নারাজ। অথচ, ওই টাকা না পেলে উন্নয়নশীল দেশগুলি কয়লা থেকে স্বচ্ছ জ্বালানির ব্যবহারে যেতে পারবে না। প্রতি বছর হাজার কোটি ডলার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়নি, এখন কথা চলছে ২০২৫ সালে সহায়তার নতুন অঙ্ক পেশ করার। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ নিঃসরণ কমাতেই চায়, কিন্তু দারিদ্র, অপুষ্টি, খাদ্যসুরক্ষার কথা মাথায় রাখলে কয়লার মতো জ্বালানির ব্যবহার কমানোও কঠিন।
জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কাজটিও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ। এ বিষয়ে এ বছর একের পর এক রিপোর্ট বেরিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে আইপিসিসি-র রিপোর্টও, যার ‘অ্যাডাপ্টেশন’ বিভাগের নেতৃত্বে আমি ছিলাম। দেখা গিয়েছে যে, ব্যক্তি বা সমাজ বৃষ্টির হেরফের, উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা মিলছে না। আমাদের চাষিরা তাঁদের ফসল ফলানোর নকশা বদলাচ্ছেন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে, কিন্তু সেটা করছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, সরকারের থেকে সহায়তা মিলছে না। গোটা বিশ্বে কমবেশি একই চিত্র। সাম্প্রতিক সিওপি অ্যাডাপ্টেশন-এর একটি বিশ্বজনীন লক্ষ্য স্থির করেছে, তাই আশা করা যায়, আরও কিছু সহায়তা পাওয়া যাবে।
২০২৩ সালে মনে রাখার মতো বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষতিপূরণ তহবিল (লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড) কাজ শুরু করা। একে বলা চলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের জন্য কাজের তৃতীয় স্তর। যখন উষ্ণায়ন প্রতিরোধের উদ্যোগগুলি (যেমন, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ) যথেষ্ট কাজ করে না, যেমন এখন করছে না, তখন নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়। খরা, বন্যা, প্রবল বৃষ্টিতে জীবন-জীবিকা, সম্পত্তি হারিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে পরম্পরা এবং সংস্কৃতির ক্ষয়। বিশেষ করে হিমালয়ে দেখা যাচ্ছে, তুষার গলে যাওয়ায় বহু জনগোষ্ঠী অন্যত্র বসবাসে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে তাদের জীবনযাপনের ধারা নষ্ট হচ্ছে। মিশরে এর আগের সিওপি সম্মেলনে দেশগুলি রাজি হয়েছিল এই ক্ষতিপূরণ তহবিল শুরু করতে। বাংলাদেশের প্রয়াত অধ্যাপক সালিমুল হক এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। দুবাইয়ের সম্মেলনে তহবিলটি শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হল। উন্নত দেশগুলি এই তহবিলে পঞ্চাশ কোটি ডলার জমা করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য— কেবল এ বছরই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষয়ক্ষতি কয়েকশো কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।
শেষে বলি— ভারতে পুনর্ব্যবহারের জ্বালানি ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে, যেমন গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন, পরিবহণ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহারে বৃদ্ধি। ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যার নিরিখে কলকাতা এগিয়ে রয়েছে মহানগরগুলির মধ্যে। কৃষিতে তিন লক্ষেরও বেশি সোলার পাম্প বসেছে গত কয়েক বছরে, যা এ বিষয়ে ভারতকে বিশ্বে শীর্ষের দিকে রেখেছে। এ বছরটি দেখাল যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অনেক ভাল কাজ হচ্ছে, কিন্তু যত দ্রুত দরকার, যত বেশি দরকার— ততটা হচ্ছে না।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)