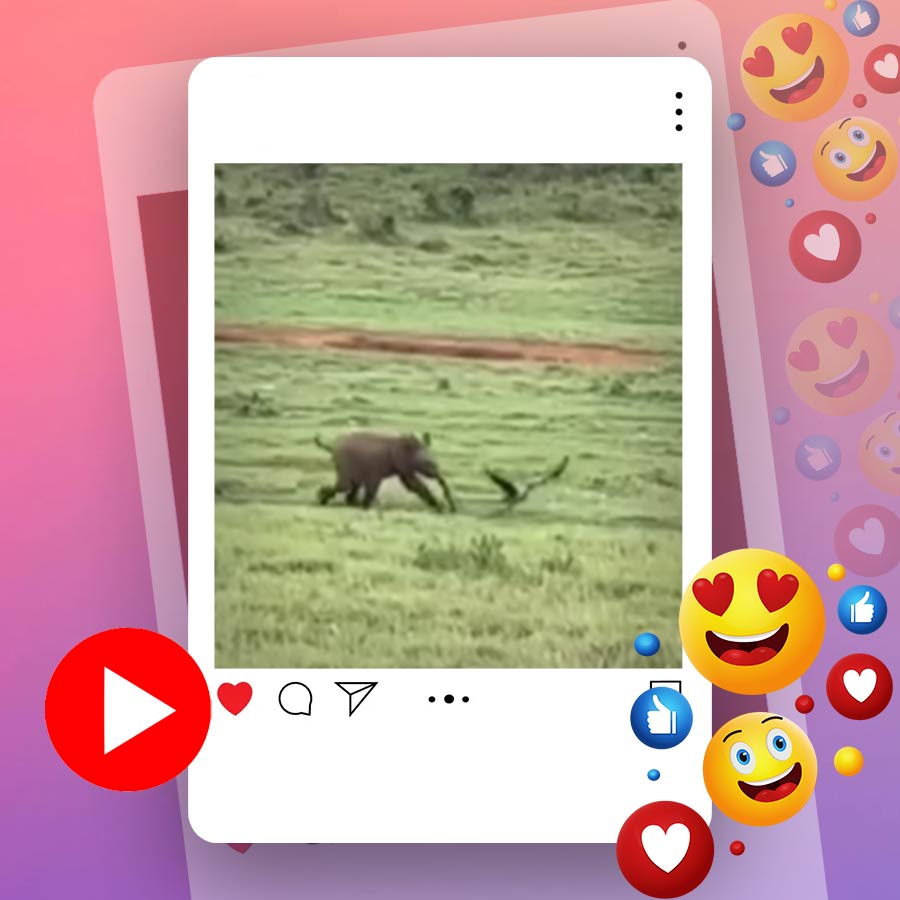গত দুটো নির্বাচনের মতো এ বারেও জাতপাতের প্রসঙ্গটা নিবার্চনী আলোচনায় উঠে আসছে। বিশেষত, মতুয়া ভোট কোন দিকে যাবে, এই প্রশ্ন অনেকেই করছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর বহু দিন এই জাতি-বর্ণ ভেদ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি, যদিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নটা। বাম আমলে শ্রেণিভিত্তিক উন্নয়ন নীতি ও পার্টি নিয়ন্ত্রিত সমাজে জাতপাতের ব্যাপারটা অনেকটা চাপা পড়ে গেলেও জাতপাতের ভিত্তিতে সামাজিক বৈষম্য, নিম্নবর্ণের সামাজিক সম্মানের প্রশ্ন ও জাতি সংগঠনের আবেদন, কোনওটাই অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তাই এখন সেগুলি আবার রাজনৈতিক পরিসরে ফিরে আসছে। তবে কি ‘পার্টি সোসাইটি’ ছেড়ে বাঙালি সমাজ এখন কাস্ট পলিটিক্স বা জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির দিকে এগোচ্ছে? প্রশ্নটা কেউ কেউ তুলছেন। একটু খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন।
প্রথমে মতুয়াদের কথা ধরা যাক। এঁরা সংগঠিত, এঁদের অস্তিত্ব এবং সমস্যাগুলির সঙ্গে জাতপাতের প্রশ্ন অবশ্যই জড়িয়ে আছে, তেমনই আছে দেশভাগের এক বেদনাময় অসমাপ্ত ইতিহাস। তাঁদের আন্দোলনকে শুধুমাত্র জাতপাতভিত্তিক আইডেন্টিটি পলিটিক্সের প্রচলিত ছাঁদে আমরা এর জটিলতাগুলো বুঝতে পারব না। এই নির্বাচনে এঁদের অবস্থান আলোচনার আগে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা একটু বোঝা দরকার।
প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিই, মতুয়া কোনও বিশেষ জাতির বা কাস্টের নাম নয়। এটি একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে মূলত পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটি প্রবর্তন করেন শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর; একে সংগঠিত করেন তাঁর পুত্র শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। তাঁর নেতৃত্বেই ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রাম মতুয়া আন্দোলনের তথা বঙ্গীয় দলিত আন্দোলনের এক অন্যতম কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে।
গুরুচাঁদ ঠাকুর মূলত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও আচারনিষ্ঠ বৈদিক হিন্দু ধর্মের থেকে মুক্ত করে নিম্নবর্গের কৃষক সমাজকে বিশ্বমানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ‘হাতে কাম, মুখে নাম’-এর মন্ত্র এক বস্তুনিষ্ঠ ভক্তিনির্ভর মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। নমশূদ্র ছাড়াও অন্য অনেক দলিত ও অদলিত সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেন। ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষক সমাজকে শিক্ষিত ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলন তাই অনেক দিন থেকেই জোরদার।
অন্য দিকে, স্বদেশি ও গাঁধীবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেও দূরে থাকে মতুয়া সম্প্রদায়। কারণ, বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল উচ্চবর্ণের কুক্ষিগত, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বা দলিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত উপকারে তাদের উৎসাহ ছিল সীমিত। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনসভায় আসন সংরক্ষণ শুরু হলে, মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। তফসিলি জাতির এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেকেই কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ জোটকে সমর্থন করায় ১৯৩৭-এ কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গড়া সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই দলিত-মুসলিম জোট।
কিন্তু দেশভাগের রাজনীতির চাপে এই জোট গেল ভেঙে। এবং দেশভাগের প্রশ্নে বাংলার স্বনির্ভর দলিত আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক দল যোগ দিলেন অম্বেডকরের অল ইন্ডিয়া শেডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন-এ এবং মুসলিম লীগের সমর্থনে এঁরা বাংলা ভাগের বিরোধিতা করলেন। অন্য দিকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে আর একটি বিরাট অংশ হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে ওঠা বাংলা ভাগের দাবিকে সমর্থন করলেন। বাংলাকে ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্গত হিন্দু-প্রধান প্রদেশ করে তোলাই ছিল তাঁদের মূল দাবি। তাঁরা চেয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গের যে জেলাগুলিতে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বাস তারা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হোক।
র্যাডক্লিফ কমিশন তাঁদের দাবি রাখেনি। গোটা নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। তা সত্ত্বেও নমশূদ্র কৃষক সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছাড়েননি। কারণ, দেশান্তরী হতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুঁজির দরকার হয় তাঁদের অনেকেরই তা ছিল না। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও তাঁদের দেশ না ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থা পাল্টাল ১৯৫০-এর দাঙ্গার পর। শ্রীমণ্ডল নিজেও চলে এলেন ভারতে, সেই সঙ্গে এলেন হাজারে হাজারে নমশূদ্র কৃষক।
কিন্তু ভারতে এসে এই দলিত কৃষক উদ্বাস্তুদের কপালে জোটে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। কারণ, এঁদের দেখা হয় জাতীয় অর্থনীতির উপর বাড়তি বোঝা হিসেবে। এঁদের প্রথমে রাখা হয় বিভিন্ন ক্যাম্পে, তার পর তাঁদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বা দণ্ডকারণ্যের গভীর জঙ্গলে। আর যাঁরা ক্যাম্পে গেলেন না, তাঁরা সীমান্তবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলাতে বসতি স্থাপন করলেন।
দেশভাগ-পরবর্তী দশকে তাই তফসিলি জাতির এক বড় অংশের প্রধান সমস্যা ছিল পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব। তাঁদের দুই নেতা যোগেন মণ্ডল ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের মনোযোগ এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যাতেই নিবদ্ধ থাকল বেশি। উদ্বাস্তু আন্দোলন জাতপাত-বিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলনের পরিসরটি দখল করে নিল।
এই তফসিলি কৃষক উদ্বাস্তুদের সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হল না পরবর্তী দশকগুলিতেও। কারণ, কোনও সরকারই তাঁদের সমস্যাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়নি। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর অচিরেই কংগ্রেসের উপর আস্থা হারালেন। ১৯৬৪-তে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি মতুয়া মহাসঙ্ঘকে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আদর্শে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন হিসেবে পুনরুজীবিত করতে আগ্রহী হলেন। পরবর্তী কয়েক দশকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া এই নমশূদ্র উদ্বাস্তু সমাজের একটা বড় অংশ আবার একটি নতুন সামাজিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ হলেন।
এই ভাবে তাঁরা নিজেদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই সময়ে, ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার আনল এক নতুন নাগরিক আইন। বলা হল, ভারতের নাগরিকত্ব পেতে হলে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের আগে ভারতে প্রবেশ করতে হবে। তখন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ১৯৭১-এর পর যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা বেশির ভাগই মুসলিম। কিন্তু এই আইনের ফলে দলিত উদ্বাস্তুদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনও রকম পরিচয়পত্র (যেমন পাসপোর্ট) পেতে গেলেই তাঁরা যে ১৯৭১-এর আগে এসেছেন, তার প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজন পড়ল। অর্থাৎ, এ দেশে এত দিন বসবাসের পরেও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু হল। এই সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁদের অনেকেই আর রাখেননি। এই হয়রানির বিরুদ্ধে সরব হল মতুয়া মহাসঙ্ঘ।
এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০০৯ থেকে তাঁরা মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করলেন, কারণ রাজনৈতিক সাহায্য ছাড়া এই নাগরিকত্ব আইন সংশোধন সম্ভব নয়। সিপিএম ও তৃণমূল উভয়েই তখন এই সংগঠিত জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেতে উদ্যোগী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভ্য হয়ে তাঁদের এক জন হয়ে গেলেন, এবং মহাসঙ্ঘের শীর্ষ নেত্রী বড়মা-র স্নেহধন্যা হলেন। ২০১১-র নির্বাচনে মতুয়া ভোট গেল তৃণমূলের দিকে। মমতা এঁদের অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের যে মূল সমস্যা, অর্থাৎ নাগরিকত্ব আইন, তা সংশোধনের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে নেই। কাজেই মহাসঙ্ঘের সমস্যা ও আন্দোলন শেষ হল না। এই আন্দোলন কিন্তু ঠিক সাধারণ জাতপাতের রাজনীতি নয়!
এই প্রেক্ষাপটে ২০১৯-এ এল নতুন নাগরিকত্ব আইন (সিএএ), যা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করল। অর্থাৎ, ‘হিন্দু’ হওয়ার সুবাদে এই দলিত উদ্বাস্তুদের নাগরকিত্ব সহজেই স্বীকৃতি পাবে, এমন একটা আশা সৃষ্টি হল। ২০০৩-এ বাজপেয়ী সরকার যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, ২০১৯-এ মোদী সরকার তার সমাধানসূত্র দিল। এই প্রতিশ্রুতির সুবাদে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোটের বিরাট অংশ গেল বিজেপির দিকে।
কিন্তু গত দুই বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কোনও নিয়মবিধি তৈরি করে উঠতে পারেনি। ফলে মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকের মনেই খানিকটা উষ্মা জেগেছে। এ বার বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনেই নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দেবে। লক্ষণীয়, নাগরিকত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে, প্রাদেশিক সরকারের এতে কোনও ভূমিকা নেই। তা সত্ত্বেও শোনা যাচ্ছে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনেকেই এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন, যার প্রতিফলন পড়তে পারে ত্রিশটির মতো বিধানসভা কেন্দ্রে।
কিন্তু এই ব্যাপারে আর একটি সমস্যা আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতপাতের প্রশ্ন ও স্বীকৃতির রাজনীতি। মতুয়া মহাসঙ্ঘ একটি সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন, যা জাতপাত, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও বৈদিক হিন্দু ধর্মের বিরোধী। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও তাঁদের আচার-পদ্ধতি বর্জন করে মতুয়া নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রশ্ন হল, তাঁরা কী ভাবে হিন্দুত্বের আদর্শবাদকে মেনে নেবেন, যা প্রকাশ্যেই মনুবাদী?
এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সব মতুয়াই যে দৈনন্দিন জীবনে সচেতন ভাবে নিজেদের ‘অহিন্দু’ মনে করেন, তা নাও হতে পারে। আর, নতুন নাগরিকত্ব আইনের সুযোগ নিতে নিজেদের ‘হিন্দু’ বলে পরিচয় তাঁদের দিতেই হবে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাংলাদেশে ওড়াকান্দি দর্শন তাঁদের কাছে এক বিশেষ অর্থবহ ঘটনা। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যদের কাছে গুরুচাঁদের জন্মস্থান ওড়াকান্দি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। এঁদের কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে দাবি করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ওড়াকান্দি দর্শন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মতুয়া ধর্মকে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও পরিচিতি এনে দিয়েছে। এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী এই সৌজন্য দেখাননি। মতুয়া প্রচারক ও গোসাঁইদের কাছে এর যে একটা আবেগময় আবেদন থাকবে, সে কথা অনুমান করা কঠিন নয়। এই ভাবেই স্বীকৃতির রাজনীতি কাজ করে।
ঐতিহাসিক দিক দিয়ে একে অভূতপূর্ব ঘটনা বলা যাবে না। প্রাচীন কাল থেকেই লোকধর্মের দেবদেবীদের আত্মসাৎ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯২০-র দশক থেকে হিন্দু মহাসভা ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বাংলায় হিন্দু সংগঠনের পক্ষে দলিত সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করে। বদ্রী নারায়ণ তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইতে দেখিয়েছেন, এ-কালেও সঙ্ঘ পরিবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় লোকায়ত দেবদেবীদের আত্মসাৎ করেই দলিত-আদিবাসীদের হিন্দু জাতির অঙ্গ করে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা বিস্তারের সংবাদ আমরা দেখেছি। আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অনেকের মন থেকেই দেশভাগের দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও তা চালিত হয়েছে। অর্থাৎ, হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্য এক উড়বার ক্ষেত্র ঐতিহাসিক ভাবে এখানে প্রস্তুত হয়ে আছে বলেই অনেকে মনে করেন।
তবে সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্ষেত্রগবেষণায় নিয়োজিত কয়েক জন সহকর্মীর কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে মনে হয় অবস্থাটা আর একটু জটিল। প্রথমত, মতুয়া মহাসঙ্ঘ এখন আর আগের মতো ঐক্যবদ্ধ সংগঠন নয়। এঁদের যাঁরা নেতৃত্ব দেন সেই ঠাকুর পরিবারই এখন রাজনৈতিক ভাবে দ্বিধাবিভক্ত। অনেক মতুয়া সদস্য সোশ্যাল মিডিয়ায় উষ্মা জানিয়েছেন যে, বর্তমান প্রজন্মের কয়েক জন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মহান ধর্মীয় আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মনুবাদী দলের অনুগামী হয়েছেন।
এঁদের মধ্যে অনেকেই এখন অম্বেডকরবাদী। ইদানীং ভারতের অন্য প্রদেশগুলিতে দলিতদের উপর আক্রমণের মাত্রা যে বিপজ্জনক ভাবে বেড়ে গিয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব। নাগরিকত্ব আইনের নিয়মকানুন ও তার সঙ্গে এনআরসি যে কাগজপত্র দেখাতে বলবে তা অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের কাছেই থাকবে না। কাজেই নাগরিকত্ব আইন যে তাঁদের দুর্দশা ঘোচাবে না, সেই বিষয়ে তাঁরা সচেতন। এই নির্বাচনে প্রচারের মধ্যে যে একটা স্ববিরোধ রয়েছে, সে কথাও তাঁরা বলছেন। যাঁরা ভোট দিচ্ছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব তো সেখানেই স্বীকৃত। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকরাই তো ভোট দিতে পারেন। তবে আবার নতুন করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে কেন?
এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছেন যে, সাম্প্রতিক কালে বাংলায় এক প্রতিবাদী দলিত সাহিত্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক দলিত সাহিত্যিক তাঁদের সম্প্রদায়ের বঞ্চনার ইতিহাস, তাঁদের সামাজিক সমস্যা ও অবিচারের কথা তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত দলিত সাহিত্য আকাদেমির মধ্য দিয়ে এই সাহিত্য আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সাংগঠনিক সংহতি পেয়েছে। এর ফলে এক নতুন প্রতিবাদী দলিত চেতনার উন্মেষ ঘটেছে বলেই মনে হয়। দলিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে অবশ্যই এর প্রভাব পড়ে থাকবে। কারণ, এই সাহিত্যিকদের অনেকেই এই ধরনের উদ্বাস্তু পরিবার থেকে উঠে আসছেন। এঁরা বৃহত্তর দলিত নির্বাচকমণ্ডলীকে কতটা প্রভাবিত করতে পারবেন, তা অবশ্য বলা মুশকিল। কারণ, তাঁরা নিজেরাই রাজনৈতিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ নন। যেমন, দলিত আকাদেমির কর্ণধার মনোরঞ্জন ব্যাপারী যখন বলাগড় কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী, তখন দলিত সাহিত্যের আর এক পথিকৃৎ, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর গাইঘাটা কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী। এই প্রতিবাদী দলিত ভোট দুই ভাগে ভাগ হলে কার ভাগে কতটা যাবে, এক্ষুনি তা বলা কঠিন। এর ফলে আখেরে কার লাভ হবে তা ভবিষ্যৎই বলবে।
তবে একটা কথা পরিষ্কার। বাংলার দলিত-বহুজন সমাজ এখনও রাজনৈতিক ভাবে এক স্বরে কথা বলে না। তারা কৌশলগত ভাবে নিজেদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। এই সমর্থন শর্তসাপেক্ষ, কখনওই চিরস্থায়ী নয়। ঠিক এমনটি আমরা দেখেছিলাম ১৯৪৬-৪৭’এ দেশভাগের সময়!
ইতিহাস বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলিংটন, নিউ জ়িল্যান্ড