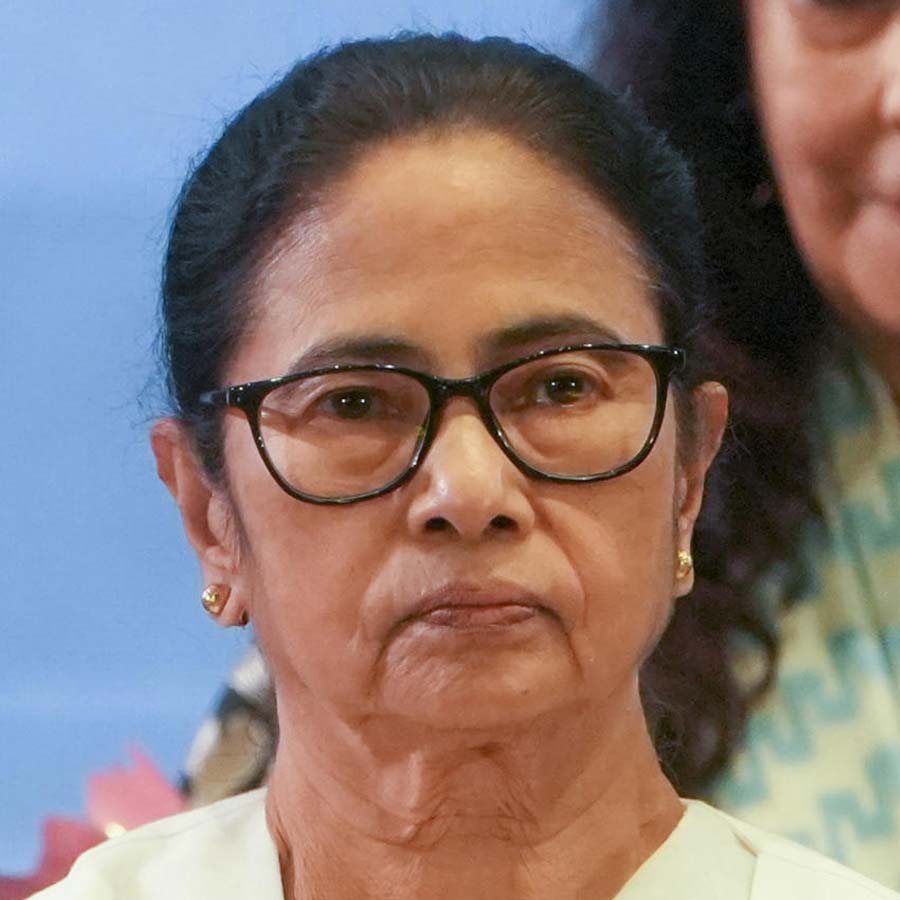নতুন বছরের প্রথম রবিবার কলকাতা শহরের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আয়োজিত সমাবেশের অন্যতম ঘোষণা ছিল: ভুল অ্যাজেন্ডা থেকে মূল অ্যাজেন্ডায়। অ্যাজেন্ডা-র বদলে স্বচ্ছন্দে কর্মসূচি বলা যেত, অভিধানেও তার পর্যাপ্ত অনুমোদন আছে। ইংরেজি শব্দ উচ্চারণে হয়তো দেহে-মনে বাড়তি বলের সঞ্চার হয়, তবে সেটা নিতান্তই অভ্যাস-নির্ভর, কিছু দিন অনুশীলন করলে বাংলা ভাষাও সমান বলবর্ধক হতে পারে।
কিন্তু আপাতত সে-কথা থাকুক। বড় কথাটা হল, এই আহ্বান আকাশ থেকে পড়েনি। ব্রিগেডে সমাবেশের আগে ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মী এবং তাঁদের সতীর্থরা রাজ্য জুড়ে যে ‘ইনসাফ যাত্রা’ করেছিলেন, তার চলার পথেও ভুল অ্যাজেন্ডা ছেড়ে মূল অ্যাজেন্ডায় উত্তরণের ডাক শুনেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। উত্তরণ না বলে উদ্ধার বলাই শ্রেয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজন, ধর্মমোহের উন্মাদনা, আপাদমস্তক দুর্নীতি, নির্লজ্জ ব্যক্তিপূজা, সর্বগ্রাসী কর্পোরেট পুঁজির কাছে অর্থনীতি এবং সমাজকে বেচে দেওয়ার বেলাগাম অভিযান— যে চক্রব্যূহে আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে চাইলে মূল কর্মসূচিতে ফেরার সর্বাত্মক উদ্যোগ চালাতেই হবে, তার কোনও বিকল্প নেই। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সুস্থ পরিবেশ, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা— সুস্থিত এবং সুস্থায়ী জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর দাবি নিয়েই গড়ে তুলতে হবে সেই উদ্যোগ। আক্ষরিক অর্থেই এটা এখন বাঁচা-মরার ব্যাপার। নিছক কোনও সংগঠন বা দলের নয়, আমাদের সকলের বাঁচা-মরা। শীতের দুপুরে ময়দানে কত লোক এসেছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল: হাল ফেরানোর এই উদ্যোগে কী ভাবে মানুষকে শামিল করা যাবে। অর্থাৎ— ভুল কর্মসূচি ছেড়ে মূল কর্মসূচির দিকে তাঁদের মন ফেরানো যাবে কী উপায়ে।
এখানেই একটা পাল্টা প্রশ্নের মোকাবিলা করে নেওয়া ভাল, কারণ অধুনা অনেকেই সে প্রশ্ন তোলেন এবং সুধীসমাজে তার বেশ সমাদরও হয়। তাঁদের বক্তব্য: কোনটা ভুল কর্মসূচি, কোনটা মূল, কে ঠিক করে দেবে? ঠিক-ভুল বেছে নেওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, তাকে লঙ্ঘন করা কি অনৈতিক নয়? প্রশ্নটা আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে এ-প্রশ্ন খুব সহজেই দুরভিসন্ধির মন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষের অধিকারের নামে ক্ষমতাবানের আধিপত্যকে আড়াল করার অভিসন্ধি। ক্ষমতা কেবল পার্থিব সম্পদ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে না, সে মানুষের চিন্তা এবং চেতনার দখল নিতে সতত তৎপর। সেই দখলদারির বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে, যে মানুষ যা ভাবছেন তাকেই তাঁর স্বাভাবিক বা নিজস্ব ভাবনা বলে মেনে নিলে এবং সেই ভাবনার অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় সাব্যস্ত করে নিষ্ক্রিয় থাকলে গণতন্ত্র সম্মানিত হয় না, তা পরিণত হয় ক্ষমতার প্রকরণে, ক্ষমতাবানের খেলনায়। দারিদ্র, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা বা বিপুল অসাম্যের দিকে না তাকিয়ে— নিজের জীবনে তার যন্ত্রণা ভোগ করেও— যাঁরা মন্দিরের মহিমায় আপ্লুত হচ্ছেন অথবা পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির খুদকুঁড়ো হাতে পেয়ে কৃতার্থ বোধ করছেন, শুধু তাঁদের মতামতকেই ‘মানুষের অধিকার’ বলে মেনে নিলে মানুষ এবং অধিকার দু’টি ধারণাই লাঞ্ছিত হয়।
তাই, গোড়ার কথাটা মনে রাখা দরকার যে, আমাদের চেতনা কোনও স্বয়ম্ভু এবং স্বনির্ভর উপত্যকা নয়, তার দখল নিয়ে নিরন্তর লড়াই চলছে, চলবে। সেই লড়াই দিয়েই ঠিক হবে মানুষের প্রকৃত অধিকার। জনচেতনাকে ভুল কর্মসূচি ছেড়ে মূল কর্মসূচিতে ফেরানোর চেষ্টায় অতএব অনৈতিকতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, বরং সেটা না করলেই ক্ষমতাবানদের ওয়াকওভার দেওয়া হয়, যা ভয়ানক রকমের অনৈতিক। সুতরাং নৈতিকতা দাবি করে যে, জনগণমন বদলানোর চেষ্টা নিরন্তর জারি রাখতে হবে। সেটা রাষ্ট্র এবং পুঁজির ক্ষমতার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিস্পর্ধী লড়াইয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। ইনসাফ ব্রিগেড জনসংখ্যার পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পরে সেই লড়াই শেষ হতে পারে না, বরং তা দ্বিগুণ উদ্যমে চালিয়ে যাওয়া আরও জরুরি হয়।
কিন্তু কী ভাবে হবে সেই লড়াই? কী ভাবে তাকে সফল করে তোলা যাবে? এটাই বড় প্রশ্ন। নৈতিকতার নয়, কার্যকারিতার প্রশ্ন। লড়াইটা যে কত কঠিন, সেটা কেবল এই রাজ্যে নয়, এই দেশে নয়, দুনিয়া জুড়েই প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রের ভেক ধরে হরেক রকমের ‘জনবাদী’ নায়কনায়িকা শ্রমজীবী মানুষের সুস্থ, নিরাপদ এবং সসম্মান জীবন যাপনের অধিকার লঙ্ঘন করে আর্থিক অসাম্য ও রাজনৈতিক একাধিপত্যের জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে, অগণন নাগরিক সেই অভিযানের দর্শক হিসাবে আমোদিত ও আপ্লুত হয়ে, এবং সিংহাসন থেকে ছুড়ে দেওয়া রুটির টুকরো ও সার্কাসের দর্শন পেয়ে, তাঁদের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁরা নাগরিক নন, প্রজা। প্রজার ভূমিকাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, কৃতার্থ। এ জন্য তাঁদের দোষী বা দায়ী সাব্যস্ত করা অন্যায় এবং অর্থহীন। নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখে এসেছেন, গণতন্ত্রের গাড়িতে তাঁরা সওয়ারি মাত্র, চালকের আসনে তাঁদের কোনও স্থান নেই। এবং চালকের উপর তাঁদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব উত্তরোত্তর কমেছে— ধর্মের নামে জাতীয় নিরাপত্তার নামে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে, সংখ্যাগুরুর স্বার্থরক্ষার নামে নাগরিকের অধিকার উত্তরোত্তর খণ্ডিত ও দলিত হয়েছে। এই বিধ্বস্ত, হতোদ্যম, প্রসাদধন্য প্রজাকুলকে ভুল কর্মসূচি ছেড়ে মূল কর্মসূচিতে ফেরানোর উপায় কী? আরও অনেক বেশি জনসংযোগ, সংগঠন এবং প্রচার? জরুরি, অবশ্যই। কিন্তু যথেষ্ট? রাম রাম!
তা হলে উপায়? আগে থেকে কোনও যথেষ্ট উপায় নির্ধারণ করে দেওয়ার ধৃষ্টতা সযত্নে পরিহার্য বলেই মনে করি। লড়াইয়ের পথই তার পথ বলে দিতে পারে। কোনও একমাত্র পথ নয়, অনেকান্ত পথের নানান সম্ভাবনা। রাজনীতি যে সম্ভাবনার শিল্প, যে সম্ভাবনা তৈরি হয় বাস্তব থেকে, বাস্তবের কোনও একটি সূত্র থেকে। যেমন ধরা যাক ওই শব্দটি: অ্যাজেন্ডা বা কর্মসূচি। বহুব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজে এই শব্দের যে অর্থ তৈরি হয়েছে, তাতে সচরাচর বোঝানো হয় একটি কাজের তালিকা। পূর্বনির্ধারিত সেই তালিকা বা সূচি অনুসারে কাজ করে চলতে পারলে অ্যাজেন্ডা রূপায়িত হবে, ইতি কর্মযোগ। মুশকিল হল, যাঁদের কাজ করতে বলা হয়, কাজের তালিকা নির্ধারণে তাঁদের কোনও ভূমিকা থাকে না, কর্মসূচিটি স্থির করে দেওয়া হয় উপর থেকে। জনসংযোগের ধারণাটিও এই ছকেই বাঁধা থাকে— উপরতলার চালকেরা নীচের তলার মানুষের কাছে পৌঁছবেন এবং তাঁদের বুঝিয়ে দেবেন কোন কর্মসূচি ঠিক, কোনটা ঠিক নয়। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সাধু: মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই জনশিক্ষার আয়োজন। কিন্তু মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব না দিলে সেই শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করবেন কেন? তাঁরা কোন বাস্তবের মধ্যে আছেন, সেই বাস্তবকে তাঁরা কী ভাবে দেখছেন এবং কী ভাবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করছেন, সে বিষয়ে গভীর ভাবে অবহিত না হলে জনসংযোগের অর্ধেকটা বাকি থেকে যায় এবং তার ফলে অন্য অর্ধেকটাও ব্যর্থ হয়।
এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আর একটি শব্দ: এজেন্সি। অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার সামর্থ্য। এ-শব্দের কোনও ঠিকঠাক বাংলা প্রতিশব্দ আজও খুঁজে পাইনি, যে দু’একটি দেখেছি বা কখনও কখনও ব্যবহারও করেছি সেগুলি কানে লাগে, মনে ধরে না। তাই আপাতত ইংরেজির আশ্রয়েই থাকা যাক। খেয়াল করা দরকার যে, শব্দটি জন্মসূত্রে অ্যাজেন্ডা-র আত্মীয়। আর সেই সূত্র ধরেই বলা চলে যে, মানুষের এজেন্সিকে অস্বীকার করে বা বাদ রেখে তাঁদের ‘মূল অ্যাজেন্ডা’ শেখাতে গেলে গোড়ায় গলদ থেকে যায়। আজকের পৃথিবীতে তার পরিণাম দ্বিগুণ ক্ষতিকর। তার কারণ, ‘আমি ১৪০ কোটির প্রতিনিধি’ বা ‘সব আসনে আমিই প্রার্থী’ বলে যে নায়কনায়িকারা তাঁদের একাধিপত্য জারি করতে তৎপর, তাঁদের রাজনীতি মানুষের এজেন্সিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই তৈরি হয়। সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেই, এবং মর্যাদা দিয়েই, সেই জনবাদী রাজনীতির যথার্থ প্রতিস্পর্ধা গড়ে তোলা সম্ভব। ব্রিগেডের মঞ্চে ও তার প্রস্তুতিপর্বে তরুণ রাজনীতিকদের কিছু কিছু কথোপকথনে এই বিষয়ে সচেতনতার সঙ্কেত মিলেছে। তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের কথা শোনার কথা বলেছেন, সেই শোনার ভিত্তিতে নিজেদের রাজনীতি নির্মাণের আকাঙ্ক্ষাও জানিয়েছেন। দেখা যাক।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)