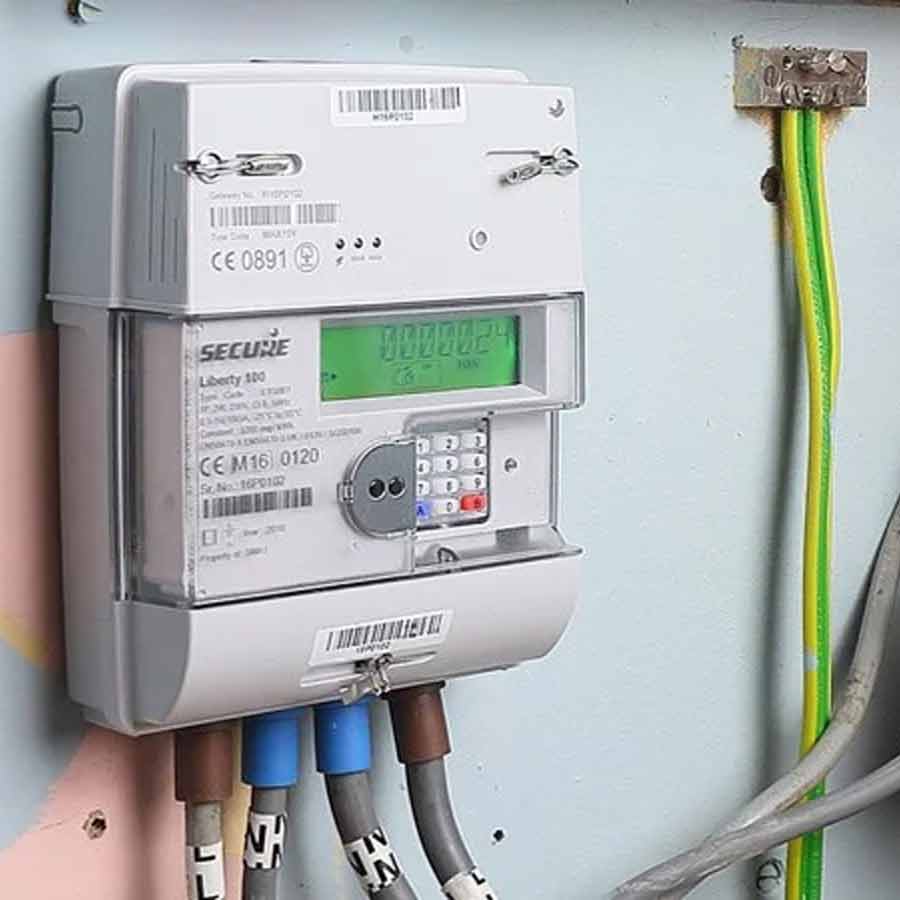ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে হয় বটে, তবে হুবহু এক ভাবে কখনও হয় না। তাই পণ্ডিতেরা মনে করিয়ে দেন, পুরনো দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বর্তমান কর্তব্য নির্ধারণ করা মূর্খামি। এই সতর্কতায় সারবত্তা আছে নিশ্চয়। কিন্তু ইতিহাসের একাধিক ঘটনার মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য থাকে, তবে সেই সাদৃশ্য থেকে কোনও ছক, অথবা ক্রম, এমনকি কার্যকারণ, অনুমান করা যাবে না, এমন নিষেধাজ্ঞা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত নয়। বিগত শতাব্দীতে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সঙ্গে আজকের আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনীতির বেশ কিছু মিল দেখিয়ে আমি প্রশ্ন তুলতে চাই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আজ ফ্যাসিবাদের কবলে পড়েছে?
মনে রাখতে হবে, যে সব দেশে আইনের শাসন আর সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, সেখানে ফ্যাসিবাদ সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। বরং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা পেয়ে তার পর রাষ্ট্রযন্ত্র আর জাতীয় সমাজকে কুক্ষিগত করেছে। ১৯২২ সালে ইটালির পার্লামেন্টে যখন বামপন্থী আর রক্ষণশীল অংশের প্রায় সমান ভাগ, কোনও পক্ষের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, রাজা ভিক্তর এমানুয়েল তখন মুসোলিনির হম্বিতম্বির সামনে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দেন, যদিও ফ্যাসিস্ট দলের তখন হাতেগোনা কয়েক জন সাংসদ। সেখান থেকে শুরু করে মুসোলিনি দ্রুত আইনি-বেআইনি দু’রকম পদ্ধতিতে, সংসদের ভিতরে ও বাইরে, তাঁর দলের শক্তিবৃদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত একনায়ক হলেন। জার্মানিতে ১৯৩২ সালে নাৎসি পার্টি ছিল পার্লামেন্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। বামপন্থীদের সরকারের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবার্গ রক্ষণশীলদের সঙ্গে নাৎসি পার্টির জোট তৈরি করেন। অচিরেই হিটলারের দল বাকি সব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একচ্ছত্র ক্ষমতা অধিকার করে ফেলে।
ফ্যাসিস্ট দল এই কায়দায় ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল, কারণ সংসদে ও বৃহত্তর সমাজে রক্ষণশীল নেতারা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। রক্ষণশীলেরা মনে করত, তাদের প্রধান শত্রু হল লিবারাল আর বামপন্থীরা। ফ্যাসিস্টরা উগ্র, দুর্বিনীত, হিংস্র স্বভাবের হলেও সাময়িক ভাবে তাদের সঙ্গে ভাব করে কাজ গুছিয়ে নেওয়ার পর তাদের অনায়াসেই ত্যাগ করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না, কারণ ফ্যাসিস্টরা সংসদীয় রাজনীতির নিয়ম মেনে খেলল না। এক বার পাদানিতে পা রেখে বাসে ওঠার সুযোগ পেয়ে কিছু কালের মধ্যে তারা গোটা বাসটার দখল নিয়ে নিল।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবন খুব দীর্ঘ নয়। তিনি প্রধানত রিয়াল এস্টেট ব্যবসা আর টেলিভিশন শো-র নায়ক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থক এবং মোটের উপর লিবারাল মতাবলম্বী। ২০০৮ সালে বারাক ওবামার নির্বাচনের সময় থেকে তিনি রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তখন থেকে তিনি ওবামা আর ডেমোক্র্যাটদের কড়া সমালোচনা শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, তথাকথিত প্রগতিশীল মতবাদের জোয়ারে আমেরিকার চিরাচরিত জাতীয় ঐতিহ্য ধুয়েমুছে যাচ্ছে, বর্ণবৈষম্য আর ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে দিনরাত শুধু দোষস্বীকার আর ক্ষমাপ্রার্থনা চলেছে, নারীস্বাধীনতা আর লিঙ্গসাম্যের নামে পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী দেশে ঢুকে কাজ কেড়ে নিচ্ছে, মাদক আমদানি করছে, বিদেশিরা আমেরিকাকে মনে করছে দুর্বল, অব্যবস্থচিত্ত, অক্ষম। ওবামা দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প পরের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি ক্লিন্টনকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হলেন।
সেই সময় ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন রিপাবলিকান গোষ্ঠী আর নেতা। রিপাবলিকান নেতারা অনেকে আন্দাজ করেছিলেন, ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ফলে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে তাঁরই নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাই তাঁরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। সমর্থকদের মধ্যে গোঁড়া খ্রিস্টান যাঁরা, তাঁরাও একই কারণে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জীবনের নানা নৈতিক স্খলন আর কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি উপেক্ষা করে তাঁকে সমর্থন করলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিতগোষ্ঠী ছিল টি পার্টি নামে পরিচিত উগ্র জাতীয়তাবাদী দল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের প্রথম শাসনকালে বিশেষ কোনও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি।
সেটা দেখা গেল যখন ২০২০-র নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে গেলেন। তিনি দাবি করলেন, ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে, আসলে তিনি হারেননি। আইনি পথে কোনও সুরাহা মিলল না। ৬ জানুয়ারি ২০২১, যে দিন নির্বাচনের ফল বিধিবদ্ধ ভাবে ঘোষিত হবে, সে দিন টি পার্টির জঙ্গি সদস্যরা ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল বিল্ডিং আক্রমণ করল। উদ্দেশ্য, ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স যেন আনুষ্ঠানিক ভাবে ফল ঘোষণা করতে না পারেন। নিরাপত্তারক্ষীরা পেন্সকে লুকিয়ে রেখেছিল, কংগ্রেস সদস্যরাও যে যার মতো লুকোলেন। ট্রাম্প সমর্থকেরা প্রচুর ভাঙচুর করল, মারামারি করল, অনেকেই গ্রেফতার হল। কিন্তু পেন্স ফল ঘোষণা করলেন। বাইডেন যথাসময় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন। জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হল, কারণ রিপাবলিকান দলের রক্ষণশীল নেতারা এবং বিচারবিভাগ এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনকে সমর্থন করল না।
২০২৪-এর নির্বাচনে জেতার পর ট্রাম্প তাঁর ক্যাবিনেটে সম্পূর্ণ অনুগত সমর্থকদেরই শুধু রেখেছেন, প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান নেতাদের আমল দেননি। বেআইনি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, সরকারি ব্যয় কমানো, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি তথাকথিত লিবারাল অধ্যুষিত প্রতিষ্ঠানের ডানা ছাঁটা— ট্রাম্প সরকারের এই সব কর্মসূচিতে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল নেতাদের আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ নেই। তবে যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তা হল— একযোগে এতগুলি বিষয় নিয়ে এমন দুরন্ত গতিতে কাজ শুরু করা। শুধু তা-ই নয়, এই কাজ করতে গিয়ে কোন পদ্ধতিটা আইনসঙ্গত আর কোনটা নয়, সেই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করছে কি না, প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে কংগ্রেস কিংবা বিচারব্যবস্থার অধিকার খর্ব করছেন কি না— প্রতিনিয়ত এই সব জটিল প্রশ্ন উঠতে থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প সরকারের বক্তব্য, দেশে জরুরি অবস্থা চলেছে। তাই প্রয়োজন দ্রুত গতিতে সমস্যার সমাধান করা। পদ্ধতি নিয়ে কূটকচালে কাজ আটকে রাখা চলবে না। ট্রাম্প-বাহিনীর উগ্রপন্থা নিয়ে রক্ষণশীল নেতাদের মনে যতই অস্বস্তি থাকুক না কেন, এখনও পর্যন্ত তাঁরা কেউ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেননি।
অবৈধ অভিবাসন ঠেকানোর জন্য গত বার তাঁর শাসনকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মেক্সিকো সীমান্ত ধরে কয়েক হাজার মাইল দেওয়াল তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু বাইডেন আমলে আইনি প্রক্রিয়া মেনে বহিরাগতদের উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশ খুব একটা কমেনি। এই বার ট্রাম্প সরকার আদালতের অনুমতি না নিয়ে হাজার হাজার অভিবাসীদের হাতকড়া পরিয়ে পায়ে শিকল বেঁধে মিলিটারি বিমানে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। যে সব দেশ ফেরত নিতে রাজি হয়নি, সেই সব দেশের অভিবাসীদের পাঠানো হচ্ছে এল সালভাদরের এক কুখ্যাত কারাগারে। উদ্দেশ্য, অভিবাসীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা: খবরদার, বেআইনি ভাবে আমেরিকায় আসার চেষ্টা কোরো না। করলে এই দশা হবে! এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংগঠনেরা আদালতে গেছে। সেখানে মার্কিন সরকারের যুক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং দু’শো বছরের পুরনো একটি আইনের বলে যুদ্ধকালীন ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের দেশ থেকে তাড়াচ্ছেন। এই ব্যাপারে কোর্টের হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার নেই। কয়েকটি আদালত এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও ট্রাম্প সরকার তা মানেনি।
লিবারালদের নানা সমাজকল্যাণ প্রকল্পের জন্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মী-সংখ্যা এবং খরচ অত্যধিক বেড়েছে, এমন অভিযোগ রিপাবলিকান নেতারা বহু দিন ধরে করে আসছেন। এই নিয়ে ট্রাম্প এই বার এক অভূতপূর্ব পন্থা অবলম্বন করলেন। ইলন মাস্ক হলেন ব্যবসায়ী, বিশ্বের বৃহত্তম ধনকুবের, ট্রাম্পের বন্ধু। তিনি কোনও নির্বাচিত পদে নেই, ট্রাম্পের ক্যাবিনেটেও নেই। কিন্তু ট্রাম্প তাঁকে দায়িত্ব দিলেন, ফেডারাল সরকারের মেদ কমাও। সমস্ত সরকারি বিভাগে নির্দেশ গেল, মাস্কের পাঠানো লোকেদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। মাস্ক তাঁর নিজের লোকেদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি দফতরে খোঁজ নিলেন, কে কোন কাজ করে, সেই কাজ সত্যি প্রয়োজন কি না। প্রতিরক্ষা দফতর আর আয়কর দফতর আপত্তি করল। তাদের বহু তথ্য অত্যন্ত গোপনীয়, তা বাইরের লোককে দেওয়া যাবে না। কোনও আপত্তি টিকল না। সরকারের বিভিন্ন দফতরে হাজার হাজার কর্মীর ছাঁটাই শুরু হল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল, বিদেশি ত্রাণসাহায্য আর শিক্ষা দফতর। সরকারের বাইরে থাকা এক ব্যক্তির নির্দেশে এই বিশাল ছাঁটাই অভিযান নিয়ে সব রিপাবলিকান খুশি হতে পারলেন না। কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে সাহস পেলেন না।
রক্ষণশীলদের উষ্মার আর একটি সূত্র আমেরিকার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সেগুলি নাকি অতি-লিবারাল প্রগতিশীলতার আখড়া। সেখানকার মোটা মাইনের অধ্যাপকেরা দুর্বোধ্য সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আর সচ্ছল উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রগতিশীলতার পাঠ দেয়। বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গরাজনীতি, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সেখানে ছাত্রদের প্রতিবাদ সারা বছর লেগে থাকে। গত বছর গাজ়ার যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবাদের সময় থেকেই রিপাবলিকান সাংসদেরা হুমকি দিচ্ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি তাদের ক্যাম্পাসে ইজ়রায়েল-বিরোধী (তাঁদের মতে, ইহুদি-বিরোধী) কথাবার্তা বন্ধ না করে এবং আন্দোলনকারীদের শাস্তি না দেয়, তা হলে তাদের সরকারি অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিস দেওয়া হয়, গবেষণার জন্য সমস্ত সরকারি অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ইহুদি-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হয়েছে, তার সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ থাকবে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সরকারি নির্দেশ মেনে নেয়। তার পর একে একে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একই নির্দেশ যাওয়ার পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় রুখে দাঁড়িয়ে বলেছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়াবেন, কী পড়াবেন, সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। জবাবে ট্রাম্প ভয় দেখিয়েছেন, হার্ভার্ডের উপর আয়কর চাপানো হবে। পাশাপাশি বিদেশি ছাত্র ও গবেষণাকর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘেঁটে কিংবা অন্য কোনও তুচ্ছ কারণে ভিসা বাতিল করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিদেশিরা যেন আমেরিকার সরকারের নীতির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি না করে।
সামাজিক মতাদর্শ নিয়ে রক্ষণশীল মহলের দাবি, তথাকথিত বৈচিত্ররক্ষার জন্য বর্ণ-লিঙ্গ-সামাজিক অবস্থান বিচার করে সরকারি দফতরে কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘুদের সুবিধা করে দেওয়া চলবে না। আসলে এই নীতির ফলে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পুরুষদের চিরাচরিত প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। এ বার ট্রাম্প সরকারের স্পষ্ট ঘোষণা, কোথাও সামাজিক বৈচিত্র নীতি প্রয়োগ করা, এমনকি উচ্চারণ করাও চলবে না। করলে শাস্তি পেতে হবে।
২০২১-এর জানুয়ারি মাসে যাদের ওয়াশিংটনে হাঙ্গামা করতে দেখা গিয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিরা আজ ট্রাম্প সরকারের শীর্ষে। সেই একই জঙ্গিপনা, গণতান্ত্রিক আইনকানুন-রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা আর অসংযত ব্যবহার প্রদর্শন করে তারা বিরোধীপক্ষ, সমালোচক আর সাধারণ মানুষের উপর ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। অন্য দিকে আমেরিকার রক্ষণশীলেরা এ বার নির্দ্বিধায় ট্রাম্পের পিছনে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরাও এখনও পর্যন্ত সতর্ক হয়ে চলেছেন, ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে নামতে চাইছেন না। সকলেই দেখছে, যে সব সরকারি উকিল কিংবা আইন সংস্থা ইতিপূর্বে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় অংশ নিয়েছিল, এক-এক করে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ট্রাম্প এ বার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রায় সব ক’টি পূর্বশর্ত পূরণ হয়েছে।
ট্রাম্প কেবল একটি বিশাল ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন, যার পরিণাম কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, বলা যাচ্ছে না। সেটা হল বিদেশি পণ্য আমদানির উপর শুল্ক বসানো। যে কোনও কলেজপাঠ্য অর্থনীতির বইতে যা বুঝিয়ে বলা থাকে, ট্রাম্প সেই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা, পৃথিবীর সব দেশের উপর আমদানি শুল্ক বসালে আমেরিকার বাণিজ্যিক ঘাটতি মিটবে, দেশের শিল্পোৎপাদন হইহই করে বৃদ্ধি পাবে, আমেরিকান শ্রমিকেরা আবার আগের মতো কল-কারখানায় ভাল মাইনের কাজ পাবে। আর চিনের উপর বাড়তি শুল্ক বসিয়ে বিশ্বের বাজারে তার আধিপত্য খর্ব করা যাবে। অন্তত সেই যুক্তিতে তিনি চড়া হারে শুল্ক বসালেন। দেখা গেল, বিশ্ব জুড়ে শেয়ার বাজার হুড়মুড় করে পড়তে লাগল। ইলন মাস্ক থেকে শুরু করে বড় বড় ব্যবসাদারেরা, যাঁরা এ পর্যন্ত ট্রাম্পের পদলেহন করে আসছিলেন, তাঁরা আতঙ্কিত হলেন। সবচেয়ে বড় বিপদ দেখা দিল যখন আমেরিকান বন্ড, যা বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঋণপত্র বলে মনে করা হয়, হঠাৎ বিক্রি হতে আরম্ভ হল। আমেরিকান ডলারের উপর যে অবিচল আস্থা এত কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা যেন হঠাৎ নড়বড়ে মনে হতে লাগল। ট্রাম্প দেরি করলেন না। একমাত্র চিন বাদে অন্য সব দেশের উপর শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করে দিলেন।
চিনের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ কত দূর যাবে, জানা নেই। টেক্সট বইতে লেখা আছে, শুল্কযুদ্ধে কেউ জেতে না, সবারই ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে আমেরিকার সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম যে বাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শেয়ার বাজারে ধস নামার দরুন সঞ্চয়, বিনিয়োগ, পেনশন ইত্যাদিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে ট্রাম্পের রক্ষণশীল সমর্থকেরা কত দূর তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারবেন, সেটা দেখার বিষয়। তাঁর কট্টর সমর্থকেরা অবশ্য সহজে দমার পাত্র নয়।
তা ছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছেন, যদিও সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী তিনি তৃতীয় বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না, সেই নিয়ম এড়ানোর উপায়ও নাকি তাঁর জানা আছে। ইউরোপের ইতিহাস আর ২০২১ সালের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা জানি, ফ্যাসিবাদীরা এক বার ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকলে সংবিধানের নিয়ম মেনে তারা সহজে ক্ষমতা ছাড়ে না।
সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)