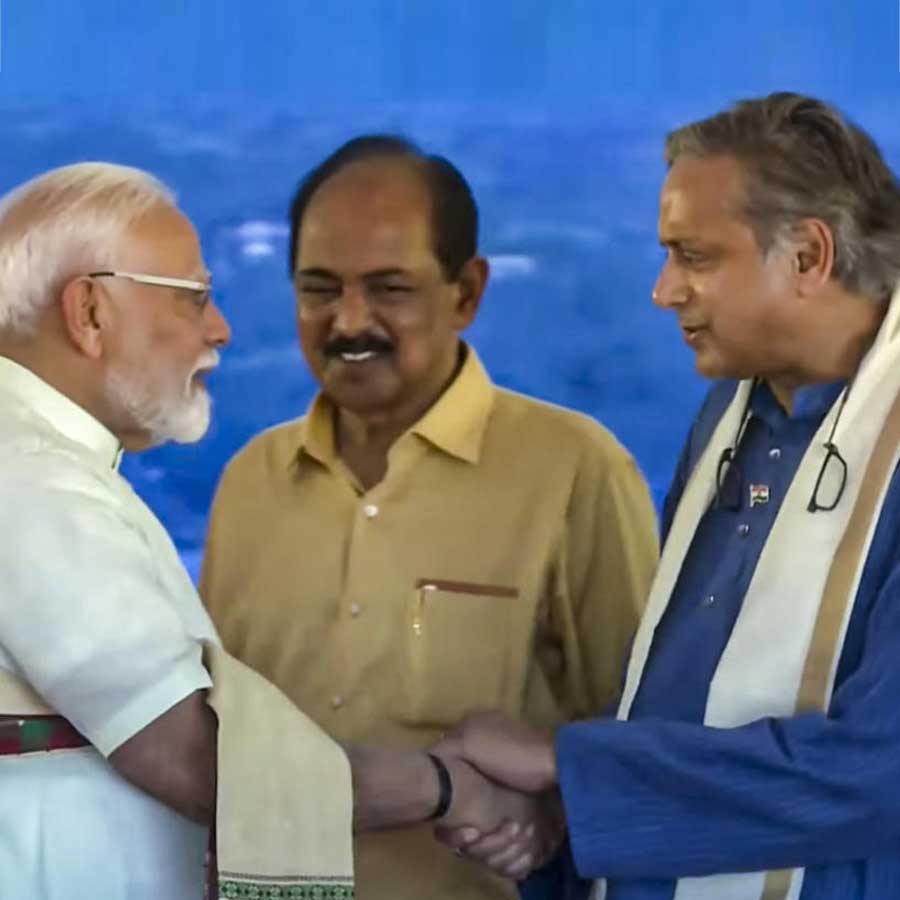পায়ে ধরে সাধা। রা নাহি দেয় রাধা।।’ না, কোনও ধাঁধা-হেঁয়ালির কথা বলছি না। বিজ্ঞান দিবসের (২৮ ফেব্রুয়ারি) থিম ঘোষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের কথা বলছি। এই বিষয়টি নিয়ে যাঁদের কিঞ্চিৎ আগ্রহ আছে, তাঁরা বছরের শুরু থেকেই অপেক্ষায় থাকেন সরকারের ঘোষণার জন্য। সেই ভাবনা অনুসারে, বিজ্ঞান দিবস পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গত কয়েক বছর ধরে এই থিমের বাজারে ভাটার টান দেখা যাচ্ছে, একই থিম বার বার ঘুরে আসছে। গত বছর ঘোষিত থিম বাতিল করে প্রায় শেষ মুহূর্তে ‘দেশীয় প্রযুক্তি’কে ‘বিকশিত ভারত’-এর কাজে লাগানোর থিম ঘোষণা করা হয়েছিল। এই বছর সেই থিম ঘোষণা হতে পেরিয়ে গেল ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।
বহু সাধ্য-সাধনার পর এই বিষয়ে সরকার যে ‘রা’ কাড়ল, তা হল— ‘এমপাওয়ারিং ইন্ডিয়ান ইয়ুথ ফর গ্লোবাল লিডারশিপ ইন সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন ফর বিকসিত ভারত’। বাংলায় বললে, “ভারতের বিকাশের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করে তোলা।” হিন্দি-ইংরেজি মেশানো এই জগাখিচুড়ি বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞান দিবসকেও আর ‘বিকশিত ভারত’ এই শব্দবন্ধ, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ— এ সবের বাইরে রাখা যাবে না। বিজ্ঞান দিবস পালনের যা মূল উদ্দেশ্য ছিল, তা এই জটিল বাক্যবিন্যাসের ঘূর্ণিতে পুরোপুরিই হারিয়ে গেল। হয়তো তাকে হারিয়ে দেওয়া হল।
সরকারি ঘোষণার দেরি দেখেই হয়তো একটি সরকারি সংস্থা তাদের মতো করে একটি থিম ঠিক করে নিয়েছিল ‘ফস্টারিং পাবলিক ট্রাস্ট ইন সায়েন্স’। এমন একটা থিম দেখে মনে ধাক্কা লেগেছিল এই ভেবে যে, স্বাধীনতার এত দিন পরে, এতগুলো বিজ্ঞান দিবস পেরিয়ে এসে বিজ্ঞানের উপর মানুষের ‘বিশ্বাস’কে গড়ে তুলতে হবে! সংবিধানের এত সব ধারা ও অনুচ্ছেদের নির্দেশ সত্ত্বেও মানুষ কি এখনও বিজ্ঞানকে এতটাই অবিশ্বাস করেন? এই রকম একটা বিষয় তো প্রকারান্তরে সেই ভাবনাকেই সমর্থন করে!
অতঃপর শুরু হল মহাকুম্ভ। সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নির্বাচিত সরকার কী ভাবে একটি ধর্মীয় সম্মেলনের প্রতি সাধারণ মানুষকে প্রায় খেপিয়ে তুলতে পারে। কয়েক বছর পর পরই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মভীরু মানুষ সেই মেলায় যোগদান করেন, ‘পুণ্যলগ্নে’ স্নান করে (নাকি) পাপমুক্ত হন। অনেকে প্রতি বছরই গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়ে স্নান করেন। কিন্তু তাঁরাও ‘১৪৪ বছর পর’-এর এই মহাযোগের গল্পটা জানতেন না। সরকারের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও বাণী-সহ ক্রমাগত প্রচারের মধ্য দিয়ে এবং হাজার কোটি অর্থব্যয়ে গত দু’-তিন মাসের মধ্যে বিষয়টিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে, সেই মহাক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এক মাসের বেশি সময় ধরে লোকজন ওই ১৪৪ বছরের বিশেষ পুণ্যের ‘অফার’টি কাজে লাগাতে প্রয়াগরাজের টিকিট কাটছেন। কেউ কি প্রশ্ন করেছেন ১৪৪ বছর পরের এই মহাক্ষণটির মাহাত্ম্য কি? এ তো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নয়, যার নয়নাভিরাম দৃশ্য জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। তা হলে কিসের আশায় দৌড়ব ওই মেলায়? পাঁচ পুরুষের মধ্যে যে ক্ষণের আবির্ভাব হয়নি, যার দাক্ষিণ্য না পেয়েই কেটে গেল এত প্রজন্ম, তা না পেলেই বা ক্ষতি কিসের!
প্রশ্ন আরও ওঠা উচিত ছিল। কুম্ভস্নানের মূল গুরুত্ব কিসে? যদি তিথিটিই আসল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে সেই তিথি পেরিয়ে যাওয়ার দেড় মাস পরেও আমি কিসের আশায় কুম্ভে যাব? কোনও নক্ষত্রসমাবেশই তো এত দিন স্থায়ী হতে পারে না! আর সেই পুণ্যলগ্নে কেন প্রয়াগেই যেতে হবে? বাড়ির কাছের গঙ্গা-দামোদর-কংসাবতীতে স্নান করলে কেন পুণ্যলাভ হবে না? কিন্তু এ সব প্রশ্ন ওঠে না। বরং প্রতি দিন নতুন নতুন মানুষ কুম্ভে যাওয়ার পরিকল্পনা করে চলেন। তাঁদের মধ্যে অজস্র মানুষ উপর্যুপরি অগ্নিকাণ্ডে, পথ-দুর্ঘটনায়, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন, লোকে বলল, তাঁরা নাকি মুক্তি পেলেন। তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরাও কি তাই ভাবতে পারছেন! কিন্তু তার পরও মানুষ মহাপুণ্য লাভের বিশ্বাস থেকে বেরোতে পারেন না। বোতলের ‘মিনারেল ওয়াটার’ ছাড়া যাঁরা হাতও ধুতে পারেন না, তাঁরা অনায়াসে সরকারি ‘গ্রিন ট্রাইবুনাল’-এর দেওয়া দূষণের হিসাব উড়িয়ে ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট ছাড়াই কোটি কোটি লোকের স্নান করা কুম্ভের জলে স্নান করলেন। ধর্মবিশ্বাস কী ভাবে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে এবং বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা বুঝতে এই ‘একা কুম্ভ’ই যথেষ্ট। তাই যাঁরা সব ছেড়ে বিজ্ঞানের উপর মানুষের বিশ্বাস গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাধুবাদ দিতেই হয়।
কিন্তু আমাদের সরকার তো সে পথে হাঁটবে না। বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁদের ধারণা এখন ‘দেশের কাজ’ ‘দেশের ঐতিহ্য’ (ভারতীয় জ্ঞানধারা) আর ‘প্রয়োগকৌশলের উদ্ভাবন’ (ইনোভেশন)— এই কয়েকটি শব্দের বাইরে বেরোয় না। কিন্তু সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টিপথ থেকে বিজ্ঞান যে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তা এই থিমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেন, একটু ব্যাখ্যা করি। বিজ্ঞানদিবস পালনের উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ ঘটানো। সরকারি থিম এমন হওয়া উচিত, যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে উদ্যাপনের পরিকল্পনা করতে পারবেন এবং তা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সেই কাজে দেশের উন্নয়নই ঘটবে। কিন্তু তাকে আশ্রয় করে সরাসরি জগৎসভায় নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখা বিজ্ঞান দিবসের পরিধির বাইরে। আর প্রয়োগকৌশল কিন্তু সর্বদা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না-ও হতে পারে। কেউ উলকাঁটায় একটা নতুন ‘ডিজ়াইন’ তুললে, একটা নতুন পদ্ধতিতে রান্না করলে বা সহজে ঘর পরিষ্কার করার একটা কৌশল আবিষ্কার করলে, তাকেও ইনোভেশন বলা যায়। বরং আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে (গত বছরের থিম) এই ইনোভেশন-এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইনোভেশন একটি প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়। সব মানুষই তাঁর প্রয়োজন অনুসারে কিছু না কিছু ইনোভেশন করে থাকেন। তাকে হাতিয়ার করে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা যায়, কিন্তু বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কী ভাবে এগোনো যাবে, তা বোঝা অসম্ভব। তবে যদি ‘ইনোভেশন’-কে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বলেও ধরে নিই, আর তরুণ প্রজন্মকে যদি সত্যিকারের বিকশিত হয়ে উঠতে হয়, তা হলে কুম্ভমেলা, শিবরাত্রি বা রামমন্দির কিছুতেই কাজ হবে না। চাই বিজ্ঞানের মৌলিক পড়াশোনা ও গবেষণা। সরকারি আগ্রহ সে দিকে ক্ষীণ হচ্ছে।
সত্যি কথা হল, বিজ্ঞানের জগতে ‘নেতৃত্ব দেওয়া’ বলে কিছু হয় না। ১৮৯৬-৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে বসে সামান্য উপকরণে যে কাজ করেছিলেন, লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা তাতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মারকিউরাস নাইট্রাইটের উপর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাজ অজৈব রসায়নে একটা নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের সঙ্গে যে কাজ করেছিলেন, তা বোস-আইনস্টাইনের যুগ্ম কাজ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। তা হলে কি সেই সময়ে ভারত পদার্থবিদ্যা-রসায়নের গবেষণায় নেতৃত্ব দিত? নিশ্চয়ই না। কারণ একটি-দু’টি উজ্জ্বল নক্ষত্র দিয়ে তারাভরা আকাশ হয় না। তাই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হোক, গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে গেলে অনেককে একই সঙ্গে বিশ্বমানের কাজ করতে হবে। তার জন্য দরকার উন্নত গবেষণার পরিকাঠামো ও অনুদান, যার দায়িত্ব সরকারের। গত প্রায় দেড় বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় গবেষণা প্রকল্প স্থগিত হয়ে আছে, চালু প্রকল্পেও নিয়মিত অনুদান আসছে না। তার পরও কী করে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো যায়, তা ওঁরাই জানেন।
সুতরাং, অনেক অপেক্ষার পর বিজ্ঞান দিবসের যে থিম আমাদের হাতে এসেছে, তা দেখে মনে হয় বিজ্ঞান দিবস পালনের প্রতি সরকার আর ততটা আগ্রহী নয়, নয়তো তারা ‘থিম’ আর ‘মিশন’ (লক্ষ্য) গুলিয়ে ফেলত না। ব্যাপারটা বোধ হয় মন্দের ভালই হচ্ছে। বিজ্ঞান দিবস তো কারও সম্পত্তি নয়। তাই সরকারি প্রস্তাবনা ছাড়াই পছন্দমতো বিষয় নিয়ে উদ্যাপন করতে বাধা নেই। বিজ্ঞানচর্চার সেই আসল বুঁদিগড় রক্ষা করার উপযুক্ত অনেক ‘কুম্ভ’ এখন দেশময় ছড়িয়ে আছে। বিভ্রান্তিকর সরকারি থিমের বদলে তারা বরং নিজেদের মতো কাজ করে চলুক।
রসায়ন বিভাগ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)