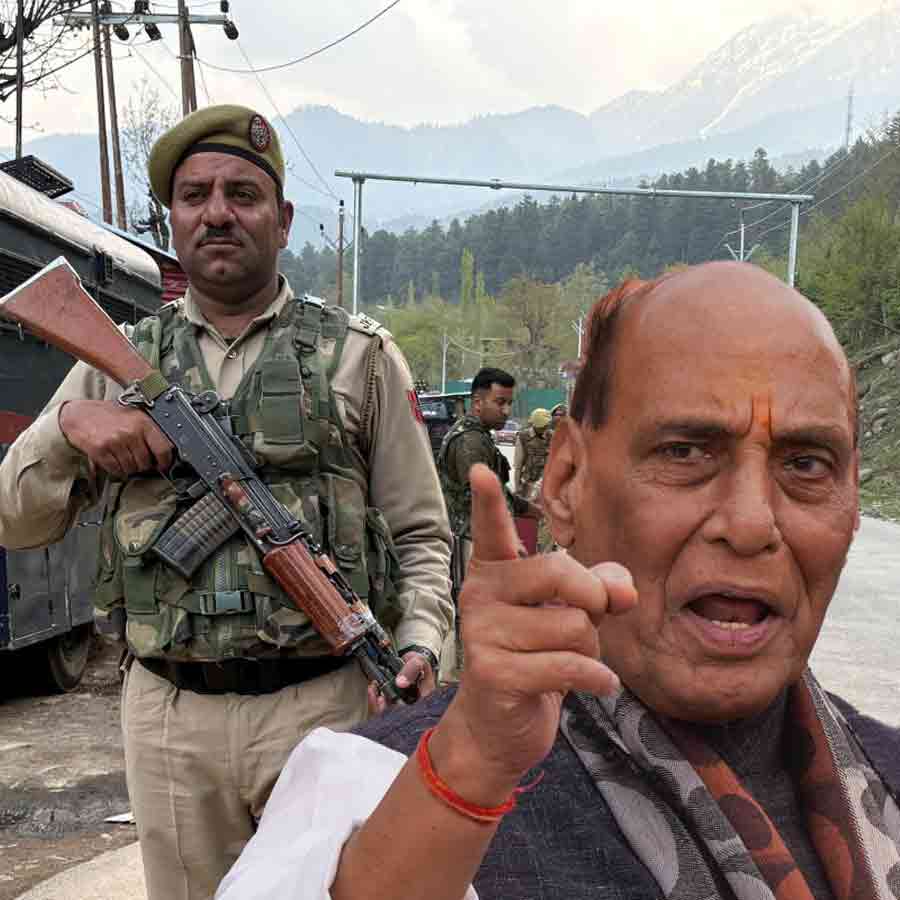রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন অশান্তি খুব আশ্চর্যজনক নয়। যে কোনও নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত আগে ও পরে অশান্তির হার বেড়ে যায়; বহু ক্ষেত্রে প্রাণহানি ঘটে। বিশ্ব জুড়ে প্রাক্-নির্বাচনী ও নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষ নিয়ে সদ্য প্রকাশিত কিছু তথ্য অনুসারে, সবচেয়ে বেশি সংঘাত ঘটে থাকে এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া আর আফ্রিকাতে; যদিও মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো বা ব্রাজ়িল-আর্জেন্টিনাও বাদ যায় না। দল ও নেতার রাজনৈতিক জমি এবং ‘সম্মান’ রক্ষা করতে যাঁরা হতাহত হন, প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে তাঁরা নেহাতই সাধারণ দরিদ্র, দলীয় কর্মী।
ব্যক্তিপরিসরে সম্পত্তি, শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতির পিছনে কি শুধুই দলীয় আবেগ এবং মনস্তত্ত্বের আদিম প্রকাশ কাজ করে? না কি, আসলে সেই চিরন্তন আর্থিক ভাগাভাগির হিসাব, যেখানে অন্য কেউ এক টুকরো খেয়ে নিলে আর এক জনের ভাগে কম পড়ে? বিভিন্ন দেশের ঘটনাপঞ্জি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এই দুটো ব্যাপারই এক সঙ্গে ঘটতে পারে। অন্য দিকে, সরকারি তরফে সদিচ্ছার অভাব না হলে, এবং প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল ও দুর্নীতিপ্রবণ করে না রাখলে আফ্রিকার কঙ্গো থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই ঘটনার বাড়াবাড়ি হোক না কেন, তা নিয়ন্ত্রণ করা তেমন শক্ত নয়।
ক্ষমতায় থাকা দলের রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা নির্বাচনী হিংসার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ। অর্থাৎ, ক্ষমতায় থেকেও যাঁরা ক্রমাগত মনে করতে থাকেন, আর বোধ হয় গদি ধরে রাখা যাবে না, তাঁরা বিরুদ্ধ-অভিমত ও অন্য দলের রাজনৈতিক কর্মীদের আক্রমণ করেন। তা হলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হল যে, হেরে যাওয়ার এই ভয় কেন? রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নান একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-নির্ভর সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যারা বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী সংঘাত ঘটবে কি না তার কিছু পরিমাপ প্রকাশ করে থাকে। তেমন একটি বিশ্লেষণ বলছে যে, ক্ষমতায় থাকা সরকার যদি তেমন জনপ্রিয় না হয়, তা হলে নির্বাচনী সংঘর্ষ বাড়বে।
রাজনৈতিক দলের কাছে জনপ্রিয়তা হারানো ভয়ের ব্যাপার। তেমনই যদি ক্ষমতায় আসার পদ্ধতি নিরঙ্কুশ না হয়ে থাকে, তা হলে সেটাও পরবর্তী কালে ভয় সৃষ্টি করতে পারে। যেমন রিগিং করে ভোটে জেতা, ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে না দেওয়া ইত্যাদি। এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ‘আকলেড’ নামে এক বহুজাতিক সংস্থা জানিয়েছে, এই বিষয়টি ভারতের ক্ষেত্রেও সমস্যা। এর সঙ্গে কম ব্যবধানে জয়লাভ, শতকরা ভোটপ্রাপ্তি কম হওয়া ইত্যাদি কারণেও নেতারা আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। দলীয় ভোটকর্মী আর মাঠে ময়দানে কাজ করা সদস্যদের মধ্যে সেই আগ্রাসন সঞ্চার করে দেওয়া হয় পরবর্তী ভোটের কথা ভেবে।
ফলে বিভিন্ন দলের সাধারণ কর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষ খুব অসম সংগঠনের মধ্যে না হলে দু’পক্ষেরই বিপুল ক্ষতি হতে পারে— যদিও ক্ষমতায় থাকা দল প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে নিজেদের সুবিধার্থে, এমন অভিযোগ সর্বত্রই। এই ধরনের সমাজে যদি পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং শত্রুতা এক বার সঞ্চার করে দেওয়া যায়, তা হলে সেই সমাজের পক্ষে বিশ্বাসের পুরনো স্থিতাবস্থায় ফিরে আসা কঠিন। বরং রাজনীতি-সৃষ্ট আগুন বহু দিন জ্বলতে থাকে। তখন নেতাদের শুভবুদ্ধিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
যখন সংঘাতের উদ্দেশ্য রাজনীতির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থের রূপ নেয়, তখন দলের গুরুত্বও কমে যায়। তা সত্ত্বেও বহু রাজনীতিক মনে করেন যে, ক্ষমতা কায়েম করার এটাই দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেতনা বাড়ে না কেন? বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, নেতাদের প্ররোচনায় পা না-দেওয়ার জন্যে যে শিক্ষাজনিত মানসিক শক্তি এবং আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন, তার থেকে বঞ্চিত বলেই কর্মীদের কাছ থেকে এই আনুগত্য আদায় করা সম্ভব। অনেক কর্মীর কাছে দল বা নেতা-নেত্রীরা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আবেগের অংশ— সেখানে কোনও বিরোধিতার স্থান নেই। এমন আবেগের নিজস্ব যৌক্তিকতা আছে। যার সঙ্গে স্বার্থসঞ্জাত দেনাপাওনার হিসাবের তুলনা করা শক্ত। তবে সংঘাতের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে হলে এই হিসাব করতেই হবে। মতাদর্শের জন্য খুন করলেও কিন্তু খুনেরই সাজা হয়।
অর্থনৈতিক কারণে যে ভাবে এই সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তার প্রধান উপকরণ হল জমির মালিকানা। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা শুধু জমির মালিকানা ধরে রাখতে চাইবেন তা নয়, বরং উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সম্পত্তি সুরক্ষা আর দুর্নীতি দমন আইন খুব নড়বড়ে, সেখানে জবরদখল করে আরও সম্পত্তির মালিক হতে চাইবেন। যদি সরাসরি সম্পত্তির মালিকানা না থাকে, তা হলেও বাড়ি তৈরি হোক বা কারখানা, সবেতেই ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের ভাগ থাকতে হবে। যাতে কোনও ভাবেই এই কাজের ভাগ বিরোধীদের হাতে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতেই হিংসার অবতারণা। আফ্রিকার বহু দেশে যেখানে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, সেখানেও এই ভাগ-বাঁটোয়ারা দীর্ঘমেয়াদি সংঘর্ষ, এমনকি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে।
যে-হেতু দলের লোক কাজ হাতে নিলে নেতারও রোজগার হয়, ফলে, ক্ষমতাসীনের কাছে এই সমীকরণের একমাত্র উত্তর হল নিজেদের সদস্যদের জন্যই সবটুকু রাখা। যদি অন্যরা দেখেন যে, রোজগার এবং জীবনধারণের উপকরণ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার একমাত্র পথ হল ক্ষমতাসীন দলের, বা কোনও বিশেষ নেতার আনুগত্য স্বীকার করা, তা হলে আরও অনেকেই এই দলে নাম লেখাতে চাইবেন। এ দিকে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যাঁদের রোজগার, দলের সদস্যসংখ্যা বাড়লে স্বভাবতই তাঁদের মাথাপিছু উপার্জনের পরিমাণ কমবে— উন্নয়নশীল দেশে সম্পদ সীমিত, এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও অঢেল নয়, সুতরাং যে হারে সদস্য বাড়ে, তার থেকে বেশি হারে আর্থিক সুযোগ না বাড়লে রাজনৈতিক খাজনা কমতে বাধ্য। এর ফল হল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তাতে অবশ্য শেষ অবধি দলের ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট নেতারও ক্ষতি। অতএব, দলের নিজের স্বার্থেই এই আর্থিক প্রক্রিয়ায় রাশ টানা জরুরি। তাতে হিংসা কমবে। অবশ্য, তার জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের কথা নিম্নতম স্তরের কর্মীদের কাছেও পৌঁছতে হবে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)