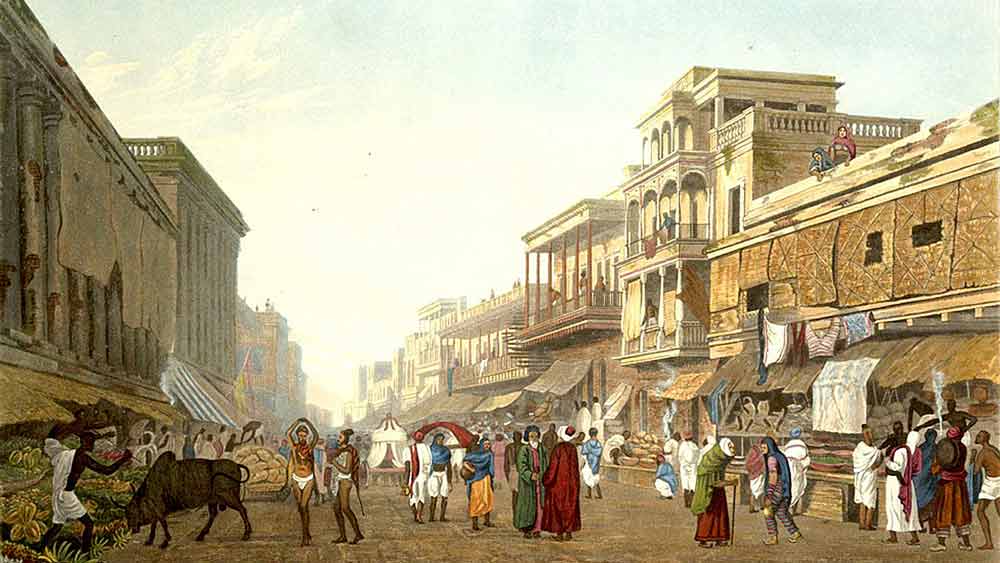ইন কোয়েস্ট অব দি হিস্টোরিয়ান’স ক্রাফ্ট: এসেজ় ইন অনার অব প্রফেসর বি বি চৌধুরী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
সম্পা: অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংযুক্তা দাশগুপ্ত প্রেয়ার
১৭৫০.০০ ও ১৭৫০.০০
মনোহর বুকস
সম্মাননা গ্রন্থ বা ‘ফেস্টস্রিফ্ট’ কোনও শোকবার্তা নয়, কিন্তু তাতেও কোনও কিংবদন্তি গবেষকের নামে বিশেষ সংখ্যা যেন ‘তিনি ছিলেন’ এই বার্তাই বয়ে আনে, বিশেষত যদি সে বই আসে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে। এই বইয়ের একাধিক প্রাবন্ধিকও বই প্রকাশের আগেই প্রয়াত হয়েছেন। কোভিড কেড়ে নিয়েছে হরি বাসুদেবনকে। আমরা হারিয়েছি সব্যসাচী ভট্টাচার্য, এবং বিনয়ভূষণ চৌধুরীর স্ত্রী তৃপ্তি চৌধুরীকে। চলে গিয়েছেন বিশ্বময় পতি, ইয়ানাগিসাওয়া। সব মিলিয়ে, ইরফান হবিব, রবার্ট ফ্রিকেনবার্গ, ইয়ানাগিসাওয়া-র মতো গবেষকেরা যখন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর সম্মাননা গ্রন্থে লেখেন, তখন তা শুধু শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ নয়— এ হল ইতিহাসচর্চার পথের সহযাত্রীর প্রতি সংহতি প্রকাশ। এই সংখ্যা দুই খণ্ডে প্রকাশের সেটাও একটা কারণ বটে। তাতে এই সময়ের ঘরে-বাইরে অনেককে ধরা যায়, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন— ছাত্র, সহকর্মী, সমসাময়িক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। তার সঙ্গে থাকে বইয়ের থিম, ‘হিস্টোরিয়ান’স ক্রাফ্ট’: বিশ শতকের গোড়া থেকে ইতিহাসচর্চার নানা দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা।
ভূমিকায়, অল্প বয়সে, গ্রামীণ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে বিনয়ভূষণের এক চমৎকার ছবি আঁকেন দুই সম্পাদক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংযুক্তা দাশগুপ্ত প্রেয়ার। তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল তখনই, লাইব্রেরিতে প্রচুর বই পড়তেন, পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং নাটকের আয়োজন করতেন। কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দুরন্ত ফল, অতঃপর কলকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, এবং পড়ানো, মূলত কলকাতাতেই। অর্থনৈতিক ইতিহাসের কিংবদন্তি অধ্যাপক হিসেবে বিনয়ভূষণকে স্মরণ করেছেন বহু লেখকই। তাঁর কাজের সম্ভার নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও আগ্রহী হন বিনয়ভূষণ। এই বহুবিধ আগ্রহের ভিত্তিতেই সম্মাননা গ্রন্থটিকে দু’খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয়টি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস।
স্বভাবতই পরিসরের কারণে মাত্র কয়েকটা প্রবন্ধই বেছে নিতে হল। তবে এই নির্বাচনের ভিত রইল একটা ভাবনায়— যাতে উৎসাহী ইতিহাস-শিক্ষার্থী বুঝে নিতে পারেন, কী বিষয়-বৈচিত্র ধরা রইল দু’টি খণ্ডের মধ্যে।
বিনয়ভূষণের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন হরি বাসুদেবন, যিনি নিজে ছিলেন রুশ ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী। ইউরোপীয় ইতিহাসের পিছনপথে গিয়ে, বিশেষত শিল্প বিপ্লবের সন্ধিক্ষণের ঘটনাবলিতে পৌঁছে যাত্রাপথটি অঙ্কন করেন প্রাবন্ধিক। কী ভাবে ইতিহাস শিক্ষণের ধারাটি এ দেশে পাল্টাতে পাল্টাতে এসেছে, তিনি সেই পরিচয় দেন পাঠককে। এই আধা-জীবনীমূলক প্রবন্ধের পর মধ্যযুগ সম্পর্কিত দু’টি প্রবন্ধের কথা বলি। মহম্মদ হাবিব, হাবিব সিনিয়রের সূত্রটি গ্রহণ করে ইরফান হাবিব দেখান— নাগরিক ও গ্রামীণ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছিল সুলতানি শাসন। তবে তাঁর মতে, এই পরিবর্তন ছিল সীমিত, এর ফলে ইউরোপের মতো ধনতন্ত্রের দিকে উৎসারণ ঘটেনি, বরং বাজারের সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতি এবং সমসাময়িক ধর্মীয় প্রতিবাদ আন্দোলন ঘটতে শুরু করেছে— যার কেন্দ্রবিন্দু অনেক সময়ই থেকেছে দেশীয় তাঁতি ও কারিগর সমাজ।
মোগল বাংলার ইতিহাস রচনার গোঁড়ামি নিয়ে সাহসী প্রশ্ন তোলেন শিরিন মুসভি। মধ্যযুগীয় ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক গবেষণার অভিমুখ নিয়ে যে ইতিহাসবিদরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁদের সমালোচনার পর বাংলার তুলনায় স্থিতিশীল অবস্থার দিকে নজর ঘোরান। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে ইসলামিকরণ বিষয়ে রিচার্ড ইটনের জনপ্রিয় তত্ত্বকে প্রশ্ন করেন। ইটন দেখিয়েছিলেন, মোগল সাম্রাজ্যে যুক্ত হওয়ার আগেই বাংলার চাষিরা মুসলমান হয়েছিলেন। আর সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত ধর্ম সম্প্রসারণের পিছনে শক্তিশালী সুফি ও পিরদের ভূমিকা ছিল— তাঁদের জন্যই জঙ্গল কেটে চাষ শুরু হয়েছিল, সম্ভবত তার পিছনে হিন্দুরাও ছিলেন। অবশ্য মুসভির সমালোচনা আমার কাছে একটু হতাশাজনক, কেননা সম্প্রতি আমি ইটনের পির-আলোচনার উপর ভিত্তি করে ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি দাঙ্গার প্রাক্-ইতিহাস নিয়ে একটি অধ্যায় লিখেছি। আমার কাহিনির সঙ্গে ইটনের তত্ত্ব খাপ খেয়ে যায়; যখন আমি দেখাই কী ভাবে শাহপুরের দিয়ারা শরিফের গোলাম সারওয়ার কৃষক প্রজা পার্টির বিধায়ক থেকে মুসলিম লীগের কর্মী হয়ে যান। পলাশির যুদ্ধের কথা বলেন মুসভি, দেখান কেবল দেশীয় নেতাদের সঙ্গে বিদেশি শক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে একে ব্যাখ্যা করা যায় না ।
‘ইন্ডিয়ান ফেমিনস: ন্যাচরাল অর ম্যানমেড’ শীর্ষক প্রবন্ধে তীর্থঙ্কর রায় ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন— অমর্ত্য সেন এবং অন্যান্য গবেষক যাঁরা এই দুর্ভিক্ষকে মানবসৃষ্ট, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের ফল হিসেবে দেখেন, তার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, এমন ‘মার্কেট পেসিমিজ়ম’ ইতিহাস-সিদ্ধ নয়। এই ‘ম্যানমেড’ আর ‘ন্যাচরাল’ দ্বিত্বের বাইরে গিয়ে মন্বন্তরের একটা তৃতীয় ব্যাখ্যা তৈরি করেন তিনি। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তীর্থঙ্কর ‘ম্যানমেড’ তত্ত্বটির ‘ক্যারিকেচার’ তৈরি করে একে বাতিলযোগ্য বলে দেখিয়ে দেন। বুঝতে অসুবিধে নেই, তীর্থঙ্কর রায় আর আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দু’টি ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের দুই মেরুর প্রতিনিধি। উল্লেখ্য, এর আগেও অন্যত্র তীর্থঙ্কর মতামতের সমালোচনা করেছেন আদিত্য, বলেছেন ‘ঔপনিবেশিকের প্রত্যাবর্তন’। আদিত্য ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতার কথা ফিরিয়ে আনেন, কী ভাবে ব্রিটিশ রাজের মধ্যেও অর্থনৈতিক স্বার্থকে দমিয়ে উপরে উঠে আসছিল বাণিজ্যিক/বৈষয়িক স্বার্থ, তার ব্যাখ্যা করেন। এও বলেন যে, মনে রাখতে হবে, উপনিবেশের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থতন্ত্র শেষ হয়ে গেল না— তবে সে এক ভিন্ন কাহিনি।
১৯১৩ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত কালপর্বের ইটালীয় ভারত-বিশারদদের নিয়ে মারিয়ো প্রেয়ারের প্রবন্ধটিও খুবই ভিন্ন স্বাদের। ভারতচর্চা ও ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার চালিকাশক্তি হয়েছিল ফ্যাসিবাদের উত্থান। ১৯২৬ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ইটালি যাওয়ার আমন্ত্রণ পান রবীন্দ্রনাথ। গাঁধী যান ১৯৩১-এ, নেতাজি ১৯৩৪-৩৫’এ। বিশ্বভারতীতে আসেন দু’জন ইটালীয় অধ্যাপক। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আসলে ঔপনিবেশিক সম্পত্তির প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বিধৃত, যার শিকড় গাঁথা হয় পশ্চিমি প্রাচ্যবাদী প্রকল্পে।
কর্নেলিয়া সোরাবজি-র উপর লেখা সুপর্ণা গুপ্তুর গবেষণাঋদ্ধ প্রবন্ধটি এই বইয়ের মূল থিম-টির সফল পরিচায়ক। ইতিহাসবিদের কারুশিল্প ফুটে ওঠে যখন কর্নেলিয়ার মধ্য দিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস বোনেন সুপর্ণা। পাশাপাশি, দক্ষিণ ভারতের নিম্নবর্ণের আন্দোলন নিয়ে রাজশেখর বসুর গবেষণায় পড়ি ফিজিতে বসবাসকারী অভিবাসী সমাজে পরিযায়ী জনতার আবেগ ও তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বের কেন্দ্রে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রভাব।
সিংভূমের হো জনজাতিকে নিয়ে প্রবন্ধে সংযুক্তা দাশগুপ্ত লেখেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলে প্রবল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানিক অর্থনীতি কী ভাবে এই জনগোষ্ঠীকে ভেঙে দেয়, আবার তার নতুন পরিচিতি তৈরি করে আধুনিক ঔপনিবেশিক প্রজা হিসেবে।
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংবিধানের মতো চিরন্তন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লিখেছেন দুই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রবার্ট ফ্রিকেনবার্গ এবং সব্যসাচী ভট্টাচার্য। সংবিধান নির্মাণ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, পূর্বলব্ধ প্রজ্ঞার প্রকাশ নয়। সব্যসাচী দেখিয়েছেন, কে টি শাহ যখন প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দ দু’টি ঢোকাতে চেয়েছিলেন, অম্বেডকর তখন ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটি নিয়েই বেশি আপত্তি করেছিলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ নিয়ে নয়। আবারও আমরা বুঝি, সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসের কতটা রাজনীতিকরণ হয়েছে— ইতিহাসকে ঠিক ভাবে পড়া কত জরুরি।
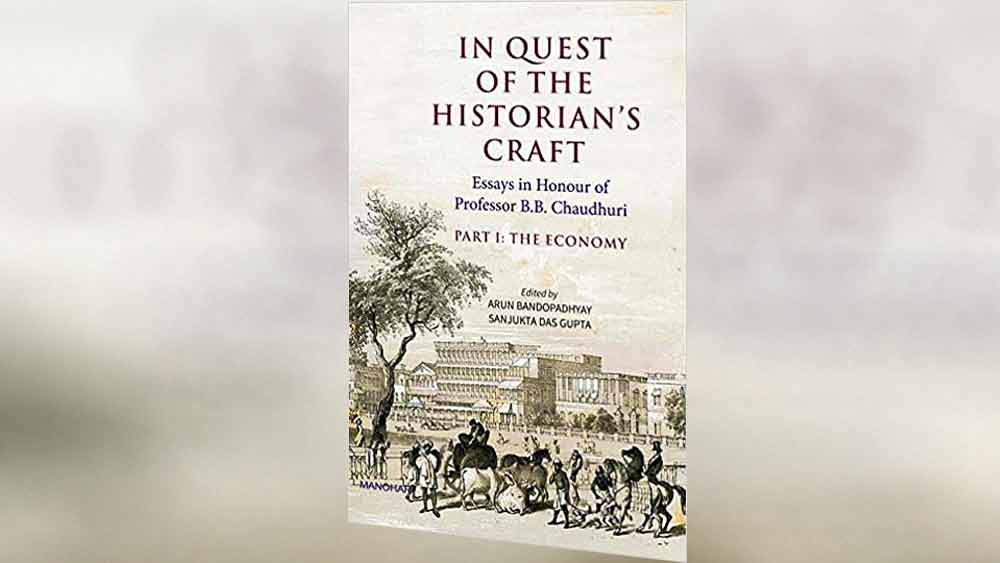
একটি জরুরি প্রবন্ধে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে ব্যাখ্যা করেছেন অমিত ভাদুড়ি। ইতিহাসের পদ্ধতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনায় তথ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন— তা কি বিকল্প খুলে দেয়, না কি তার পথ বন্ধ করে? তা কি সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করে, না কি এলোমেলো করে দেয়? তাঁর মত, প্রশ্নটা ঠিক অ্যাডাম স্মিথের হিসেবে বাজারের অনন্ত সম্ভাবনার নয়। প্রশ্নটা আসলে পরস্পর-সংযুক্ত বাজারের, যার মধ্যে মূল্যের চেয়ে ক্ষমতাই বেশি বড় নির্ধারক। কম ক্ষমতাশালীর পথ বন্ধ করে দেয় জাত, ধর্ম ও পুরুষতন্ত্র।
ভাদুড়ির কথার একট আলাদা অনুরণন আছে আমার কাছে। অর্থনীতির ছাত্রী হয়েও ইতিহাস চর্চা শুরু করেছিলাম, কেননা মনে হয়েছিল, সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চার পাশের আর সব কিছুকে অপরিবর্তনশীল, ধ্রুব ধরে নিয়ে বিশ্লেষণী মডেল তৈরি করা যায় না। ভাদুড়ি বলেন, অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের তুলনায় ইতিহাসবিদরাই পারেন মানব-অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ ছবিটি তুলে ধরতে। সেই মূল্যায়নের ছবিই পাওয়া যাবে দু’খণ্ডের গ্রন্থটিতে, যে গ্রন্থ এক ইতিহাসবিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, যাঁকে ইতিহাসের কৃতী কারুশিল্পী বলে মনে করেন তাঁর ছাত্র, শিষ্য ও বিশেষজ্ঞরা।