আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে এক্ষণ পত্রিকায় পথের পাঁচালী ও অপরাজিত-র চিত্রনাট্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী-কথিত ছবি দু’টির প্রস্তুতিপর্বের কাহিনিও ছাপা হয়েছিল। তার পর এত বছর ধরে অপু-ত্রয়ী সম্বন্ধে বিস্তর চর্চা হওয়া সত্ত্বেও অনিলবাবুর স্মৃতিচিত্রের মূল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। পাবেই বা কেন? ব্যবস্থাপক, টেকনিশিয়ান বা সহকারীরা নিজেদের বিভিন্ন অবস্থান থেকে ছবি তৈরির যে সব দিক লক্ষ করেন, তার অধিকাংশই পরিচালক বা অভিনেতার নজরে পড়ে না। অথচ চলচ্চিত্র-নির্মাণের ইতিহাস জানতে আমরা শুধু শেষোক্তদেরই দ্বারস্থ হই। দু’-এক জন প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের টেকনিশিয়ান ও সহকারীদের গবেষক, সাংবাদিক বা সমালোচকরা চিরকালই উপেক্ষা করেছেন। অনিল চৌধুরীর স্মৃতিচারণের পরও তাঁর কাছ থেকে সত্যজিতের অন্যান্য ছবির নেপথ্য কাহিনি সঞ্চয় করে রাখার প্রয়াস কেউ করেছিলেন বলে জানি না।
এই নির্দেশক ও অভিনেতা-সর্বস্ব চলচ্চিত্রচর্চার স্রোতে সহযাত্রীর কথা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তথ্যসমৃদ্ধ, উপাদেয় এ বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের নানা স্তরের নানা কর্মীর বৈচিত্রময় জীবন ও কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন সম্প্রতি প্রয়াত রমেশ (পুনু) সেন। তাঁর নাম চিরতরে জড়িয়ে আছে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে— পথের পাঁচালী-র সম্পাদক দুলাল দত্তের সহকারী হয়ে সত্যজিতের বৃত্তে প্রবেশ করলেও নায়ক-পরবর্তী বহু ছবিতে ছিলেন পরিচালকের প্রধান সহকারী— কিন্তু শুধুই সত্যজিতের ছবিতে তিনি কাজ করেননি। সহকারী ছিলেন মৃণাল সেনের প্রথম ছবি রাত-ভোর-এ, কাজ করেছেন ঋত্বিক ঘটক ও তরুণ মজুমদারের বহু ছবিতেও। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, উত্তমকুমারের সঙ্গেও; চিনতেন স্টুডিয়োপাড়ার প্রায় সবাইকে, চলচ্চিত্রকর্মীদের নানা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এবং শেষ মুহূর্তে প্রযোজক বেঁকে না বসলে চিড়িয়াখানা-র যৌথ পরিচালক রূপেও অবতীর্ণ হতেন।
সহযাত্রীর কথা
রমেশ সেন, অনুলিখন ও সম্পাদনা: জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০০.০০
সিগনেট প্রেস
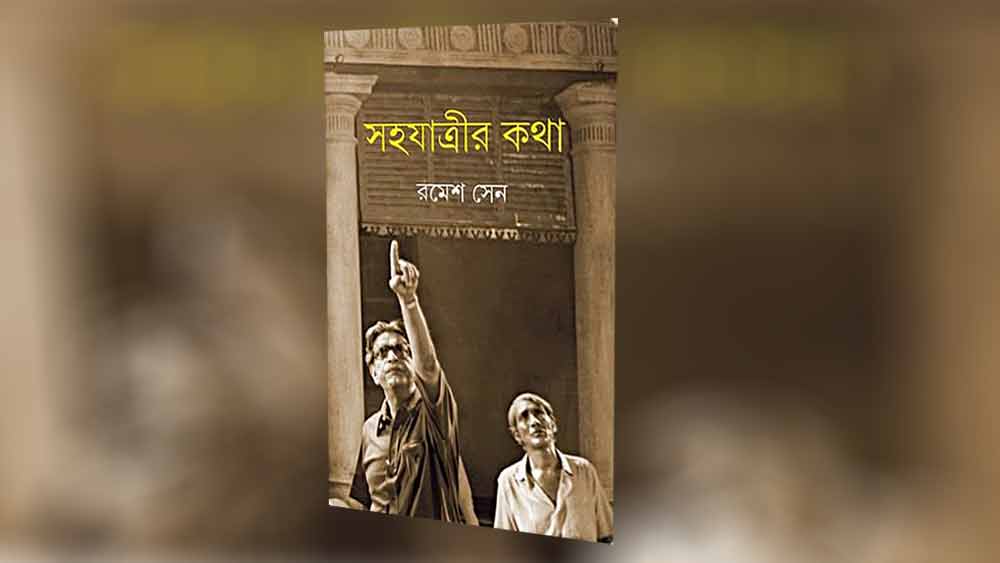
চিড়িয়াখানা বাদ দিলে কিন্তু লুই পুনুয়েল— পরিচালক লুই বুনুয়েল-এর আদলে পুনু সেনের এই নামকরণ করেছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়— কোনও দিন নিজে নির্দেশক হতে চাননি, বিশেষ করে সত্যজিতের ইউনিটে পাকাপাকি স্থান পাওয়ার পর। সত্যজিতের মৃত্যুর পর সন্দীপ রায়ের প্রধান সহকারী হয়ে থেকে যান ২০১৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত প্রোফেসর শঙ্কু ও এল্ ডোরাডো ছবি পর্যন্ত। সারা জীবন সহকারী হয়ে না কাটালে তিনি হয়তো আমাদের বহু উৎকৃষ্ট ছবি উপহার দিতেন; কিন্তু সহযাত্রীর কথা পড়তে পড়তে এটাও মনে হল যে, সহকারীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে যা দেখেছেন, যে ভাবে দেখেছেন, তা ডিরেক্টরের চেয়ার থেকে সম্ভব হত না। মেঘে ঢাকা তারা-র শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি পাহাড়, দেখি বিধ্বস্ত, মৃত্যুপথযাত্রী নায়িকাকে, শুনি সেই অবিস্মরণীয় আর্তনাদ, “দাদা, আমি বাঁচতে চাই!” পুনুয়েল এ দৃশ্যের যে অসামান্য জন্মবৃত্তান্ত দিয়েছেন তা ফাঁস করে দিয়ে পাঠকের মজা মাটি করব না, কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যমের সহজাত কিছু বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে সিসাকে কী ভাবে সোনা করা সম্ভব, তার এমন সরস বিবরণ দিতে গেলে সিনেমার টেকনিক্যাল দিকটাও যেমন বুঝতে হবে, তেমনই আবার পরিচালকের মতো দৃশ্যকল্পনায় মগ্ন হয়ে পড়লে জালিয়াতির উদ্ভট, কৌতুককর দিকগুলো চোখে পড়বে না।
ঋত্বিকের শৈল্পিক প্রতিভার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও পুনুবাবু কিন্তু পরিচালকের অগোছালো স্বভাব, আর ক্রমবর্ধমান পানাসক্তির সঙ্গে বেশি দিন যুঝতে পারেননি। চলে গিয়েছিলেন তরুণ মজুমদারের সহকারী হয়ে। তরুণ, মৃণাল, রাজেন এবং অন্য অনেকেই তাঁর স্মৃতিচারণে স্থান পেলেও পুরো বই আলো করে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর কর্মপদ্ধতি, কাজ করার সময় সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর আচরণ, ছবির ‘কন্টিনিউটি’র উপর তাঁর অবিশ্বাস্য দখল (গুপী গাইন বাঘা বাইন সম্পাদনার সময় কানের দুল নিয়ে একটা কথোপকথন পড়ে গায়ে কাঁটা দেয়), চিড়িয়াখানা-র শুটিংয়ে ছদ্মবেশী উত্তমের পিছনে শিয়ালদহের ফুটপাতে ক্যামেরা হাতে সত্যজিতের দৌড় (এবং লাফিয়ে ট্রামে উঠে কনডাক্টরের ধমক খাওয়া), জন অরণ্য-র বড়বাজারের শুটিংয়ে ভিড় সামলানোর জন্য আলাদা একটা মেকি শুটিংয়ের ব্যবস্থা করা— এ রকম অগুনতি মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে এ বইয়ে। সত্যজিতের ছবি কেমন ভাবে তৈরি হয়ে উঠত, ইউনিটের সদস্যদের প্রতি তাঁর কতটা মায়া ছিল (ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের টাকা হাতে পেয়ে কী করেছিলেন, সেটা পাঠক যেন লক্ষ করেন), সরকারি প্রযোজনার ক্ষেত্রেও কত দৃঢ় হাতে খরচ নিয়ন্ত্রণ রাখতেন (গণশত্রু-তে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়কে নেওয়ার আসল কারণ জেনে বিস্মিত হলাম), এ সব (এবং আরও অনেক কিছু) জানতে আগ্রহী হলে সত্যজিৎ-সম্বন্ধীয় যত বই, যত সাক্ষাৎকারই পড়ে থাকুন না কেন, সহযাত্রীর কথা না পড়লে পস্তাবেন।
কথক যতই ভাল হোন না কেন, মৌখিক আখ্যানের সুসংবদ্ধ গদ্যরূপ দেওয়াটা সহজ নয়। জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিপুণ অনুলিখন পুনু সেনের স্মৃতিকথার মূল্য বিপুল ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। সতর্ক, শ্রদ্ধাশীল অনুলিখন ছাড়াও সম্পাদক অশেষ পরিশ্রম করেছেন পাঠকের সুবিধার্থে। সব স্মৃতিকথার মতোই এখানেও বহু অসম্পূর্ণ নাম ও স্বল্প-পরিচিত ঘটনার উল্লেখ এসেছে, এবং তাদের প্রত্যেকটির তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে টীকায়। পুনু সেন যে সব ছবিতে কাজ করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ তালিকাও রয়েছে। এ ধরনের তথ্য জোগাড় করা যে কতটা কঠিন, তা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে সামান্যতম চর্চা করলেই মালুম হয়। পুনু সেন এ বই দেখে যেতে পারলেন না বলে জাগরী আক্ষেপ করেছেন। সে আক্ষেপ আমারও হচ্ছে। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের উজ্জ্বলতম যুগের অক্লান্ত এক কর্মীর স্মৃতিচিত্র যে এত যত্ন, এত ভালবাসার সঙ্গে রক্ষিত হল, তাতে আনন্দও কম হচ্ছে না।







