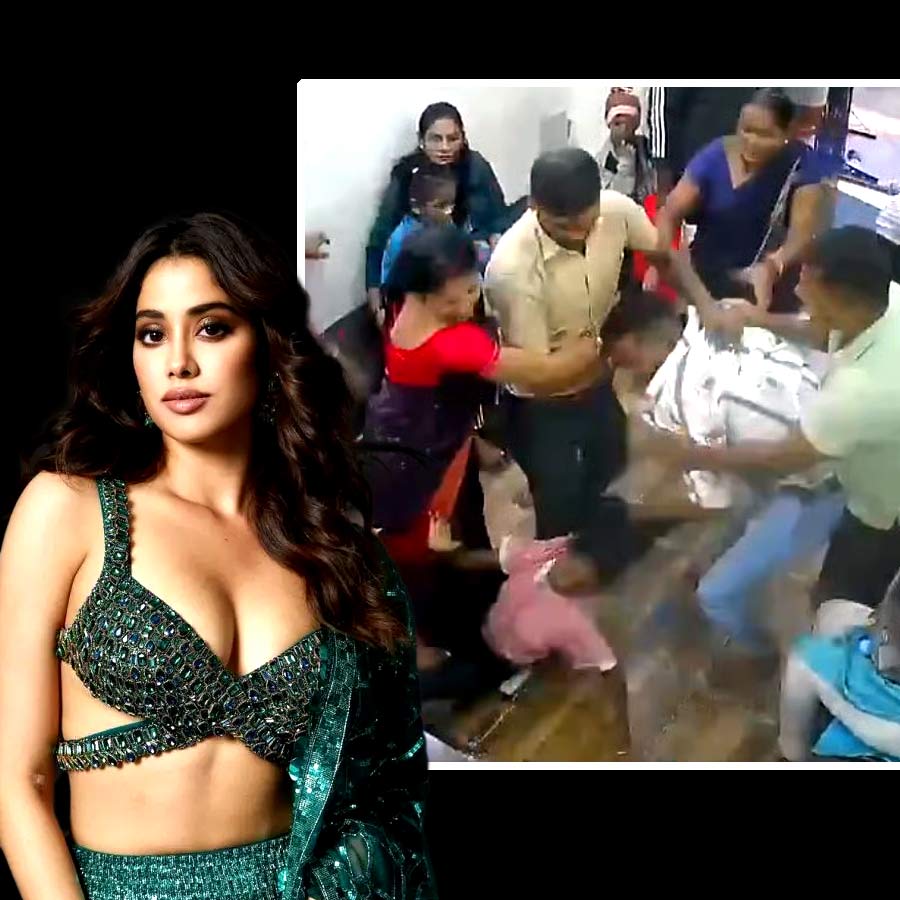পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়াতে বিশাল ধূপখোলা মাঠ। সেই মাঠে অতি ভোরে একত্রিত হবে সবাই। পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি। বুকের কাছে আঁটাথাকবে কালো এক টুকরো ফিতে। পায়ে জুতো-স্যান্ডেল থাকবে না। খালি পায়ে সার ধরে দাঁড়াবে সবাই। সামনের সারিতে থাকবেন বড়রা। তাঁরা কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও আছেন। কাপড়ের লম্বা ব্যানারে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে ‘অমর একুশে ফেব্রুয়ারি’। এক-দেড়শো বা দু’শো জন মানুষ। আমরা ছোটরা থাকব মাঝের সারিতে। গেন্ডারিয়া থেকে খালিপায়ে মিছিল করে যাব রমনা এলাকায়। সেখানে শহিদ মিনার। শহিদ মিনারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। প্রত্যেকের কণ্ঠে থাকবে একুশের অমর গান, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...’
সেই প্রভাতফেরির কথা আজও মনে পড়ে। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ১৯৬৭ সাল। লোহারপুল পেরিয়ে, লক্ষ্মীবাজার, রায়সাহেব বাজার, নবাবপুর হয়ে গুলিস্তান। পশ্চিমের রাস্তা ধরে কার্জন হলের পাশ দিয়ে চলে যাব শহিদ মিনারে। ঢাকা শহরের প্রত্যেক পাড়া-মহল্লা থেকে আমাদের মতোই মিছিল করে দলের পর দল আসছে। প্রত্যেকের কণ্ঠে ওই গান। বিনম্র শ্রদ্ধায় লাইন ধরে সুশৃঙ্খল ভঙ্গিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবে। ফুলে-ফুলে ভরে উঠবে শহিদ মিনার। চার দিকে শুধুই মানুষ। শুধুই ব্যানার। শহিদ মিনারের আশপাশে অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়া ও পলাশের গাছ। সেই সব গাছে থোকায় থোকায় ফুটেছে লাল ফুল। যেন আগুন লেগেছে গাছগুলোয়। প্রতিবাদের আগুন। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটি ছিল বাংলার ৮ ফাল্গুন। একটি ব্যানারে দেখি, লাল হরফে লেখা ‘ফাগুনে আগুন জ্বলে’।
‘উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’— জিন্নার এই সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিয়ে চায়!’ কী গভীর আবেগ এই দিনটি ঘিরে। দেশের প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধায় এই দিনে স্মরণ করে ভাষা-শহিদদের। কত আয়োজন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয় নানা আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা সেই অমর গানটি দিয়ে। ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে গানটি রচনা করেছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। শুরুতে এই গানের সুর করেছিলেন আবদুল লতিফ। প্রথম দিকে তাঁর সুরের গানটিই গাওয়া হত। পরে নতুন করে সুরারোপ করেন আলতাফ মাহমুদ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আলতাফ মাহমুদকে হত্যা করে পাকিস্তানিরা।
একুশের ঘটনার পর পরই চট্টগ্রামবাসী তখনকার তরুণ কবি মাহাবুব উল আলম চৌধুরী খুবই উদ্দীপনামূলক একটি কবিতা লেখেন। ঢাকায় গুলি চালানোর খবর একুশে ফেব্রুয়ারির বিকেলেই চট্টগ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। কবি জ্বরগ্রস্ত। জ্বরের ঘোরে তিনি রচনা করলেন একুশের প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’। সতেরো পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতা। সেই কবিতার পুরোটা বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। কবির কাছেও ছিল না। তাঁর স্মৃতি থেকে কিছুটা অংশ ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর এক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটি রচনার পর কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসে তা ছাপানো হয়। শেষ রাতে সেই প্রেসে পুলিশ হামলা চালায়। প্রেসের কর্মীরা কম্পোজ় করা ম্যাটার ভেঙে ফেলেন। তত ক্ষণে পনেরো হাজার কপি ছাপা হয়ে গেছে। ২২ ফেব্রুয়ারি লালদিঘির ময়দানের বিশাল জনসভায় কাব্যপুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুনর রশীদ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। মুসলিম লীগ সরকার পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৫৪ সালে কবির বাড়ি সার্চ করে যে কয়েকটি কপি পাওয়া গিয়েছিল, তা-ও পুলিশ নিয়ে যায়। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন এই রকম,
‘যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে হত্যা করেছে,
যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময়ভাষায় অভ্যস্ত
মাতৃসম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে
আমার এইসব ভাইবোনদের হত্যা করেছে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।’
এই সব তথ্য পাওয়া যায় হায়াৎ মামুদের ‘অমর একুশে’ গ্রন্থে।
১৯৫২-র ২৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার নির্মিত শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কবি ও কথাসাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ শিরোনামে কবিতা লিখলেন তিনি।
‘ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কী বন্ধু, দেখ একবারআমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার।’
ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ঘিরে শুরু হয়েছিল মানুষের গভীর আবেগ ও ভালবাসা। ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সালাম রফিক বরকত জব্বার, এই শহিদদের নাম মানুষের মুখে মুখে। তাঁরা জাতীয় বীর। তাঁদের প্রতি ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রত্যেক পাড়া-মহল্লা থেকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার থেকে, ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ছোট-বড় অসংখ্য সঙ্কলন প্রকাশিত হত। কত প্রতিষ্ঠিত, তরুণ ও নবীন কবির লেখা সেই সব সঙ্কলনে। সঙ্কলন ঘিরে নবীন কবি-লেখকদের সাহিত্যচর্চার আয়োজন। শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেই সব সঙ্কলন নিয়ে আসতেন শহিদ মিনারে। সঙ্কলনগুলোর কোনও মূল্য নির্ধারণ করা থাকত না। টিনের মুখবন্ধ কৌটো থাকত বিক্রেতাদের হাতে। গভীর আগ্রহে সঙ্কলন হাতে নিচ্ছেন ভাষাপ্রেমী মানুষ। যাঁর যেটুকু সামর্থ্য, সেইটুকু পয়সাই ফেলে দিচ্ছেন টিনের কৌটোয়। কৌটোগুলোর ঢাকনা ঝালাই করা। ঢাকনার মাঝখানটায় শিশুদের মাটির ব্যাঙ্কের মতো মুখ কাটা। স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক বছর ওই ধরনের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। তার পর ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আর ওই রকম সঙ্কলন প্রকাশিত হয় না। প্রভাতফেরিও আগের মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে হয় না। দিনে দিনে ভাষা দিবসটি অন্য চেহারা নিয়েছে।
এখন ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকেই ভাষা-শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে ব্যাপক আয়োজন হয় জাতীয় শহিদ মিনারে। যে পূর্ব বাংলায় ১৯৫২ সাল নাগাদ জনসংখ্যা ছিল চার কোটি, এখন শুধু ঢাকাতেই বসবাস করে প্রায় দুই কোটি মানুষ। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি এখন জাতীয় উৎসবের অংশ। হয়েছে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। রমনা এলাকায় ২১ ফেব্রুয়ারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন। বাংলা একাডেমি আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল একটি অংশ নিয়ে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজন করা হয় ভাষা-শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে বইমেলা। এই উপলক্ষে চার-পাঁচ হাজার বই প্রকাশিত হয় প্রতি বছর। পনেরো-ষোলো কোটি টাকার বই বিক্রি হয়ে যায় এক মাসে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৈরি করা হয়েছে শহিদ মিনার। যেন এই মিনারের দিকে তাকিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনই স্মরণ করতে পারে ভাষা-শহিদদের। ভালবাসতে শেখে প্রিয় বাংলা ভাষাটিকে।
সেই প্রভাতফেরির কথা আজও আমার মনে আছে। শহিদ মিনারের সামনে গিয়ে প্রথম দাঁড়ানোর কথা মনে আছে। গাছে গাছে কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ ফুটেছে। হাজার হাজার মানুষ শহিদ মিনারে। মিছিলের পর মিছিল আসছে। প্রত্যেকের কণ্ঠে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’। আমি শিহরিত হচ্ছি। দিনে দিনে দিন গেছে। ফেব্রুয়ারি এলেই রক্তে দোলা লাগে। শহিদ মিনারে যাই। আর ধীরে ধীরে জানার চেষ্টা করি কী ঘটেছিল ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে। কত কবিতা গল্প লেখা হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে। আমাদের বড় কবিরা প্রত্যেকেই লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস লিখলেন জহির রায়হান, ‘আরেক ফাল্গুন’। কত গল্প লেখা হল। প্রবন্ধ লেখা হল। গবেষণা হল কত। ভাষা আন্দোলন নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করলেন বদরুদ্দীন উমর। তিন পর্বে লিখলেন ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’। এ এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। ভাষা আন্দোলন ও তখনকার রাজনীতি নিয়ে এত বড় কাজ আর কেউ করেননি। বদরুদ্দীন উমরের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ‘ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল’। দুই পর্বের এই গ্রন্থটিরও কোনও তুলনা হয় না। বশীর আল হেলাল রচনা করলেন ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’। বিশালায়তন গ্রন্থ। এ ছাড়া আরও অনেক লেখক গবেষক ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের ভিতর আমি ঢুকে যাচ্ছিলাম। অগ্রজদের কাছ থেকে সেই আন্দোলনের কথা শুনি। শুনি আর রক্তে দোলা লাগে। গল্প কবিতা উপন্যাস পড়ি। পড়ি, আর উদ্বেলিত হই।
হাকিম মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নব্বই দশকের গোড়ার দিকে। এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি তাদের গ্রামের বাড়িতে। ভারী সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্রের সরু একটি শাখা। নদীতীরে প্রাচীন বটগাছ। বাজার। সুন্দর একটা হাই স্কুল আছে। সেই স্কুলের হেডমাস্টার আবদুল হাকিম সাহেব। আমি লেখালিখি করি শুনে দেখা করতে এসেছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র সজ্জন মানুষ। চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রবল। সৎ, সাহসী, নির্ভীক। সত্যের পথ থেকে এক পা সরেন না। কিছু দিন আগে এই গ্রামে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছিল। কদম নামে অসহায় এক যুবক আছে গ্রামে। এক সময় সচ্ছল গৃহস্থ ছিল তার বাবা। মা-বাবা দু’জনেই মারা গেছে। সামান্য জায়গা-সম্পত্তি যা ছিল, চাচারা জবরদখল করেছে। কদমের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। গ্রামের এ বাড়ি সে বাড়ির গোয়ালে কিংবা খড়ের গাদায় ঘুমোয়। চেয়েচিন্তে খায়। প্রায়ই চুরি করে। অন্য কিছু নয়, চুরি করে খাবার। বিভিন্ন বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে চুরি করে খেয়ে আসে। অনেক দিন ধরেই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের গৃহস্থ খুবই বিরক্ত। চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দিয়েছে। কদমকে ধরে আনা হয়েছে চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বকুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বিচারে সাব্যস্ত হল, কদমের জিভের ডগাটা কেটে দেওয়া হবে। এ হচ্ছে তার চুরি করে খাওয়ার শাস্তি। হাকিম মাস্টার সে দিন অসুস্থ। কদমের জিভ কেটে দেওয়া হবে শুনে অসুস্থ শরীর নিয়েই চেয়ারম্যানের বাড়িতে এলেন। খাবার চুরির অপরাধে এক জন মানুষের জিভ কাটা হবে, এ তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন না। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, “যে ভাষার জন্য আমরা লড়াই করেছি, বুকের রক্ত দিয়েছি, আজ স্বাধীন বাংলাদেশে আমরাই এক জন মানুষের ভাষা কেড়ে নিচ্ছি? জিভ কেটে দিলে কদম কথা বলতে পারবে না। গ্রামের এতগুলো মানুষ এক জন মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না, এটাই তো বড় লজ্জার ঘটনা। তার ওপর জিভ কেটে দিয়ে তার ভাষাটাও কেড়ে নেব? এর চেয়ে বড় অন্যায় হতে পারে না।” কদমকে বাঁচালেন তিনি।
১৯৫২ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আইএ পড়েন হাকিম মাস্টার। বিশ-একুশ বছর বয়স। সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ও তার আগে পরের কয়েকটি দিনের অনুপুঙ্খ বিবরণ শুনেছিলাম আমি। পরে বদরুদ্দীন উমর সাহেবের ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড পড়ে দেখি, হাকিম সাহেবের মুখে শোনা সব কথাই প্রায় মিলে যায়। ড. আনিসুজ্জামানের লেখায়ও পাই একই ইতিহাস।
১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাংলায় শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদ্দীন ছাত্রদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করলেন ১৯৫২ সালে। ঢাকার পল্টন ময়দানে ২৭ জানুয়ারি এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।” তখন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই বক্তব্যের ফলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয় ধর্মঘট। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরির সম্মেলনকক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। সভায় সভাপতিত্ব করেন জননেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ -এর সিদ্ধান্তে সারা দেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় ৪ ফেব্রুয়ারি। পতাকা দিবস উদ্যাপিত হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। ফলে আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি হতে থাকে। দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিটি জেলা শহরে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। এল ২১ ফেব্রুয়ারি। সে দিন ‘পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ’ এর অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মূল ভবনে। এ দিকে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে ঢাকা শহরে। মিছিল নিয়ে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ব্যবস্থাপক পরিষদে গিয়ে স্পিকারের কাছে স্মারকপত্র পেশ করার কর্মসূচি নেয়। কর্মসূচি যাতে সফল না হয়, সেই কারণে আগের দিন, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কোনও জায়গায় পাঁচ জন বা তারও বেশি মানুষের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে কী করা হবে সেই উদ্দেশ্যে ওই রাতেই সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় আবুল হাশিমের নেতৃত্বে। পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের পরও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয় সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত না হলে সংগ্রাম পরিষদ আপনা আপনিই ভেঙে যাবে।
সেই রাতেই ফজলুল হক মুসলিম হলের পুকুরপাড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় ছাত্র-জনতার সভা অনুষ্ঠিত হয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে। আবদুল মতিন ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর আহ্বায়ক। তিনি প্রস্তাব করেন, দশ জনের এক-একটি দল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে যাত্রা করবে। ১৪৪ ধারা ভাঙবে। এ ভাবে কয়েকটি দল রাস্তায় নামে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কলা ভবনের সামনে লাঠি চার্জ শুরু করে। ছাত্ররা পুলিশদের লক্ষ করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ছাত্র-জনতা কলা ভবন ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাঝখানকার লোহার পাঁচিল ভেঙে ফেলে। হাসপাতাল প্রাঙ্গণ ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-হস্টেল এলাকায় অবস্থান নেয়। এই হস্টেলের অদূরেই ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাস্থল। ছাত্র-জনতা এক সময় হস্টেলের গেট পেরোনোর চেষ্টা করে। বেলা তিনটে নাগাদ পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন রফিকউদ্দীন আহমদ, আব্দুল জব্বার ও আবুল বরকত। আহত হন অনেকেই। আহতদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করেন আবদুস সালাম।
তার পর আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হস্টেল। ২৩ ফেব্রুয়ারি নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলেন, শহিদদের স্মরণে একটি মিনার স্থাপন করবেন। প্রথম যে স্থানটিতে শহিদদের রক্ত ঝরেছিল, ১২ নম্বর ব্যারাকের কাছে, সেখানেই হবে মিনার। মিনারের নকশা করলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বদরুল আলম। তাঁদেরকে নির্মাণ সামগ্রী দিলেন পিয়ারু সরদার। ২৪ তারিখে শহিদ সফিউর রহমানের পিতা মাহাবুবুর রহমান মিনার উদ্বোধন করেন। ২৫ তারিখে আবার মিনারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ‘দৈনিক আজাদ’ পত্রিকার সম্পাদক ও সাহিত্যিক আবুল কামাল শামসুদ্দীন। তিনি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। তার পরও ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তিনি সেই দিনই ‘পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ’-এর সদস্য পদ ত্যাগ করেছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে এই শহিদ মিনার ভেঙে ফেলে পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী। তার পর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে সেটিও ভেঙে ফেলা হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের আগের সেই জায়গাতেই আর একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালে শুরু হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণ। এই শহিদ মিনারের নকশা করেন ভাস্কর হামিদুর রহমান। তাঁর রূপকল্পনায় আনতমস্তক মায়ের প্রতীক কাঠামোর মাঝখানে দু’পাশে সন্তানের প্রতীক দুটো করে কাঠামো। সামনে বাঁধানো বড় চত্বর। এই আমাদের জাতীয় শহিদ মিনার। ১৯৭১-এ পাকিস্তানিরা আমাদের এই প্রাণের মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর আবার তা নির্মিত হয়। দেশের যাবতীয় লড়াই আন্দোলন ও দাবি আদায়ের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই শহিদ মিনার। এখান থেকেই শুরু হয় যাবতীয় আন্দোলন সংগ্রাম। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। বন্ধ হয়ে যায় শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ।

ভাষার দাবিতে সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রধান ও অপ্রধান ছাপ্পান্নটি অঞ্চলে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর ‘ভাষা আন্দোলন, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া’ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন আহমদ রফিক। ১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ কুমিল্লায় ‘পূর্ববঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন’-এ সভাপতির ভাষণে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, “বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব।” বদরুদ্দীন উমর তাঁর ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন, “১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল না। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাঙলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার পাকিস্তানী শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন।”
আহমদ রফিক তাঁর ‘ভাষা আন্দোলন; টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া’ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, “পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ থেকে একাধিক পর্বে বিস্তার লাভ করে। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে তা বিস্ফোরক হয়ে ওঠে ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন বিশেষ বিশেষ কারণে ‘মহান একুশে’ নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রথমত এ পর্বের আন্দোলনের চরিত্র ছিল তীব্র প্রতিবাদী, সেই সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তও। এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রতিবাদের সূচনা ঘটিয়েছে, কোথাও কোথাও দাবানল সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে জনতার অংশগ্রহণ।”
হাসান আজিজুল হক তাঁর ‘একুশের ভাষা আন্দোলন’ প্রবন্ধে লেখেন, “বাংলাভাষার ওপর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় বদল ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা অনুকূল ও মুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করাই যে পাকিস্তান শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরেই কিন্তু আমরা খেয়াল করি, ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে জনসাধারণ নয়, ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই ছিল। জনসাধারণের নেতৃত্ব বলতে সাড়ে চার কোটি মানুষের শারীরিক নেতৃত্ব বোঝানো হচ্ছে না। আসলে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তুই আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। ভাষা আন্দোলনের যেসব লক্ষ্য স্থির হয়েছিল, তা সমাজের ওপর-কাঠামোর সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল— আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নয়।”
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থটির নাম ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’। এই গ্রন্থের ‘একুশে ফেব্রুয়ারির উত্তাপ ও গতি’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন, “২১শে ফেব্রুয়ারি গোটা জনগোষ্ঠীকে উদ্ধুদ্ধ করল একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের দিকে, ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদের অনুভব করতে লাগল একটি জাতি হিসাবে কিংবা জাতি হিসাবে নিজেদের পরিচয়-অনুসন্ধানে নিয়োজিত হল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতিরোধ, হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আপোস করে সম্ভব নয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি যে-প্রতিরোধের স্পৃহার জন্ম দিল, দিনে-দিনে ঐ দিনটি উদ্যাপনের সঙ্গে তাই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল।”
ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটিকে আমরা বলি ‘মহান একুশে’। দিনটি শোকের। যে কারণে ‘শহিদ দিবস’। দিনটি আমাদের চেতনা জাগ্রত করার দিন। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি তৈরি হয় এই দিনের স্মৃতিতে। ভাষা আন্দোলনই এ দেশের প্রথম বৃহত্তর আন্দোলন, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি প্রতিবাদী হতে। শিখেছি কী ভাবে অধিকার আদায় করে নিতে হয়, কী ভাবে জাতির স্বার্থে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে। একুশ আমাদের জীবনের প্রধান শিক্ষক। জাতীয় শহিদ মিনার সেই শিক্ষার পীঠস্থান। আমরা বলি, বাংলা ভাষা রক্ত দিয়ে পাওয়া ভাষা। ভাষার প্রতি ভালবাসা থেকেই কালক্রমে বহু আন্দোলন ও লড়াই। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলানোর মূলমন্ত্র আমরা পাই ভাষা আন্দোলনের ওই দিনটি থেকেই। সেই অর্থে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পরবর্তী কালের যাবতীয় আন্দোলনের বীজ হিসেবে কাজ করেছে। যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষে রূপ নিয়েছে। ডালপালা ছড়িয়ে মহীরুহ হয়েছে কালে কালে। সেই মহীরুহের নাম বাংলাদেশ।
শামসুর রাহমান তাঁর কবিতা ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ কবিতায় লেখেন,
“তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে,কী থাকে আমার?
উনিশশো’ বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছ সগৌরবে মহীয়সী।”
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সেই কবে তাঁর ‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতায় লিখলেন,
“মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা, তাই কি হয়?”
আবেগ আমাদের জাতির বড় সম্পদ। সেই আবেগে যখন আঘাত করা হয়, তখন আমরা জ্বলে উঠি বিশাল ক্রোধে। ভাষার উপর আক্রমণ করে পাকিস্তানিরা আমাদের আবেগে তীব্র আঘাত করেছিল। পূর্ববঙ্গ হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। রক্তে আগুন লেগেছিল প্রতিটি মানুষের। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম বুক চিতিয়ে। মাথা নত করে নয়, দাঁড়িয়ে ছিলাম মাথা উঁচু করে। মনীষী আবুল ফজল আমাদের এই চেতনার কথাটি একবাক্যে বলে দিলেন, ‘একুশ মানে মাথা নত না করা।’
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)